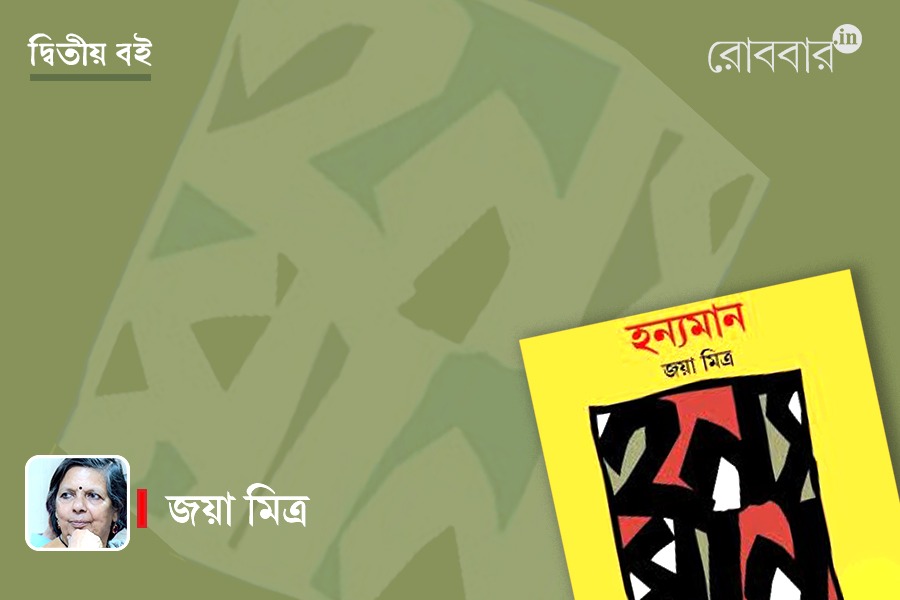
ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে লেখা। চিন্তার মধ্যে চাপ দিচ্ছে লেখার ইচ্ছা, লিখবার তীব্র আবেগ। ততদিনে আমি জেনে গেছি অন্য আর কোনও কারণে নয়, যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি, যা আমি প্রত্যক্ষ জেনেছি, তাকে লিখে ফেলা ছাড়া মুক্তি নেই আমার। আমি যে বেঁচে আছি, চিন্তা করতে পারছি, আমি যে কিছু বলতে চাই তার জন্য, শুধু তার জন্যই লিখতে হবে আমাকে। জেলে যারা বন্দি আছে, তাদের করুণ গল্প লিখতে চাই না। আপাদমস্তক সমস্ত উদ্ভট, অবাস্তব, অর্থহীন সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থানের বিরুদ্ধে লেখক না হয়ে যদি ভূমিকম্প হতে পারতাম কিংবা বজ্রপাতের ক্রোধ, হয়তো হতে চাইতাম তাইই। কিন্তু হায়, এত সীমিত মানুষের ক্ষমতা– ক’টি শব্দই কেবল আছে তার হাতে, তাই তার ক্রোধের উড়াল, তাই-ই তার মুক্তির স্বপ্ন।

দ্বিতীয় বইয়ের নাম ‘হন্যমান’। প্রথম গদ্যের বই। প্রথম বইখানা ছিল কবিতার– ‘উদ্দালক নামে ডাকো’।
জেল থেকে বেরিয়েছি ১৯৭৪। যুদ্ধ থেকে ফেরা ’৭৫। অতঃপর সমাজ, সংসার, পরিবার। ধারাবাহিক ইশকুল থেকে ইশকুলে ব্যক্তিগত শিক্ষালাভ। কোথাও হোঁচট খেয়ে, কোথাও কাঁধ ঘষটে পাশ। ছাত্রজীবন থেকেই অন্যরকম সমাজের খোঁজে চলে যাওয়ার দরুন, প্রায় কোনও ধারণা তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি সাধারণ সামাজিক জীবন সম্পর্কে। ফলে প্রতিদিনই বোঝা, শিক্ষা পাওয়া। নিজেরা দাঁড়াতে হলে যে পায়ের তলায় কোনও নিজস্ব জমির দরকার হয়, সেই আবশ্যিক শর্ত শেখা। পরিচিতরাও যে ঠকাতে পারে, বন্ধুরাও বলতে পারে মিথ্যে কথা, ২৪-২৫ বছরের দুই অনভিজ্ঞ যাত্রীর দুর্বল বা অসহায় অবস্থার সুযোগ নেওয়া যে মোটেই আশ্চর্যের কিছু নয়– এই সব শিক্ষায় ভরতে লাগল অভিজ্ঞতার ঝুলি।
১৯৭৭-এ জরুরি অবস্থার নিরসনে দিল্লিতে জনতা সরকার এলে চাকরি জুটল। কিন্তু তখনও নিজের ভিতরে চলে নিরন্তর ভাঙচুর। জীবিকাক্ষেত্রে চারপাশ দেখে মনে হয়, সবকিছুই যেন একেবারে ঠিক আছে, যেন কোনও রক্তচিহ্নই নেই এই উন্নতিচিহ্নময় অবস্থার চাদরের নিচে। সমস্ত সময় ধরে চলে নিজেকে একটা খাপে ধরানোর চেষ্টায় ভেতরে ভেতরে নিজেকে নানারকম ভাবে ভাঙা। শর্তমতো চাকরিতে যাই, সংসার গোছানোর অনভ্যস্ত চেষ্টা করি, চলে একেবারে ছোট শিশুটিকে নিয়ে নানা রকম আপদবিপদ পার করা। অথচ প্রতিদিন প্রতি প্রহর পুড়ে যেতে থাকে অন্য দহনে। একদিকে নানারকম জটিলতার ভাঙনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া, হারিয়ে ফেলা যুদ্ধের সঙ্গীদের জন্য যন্ত্রণা অন্যদিকে যাদের রেখে এসেছি জেল প্রাচীরের ওপারে, সেই ভাঙাচোরা সাথীসঙ্গিনীদের, আপনজনেদের ভাবনা জেগে থাকে সারাক্ষণ। খাটে পাতা পরিষ্কার বিছানায় শুতে ইচ্ছে করে না, খাবার পাতে নিজেই বেড়ে নেওয়া আস্ত একটা ডিম যেন একজন দলত্যাগী সুবিধাপাওয়া ভুলে-যাওয়া লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও সেই উঠোনে ঝোপঝাড় ভরা বাড়ি পরিষ্কার করার জন্যও সহ্য করতে পারি না ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, যা জেলখানায় রক্তের গন্ধ ঢাকার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
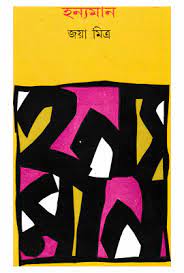
………………………………………..
বাইরে যত বাড়ছে নিত্যদিনের অভ্যস্ত হওয়ার চাপ, ততই নিজের ভেতরে স্মৃতিকে সর্বক্ষণ ছুঁয়ে থাকা, যেন আরও বেশি করে বাস করতে চাইছি তারই মধ্যে। স্কুলের চারিপাশের জনবসতিতে সাঁওতাল মানুষদের গ্রাম, তাদের মুখ মিশে যায় ছেড়ে আসা কত মুখের সঙ্গে। বেশি করে মনে হয়– এমনিই কি ছিল পানমণিদের গ্রাম? এমন কোনওখানে বুধার বসতি ছিল? রিকশাওয়ালা, রাজমিস্ত্রি, বাজারের মাটিতে বসা তরকারিওয়ালিদের মুখ দেখি। এদের বাড়ির কেউ? গ্রামের কেউ? অনেক সাঁওতাল মেয়ে পড়ে আমার স্কুলে কিন্তু দেখি তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে না আর। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওদের গ্রাম থেকেও কি কোনও মেয়ে-পুরুষ জেলে বন্ধ থেকেছে কখনও?
………………………………………..
এইসব সময়ে কিন্তু কখনও কারও সঙ্গেই করি না জেলখানার গল্প। সঙ্গে বাস করা মানুষটির সঙ্গেও না করারই মতো। কখনও কোনও প্রসঙ্গে উল্লেখ এলেও এড়িয়ে যাই। সেই মাত্র দু’-তিন বছর পরেও ঘা বড় বেশি কাঁচা। যেন ছুঁয়ে গেলে রক্ত পড়ে। সমস্ত বাস্তবতার নিচে বয়ে চলে অন্য এক জীবনযাপন। লেখার কথা ভাবিও না কখনও।
বাইরে যত বাড়ছে নিত্যদিনের অভ্যস্ত হওয়ার চাপ, ততই নিজের ভেতরে স্মৃতিকে সর্বক্ষণ ছুঁয়ে থাকা, যেন আরও বেশি করে বাস করতে চাইছি তারই মধ্যে। স্কুলের চারিপাশের জনবসতিতে সাঁওতাল মানুষদের গ্রাম, তাদের মুখ মিশে যায় ছেড়ে আসা কত মুখের সঙ্গে। বেশি করে মনে হয়– এমনিই কি ছিল পানমণিদের গ্রাম? এমন কোনওখানে বুধার বসতি ছিল? রিকশাওয়ালা, রাজমিস্ত্রি, বাজারের মাটিতে বসা তরকারিওয়ালিদের মুখ দেখি। এদের বাড়ির কেউ? গ্রামের কেউ? অনেক সাঁওতাল মেয়ে পড়ে আমার স্কুলে কিন্তু দেখি তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে না আর। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওদের গ্রাম থেকেও কি কোনও মেয়ে-পুরুষ জেলে বন্ধ থেকেছে কখনও? একেবারে বি-জন সুদূর নিষ্ঠুর কারাগারে? স্কুলের উৎসবে রবীন্দ্রসংগীত গায় ওরা সকলে, জিজ্ঞেস করে দেখি নিজেদের গান গাইতে লজ্জা পায়। একবার কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে এসে ঘুরে গেল জেলের সাথী কৃষ্ণা। কয়েক দিন আমরা কেবলই ভাগ করলাম রেখে আসা মেয়েদের স্মৃতি। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যেন শক্ত করে বন্ধ দরজার আগল খুলল কোথাও। কৃষ্ণা বলল, ও ভাবছে জেলখানা নিয়ে লেখার কথা। ততদিনে স্কুলে দু’-একজন খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেন,
–কেমন করে রাখত জেলে? খুব কষ্ট দিত? একটু একটু করে মাথার মধ্যে ঘনিয়ে উঠছে লেখা। কখনও গদ্য লিখিনি আগে। কিন্তু যে কথাগুলি তৈরি হচ্ছে, কবিতায় তাদের ধরানোর ভাষা আমি জানি না। বছরখানেকের মাথায় প্রথম বসা কাগজকলম নিয়ে। কেমন করে লিখব, কোথা থেকে শুরু করব, সেই সমস্যা। কারও প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত নিজেদের কথাই বলি, হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু যে কথা, যাদের কথা লিখতে চাইছি, সে কথা বলতে যে চোখ ফেটে রক্ত গড়িয়ে আসে। সেই শব্দ আমি কোথায় পাব?
ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে লেখা। চিন্তার মধ্যে চাপ দিচ্ছে লেখার ইচ্ছা, লিখবার তীব্র আবেগ। ততদিনে আমি জেনে গিয়েছি, অন্য আর কোনও কারণে নয়, যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি, যা আমি প্রত্যক্ষ জেনেছি, তাকে লিখে ফেলা ছাড়া মুক্তি নেই আমার। আমি যে বেঁচে আছি, চিন্তা করতে পারছি, আমি যে কিছু বলতে চাই তার জন্য, শুধু তার জন্যই লিখতে হবে আমাকে। জেলে যারা বন্দি আছে, তাদের করুণ গল্প লিখতে চাই না। আপাদমস্তক সমস্ত উদ্ভট, অবাস্তব, অর্থহীন সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থানের বিরুদ্ধে লেখক না হয়ে যদি ভূমিকম্প হতে পারতাম কিংবা বজ্রপাতের ক্রোধ, হয়তো হতে চাইতাম তাই-ই। কিন্তু হায়, এত সীমিত মানুষের ক্ষমতা– ক’টি শব্দই কেবল আছে তার হাতে, তাই তার ক্রোধের উড়াল, তাই-ই তার মুক্তির স্বপ্ন। অথচ এই ঘনিয়ে ওঠা সত্ত্বেও ঘটছে না সেই বিস্ফোরণ, যা লেখার ক্রিয়াটিকে শুরু করিয়ে দেবে। কার কথা লিখব কাকে বাদ দিয়ে? কতখানি? প্রতিজনের দুঃখের বোঝা আলাদা আলাদা, যা সে একা বহন করে, কিন্তু যে পড়বে তার কাছে কি পৌঁছবে সব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত যন্ত্রণা একটি বেদনার মহানদী হয়ে?
এসবেরই মধ্যে একদিন, যেমন লোকে বলে, উটের কাঁধে শেষ খড়টি পড়ল। চোখে পড়ল কোন জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট। এমন ঘটনার কথা রোজ বেরয় কাগজে। অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রাম থেকে মেয়েদের আকর্ষণীয় শর্তে সামুদ্রিক চিংড়িমাছ ছাড়িয়ে টিনে ভরার কাজ দিয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা– রত্নগিরিতে, আরও কোথায় কোথায়! অন্ধ্রের মেয়েদের হাত নাকি খুব নরম, মাছ ভাঙে না। গ্রাম ছেড়ে দূরদেশে পৌঁছনোর দু’দিনের মধ্যেই মেয়েরা বুঝতে পারে চিংড়ি নামেমাত্র, আসলে তাদের ছাড়াতে হবে ছুরির মতো ধারওয়ালা ক্যাটল ফিশের খোলা আর কাঁটা। কাজের সময় রাত্রি তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা। লবণাক্ত ভেজা বালিতে লম্বা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটানা কাজ করা। দুপুরে খাবার ছুটি নেই। সামুদ্রিক জাহাজ মাছ এনে ফেলতে থাকে বালিতে, সেখান থেকে সরাসরি এই মেয়েদের টেবিলে আসে সেগুলো। প্রথম কি দ্বিতীয় দিনেই কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় আঙুল। ‘রাত্রে ঝোপড়িতে ফিরে ঘাটাসিদ্ধ খেয়ে আমরা ঘুমাতে পারি না, হলুদজলে হাত ডুবিয়ে বসে আঙুলের যন্ত্রণায় সারারাত কাঁদি।’ অথচ তখন চলে যাওয়া যায় না, এক বছর কাজ করার শর্তে টিপছাপ দিয়ে এসেছে। কবে যেন চা বাগানের কুলিদের আসাম কি তরাই পৌঁছে দিয়ে রেললাইন তুলে ফেলে দিত! এই ১৯৮৭ সাল! আর, পরদিন সকালে দূরদর্শনের পর্দায় ফ্লানেল বোর্ড তৈরি করতে শেখাচ্ছে দু’টি হাত। নরম, ফরসা, বাহারি। নরম হাত, ‘মাছ’-এর শক্ত খোলা-কানকোয় ছিঁড়ে যাওয়া হাত, হলুদগোলা জলে ডুবিয়ে রাখা হাতের পাশে টুপিয়ে পড়া চোখের জল। মাথার মধ্যে, অনেক দিন পরে, আবার যেন কিছু ছিঁড়ে ফেটে যায়। সারাদিন ছন্নের মতো গুম হয়ে থেকে সেদিন অনেক রাত্রে লিখতে বসি। মানুষকে মানুষের জেনেবুঝে যন্ত্রণা দেওয়ার কথা, সহ্য করার কথা, চেতনাহীন বন্দিশালার অনির্দিষ্ট দেওয়ালের কথা, বেঁচে থাকার বুক ফেটে যাওয়া উপকথা।
শুরুর পর্যায়ে এই লেখা ছিল ক্রোধে বিদ্রুপে তীক্ষ্ণ, কান্না চাপার জন্য ব্যঙ্গে তির্যক। তখনও নিঃসম্পর্কিত ভাবে ছড়িয়ে বলতে পারছি না– বহরমপুর পর্যায় শেষ হয়ে গেল ২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে। দু’-একজনকে পড়ে শোনাই ’৮৬-’৮৭ সালের সেই ঠাসা খসড়া। কেউ বলেন, এই লেখা ছাপলে আবার পুলিশের ঝামেলায় পড়বে, কেউ বা উৎসাহ দেন। মাঝে মাঝেই বসি লেখাটা নিয়ে। লিখি হয়তো দু’চার লাইন, বেশিটাই ভাবনা। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। লেখাটায়, তখনও ওটার নাম ‘হন্যমান’ হয়নি, মন দিলে আমি আবার চলে যাই সেইখানে, যেখানে প্রেসিডেন্সি জেলখানার দোতলায় সেলে ওঠার সিঁড়ির ঠিক মুখোমুখি একটা ব্যাফল ওয়াল। তার ওপর কম্বল রোদ্দুরে দিয়েছি পোকা মারার জন্য। তার তিনহাত তফাতে, ভাঁটিঘরের পিছনদিকে ফিমেল ওয়ার্ডের বাউন্ডারি ওয়ালের কোনায় পাঁচিলের ওপর বসান একটা লোহার গোলক, তার সারা গা থেকে একফুট করে লম্বা লোহার কাঁটা বেরিয়ে আছে। দেখলে কেমন গা শিউরে ওঠে! উঠোনময় ছড়ানো ছোলা, পায়রা আর বাচ্চারা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। মুকুল আর ক্ষীরোদার সেলের সেই চাপা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ, যা আজ এখনও স্পষ্ট লেগে আছে নাকে। তখন অবান্তর হয়ে যায় আমার পরিপার্শ্বের বাস্তব, আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, টিফিন গুছিয়ে মুখে চুমু দিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠানো। একসঙ্গে ওই দুই বাস্তবতায় বাস করার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি না। যে জন্য লেখাটা নিয়ে বসতে চাই, আবার চাইও না।
ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছি নিজের শহরের চোরাগোপ্তা সাংস্কৃতিক স্রোতে। লেখাটা এগচ্ছে না ঠিক, বলা যায় যেন– ছড়াচ্ছে। একটু একটু করে খুব আড়ষ্টভাবেই ২৫ পৃষ্ঠার সেই আঁট বাঁধন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। একটি বাক্য ভেঙে গড়িয়ে যাচ্ছে দু’টি-তিনটি প্যারাগ্রাফে। খুব যে কাটাকুটি করতে হচ্ছে বা ফিরিয়ে লিখতে হচ্ছে অনেক বেশি– তা নয়। প্রসঙ্গ পেয়ে যাওয়ার পর আমি তো লিখছি আমার দৃষ্ট জিনিস। সে যেন নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে আসছে নিজের ভাষা। প্রত্যক্ষত জ্বালা হয়তো একটু কমেছে কিন্তু লেখা নিয়ে বসলে সেই দিনগুলি একই রকম দখল করে আমাকে। বন্ধুজনেরা কেউ কেউ একটু তাড়া দিচ্ছেন শেষ করার জন্য। আশপাশের কোনও কিছুই দাঁড়িয়ে নেই।
ঘটে গেল ভূপালের ইউনিয়ন কারবাইড দুর্ঘটনা, যার নারকীয়তার জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা। অন্য সাধারণ মানুষদের মতো একটু একটু করে বুঝতে চাইছি, পরিবেশবাদীদের কথা। জড়িয়ে যাচ্ছি পরমাণুশক্তি বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে দেখলাম, সমস্ত পৃথিবী থেকে প্রায় ২০০ জন বিজ্ঞানীর সই করা এক যৌথ সতর্কবাণী– গ্রিনহাউস এফেক্ট বিষয়ে। মোচড় খেয়ে যাচ্ছে চেতনার গভীরতম তল পর্যন্ত। সেই একই অসহায়তার বোঝা– গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে দেখি টেহরি ড্যাম, পাহাড়ের গা থেকে কেটে নেওয়া কাঁচা মাংসের মতো। প্রতিবাদ শোনার কেউ নেই। মুকুল বন্ধ সেলের মধ্যে থেকে জল চাইছে আর মাথা ঠুকছে, উঠোনে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে জল ঢেলে হাত ধুচ্ছে ওয়ার্ডার। দিল্লি রায়টের দেরিতে প্রকাশ পাওয়া রিপোর্ট, আসানসোলের বন্ধ পিলকিংটন গ্লাস ফ্যাক্টরির ভিখারি হয়ে যাওয়া গৃহস্থজন। চারিপাশের এইসব অসহনীয়তার মধ্যে নিজেকে সংহত করে লেখায় রাখা বড় কঠিন হচ্ছিল এক একবার। শেষ করার আগে কেবলি মনে হচ্ছিল– হল না। আরও কী যেন দেওয়ার ছিল, বলার ছিল আরও কত কথা।
তারপর ’৮৮ সালের আগস্ট মাসের এক রাত্রি সোয়া দুটোয় টুরার শরীরে সাদা কাপড় ঢাকা দিলাম। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় কয়েকজন বন্ধুর কাছে পড়ে শোনালাম– ‘হন্যমান: প্রেসিডেন্সি জেল পর্ব’। প্রথমার্ধ তাঁদের আগে পড়া হয়ে গিয়েছিল।
১৯৮৯ সালের বইমেলায়, তখনও বোধহয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠেই হত বইমেলা, অখ্যাত এক প্রকাশনা থেকে, সেই প্রকাশক বন্ধুর অসম্ভব জেদে, প্রকাশিত হল ‘হন্যমান’। প্রথম কভার ডিজাইন নিয়ে নিজের আপত্তি, কবি অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, প্রদীপ ভট্টাচার্যদের মিলিত আপত্তিতে, সেই কভার পালটানো হল। বইমেলার মাঠে ঢুকতেই একজন এসে বলে গেলেন, ‘একুশে’র অসিতদা ডাকছেন আপনাকে। তখনও মাঠে চেনা সকলের কাছে আমার পরিচয় কবি বলে। গেলাম ‘একুশে’। নিজের নাম বলতে হইহই করে উঠে আশপাশের অনেককে ডাকলেন অসিতদা। মাঠের কয়েক জায়গায় জটলায় ডাক পেলাম। অনেকেই অভিভূত ভাবে কথা বলছেন।
ওই দ্বিতীয় বইয়ের সূত্রে আরও কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছিল অন্যরকম। সেগুলো নিজের মূর্খতারই অভিজ্ঞান। তখনও জানতাম না, বই প্রকাশের পর সেই বইয়ের প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের কোনও দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক থাকে। কলকাতা কিংবা কলেজ স্ট্রিটের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বইমেলায় যেতাম, চার-পাঁচদিন পর ফিরে আসতাম নিজের সংসার, চাকরির জায়গায়। লেখা কিংবা প্রকাশন নিয়ে কোনও কথা কখনও হয়নি কারও সঙ্গে। তেমন বন্ধুও ছিলেন না কেউ। প্রকাশের দ্বিতীয় বছর বইটা একটা বিখ্যাত সাহিত্য পুরস্কার পায়। ফলে খুব দ্রুত অনেক মানুষ পড়তে থাকেন। প্রথম চার বছর বই সেই একই প্রকাশনে রয়ে যায়। সেই বন্ধু বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যেন বইটা তাঁর প্রকাশনা থেকে তুলে না নিই। যদিও প্রায় পাঁচ বছর সেই প্রকাশনায় থাকাকালীন আমি ওটার জন্য পেয়েছিলাম ১,০০০ টাকা আর পরে তাঁর ‘অবিক্রিত কপিগুলো’র জন্য তাঁকে ৭,০০০ টাকা দিয়ে বই অন্য প্রকাশনাকে দিতে পারি। এ অংশটা হয়তো না লিখলেও হত, কিন্তু আজ এতদিন পর অনভিজ্ঞ বিশ্বাসীজনের শিক্ষা কত জায়গায় কতভাবে অর্জন করতে হয়, তার এই উদাহরণটা দিতে লোভ হল। আদর্শের নামও যে প্রবঞ্চনার হাতিয়ার হয়, তার এই প্রথম শিক্ষাটা বড্ডই গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল। একথা খুব সত্যি যে, ওইটুকু ছাড়া এই দ্বিতীয় বই আমাকে যা দিয়েছে– পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে এত অসংখ্য এত রকম মানুষের যে আকুল ভালোবাসা, তার কাছে আর সবকিছুই তুচ্ছ! মনে রেখেছি যে, ওই অকূল ভালোবাসা, অজস্র চিঠি, জড়িয়ে ধরা কান্না– এর কোনওটাই আসলে আমার নয়। এগুলি ওই বইয়ে যে মানুষদের কথা আছে, তাদের জন্য। মানুষ যে শেষ পর্যন্ত মানুষকেই ভালোবাসে, এসব তারই অভিজ্ঞান। আমি তার আধার মাত্র। কিন্তু এর সাক্ষী থাকাই কি কম কথা?
……………………………………………
ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল
……………………………………………
তাই আজও কুড়ির কোঠায় বয়স পাঠকদের যখন এই ৩৫ বছর বয়সি বইটা কিনতে দেখি, সত্যিই আশ্চর্য লাগে। ওই একই কথা মনে হয়– মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। ‘কারো সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে’।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
