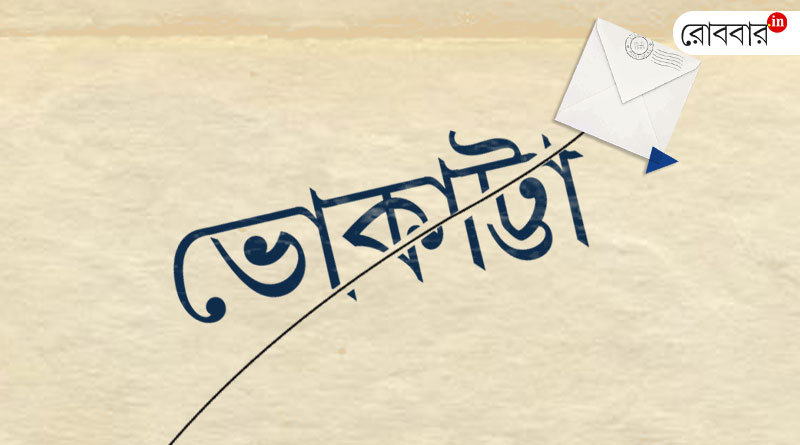
গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকো দীঘি আছে, সেই দীঘির এক এক পাড়ে এক একটি পাড়া। প্রাচীন কালে কারও বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে আগের দিন গিয়ে দীঘির পাড়ে গিয়ে কী কী বাসন লাগবে, তা বলে আসতে হত। পরের দিন সকালে দীঘির পাড়ে নাকি ঠিক ঠিক ফর্দ মিলিয়ে বাসন রাখা থাকত। কাজ মিটে গেলে বাসনপত্র ধুয়েমুছে আবার দীঘির পাড়ে রেখে আসতে হত। পরের দিন সকালে দেখা যেত সব বাসন গায়েব হয়ে গেছে। ভোকাট্টা-র শেষ চিঠিটি লিখছেন সীমা দাস।
প্রিয় বাংলাদেশ,
আমাদের একটাও মামা নেই, তাই আমাদের কোনও মামাবাড়িও নেই। অথচ ছোটবেলায় অন্য সব বাচ্চার মতো আমরা পাঁচ ভাইবোনও নিশ্চয়ই আধো আধো স্বরে, হাততালি দিয়ে ‘তাই তাই তাই, মামাবাড়ি যাই, মামাবাড়ি ভারি মজা, কিল চড় নাই’– এই ছড়াটা আওড়েছি।
আমাদের কোনও মামাবাড়ি ছিল না তো বটেই, কোনও দাদু-দিদার বাড়িও ছিল না। না, ছিল, কিন্ত সেটা এত দূরে যে, সেখানে আমরা কোনও দিনই যেতে পারিনি। আসলে আমার দাদু-দিদা বাংলাদেশে থাকতেন, তাই আমাদের কাছে দাদু-দিদার বাড়ি অধরা থেকে গিয়েছিল। শুধু আমরা কেন? বিয়ের চার বছর পর আমার মা-বাবা যখন কলকাতায় চলে আসে, তারপর তাদের আর বাংলাদেশে যাওয়াই হয়নি। আমার মায়েরও বাপের বাড়ি যাওয়ার ওখানেই ইতি। শুধু পঁচিশ বছর পর দিদা মারা গেলে, মা দাদুকে আনতে ও জমি-বাড়ি বিলি, ব্যবস্থা করতে নিজের জন্মভিটে ছুঁয়ে এসেছিল।
আমার মায়ের বাপের বাড়ি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া সাব ডিভিশনের সামন্তগড় নামে এক অজগাঁয়ে। সেখানে না আছে বৈদ্যুতিক আলো, না আছে কোনও পাকা রাস্তা, না কোনও স্কুল, এমনকী, প্রাইমারি স্কুলও নেই। তখনও ছিল না, যতদূর জানি এখনও নেই। তবু সেই অজগাঁয়ের কথা মা আজও বলে। সেখানেই যে মায়ের জন্ম, জীবনের ১৬টা বছর মা সেখানেই কাটিয়েছে। আমার মা সামন্তগড়ের পাশের গাঁ বিদ্যাকূটের প্রাইমারি স্কুলে পড়েছে। ব্যস, ওখানেই মায়ের পড়ার ইতি।
ছোটবেলায় মায়ের জবানিতে দাদু-দিদার কাছে কত চিঠি লিখেছি। মা বলে দিত, আর তা শুনে শুনে আমরা লিখতাম। ঠিকানাটা এখনও মনে আছে। শশীমোহন সাহা (আমার দাদুর নাম), মেরকুটা বাজার, পোস্ট অফিস: বিদ্যাকূট, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। চিঠি আসতে যেতেও প্রচুর সময় লাগত, দু’-তিন মাস পরে গিয়ে চিঠি পৌঁছাত। ঠিক এরকম ভাবেই দিদা মারা যাওয়ার আড়াই মাস পরে আমরা চিঠি পাই যে দিদা আর নেই।

কী ছিল তাহলে সেই গাঁয়ে? ছিল, ছিল, অনেক কিছুই ছিল, সাধারণত গ্রামদেশে যা যা থাকে, সেই সমস্ত কিছুই ছিল। ছিল অনেকটা করে জমি নিয়ে এক একটা বাড়ি, সেইসব বাড়িতে অগুনতি ফল-ফুলের গাছ, পুকুর, আমবাগান, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গরু-সহ গোয়ালঘর। আর ছিল আদিগন্ত ফসলের মাঠ। বিভিন্ন ঋতুতে সেই ফসলের মাঠ নানা ফসলে আলো হয়ে থাকত। মায়েদের বেশ কয়েক বিঘা জমি ছিল, সেই জমিতে বছরে তিনবার ফসল হত। ধানের সময় মরাইয়ে ধান তোলা, সেই ধান সিদ্ধ করা, রোদে মেলে দেওয়া– শত সহস্র কাজের পাহাড় প্রমাণ চাপ ছিল। শহরে বসে এসব আমরা ভাবতেও পারি না।
ঝড় উঠলে দৌড়ে আমবাগানে গিয়ে আম কুড়ানোর ধুম পড়ে যেত। ঠিক যেমন অপু-দুগ্গারা করত, আমার মাও আঁচল ভরে আম কুড়াত, ফসলের মাঠের আলপথ ধরে স্কুলে যাওয়া, পুকুরের থেকে কলস ভরে জল আনা– এসব আমার মা করেছে। হ্যাঁ, আমার মায়েরা পুকুরের জল খেত, কিন্তু বর্ষাকালে পুকুরের জল খাওয়া বারণ। তখন অনেক দূরের এক বাড়ি থেকে নলকূপের জল আনতে হত।
আমার দাদু-দিদা বৈষ্ণব ছিলেন, মাংস খেতেন না। তা বলে আমার মায়ের খাওয়া বারণ ছিল না। উঠোনের এক কোণে উনুন পেতে আমার মা একা একা মাংস রান্না করতেন। কী সুন্দর না? ঠিক যেন চড়ুইভাতি! এখানেও আমি পথের পাঁচালীর অপু দুগ্গার চড়ুইভাতির সঙ্গে মিল খুঁজে পাই।
অনেক অনেক দিন আগে এই গাঁয়ে কোনও এক সামন্ত রাজা গড় বানিয়েছিল। তারপর কালের প্রকোপে সেই গড় পরিত্যক্ত হয়ে বনজঙ্গল ভরে ওঠে, কিন্তু গাঁয়ের নামে সেই পরিচয় আজও রয়ে যায়। আরেকটা গল্পকথা শোনা যায়, গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকো দীঘি আছে, সেই দীঘির এক এক পাড়ে এক একটি পাড়া। প্রাচীন কালে কারও বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে আগের দিন গিয়ে দীঘির পাড়ে গিয়ে কী কী বাসন লাগবে, তা বলে আসতে হত। পরের দিন সকালে দীঘির পাড়ে নাকি ঠিক ঠিক ফর্দ মিলিয়ে বাসন রাখা থাকত। কাজ মিটে গেলে বাসনপত্র ধুয়েমুছে আবার দীঘির পাড়ে রেখে আসতে হত। পরের দিন সকালে দেখা যেত সব বাসন গায়েব হয়ে গেছে। এসবই গল্পকথা নিশ্চয়ই। মায়েরা নিজের চোখে কিছু দেখেনি, গুরুজনদের কাছে শুনেছে।
মায়ের কাছে সামন্তগড়ের কথা শুনে শুনে আমাদেরও খুব ভাল লাগে। কোনও গাঁয়েই কখনও থাকিনি, কিন্তু পূর্বপুরুষদের গাঁয়ে বংশানুক্রমিকভাবে থাকার অভিজ্ঞতা, গাঁ-কে ভালোবাসা, জিনগতভাবে পেয়েছি। তাই গ্রামবাংলা, কুঁড়েঘর, প্রকৃতি, মায়ের আঁচল বড্ড প্রিয়। সেই ভালোবাসায় ডুবে থাকি যেন চিরদিন।
ইতি,
সীমা
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
