
১৯৮৯। ইউক্রেনের লিয়াভ্যুভ শহরে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য এক অপেরা গায়ক খুন হন। গায়কের ১২ বছরের মেয়ের মুখ দিয়ে উন্মোচিত হল সেই সংকটময় পরিস্থিতি। মায়ের ও পরিবারের চার প্রজন্মের নারীদের এক আখ্যান পোলিশ সাংবাদিক ও লেখক জানা স্লোনিহ্বোস্কোর উপন্যাস ‘রঙিন শার্সিওয়ালা বাড়ি’ (পোলিশ নাম– ‘Dom z witrazem’, ইংরেজি নাম– ‘The House With The Stained-Glass Window’)। সুলগ্নার দ্বারা বাংলায় অনুবাদিত বইটা ‘ঋতবাক’ প্রকাশনী বার করেছে এই জুনে।
সুলগ্না মুখোপাধ্যায়, বয়স ৬০, প্রাথমিকভাবে জার্মান থেকে বাংলাতে বই অনুবাদ করেন। জার্মান ভাষার গল্প-কবিতা নিয়ে আসেন বাঙালি পাঠকের কাছে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এই প্রাক্তন শিক্ষকের দীর্ঘ চার দশকের সম্পর্ক জার্মান ভাষার সঙ্গে। ১৯৮৫-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে স্নাতকের সময় শুরু তাঁর জার্মান শেখা। পরে ম্যাক্সমুলার ভবন ও রামকৃষ্ণ মিশনে ভাষাটা আবার নতুন করে শুরু করেন এবং জার্মান শিক্ষক হিসেবে পড়ান কলকাতার জি. ডি. বিড়লা স্কুল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং Institute of Language Studies and Researches-এ। প্রায় ৭-৮টি বইয়ের অনুবাদক সুলগ্নার সঙ্গে আজকের কথপোকথন সাহিত্য, অনুবাদ ও সমাজ নিয়ে।

আপনি জার্মান সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ কবে থেকে শুরু করেন?
আমি প্রথম অনুবাদ করি ২০০০ সালে। সেই সময় ইন্দো-জার্মান ফেস্টিভ্যালে জার্মান লেখক কাটরিন স্মিটের সঙ্গে পরিচয়। ফেস্টিভ্যালের পরে ওঁর তিনটে কবিতা অনুবাদ করি। তখন অমিতেশ মাইতি ছিলেন সংবাদ প্রতিদিনে। উনি এবং কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমাকে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন কবিতাগুলো অনুবাদ করার জন্য। সেই কবিতাগুলোর পর বহু বছর আর সেইভাবে আমি কিছু করিনি। তারপর ২০১৯-এ কাটরিনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আবার ওঁর লেখা অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। অনুবাদ করলে কে বই ছাপবে, তা জানতামও না। কিন্তু ঠিক সেই সময় জার্মানি থেকে একটা দল কলকাতায় ম্যাক্সমুলার ভবনে আসে। ওদের একটা প্রোজেক্ট নিয়ে– City of Translators। আমাদের যেমন এখানে বাংলা আকাদেমি, তেমনি জার্মানিতে আছে Literarisches Colloquium Berlin। ওঁরা এই প্রোজেক্টটা নিয়ে আসেন। সেখানে আমার আলাপ হয় জার্মান লেখক ইউর্গেন বেকার আর অরেলি মরিনের সঙ্গে। তাঁদের উৎসাহে আমি সেই বছরই জার্মানিতে একটা কবিতা অনুবাদের কর্মশালায় যোগ দিই। ওখানে গিয়ে আমার চোখ খুলে যায় এবং ফিরে এসে আমি আবার অনুবাদ শুরু করি। তারপর বিভিন্ন বন্ধুদের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রেসের সঙ্গে। তাঁরাই কাটরিনের কবিতার ‘নদী ও দেবদূত’ (Flussbild mit Engel) বইটা ছাপান।
আপনার নতুন বই ইউক্রেনের লেখক জানা স্লোনিহ্বোস্কোর একটা পোলিশ বই। এইটা অনুবাদ করার পিছনে কোনও বিশেষ কারণ?
আমাদের এখানে Long Night of LiteratureS বলে প্রত্যেক বছর একটা প্রোগ্রাম হয়। কলকাতা ও দিল্লিতে বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশের এমব্যাসি মিলে আয়োজন করেন। তাঁদের দেশের লেখকদের নিয়ে আসেন, যাঁরা নিজেদের লেখা পাঠ করে শোনান। ২০২৩-এ কলকাতাতে ম্যাক্সমুলার ভবন ও আলিয়ঁস ফ্রঁসে এইটার আয়োজন করে। এই প্রোগ্রামে জানার মুখে তাঁর উপন্যাসের একটা অংশ শুনি। গল্পটা শুনতে শুনতে বুঝলাম জানা ইউক্রেনের চারটে প্রজন্মের নারীর কথা লিখেছেন। এই যে বিভিন্ন প্রজন্মের নারীদের কথা, এইটা আমি প্রথম পেয়েছিলাম আশাপূর্ণা দেবীর লেখায়। এটা আমাকে নাড়া দেয়। এবং অবশ্যই ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধের কথা আমাকে টানে। পরে জানার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি, ওঁর পরিবারেই মাইগ্রেশনের একটা গল্প আছে। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে এই বইটা অনুবাদ করব।

জানার গল্প শুনে যেমন আশাপূর্ণা দেবীর লেখা মনে পড়েছিল, তেমনই কোনও জার্মান গল্প অনুবাদ করেছেন– যা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল যে এটা বাংলারই কথা অন্য ভাষায় লেখা?
হ্যাঁ। একবার ম্যাক্সমুলার ভবনে আলাপ হয় লেখক ইজাবেল ফার্গো কোলের সঙ্গে। উনি আমেরিকান। জার্মানিতে পড়তে এসে থেকে যান। তাঁর বই ‘সবুজ সীমানা’-র (Die grüne Grenze) একটা পাঠ হয় ম্যাক্সমুলারে। এবং আমার শুনেই ভালো লাগে। কারণ বইটা বিভক্ত জার্মানির সীমান্তের সংঘর্ষ নিয়ে। বইটাতে জাদুবাস্তবতাও আছে। গল্পের এক বাচ্চা মেয়ে, পূর্ব জার্মানির বাসিন্দা, একদিন পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যায়। পাখির তো কোনও সীমানা থাকে না। বইটা অনুবাদের সময় বার বার মনে পড়েছে আমার দাদু-ঠাকুমার কথা। বরিশালের এক দাপুটে আইনজীবী ছিলেন আমার দাদু। দোতলা বিশাল বাড়ি ছিল। দেশভাগের সময় দাদুর কিছু ক্লায়েন্ট তাঁকে এসে জানান যে ওঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমার ঠাকুমাকে বোরখা পরিয়ে সীমান্ত পার করাতে হয়েছিল। দাদু নিজের প্র্যাকটিস ও বাড়ি ফেলে আসার ক্ষোভ ও যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন শেষ অবধি। আমার বাবাও ওপার বাংলার বলে অনেক বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছেন। পুরোটাই স্বীকৃতি ও মর্যাদার ব্যাপার। আমি ১৯৯০ সালে বার্লিনে ছিলাম যখন প্রাচীর ভেঙে পূর্ব ও পশ্চিম এক হয়। সেখানেও দেখেছি একই দেশের দুই পক্ষ একে অপরকে স্বীকার করছে না। জার্মান সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে করতে মনে হয়েছে যে এই গল্পগুলো আমি আমার ঠাকুমার মুখে শুনেছি। ক্রিস্টা হ্বল্ফের ‘দ্বিখণ্ডিত আকাশ’-এও (Der geteilte Himmel) প্রায়ই আমাদেরই মতো পূর্ব-পশ্চিমের কাহিনি। প্রেমিক পশ্চিম জার্মানিতে থাকতে চায়, কিন্তু প্রেমিকার পূর্ব জার্মানি ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পছন্দ। তাছাড়াও আরেকটা মিল– পূর্ব ইউরোপের পারিবারিক গঠন অনেকটা আমাদেরই মতো। দাদু, ঠাকুমা, যুক্ত পরিবারের মর্যাদা ছিল যেটা পশ্চিমের পুঁজিবাদী সমাজে নেই। এখন যদিও পূর্ব জার্মানিতেও আর সেইভাবে নেই।
তার মানে যখন অনুবাদের জন্য উপন্যাস বাছেন তখন নিজের বা পারিবারিক ইতিহাসের একটা প্রভাব থাকে…
একশোবার। আর হচ্ছে লিঙ্গ রাজনীতি। আমি মহিলাকেন্দ্রিক গল্প অনুবাদ করতে পছন্দ করি।
আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি আপনার অনূদিত উপন্যাসের মধ্যে দুটো উপন্যাস, যা পাঠকের পড়া উচিত জার্মান দেশটাকে চেনার জন্য, তাহলে কোন বইগুলো পড়তে প্রস্তাব করবেন?
ক্রিস্টা হ্বল্ফের ‘দ্বিখণ্ডিত আকাশ’ আর ইজাবেল ফার্গো কোলের ‘সবুজ সীমানা’।
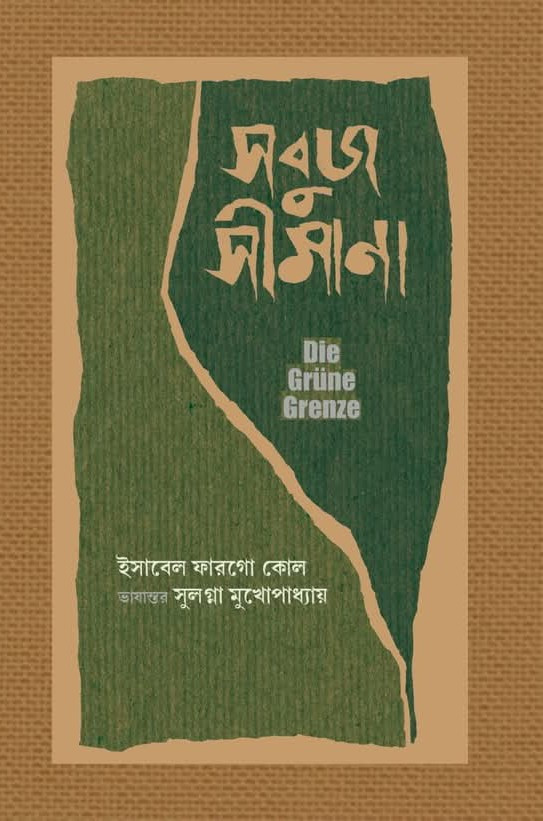
এখন তো অনূদিত উপন্যাসের পৃথিবীব্যাপী চাহিদা। গীতাঞ্জলি শ্রী এবং বানু মুশতাকের বুকার জয় সেটারই প্রতিফলন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের চাহিদা বেশি। আপনার কি মনে হয় বাংলাতেও অন্য ভাষার উপন্যাসের পাঠক বাড়ছে? নাকি বাংলার গল্পটা অন্য?
বাংলার গল্পটা আলাদা। এখানে ইংরেজিতে অনুবাদ পড়বে। কিন্তু বাংলা অনুবাদ পড়ে না সহজে। যদিও এটা শহরের কথা। বাংলার চাহিদা আছে কলকাতার বাইরে। সেখানে তাঁরা হয়তো ইংরেজিতে অতটা সড়গড় নন। তাছাড়া আমাদের এখানে তো বড় প্রকাশক নেই, তাই ভালো প্রচারও নেই। আমার বেশিরভাগ অনুবাদ বেরয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রেস বা ঋতবাক থেকে, যাদের অত প্রচার ক্ষমতা নেই। সুতরাং আমার বইগুলোর প্রচার কম হয়। আমাদের, অনুবাদকদের, নিজের বই নিজেদেরই প্রচার করতে হয়। তাই হয়তো এখানে পাঠক কম। মারাঠি বা হিন্দিতে তা নয়। সেখানে কিন্তু অনূদিত সাহিত্য অনেক বেশি পড়া হয়। এছাড়াও বাংলাদেশেও এখানকার অনূদিত বই যায় না। ওঁদের নিজেদের অনুবাদক ও অনুবাদ আছে।
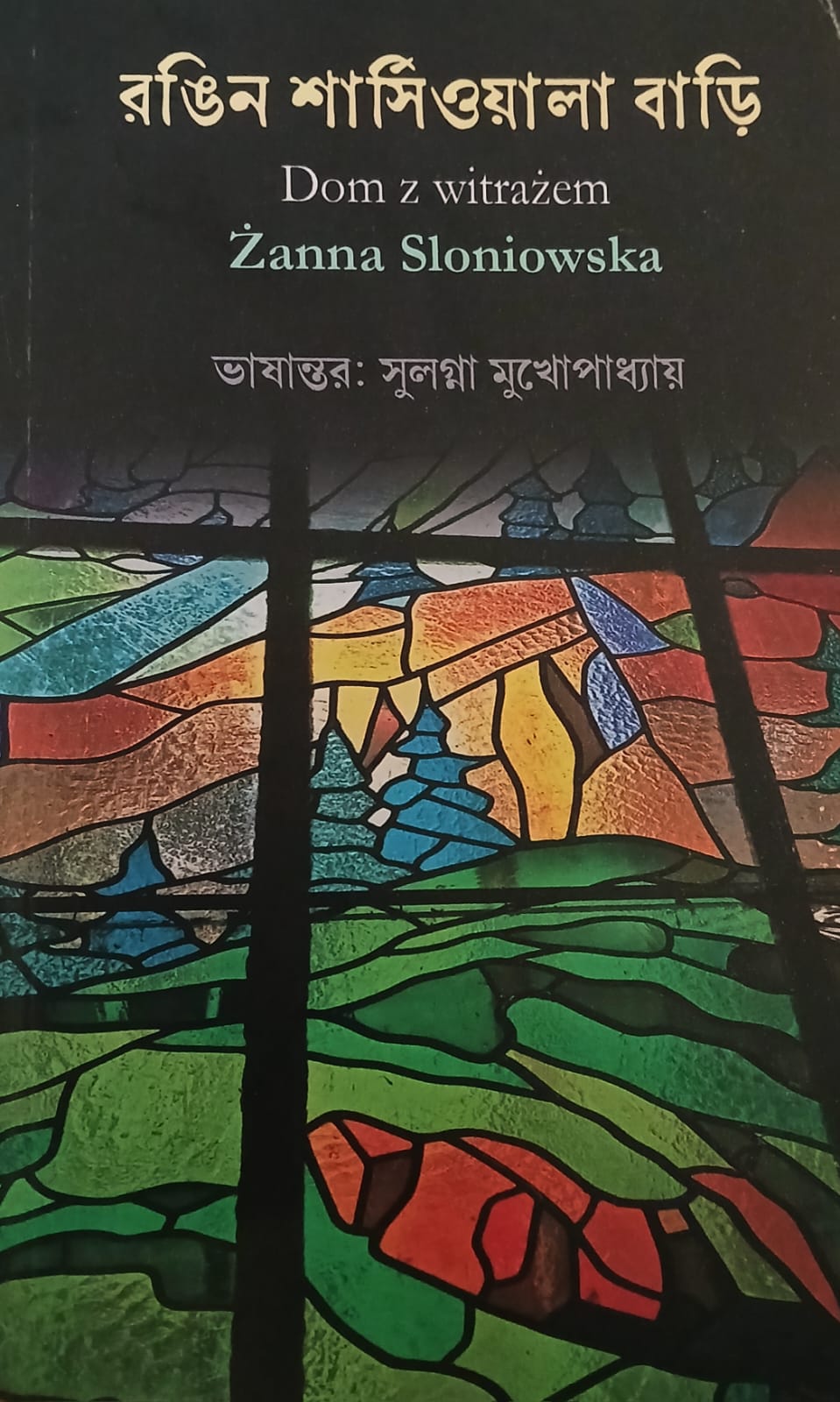
প্রচার ছাড়াও কি এখানে অনুবাদকদের আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়?
এখানে অনুবাদকদের পারিশ্রমিকও কম দেওয়া হয়। প্রকাশকরা বলে, ‘হ্যাঁ লিখুন। দিচ্ছি পাঁচ হাজার, দশ হাজার।’ আমায় একজন টোমাস মানের ‘The Magic Mountain’ অনুবাদ করতে বলেছিলেন, কিন্তু টাকা দিতে পারবেন না। আমি মানা করে দিলাম। অনেক বছর ধরে অনুবাদ করছি, তাই আমি না করার মতো পরিস্থিতিতে আছি। কিন্তু যারা সবে অনুবাদ করা শুরু করছে তাদের কী হবে? আমার একজন চেনা অনুবাদক টাকা পান না। বই বিক্রির রয়্যালটির ওপর ভরসা। যেখানে অনুবাদের বই পড়তে চায় না কেউ, সেখানে রয়্যালটি থেকে কতই বা টাকা পাওয়ার আশা করা যায়? এই সংস্কৃতিটাকে পালটাতে হবে।
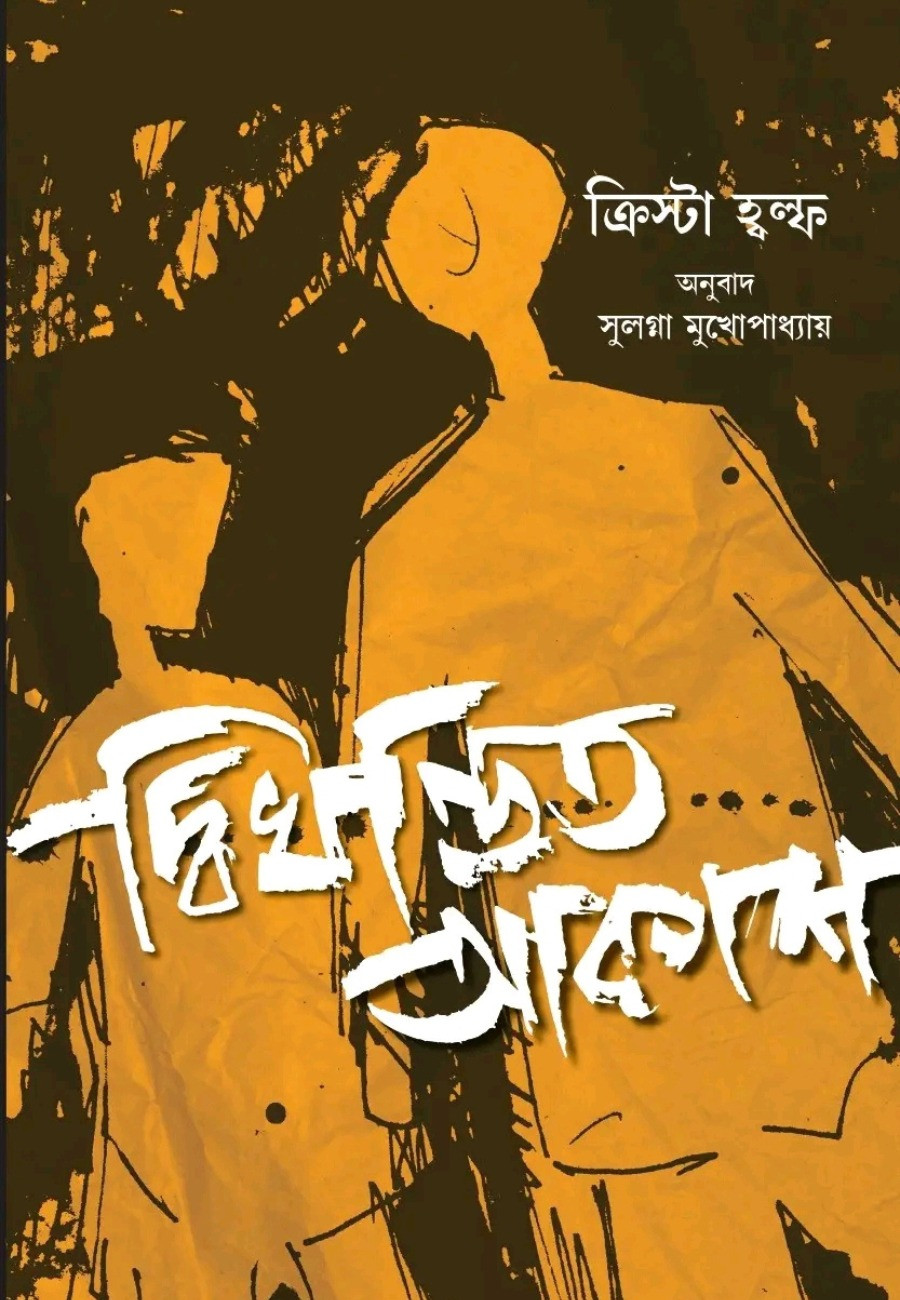
কীভাবে এই সংস্কৃতি পালটানো যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?
সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের দেশে কোনও গ্রান্ট নেই। একমাত্র আমি যদি সাহিত্য আকাদেমির কাজ করি তবেই গ্রান্ট পাব। সেখান থেকেও পাওয়া সমস্যা। আমাদের সরকার চাইছেন এখানকার লেখা ওখানে অনুবাদ হোক। নিশ্চয়ই। কিন্তু সেগুলোর জন্য আমাদের অনুবাদকরা যথেষ্ট নয়। আমি যদি বাংলা থেকে জার্মান করি, সেইটা ওখানকার স্থানীয়দের মতো জার্মান হবে না। ওখানকার অনুবাদক লাগবে। আমার এক বন্ধু, হান্স হার্ডার, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক– উনি যখন বাংলা থেকে জার্মানে অনুবাদ করেন, তখন আমাদের সবার সঙ্গে কথা বলেন সঠিক অনুবাদের জন্য। আমাকেও তাই করতে হয় যখন বাংলায় অনুবাদ করি। ইতিহাসটাকে, সংস্কৃতিকে জানতে হয় এবং এমনভাবে লিখতে হয় যাতে এখানকার পাঠক ভালো করে বুঝতে পারেন। এগুলোর পেছনে অনেক সময় ও শ্রম যায়। আমাদের এখানে, বড় নামকরা লেখক ছাড়া অন্য লেখকদের সম্মান নেই। অনুবাদক তো আরও নিচের শ্রেণির। আমাদের কোনও সরকার অনুবাদকদের প্রাপ্য সম্মান এখনও দিতে পারেননি। ওদেশে (জার্মানিতে) আমি দেখেছি কীভাবে সম্মান দেন। তাঁরা মনে করেন অনুবাদকরা আছে বলেই তো আমাদের সাহিত্য অন্য দেশে যেতে পারছে। সেইটা এখানে নেই।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
