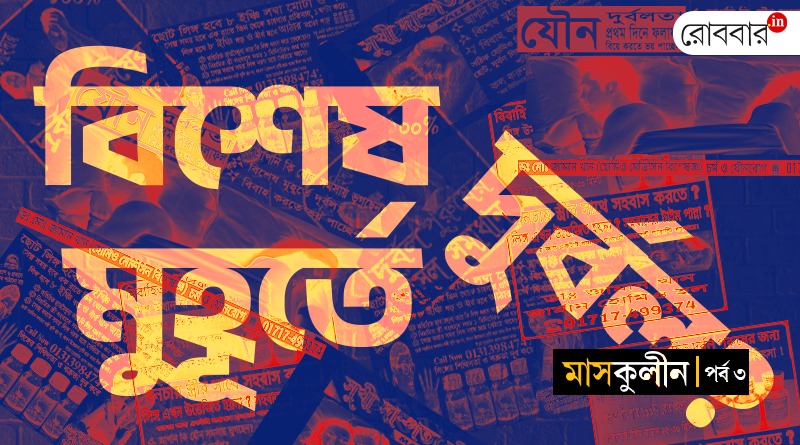
গেরস্তের তথাকথিত সংসারী মহিলাদের জন্য যেন ঠিক রাজনীতির ময়দান নয়। তাদের জন্য বরাদ্দ রান্নাঘর, সন্তানজন্ম ও পালন। সে-কারণেই আজও প্রতিষ্ঠিত মহিলা রাজনীতিবিদদের টিভি-সাক্ষাৎকারে লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা রান্নাবান্না জানেন কি না এমন একটা প্রশ্ন থাকবেই! এসব সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক যেসব মেয়েরা রাজনীতিতে এসেছেন, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁরা কোনও পুরুষের থেকে এতটুকু কম সফল হয়েছেন, বলা যায় না। ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে এবং এখনও যে পুরোপুরি তা সমতা লাভ করেছে, তা নয়।

৩.
ছোটবেলায় ইতিহাসের ক্লাসে আমাদের পড়ানো হয়েছিল ‘হিস্ট্রি’ শব্দের অর্থ ‘হিজ স্টোরি’, মানে ‘তার গল্প’। এই ‘তার’ বলতে ‘পুরুষ’কে বোঝানো হত আর প্রমাণ করার চেষ্টা চলত যে মানুষের ইতিহাস গোটাটাই শুধু পুরুষের গল্প। অন্য কোনও লিঙ্গ বা যৌনতার মানুষের গল্প সেই ইতিহাসে স্থান পেত না। হ্যাঁ, তাই তো। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যে পড়েছি, সেখানে সিংহভাগ জুড়ে শুধু পুরুষদের কথাই পড়তাম আমরা। হাতে গোনা কয়েকজন নারীর কাহিনি বলা হত। কিংবা নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলাদা আলোচনা থাকত। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষ ও নারীর সমান লড়াইয়ের বিষয়টা অনালোচিত থেকে যেত।
পুরুষের ইতিহাসে, পুরুষের রাজনীতিতে নারীকে কেবল আলাদা একটা পরিচয় দিয়ে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে এক নয়, দুই নয়, ১১ জন নারী যে ছিলেন– সেই আলোচনা এখন যেন কোথাও ঢাকা পড়ে গেছে। ভারতে স্বাধীনতার পর মেয়েরা ভোটাধিকার পেলেও শতাংশের বিচারে ভোট দিতে পারত বা দিতে দেওয়া হত খুবই কম সংখ্যক মেয়েদের। প্রকৃত ভোটাধিকার পেতে যাদের এত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ তলানিতে থাকবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।
ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রথম থেকে এবং আজ অবধি নির্লজ্জভাবে পুরুষের ক্ষেত্র। পুরুষ বলতে উচ্চজাতি, উচ্চবিত্ত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের তথাকথিত ‘স্ট্রেট’ (বিসমকামী) পুরুষ। সেই পুরুষ যেমনভাবে চাইবে নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক, নারীকে সেভাবেই অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কেন? এর গভীরে আছে নারীর সঙ্গে পুরুষের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
পুরুষ তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্র নারীকে ক্ষমতাহীন করে রাখতে চায়। নারী কেবল বংশবৃদ্ধির যন্ত্র। তার বাইরে নারীর কোনও উপযোগিতা যেন নেই। সে-কারণে রাজনীতিক্ষেত্রে নারীকে একচিলতে জমি ছাড়া হয় না। স্বাধীন ভারতেও আমরা যে মহিলা রাজনীতিবিদদের দেখেছি, সে ইন্দিরা গান্ধী হোক নন্দিনী শতপথী হোক বা মায়াবতী, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, সোনিয়া গান্ধী, জে. জয়ললিতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সুপ্রিয়া সুলে; এক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া রাজনীতিতে মোটামুটি সকলেরই প্রাথমিক পরিচয় থেকেছে কোনও প্রতিষ্ঠিত পুরুষ রাজনীতিবিদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, সঙ্গী বা শিষ্যা হিসেবে।

কমিউনিস্ট পার্টিতেও মেয়েদের জায়গা সব সময় পুরুষের সঙ্গে সমান পঙক্তিতে থাকেনি। বহু কমিউনিস্ট নেত্রীদের স্মৃতিরচনা পড়লে দেখা যায় পার্টি যখন নিষিদ্ধ ছিল, সে-সময় মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত, সংগ্রাম করত কিন্তু পার্টিকমিউনে দেখা যেত মেয়েদের যা তথাকথিত সামাজিক কাজ সেকালে (এখনও চলছে যদিও) ছিল যথা রান্নাবান্না, ঘর-সামলানো, সন্তানপালন– সেগুলিই তাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। সুতরাং, মহিলাদের অর্থাৎ ভারতীয় মহিলা রাজনীতিবিদদের তেমন স্বাধীন সত্তা গড়ে উঠেছে, তা বলা চলে না। শুধু তাই নয় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও কোথাও একটা জৌলুসহীন, সাধ্ববী-মার্কা ছাপ বজায় থেকেছে যাতে তাদের দেখে আমজনতার মনে একজন নিঃস্বার্থপর, বিবাহ-সংসারবিহীন ব্যক্তিত্বের অবয়ব ফুটে ওঠে।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
সমকামী-রূপান্তরকামী পুরুষদের খোলাখুলি অংশগ্রহণ স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে এখনও অবধি প্রায় নেই বললেই চলে। যেখানে ইউরোপের বহু দেশের রাষ্ট্রনায়ক সমকামী-রূপান্তরকামী যৌনপরিচয়ের মানুষ সেখানে ভারতে এতগুলো লোকসভা, বিধানসভা কিংবা পৌরসভার ভোটে দু’-একজন ছাড়া কোনও ঘোষিত সমকামী বা রূপান্তরকামী প্রার্থীকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি এই কারণেই যে, ভারতীয় সমাজ আজও সমকাম-বিদ্বেষী। এই রাজনীতির ক্ষেত্রটি কেবল তথাকথিত ‘স্ট্রেট’ পুরুষের জন্য। সেই পুরুষকে সমাজের সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার তাঁবেদারি করে এই রাজনীতি।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
গেরস্তের তথাকথিত সংসারী মহিলাদের জন্য যেন ঠিক রাজনীতির ময়দান নয়। তাদের জন্য বরাদ্দ রান্নাঘর, সন্তানজন্ম ও পালন। সে-কারণেই আজও প্রতিষ্ঠিত মহিলা রাজনীতিবিদদের টিভি-সাক্ষাৎকারে লক্ষ করা যায়, তাঁরা রান্নাবান্না জানেন কি না এমন একটা প্রশ্ন থাকবেই! এসব সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক যেসব মেয়েরা রাজনীতিতে এসেছেন, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁরা কোনও পুরুষের থেকে এতটুকু কম সফল হয়েছেন, বলা যায় না। ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে এবং এখনও যে পুরোপুরি তা সমতা লাভ করেছে, তা নয়।
চলতি বছরের লোকসভা ভোটের কথা ধরি যদি তাহলে দেখি যে-পার্টি এতদিন সরকারে ছিল তাদের প্রার্থী তালিকাতে মহিলার সংখ্যা এখনও যথেষ্ট নগণ্য। শুধু তাই নয়, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি মহিলাদের সামাজিক দিক থেকেও নানাভাবে বিপর্যস্ত করে। হিন্দু ছেলেরা অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করলে সেটা গর্বের কারণ হয়ে ওঠে, অথচ হিন্দু মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছেতে অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে তো দূরের কথা ভালোবাসলেই তথাকথিত ‘লাভ-জিহাদ’-এর ভূত দেখতে পাওয়া যায়!
এই একই ধারা বজায় থাকছে জাতীয়তাবাদী, বাংলাবাদী সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও। বাঙালি ছেলে বিহারি মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে অসুবিধা নেই, কিন্তু বাঙালি মেয়ে বিহারি পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে তাকে ‘ফাঁসানো’ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং বাঙালিকে এ সমস্ত ‘বেচালপনা’র বিরুদ্ধে জাগতে অনুরোধ করা হচ্ছে! প্রশ্ন হতে পারে, রাজনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যদি পুরুষ হয়, কেবল তবে মেয়েদের জন্য নানা প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রত্যেকটি পার্টি সরকারে আসলে কেন করে বা অগ্রাধিকার দেয়? আর কেন-ই বা সেসবের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়? সেগুলো এ-কারণেই– মহিলারা যে আদপে রাজনীতিতে পুরুষের সঙ্গে সমান স্তরে নেই, সেই চিত্র কিঞ্চিত ঢেকে দেওয়ার জন্য। তা না হলে মেয়েদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ প্রকল্প সরকারের পক্ষ থেকে থাক কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে মহিলা ও পুরুষ প্রায় সমান সমান যখন, তখন সংসদেও সেই সমতা দেখা যাবে না কেন? কেন আপাতত সংরক্ষণ দিয়ে সেই সংখ্যা সমান করা হবে না? দুঃখের বিষয়, ভারতে মহিলা-সংরক্ষণ বিলের বাস্তবায়নের পরিকল্পনা এখনও বিশ-বাঁও জলে। এবং সেই বিলে রূপান্তরকামী-নারীদের কোনও সংযুক্তি নেই!

এর পাশাপাশি সমকামী-রূপান্তরকামী পুরুষদের খোলাখুলি অংশগ্রহণ স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে এখনও অবধি প্রায় নেই বললেই চলে। যেখানে ইউরোপের বহু দেশের রাষ্ট্রনায়ক সমকামী-রূপান্তরকামী যৌনপরিচয়ের মানুষ সেখানে ভারতে এতগুলো লোকসভা, বিধানসভা কিংবা পৌরসভার ভোটে দু’-একজন ছাড়া কোনও ঘোষিত সমকামী বা রূপান্তরকামী প্রার্থীকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি এই কারণেই যে, ভারতীয় সমাজ আজও সমকাম-বিদ্বেষী। এই রাজনীতির ক্ষেত্রটি কেবল তথাকথিত ‘স্ট্রেট’ পুরুষের জন্য। সেই পুরুষকে সমাজের সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার তাবেদারি করে এই রাজনীতি। মহিলারা যেমন এই রাজনীতির দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনই সমকামী-রূপান্তরকামী যৌনপরিচয়ের মানুষদের দম আটকে দিয়েছে এই রাজনীতির ধারক-বাহকরা। ভারতে সমকামী-রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিসমকামীদের মতো বিবাহ, যৌথজীবন, উত্তরাধিকার বা সন্তান-পালনের কোনও অধিকার আজ অবধি নেই এবং কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকার পক্ষ এই বৈষম্য বন্ধ করতে সচেষ্ট নয়।
প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ সিমুর মার্টিন লিপসেট তাঁর সাড়া-জাগানো ‘পলিটিক্যাল ম্যান: দ্য সোশাল বেসেস অফ পলিটিক্স’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘…লেজিটিম্যাসি ইনভলবস দ্য ক্যাপাসিটি অফ আ পলিটিক্যাল সিস্টেম টু এনজেন্ডার অ্যান্ড মেনটেন দ্য বিলিফ দ্যাট এক্সিস্টিং পলিটিক্যাল ইন্সটিটিউশন আর দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর প্রপার ওয়ান্স ফর দ্য সোসাইটি।’ অর্থাৎ রাজনীতির ততক্ষণ বৈধতা আছে যতক্ষণ সে একটা রীতি বজায় রাখতে পারে যে, যা চালু আছে তা-ই সমাজের জন্য যথাযথ। পুরুষের রাজনীতিও ঠিক এমনই। পুরুষ তার রাজনীতির একচ্ছত্র নায়ক। সে কাউকেই তাতে জায়গা দেয় না। অন্য লিঙ্গ বা যৌনতার মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অন্তত ভারতে আজও উচ্চবিত্ত, উচ্চজাতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম ও তথাকথিত বিসমকামী যৌনতার পুরুষদের অঙ্গুলিহেলনেই অনুমোদিত হয়।
(চলবে)
পড়ুন মাসকুলীন-এর অন্যান্য পর্ব
পর্ব ২: সেই তরুণরা আলোচনায় আসে না, যাদের কল্পজগতে নেই কোনও মনিকা বেলুচ্চি
পর্ব ১: কেন ‘যৌন’ শব্দের সঙ্গে ‘ক্ষমতা’ বা ‘শক্তি’ জুড়ে পুরুষের যৌনতা বোঝানোর দরকার পড়ে?
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
