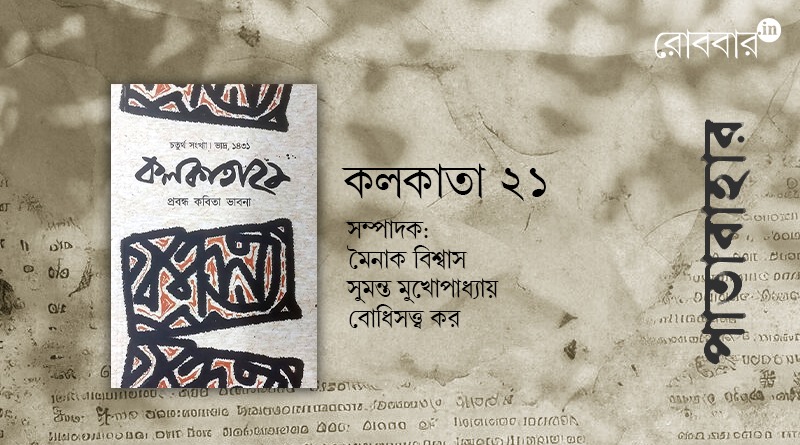
মৈনাক বিশ্বাস, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, বোধিসত্ত্ব কর সম্পাদিত ‘কলকাতা ২১’ প্রথম বেরিয়েছিল একুশ শতকের একুশ-তম বছরে। চিন্তানির্মাণের মাধ্যম হিসেবে কোনও একটি সংরূপে আটকে না থেকে, এ পত্রিকা সাজিয়ে দেয় নানা কিসিমের লেখাপত্তর। আপাতত, নজর দেওয়া যাক সর্বশেষ প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যায়।

মৈনাক বিশ্বাস, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, বোধিসত্ত্ব কর সম্পাদিত ‘কলকাতা ২১’ প্রথম বেরিয়েছিল একুশ শতকের একুশ-তম বছরে। চিন্তানির্মাণের মাধ্যম হিসেবে কোনও একটি সংরূপে আটকে না থেকে, এ পত্রিকা সাজিয়ে দেয় নানা কিসিমের লেখাপত্তর। আপাতত, নজর দেওয়া যাক সর্বশেষ প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যায়।
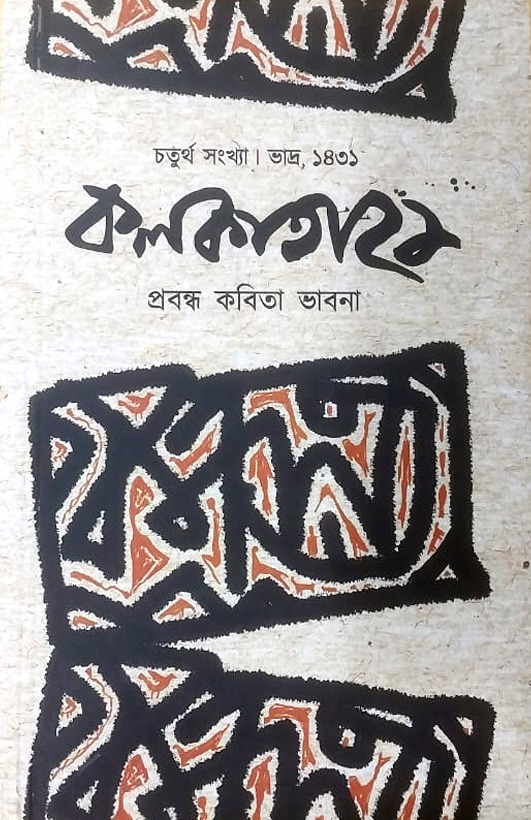
প্রবন্ধ
‘কলকাতা ২১’ যেসব কাজ নিয়মিতভাবে সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছে, তার একটি হল কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ। বিশেষ উল্লেখ্য, প্রথম সংখ্যায় স্বপন চক্রবর্তীর ‘কবির ঠিকানা’ ও দ্বিতীয় সংখ্যায় শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবিতা বিষয়ে’ প্রবন্ধ। এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত ‘পা যেদিকে চলে’-র লেখক সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিষয়, বাংলা সাহিত্যজগতে রাজনীতি ও নান্দনিকতার দ্বন্দ্বমিতালির প্রেক্ষিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখি। দেখিয়েছেন প্রাবন্ধিক, সুভাষের রচনাকর্ম যেমন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের রোষদৃষ্টির শিকার হয়েছিল, তেমনই আবার ‘ব্যক্তি-বিশ্ব’ দ্বিত্বের বাইরে এক বিকল্প নান্দনিকতার সন্ধানে নেমেছিল তা। মন্তব্য তাঁর: “কবিও যে কর্মী, এবং রাজনৈতিক কর্মী, সেটা নন্দনতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারা সহজ ছিল না। একক কর্মী, সকলের সহযাত্রী হয়ে থাকাই কবির রাজনীতি।” পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রাজনীতি ও নান্দনিকতার সম্পর্কবিচার সাহিত্যপাঠ, বিশেষত মার্কসীয় সাহিত্যপাঠের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকাশিত হয়েছে সেসবের প্রামাণ্য সংকলন, যেমন ফ্রেডরিক জেমিসন সম্পাদিত Aesthetics and Politics (১৯৭৭)। সুমন্তের প্রবন্ধ বাংলা ভাষার এ-সংক্রান্ত বিতর্কগুলিকে ফিরে দেখার পরিসর তৈরি করেছে।
চমৎকার এ প্রবন্ধের নিরিখে চটুল চুটকির মতোই শোনাবে, কিন্তু দলীয় মার্কসবাদের সূত্রে, মার্কসের নিজের কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নিজদেশ জার্মানি হতে বিতাড়িত, তরুণ মার্কসের সম্পাদনায় যখন প্যারিস থেকে প্রকাশিত হল ‘Franco-German Yearbook’-এর প্রথম সংখ্যা, তখন সেখানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান লেখক বলতে একজনই ছিলেন, কবি হাইনরিশ হাইনে। মার্কসীয় অর্থে কমিউনিস্ট তো দূরের কথা, পরন্তু হাইনে ছিলেন নিবিড় ঈশ্বরবিশ্বাসী। তৎসত্ত্বেও মার্কসের ক্ষুরধারনিশিত আক্রমণ থেকে যে বেঁচে গেছিলেন তিনি, তার কারণ ছিল তাঁর কবিসত্তাই। মত ছিল মার্কসের, কবি শ্রেণির লোকেরা আদতে ‘queer fish’, ‘সাধারণ শুধু নয়, অসাধারণ যাঁরা, তাঁদের নিরিখেও কবিদের বিচার করা চলে না।’ দুর্ভাগ্য আমাদের, চরিত্রবিচারের নিক্তি যে শিল্পীমানুষের ক্ষেত্রে একেবারেই অন্যধারার হবে, সেটা বোঝার মতো সাধারণ বুদ্ধি বঙ্গীয় দলজীবীরা দেখিয়ে উঠতে পারেননি।
এ নিবন্ধটির আলোচনার জন্য ফিরে যেতে হবে পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায়, সুকন্যা সর্বাধিকারীর লেখা ‘অব্যক্ত লহরী: অশব্দ, শব্দ, ও সংখ্যার আবছায়া’ প্রবন্ধের কাছে। শঙ্খের গড়নের ভিতর লুকিয়ে থাকে যে সাড়ে তিন প্যাঁচ, তার সূত্র ধরে সুকন্যা একদিকে পৌঁছেছিলেন গণিতশাস্ত্রের গোল্ডেন রেশিও-র কাছে। অন্যদিকে, উপনিষদ ও তন্ত্র থেকে শুরু করে শাঁখারি ও কুম্ভকারদের যাপন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন শঙ্খের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দার্শনিক প্রশ্নগুলি। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের প্রবন্ধটি লিখেছেন দীপেশ চক্রবর্তী। তবে, তাঁর লেখার অবলম্বন মানুষের সাহিত্য, নিত্যাচার, মঙ্গলামঙ্গলবোধের বাইরে থেকে যাওয়া খোদ শামুক প্রাণীটিই। পাশাপাশি, ঔপনিবেশিক পর্বের প্রাণীতত্ত্ববিদ জেমস হরনেল-এর লেখালেখির ওপর ভিত্তি করে তিনি বলেছেন সেই ডুবুরি জনগোষ্ঠীর কথা– শাঁখ তৈরি প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকা সত্ত্বেও– যাদের শ্রম উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি সাধারণত মনে রাখে না।
উচ্চবর্ণের ইতিহাসে ঠাঁই না পেলেও, অপরায়নের তরিকার মধ্যে নানা ইঙ্গিত অবশ্য রয়েই যায়। লক্ষণীয় বিষয়, আনু. পনেরো শতকে লেখা বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এ শাঙ্খিক/শঙ্খকার জাতির জন্য বরাদ্দ হয়েছে বৈদ্য/কায়স্থদের সমতুল্য ‘উত্তম সঙ্কর’ শ্রেণি। কিন্তু দীপেশ যে ডুবুরিদের কথা বলেছেন, শামুক সংগ্রহ করে, তাকে পচিয়ে-গলিয়ে শঙ্খ প্রস্তুত করেন যাঁরা, তাঁদের উল্লেখ ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধিগ্রন্থে সেভাবে নেই। এও আশ্চর্য, বৃহদ্ধর্মপুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এর মতো গ্রন্থে ‘অধম সঙ্কর’/‘অসৎশূদ্র’ বর্গভুক্ত জাতির মধ্যে অধিকাংশের পেশার সঙ্গেই ঘ্রাণের যোগাযোগ রয়েছে: ‘ধীবর/জালিক’ (মৎস্যজীবী), ‘চর্মকার’, ‘মাংসচ্ছেদ’, ‘ডোম’, ‘চণ্ডাল’ ইত্যাদি। শঙ্খের ভিতর থাকা শামুককে হত্যা করার সময় ‘অসহ্য মাংসল গন্ধের’ কথা উল্লেখ করেছেন দীপেশ। যে পেশার আবশ্যিক শর্তই হল দুর্গন্ধের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, সেই পেশাজাত পণ্যকে আত্মসাৎ করার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যবাদ কীভাবে সেই পেশাজীবীকে অপরায়িত করে, তা নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে নিশ্চয়ই। বস্তুত, সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের প্রশ্ন নিয়ে সুকন্যা ও দীপেশ যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন ‘কলকাতা ২১’-এর পাতায়, তা থেকে চিন্তার বিভিন্ন আঙ্গিকে বিচরণের রসদ মিলবে।
রবীন্দ্রনাথের ‘কাব্যিক লেখা’য় প্রশ্ন ও সংশয়মূলক বাক্যের প্রয়োগে, কীভাবে এক ‘প্রাশ্নিকতা’-র রসতত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন সুদীপ্ত কবিরাজ। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে ‘মনে কী দ্বিধা রেখে চলে গেলে’ (১৯৩৭) গানের উল্লেখে। স্মরণ করা যেতে পারে, এর ঠিক বছর ছয় আগে, জীবনময় রায়কে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রশ্নবাচক অব্যয় আর প্রশ্নবাচক সর্বনামে যেহেতু ফারাক বিস্তর, তাই বানানের ক্ষেত্রেও ওদের আলাদা করে দেওয়াই সমুচিত। বিখ্যাত উদাহরণ ছিল তাঁর, ‘তুমি কি রাঁধছ?’ (প্রশ্নবোধক অব্যয়) আর ‘তুমি কী রাঁধছ?’ (প্রশ্নবাচক সর্বনাম)। আলোচ্য গানেও এই স্বাতন্ত্র একেবারে স্পষ্ট। ‘মনে কী দ্বিধা রেখে চলে গেলে’ বা ‘কী ভেবে ফিরালে মুখখানি’-তে তোমার দ্বিধা বা ভাবনার বিষয়টি আমার অজানা। অন্যদিকে, ‘তুমি সে কি হেসে গেলে’ বাক্যে তুমি আদৌ হেসে গিয়েছ কি না, তা নিয়েই আমার সংশয়। সুদীপ্ত কবিরাজের ধরিয়ে দেওয়া চিন্তার সূত্রে ভাবা যায়, এ দুয়ের ভেদ সম্পর্কে অতীব সচেতন রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় প্রাশ্নিকতার রূপভেদ ছিল কেমনতরো?
রবীন্দ্র-সমালোচনায় প্রাশ্নিকতার বয়ানকে নিয়ে আসার জন্য সুদীপ্ত সবিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে প্রবন্ধের মূল বিষয় বহির্ভূত একটি সিদ্ধান্তে আমাদের সামান্য সংশয় রয়েছে। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্যকে ভাষাবন্ধনে ধরার লক্ষ্যে, আরও অনেক মহান রচয়িতার মতো রবীন্দ্রনাথও একটা ‘সরল সমাধান’ খুঁজে বের করেছেন। সেটি হল, অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করার জন্য অস্তিত্বমূলক বাক্যকে প্রশ্নমূলক বাক্যে বদলে দেওয়া। নিসর্গচিন্তা প্রসঙ্গে আবার বলছেন তিনি, ‘নিসর্গের পৃথিবীতে কোনো সৌন্দর্য দেখলেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির আনন্দের কথা মনে হয়।’ রবীন্দ্রনাথের সার্বিক রচনাকর্মের নিরিখে এহেন বক্তব্য যে আরোহী-যুক্তিনিষ্পন্ন অতি-সাধারণীকরণ, তা প্রমাণের জন্য অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়, যদিও একটি নজিরই যথেষ্ট। ‘অপঘাত’ (১৯৪০) কবিতার কথাই ধরা যাক। আছে সেখানে, শুকনো নদীর চর, কেটে-নেওয়া আখখেত, জারুলের শাখায় কোকিলের প্রলাপ— চৈত্রের নিসর্গচিত্রণ। তবে অলস সে নেশার বাতাবরণ এক লহমায় কেটে যায়, সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় কর্তামি একেবারে অবান্তর হয়ে যায় কবিতার শেষ দুই পঙক্তিতে: ‘টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে/ ফিন্ল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।’
নিসর্গসৌন্দর্যের রূপটি যে নেহাতই নশ্বর, মানুষী জিঘাংসার সামনে তা যে বুদ্বুদের মতোই ফেটে পড়ে, কোনও মহামহিম ঈশ্বর যে ত্রাতার ভূমিকায় আসেন না– এমনতরো নিদর্শন রবীন্দ্র-কবিতায় আরও আছে।
নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার নিরিখে, অস্তিত্বের সীমানায় অবস্থিত, অভিবাসী, উদ্বাস্তু মানুষের রাজনীতিবিচ্ছিন্ন জীবনযাপনকে ‘নগ্ন জীবন’ (বেয়ার লাইফ’) নাম দিয়েছিলেন জর্জিও আগামবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রাজর্ষি দাশগুপ্ত ‘নগ্ন জীবন’-এর বিপরীতে নিয়ে এসেছেন ‘নগ্ন রাজনীতি’-র ধারণা। প্রস্তাব তাঁর, পরিযায়ী বা শরণার্থী বিষয়ীর ক্রমাগত মৃত্যু এড়িয়ে বেঁচে থাকার কৌশলের মধ্যেই নিহিত থাকে এই রাজনীতি। পৌরসমাজ বা রাজনৈতিক সমাজ থেকে পৃথক এই রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ‘ক্যামোফ্লাজ’-এর কথা বলেছেন তিনি। তিনটি ভিন্ন স্থানিক প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন মানুষের আলাদা রকমের জীবনযাপন পদ্ধতির কেস স্টাডি করে এ তত্ত্বায়নকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন রাজর্ষি। ‘ক্যামোফ্লাজ’, তাঁর মতে, ‘‘রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যক্তিকে শনাক্তকরণের প্রক্রিয়াকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা, পরিচিতির নিশ্চয়তার বদলে ক্রমাগত দ্বিধাকে প্রসারিত করা’-র প্রক্রিয়া। একইসঙ্গে আবার, ‘নিজের পরিচিতি নিয়ে নিরন্তর এই দ্বন্দ্ব রচনা ছদ্মবেশীকে ভঙ্গুর করে তোলে, অস্থির এই আমিত্ব বড় দুর্বল, রক্তাল্পতাগ্রস্ত।’’ কোনও সন্দেহ নেই, আজকের দুনিয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যার দিক-পরিবর্তন ও ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে (এর সঙ্গে জলবায়ুজনিত অভিবাসনকে জুড়লে ভয়াবহতার কোনও সীমা থাকে না) প্রবন্ধটি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বাংলা ভাষায় ‘নগ্ন-রাজনীতি’ আলোচনার গোড়াপত্তন সম্ভবত রাজর্ষির হাত ধরেই হল। ধন্যবাদ তাঁকে।
অভিজ্ঞতা
‘কলকাতা ২১’ পত্রিকার আরেকটি জরুরি দিক, প্রত্যেক সংখ্যায় কোনও না কোনও স্মৃতিকথা/অভিজ্ঞতাকে জায়গা করে দেওয়া। আগে আমরা পড়েছি সৌরীন ভট্টাচার্য এবং শেফালী মৈত্রের স্মৃতিচারণা, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মার্কস পড়ানোর অভিজ্ঞতা। চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত মেরুনা মুর্মুর লেখাটি সেসবের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার কোলাজে তৈরি হয়েছে এ লেখা; জানিয়েছে আমাদের, ভারতের প্রথম আদিবাসী আইপিএস অফিসার গুরুচরণ মুর্মু (লেখিকার বাবা) এবং শেলী মণ্ডলের (লেখিকার মা) সমাজবিধি বর্হির্ভূত যৌথযাপন ও তার নানা সংকটের কথা। তবে মেরুনার কৃতিত্ব সেখানেই শেষ নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ, রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক উচ্চমন্যতার চাপেতাপে বহুখণ্ডিত এক আত্মসত্তার নির্মাণালেখ্য তুলে ধরেছেন তিনি। আছে তাতে, আদিবাসী হওয়ায় মার্গসঙ্গীত বিষয়ে গবেষণার সুযোগ হারানোর ক্রূর বৃত্তান্তের পাশাপাশি আদিবাসীদের দেখতে কেমন, তা নিয়ে ভদ্রলোক সমাজের লোলুপ কৌতুহলের মুখোমুখি হওয়ার বিবরণ। উত্তমপুরুষে বিবৃত সেই বিষয়িতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বারবার ধাক্কা খাই আমরা। দয়াদাক্ষিণ্যের সহমর্মিতা নয়, লেখক-পাঠকের ভিতর সমমর্মিতার সেতু রচে মেরুনার আখ্যান।
পুনর্মুদ্রণ
পত্রিকার ‘পুনর্মুদ্রণ’ শাখাটিও জমকালো। এবারের সংখ্যায় রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর অর্থ ব্যবহার (১৮৭৬) সম্পাদনা করেছেন ইমন মিত্র। রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষীণতনু পুস্তিকাটি পাঠকের জন্য ছেড়ে রেখে, ইমনের উত্তরভাষ নিয়ে সামান্য কয়েক কথা বলা যেতে পারে। ১৮০০-১৮৭৬ সময়পর্বে বাংলা ভাষায় অর্থনীতিচর্চা বিষয়ে লিখেছেন তিনি। প্রেক্ষিত, ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিস্তারের রাজনীতি। জানছি সেখান থেকে, মুখ্যত ইংরেজি অর্থনীতিগ্রন্থের ছায়ানুবাদ হলেও, বাংলা বইগুলিতে মাঝেসাঝেই উঁকি দেয় স্বকীয় তত্ত্বপ্রস্তাব। রাজকৃষ্ণের অর্থ ব্যবহার যেমন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রিচার্ড হোয়েটলি প্রণীত Easy Lessons on Money Matters অবলম্বনে লেখা হলেও, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির প্রশ্নে লেখকের নিজস্ব চিন্তার ছাপ যথেষ্ট, আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে পলিটিকাল ইকোনমির সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টা করেছেন নিজের মতো করে।
মনে পড়ে আমাদের, এ বইয়ের বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত সাম্য (১৮৭৩) বইতে জোসেফ প্রুধোঁ-র ‘Property is theft’ বাক্যটির বাংলা তর্জমা করে দিয়েছিলেন বঙ্কিম: ‘অপহরণের নামই সম্পত্তি।’ জানিয়েছিলেন, সে অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নামই আইন। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, চিন্তার স্তরে এ দু’টি ধারা, দর্শন ও অর্থনীতির সংলাপ সেভাবে ঘটে ওঠেনি। উত্তরভাষ হিসেবে ইমনের লেখা ১৮৭৬ সালেই থেমেছে। তবে যে কোনও ভালো লেখার মতোই, তা আমাদের আগ্রহের সীমানাকে প্রসারিত করে। জানতে ইচ্ছে হয়, বাংলার চিন্তামহলে মার্কসের ভূত অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর, বাঙালির অর্থনীতি-ভাবনা বয়েছিল কোন খাতে? এরিক হবস্বম কলকাতায় মার্কসের চিন্তা প্রচলনের প্রথম নজির হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মাইকেল প্রোথেরো রচিত Political Economy (১৮৯৫) পাঠ্যপুস্তকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ‘অর্থনৈতিক তত্ত্ব’-র কোনও কাটান কি উঠে এসেছিল অন্ত্য উনিশ শতক, আদি বিশ শতকের বাঙালি চিন্তকদের অর্থনীতি বিষয়ক লেখালেখিতে?
কবিতা
‘কবিতা আর প্রবন্ধ ভাবনার দুই সমান্তরাল পথ’– এ বিশ্বাস থেকেই ‘কলকাতা ২১’-এর পথচলা শুরু হয়েছিল। চতুর্থ সংখ্যায় রয়েছে মৃদুল দাশগুপ্ত, শ্যামলকান্তি দাশ এবং সার্থক রায়চৌধুরীর কবিতা। স্বল্প পরিসরে কবিতার আলোচনা ফাঁদা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। ও ভার পাঠকের ‘পরে।
পড়া বই
ইতালীয় দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যচ্চা-র দ্য লাইফ অফ প্ল্যান্টস: এ মেটাফিজিক্স অব মিক্সচার (২০১৯) বইটি নিয়ে লিখেছেন শেফালী মৈত্র। প্রাচীন যুগ থেকে দর্শনচর্চায় নৃকেন্দ্রিকতার যে সমস্যা রয়ে গেছে, রয়ে গেছে উদ্ভিদের প্রতি দার্শনিকের অবজ্ঞাজনিত অনবধানতা– তার প্রেক্ষিতে বৃক্ষপ্রাণনাকে চিন্তার প্রবেশবিন্দু করে তোলার প্রস্তাব করেছেন ক্যচ্চা। সীমিত পরিসরে সেই প্রস্তাবের খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন শেফালী।
খালিদ এল-রুইয়েহেব প্রণীত দ্য ডেলেভপমেন্ট অফ অ্যারাবিক লজিক (১২০০–১৮০০) প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন অমিতা চ্যাটার্জি। ওই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায়, একেবারে বুনিয়াদী স্তর থেকে গবেষণার এলাকায় – যুক্তিবিদ্যার চর্চা যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল, তা বিস্ময়কর। গ্রিক অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিকাঠামোর অনুবর্তন নয়, বরং লজিক চর্চার নতুন গতিপথ যেভাবে খুঁজে নিয়েছিলেন আরবের বুধমণ্ডলী– তা বিস্তারে জানার আগ্রহ জাগায় অমিতার পাঠ-প্রতিক্রিয়া।
শেষে যা বলার, প্রতিটি প্রবন্ধের গদ্যেই সুস্পষ্ট যত্নের ছাপ। অভিনব বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য স্বাদু গদ্যশৈলী গড়ে নিয়েছেন রাজর্ষি এবং ইমন। দৃষ্টিসুখকর পত্রিকার প্রচ্ছদ আর মুদ্রণসজ্জা। আরও বেশি করে পাঠকের কাছে পৌঁছে যাক ‘কলকাতা ২১’।
কলকাতা ২১
চতুর্থ সংখ্যা
সম্পাদক: মৈনাক বিশ্বাস, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, বোধিসত্ত্ব কর
মূল্য ৩০০ (ভারতীয় টাকা)
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
