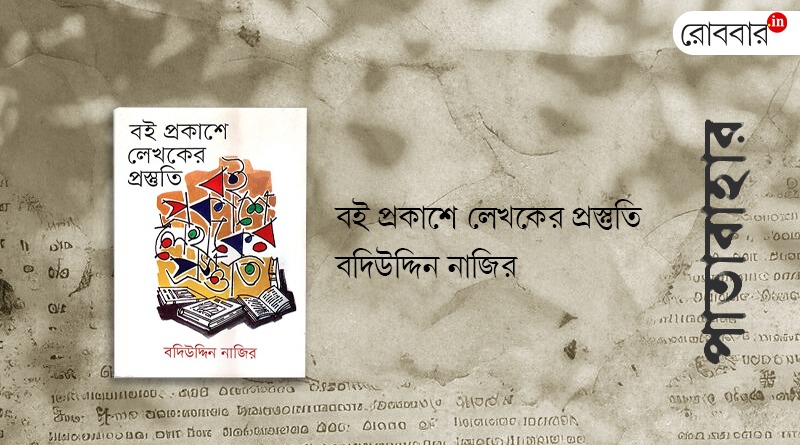
ঢাকার ‘কথাপ্রকাশ’ থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থ পদে পদে লেখককুলেরই পাশে দাঁড়িয়েছে। তথাপি আরও একটি অধ্যায়কে বিশেষ ভাবে ‘লেখকবন্ধু’ বলতে হবে। সেটি হল ‘প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি’। আগে আলোচিত কপিরাইটের সঙ্গে এই বিষয়ের নিকট আত্মীয়তা রয়েছে। ঢাকার কথা বলতে পারব না, তবে কলকাতার কিছু প্রকাশকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ পুরনো। কয়েকটি প্রকাশনা তো রীতিমতো ‘কুখ্যাত’। তরুণ লেখকদের এই বিষয়ে সতর্ক করেন ‘ঘরপোড়া’ প্রবীণরা।

‘বই প্রকাশে লেখকের প্রস্তুতি’ অনুসন্ধিৎসু লেখক এবং উৎসাহী প্রকাশক উভয়ের জন্য একটি ‘আত্ম-উন্নয়নমূলক’ কাজ। গ্রন্থ বিশেষজ্ঞ বদিউদ্দিন নাজির লিখিত বইটি কি বাংলা ভাষায় গ্রন্থপ্রকাশ সংক্রান্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাজ? এ বই প্রশ্ন তোলে– চলচ্চিত্র নির্মাণে বিশেষজ্ঞ ‘সম্পাদক’ থাকলে গ্রন্থ নির্মাণে থাকবে না কেন? ভেবে দেখলে পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ রিডিং, পেজ মেকআপ থেকে বইয়ের বিষয় বুঝে পুস্তানি-কাগজ নির্বাচন, প্রচ্ছদ থেকে বাইন্ডিং– সবটা মিলিয়ে একটি গ্রন্থ নির্মাণও এক দক্ষযজ্ঞ! বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এক্ষেত্রেও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে ‘প্রোডাকশান’। এই ‘প্রোডাকশান’ শব্দে আপত্তি তুলতে পারে লেখকসমাজ। শিল্পের ‘ব্যবসা’ করেও শিল্প যে ব্য়বসা, তা মেনে নিতে পারি না আমরা। জীবনানন্দ ধার করে কটাক্ষ করি, ‘বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা…।’ সেক্ষেত্রে বলে রাখি, ‘বই প্রকাশের প্রস্তুতি’ কেবল প্রকাশকের হয়ে কথা বলেনি, কবি-লেখকদেরও পাশে থেকেছে। কীভাবে?

এই গ্রন্থের এগারোটি অধ্যায়ই সেই উত্তর দিয়েছে। সেগুলি হল ‘পাণ্ডুলিপির বিষয় প্রকাশকদের পছন্দ অপছন্দ’, ‘লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা’, ‘বই লেখার জন্য গবেষণা’, ‘পাঠক আকর্ষণের অব্যর্থ তিনটি উপায়’, ‘বই লেখার কয়েকটি গুপ্ত বিপদ’, ‘কপিরাইট ও অনুমতিপত্র’, ‘থিসিস থেকে বই’, ‘রিভিজন ও সেল্ফ-এডিটিং’, ‘প্রুফরিডিং’, ‘বইয়ের ইনডেক্সিং বা নির্ঘণ্ট প্রণয়ন’ এবং ‘প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি’। শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যিটা হল, কপিরাইটের বিষয়ে অধিকাংশ লেখক এই ২০২৪ এ-ও ‘অশিক্ষিত’। এমনকী, বহু প্রকাশকের কাছেও বিষয়টা ‘জানা তবু অজানা’ টাইপ। অথচ একজন লেখকের অধিকার তাঁর কপিরাইট। যে ফসল তিনি ফলিয়েছেন মেধাবৃত্তির পরিশ্রমে, তার অধিকার বুঝে নেওয়াও এক রকমের নীতিশিক্ষা।

নাজিরের গ্রন্থ জানিয়েছে, কপিরাইট আইনের গুরুত্ব, কপিরাইট ও অনুমতিপত্রের সম্পর্ক, সৃজিত কর্মের ওপর লেখকের কপিরাইটের মেয়াদ, রচয়িতার নৈতিক অধিকার বা Moral Right। কখন লেখকের অনুমতির প্রয়োজন হয় প্রকাশের জন্য, কখন হয় না ইত্যাদি বিষয়ে। এই অধ্যায়টি যাকে বলে ‘লেখকবন্ধু’। তবে বর্তমান গ্রন্থটি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, তাই সেদেশের কপিরাইট আইন অনুযায়ী আলোচনা হয়েছে। যদিও ষষ্ঠ অধ্য়ায়টি পাঠে উপকৃত হবেন এপার বঙ্গের লেখকরাও, এ হলফ করে বলা যায়। উল্লেখ্য, ‘কপিরাইট ও অনুমতিপত্র’ অধ্যায়টি নাজির শুরু করেছেন ভারতীয় লেখক যিনি সৃজনশীল সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনজীবীও, সেই ড. কল্য়াণ চক্রবর্তী কাউকানালার উদ্ধৃতি দিয়ে। অন্ধ্রের বাসিন্দা এই তরুণ লেখকের বক্তব্য, ‘The right to be attributed as an author of a work is not merely a copyright, it is every author’s basic human right’। সহজ বাংলায়– লেখার কপিরাইট আদতে লেখকের মানবাধিকার।

ঢাকার ‘কথাপ্রকাশ’ থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থ পদে পদে লেখককুলেরই পাশে দাঁড়িয়েছে। তথাপি আরও একটি অধ্যায়কে বিশেষ ভাবে ‘লেখকবন্ধু’ বলতে হবে। সেটি হল ‘প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি’। আগে আলোচিত কপিরাইটের সঙ্গে এই বিষয়ের নিকট আত্মীয়তা রয়েছে। ঢাকার কথা বলতে পারব না, তবে কলকাতার কিছু প্রকাশকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ পুরনো। কয়েকটি প্রকাশনা তো রীতিমতো ‘কুখ্যাত’। তরুণ লেখকদের এই বিষয়ে সতর্ক করেন ‘ঘরপোড়া’ প্রবীণরা। মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী, সেই সংখ্যক বই প্রকাশ না করা, জমকালো স্বপ্ন দেখিয়ে নিম্নমানের প্রোডাকশন, ভুলে ভরা প্রুফ, বিজ্ঞাপন না দেওয়া, বিপণীতে বই রাখা নিয়ে মিথ্যাচার… অভিযোগের শেষ নেই। অথচ গোড়ায় গলদ কিন্তু লেখকের। কেন?
…………………………………………….
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার, পাইলট হওয়ার মতো লেখক বা শিল্পী হয়ে ওঠার ছাঁচে ফেলা পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা ট্রেনিং এখনও অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। ভবিষ্য়তে তা হলে ‘শিল্পকর্ম’ থেকে ‘শিল্প’কে বাদ দিতে হবে, মন খারাপ করে ‘কর্ম’ একা পড়ে থাকবে। তবে ‘পাঠক আকর্ষণের অব্যর্থ তিনটি উপায়’ এবং ‘বই লেখায় কয়েকটি বিপদ’ অধ্যায়ে লেখকসমাজের উদ্দেশে যে পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশে বিগত পঞ্চাশ বছর গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকা নাজির, তা গ্রহণযোগ্য।
…………………………………………….
যেহেতু প্রকৃত প্রশ্ন, প্রকাশকের মৌখিক আশ্বাসে মন ভিজবে কেন লেখকের? সামান্য় কলম কেনার সময়ও তো কোম্পানির মৌখিক দাবিতে বিশ্বাস করি না। কলমকেও হাতেকলমে ঘষে দেখি কালি পড়ে কি না! এক্ষেত্রে লেখক-প্রকাশক চুক্তি সেই যৌক্তিকতার কাজই করে। যেখানে কয়েক হাজার টাকার একটি প্রোডাকশন, সেখানে আইন মোতাবেক ‘কাগজ’ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণেই নাজির সাহেব এই অধ্যায়ে ‘চুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং বইয়ের জন্য লেখকের অর্থনৈতিক অধিকার’ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও অতি গুরুত্বপূর্ণ একাদশ অধ্যায়ে ‘প্রকাশকের দায়িত্ব’, ‘লেখকের রয়্যালটি ও অন্য়ান্য পাওনা প্রদান’, ‘লেখকের দায়িত্ব’, ‘স্বাক্ষর’, ‘চুক্তিপত্রের অবয়ব’, ‘চুক্তির বিষয়ে শেষ কথা’ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে।

তবে লেখক-প্রকাশক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কেই আটকে থাকেনি এ গ্রন্থ। গ্রন্থরচনা তথা সম্পাদনার বিষয়েও মূল্যবান পরামর্শ রয়েছে। এমনকী, ‘লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা’ অধ্যায়ে কীভাব একজন লেখক অ্যামেচার থেকে পেশাদার হয়ে উঠতে পারেন, সেই বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে সেই ‘অভ্য়াস’ বা রুটিন পালন করলেই কেউ দুরন্ত কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক হয়ে উঠতে পারবেন কি না, তা এক প্রশ্ন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার, পাইলট হওয়ার মতো লেখক বা শিল্পী হয়ে ওঠার ছাঁচে ফেলা পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা ট্রেনিং এখনও অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। ভবিষ্য়তে তা হলে ‘শিল্পকর্ম’ থেকে ‘শিল্প’কে বাদ দিতে হবে, মন খারাপ করে ‘কর্ম’ একা পড়ে থাকবে। তবে ‘পাঠক আকর্ষণের অব্যর্থ তিনটি উপায়’ এবং ‘বই লেখায় কয়েকটি বিপদ’ অধ্যায়ে লেখকসমাজের উদ্দেশে যে পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশে বিগত পঞ্চাশ বছর গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকা নাজির, তা গ্রহণযোগ্য।
‘পাঠক আকর্ষণের অব্যর্থ তিনটি উপায়’ অধ্য়ায়ে গ্রন্থ নির্মাণ পরিকল্পনা বা ‘ছক’ এর কথা বলা হয়েছে। উপযুক্ত শিরোনামের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও গ্রহণযোগ্য লেখার স্টাইল, যেখানে থাকতেই হবে ‘হুক’, জানিয়েছেন নাজির। কী এই ‘হুক’? গ্রন্থের ক্ষেত্রে ‘হুক’ বা আঁকশি বলা হয়েছে লেখা শুরুর এক বা একাধিক চুম্বক লাইনকে। যা আকর্ষণ করবে পাঠককে। দরজা সুন্দর হলে ঘরে ঢুকতে চাইবেন পাঠক। আর ‘বই লেখায় কয়েকটি বিপদ’ বলতে বোঝানো হয়েছে, লেখায় ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বিষয় আনা, ‘আলস্যে’র কারণে প্রাথমিক লেখা প্রকাশ করা, ঘষা-মাজা না করা, ‘ত্রুটিপূর্ণ তথ্য’, ‘পারম্পার্য’ না রাখা, অহেতুক ‘বাগড়ম্বরতা’, ‘লোকলজ্জার ভয়ে’ সত্যিটা না বলা, কোনও বিষয়ে ‘আগ্রহ নেই তবু লেখা’ ইত্যাদি। লেখক মাত্রাই জানেন উল্লিখিত বিষয়গুলি লেখা ও লেখক উভয়কেই কীভাবে ধ্বংস করে।
‘বই প্রকাশে লেখকের প্রস্তুতি’র ব্লার্বে বলা হয়েছে, ‘পেশাদার, অপেশাদার, শৌখিন– সব ধরনের লেখক এ বইয়ে শিক্ষণীয় ও অনুশীলনযোগ্য কিছু না কিছু পাবেনই।’ সামান্য শুধরে বলতে হয় শুধু লেখক নয়, প্রকাশকদের জন্য়ও শিক্ষণীয় বহু কিছু রয়েছে ৩৭১ পৃষ্ঠার ঝকঝকে এই ‘প্রোডাকশন’-এ। আরেকটা কথা, বাংলাদেশে যেমন এ ধরনের বই এই প্রথম, পশ্চিমবঙ্গেও এমন গ্রন্থ নেই। অতএব, পাঠক, লেখক-প্রকাশক উভয় সমাজের তরফে জনাব বদিউদ্দিন নাজির সাহেবকে বড় ধন্যবাদ ও বড় কৃতজ্ঞতা জানাতেই হচ্ছে। কারণ বড় কাজ করেছেন তিনি।
বই প্রকাশে লেখকের প্রস্তুতি
বদিউদ্দিন নাজির
কথাপ্রকাশ
(ঢাকা, বাংলাদেশ)
৬০০্
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
