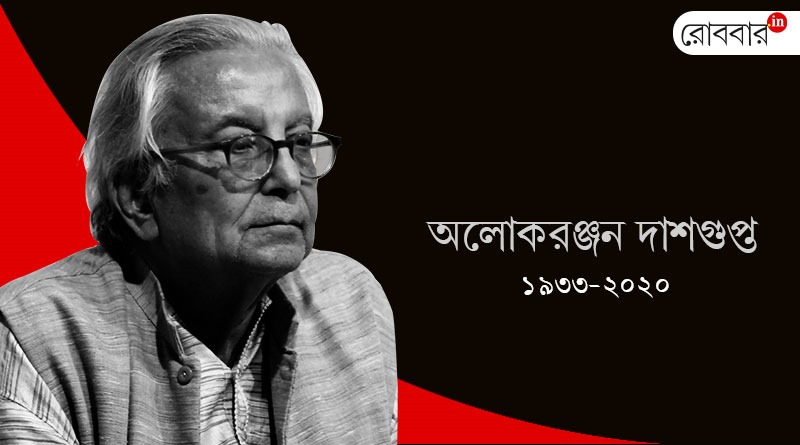
উপসাগরীয় যুদ্ধের পর কত শরণার্থী মানুষের সঙ্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর গাঢ় আত্মীয়তা! কখনও এই শরণাগত মানুষদের আশ্রয় দিয়েছেন বাড়িতে, শিখিয়েছেন জার্মান ভাষা আবার কঙ্গো ভাষার শরণার্থী কবি ময়প্পো মোয়েম্বা তাঁর ভীষণ বন্ধু। কেন বলছি এই কথা? কেননা তাঁর কবিতার বড় জায়গা জুড়ে আছে সমগ্র অস্তিত্বের জন্য অনন্য মূল্যবোধ।

‘দেশ’ পত্রিকার ১৯৭২ সালে মে মাসের এক সাহিত্যসংখ্যায় ‘নিজেকে নিয়ে’ এক দীর্ঘ রচনায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছিলেন: ‘আত্মবিবরণী অথবা আদর্শ বিবৃতির পথে না গিয়ে পাঠকের সঙ্গে আমি আড়াআড়ি অথচ নিবিড় আত্মীয়তা চেয়েছি… পরিণতিশীল পাঠককে আমি নিগূঢ় আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার স্বরলিপি পরিকীর্ণ বসতির গর্ভগৃহে যেখানে আমার সমস্ত দুর্বলতা ও সার্থকতাকে তিনি নিজে থেকে শনাক্ত করে নিতে পারেন’। জবাবদিহির টিলায় দাঁড়িয়ে তিনি একজন চিরকালীন আড়ভাবুক (Querdenker)। এই তো কয়েক বছর আগের কথা। শীতের সকাল। রোদ এসে পড়েছে তাঁর ঘরের টেবিলে। বই-বোঝাই ছোট্ট ঘরে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন গ্যোয়েটের দিভানের ওপর। West-öestlicher Divan/১৮১৯। তাঁর মুখের কুঞ্চিত চামড়ার ভেতর দিয়ে একটি শিরা তখন তিরিতির করে কাঁপছে। আমার হাতে ধরা আছে এই বইয়েরই অনুবাদ। ‘প্রাচী-প্রতীচীর মিলনবেলার পুঁথি’। যে বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখা আছে: ‘মৌলবাদের বিরুদ্ধে, প্রেমের সপক্ষে’।

আমি এসেছি এই বইটিকে ঘিরে সাক্ষাৎকার নিতে। তার আগে দিভান থেকে নিজের আরোধ্য একটি পঙ্ক্তি ‘ঈশ্বরের নিজস্ব এই প্রাচী!/ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতীচী’ আমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন। এই মন্ত্র দিয়েই তো শুরু হয় তাঁর কবিতাসংগ্রহের ভূমিকা। যে মন্ত্র তাঁর মনোভঙ্গির ভেতর থেকে গেছে কবিতা রচনার বিশেষ একটি পর্যায় অবধি। এই সূত্র ধরে তাই সেদিন তাঁকে প্রশ্ন করে বসেছিলাম, ‘‘আপনি বরাবর ‘যুগাবর্তে’ শামিল হতে চেয়েছেন ‘কবিতাকে শাশ্বতে ন্যস্ত’ রেখেই…!’’ চকিতে সেদিন তাঁর উত্তর এসেছিল: ‘সমীপকালীন থেকে শাশ্বতের প্রতি আমার মজ্জাগত টান, সেখানে কোনও মেরুময়তা আছে বলে আমার মনে হয় না।’ এখানেই তাঁর কবিতার ইতিহাসবোধ এক অনন্ত পথ-পরিক্রমা হয়ে ওঠে। বিষয়টা আরও প্রসারিত করে বলি। কীভাবে?

১৯৭২ সালে লেখা ‘নিজেকে নিয়ে’ যে গদ্যরচনার কথা বলছিলাম প্রথমে, তার পরের বছর প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর চতুর্থ কবিতার বই ‘ছৌ-কাবুকির মুখোশ’। যে বইতে আমরা দেখতে থাকি এক বড় রকমের বদলের চিহ্ন। যিনি ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’-য় লিখেছিলেন ‘একটা শালিখ অমাঙ্গলিক, দুটো শালিখ ভালো,/তিনটে শালিখ শুধু চিঠির ডাকঘর বসাল।’ শান্তিনিকেতন, কলকাতা বা বাংলার গ্রামকে সামনে রেখেও ‘ছৌ-কাবুকির মুখোশ’-এ তাঁর কবিতার শিরোনাম হয়ে উঠবে ‘ট্র্যাক্টর চালাও নারী, ট্যুবিঙ্গেনে’, ‘জাপানি ট্যুরিস্ট, আমি এবং শিলার’ কিংবা তিনি বলে উঠবেন এইসব অক্ষরমালা: ‘হ্যাঁ, আমি– আমিই প্রথম হয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমার সেই শ্রেষ্ঠতা খারিজ করে দিয়েছিল/যেহেতু আমি নিগ্রো’ বা ‘খুব সাবধান/লোকটার নাম হ্যোল্ডারলীন/ছ’ফুট উঁচু/বাদামি চুল/মন-মজানো উঁচকপালে/বাদামি ভুরু বাদামি চোখ অ-ঋজু নাসা/খুব সাবধান/হ্যোল্ডারলীন!/হ্যোল্ডারলীন!’ এইসব কবিতা যখন তিনি লিখছেন ততদিনে তাঁকে জার্মানি চলে যেতে হয়েছে ভারততত্ত্ব বিষয়ে পড়ানোর কাজে। পারিপার্শ্বের সঙ্গে বদলে গিয়েছে শব্দচর্যা। গালফ যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আরও বদলে যাবে অলোকরঞ্জনের কবিতার আকাশরেখা: ‘গণসমাধি দেখে বুঝিনি একবারও/আমার বন্ধুটি কোথায় শুয়ে আছে/বুকপকেটে তার গুঁজে কি রেখেছিল/গীতাঞ্জলি থেকে সান্ত্বনার স্তোক?’
এই পর্বে অলোকরঞ্জনের কবিতার শুরুতে আঁদ্রে ব্রেতোঁর শ্লোক– ‘শিল্পের মুক্তি বিপ্লবের জন্য’ হয়ে ওঠে একপ্রকার ঘোষণা। রুমানিয়ার ক্ষুব্ধ কবি মীর্চা দীনেস্কু হয়ে যান প্রিয় কবি! যেখানে তাঁর কবিতায় আলজেরিয়ার সতীর্থ হামিদ বারুদি নির্বাসনের গান বাঁধেন। গ্যাস-মুখোশ, সাইরেন, যুদ্ধের উদ্বাস্তু, বারুদ বৈরাগ্য, মিত্রপক্ষ, ক্রুজ মিসাইলের মতো শব্দে তাঁর কবিতা ভরে ওঠে। শুধু কি তাই!
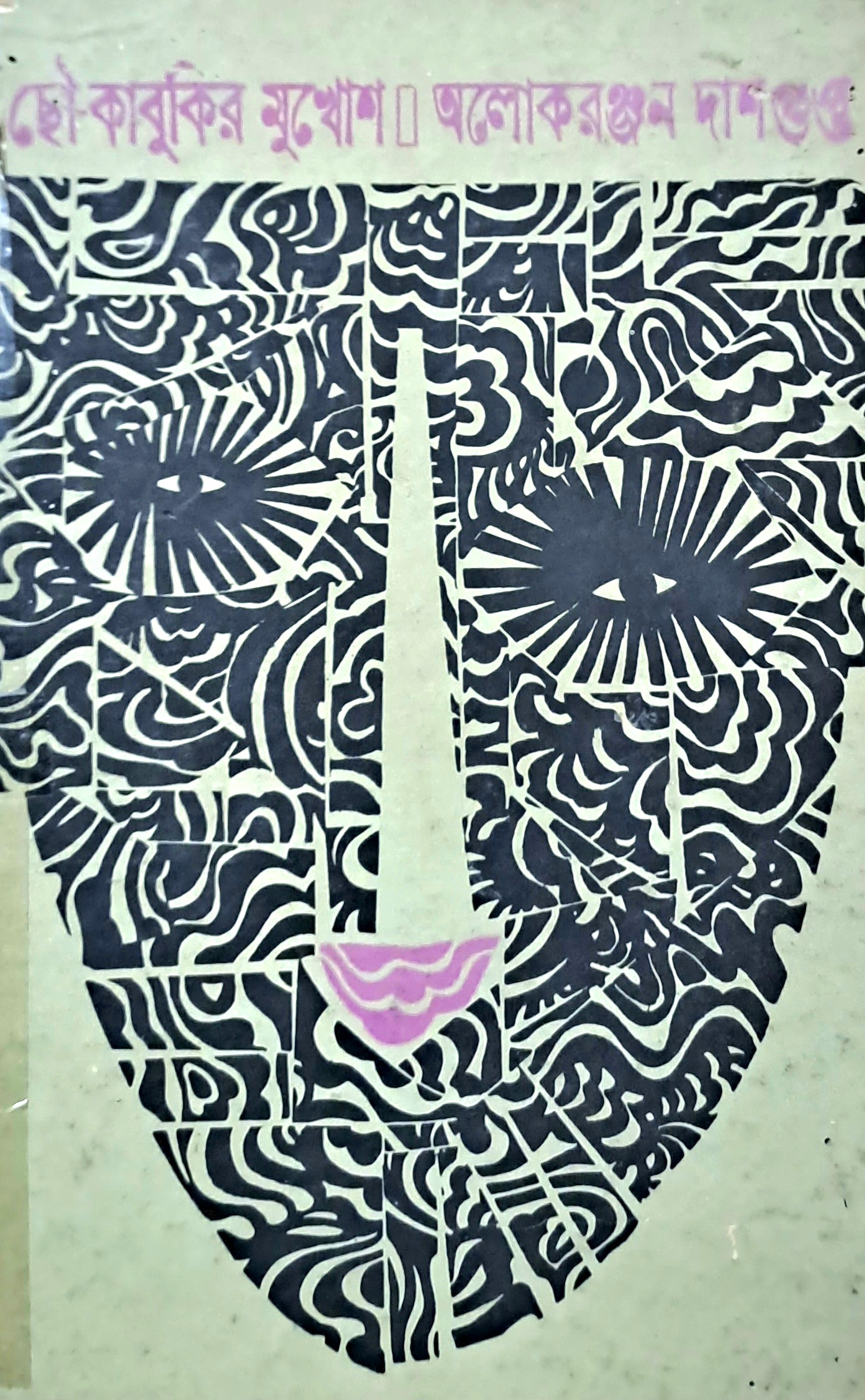
উপসাগরীয় যুদ্ধের পর কত শরণার্থী মানুষের সঙ্গে তাঁর গাঢ় আত্মীয়তা! কখনও এই শরণাগত মানুষদের আশ্রয় দিয়েছেন বাড়িতে, শিখিয়েছেন জার্মান ভাষা আবার কঙ্গো ভাষার শরণার্থী কবি ময়প্পো মোয়েম্বা তাঁর ভীষণ বন্ধু। কেন বলছি এই কথা? কেননা তাঁর কবিতার বড় জায়গা জুড়ে আছে সমগ্র অস্তিত্বের জন্য অনন্য মূল্যবোধ। যেখান তাঁর প্রস্বর অনুভব করা যায়। ইতিহাসের দিক থেকে নিজের শব্দ দিয়ে তিনি অনবরত কাজ করে গেছেন শান্তির সপক্ষে। মৌলবাদের বিরুদ্ধে। কবির দায়বদ্ধতায়। যা ছিল তাঁর অঙ্গীকারব্রত। ঠিক লিরিক কবিতার অক্ষয় কবর নয়, অলোকরঞ্জনের স্পষ্ট ভাবনা ছিল: ‘চারিদিকে যে কাণ্ডকারখানা ঘটছে, কবিতা হবে তার ভূকম্পলেখ। এখন বিহারীলালের মতো সরলভাবে হেঁটে মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়াটা আর কবিকে মানায় না।’ যে বিশ্বচেতনা থেকে লেখা যায়: ‘সাদী-র ছিল গুলিস্তান, শিল্পসরস্বতীকে নজরানা/দিতে হলেও সুফী কবির ডানা/ছেঁটে দেবার স্পর্ধা কারো ছিল না; নজরুল/যতোটা বিপ্লবী ছিলেন ততোটাই মঞ্জুল;/…লিখতে গিয়ে দেখছি আজ যোজনব্যাপী গুলবাগিচা, আমার তকদির:/বিবদমান বন্ধুদের গুলিগালাজ, জম্মু ও কাশ্মীর!’
এপিকের ইতিহাস আর পুরাণও তাঁর কবিতার উৎস হয়ে ওঠে। যাকে বলা চলে পঠনপাঠনের অনুষঙ্গ। তাইরেসিয়াস, জিউস, হাফিজ কিংবা বুদ্ধকে বুনে তুলেছেন কবিতার পিলসুজে, বন্ধু বা অগ্রজরাও কবিতায় সতীর্থ হয়ে আছেন সময়সন্ধির দাবিতে। শম্ভু মিত্র বা বিজন ভট্টাচার্যকে তাঁর উচ্চারণে খুঁজে পাই। ‘শতভিষা’ থেকে বেরনো বইয়ের নাম হয় ‘দুই বন্ধু’। এ-যাবৎ অপ্রকাশিত তাঁর সাহিত্যিক টীকা-টিপ্পনী আর ডায়েরি থেকে যদি তুলে ধরি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর সঙ্গে কথোপকথনের খসড়া (যা একটি অভিভাষণ ও লেখার প্রস্তুতি) তাহলে এই ভাবনার উৎসমুখ ধরা সহজ হবে। যে খসড়ায় তিনি লিখে রেখেছেন:
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র: ফাউস্টের তর্জমা করো, আমি সুর দেব।
অলোকরঞ্জন: ফাউস্ট?
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র: এর মধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্যের নির্যাস আছে।
এর পাশে নীল কালিতে লেখা রয়েছে: ‘তিনি Tradition শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন’।
এই ভাষণে তিনি ঐতিহ্য শব্দটির পাশে দু’দণ্ড দাঁড়িয়েছিলেন বলে জানি। এইরকম কত বোধের ইতিহাস অলোকরঞ্জনের লেখায় আর বক্তৃতায় লুকিয়ে আছে আগামী পাঠকের জন্য। যা তাঁর কবিতার নির্যাসকেই চিহ্নিত করে। আজ সময় এসেছে তাঁর কবিতা-গদ্য-অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে পড়ার। কীসব মারাত্মক কাজ সেখানে লুকিয়ে! না হলে বড় অন্যায় হবে। তাঁর দীর্ঘ জীবনের পথটুকু আমাদের জানা দরকার।
যে পথে তিনি বলতে পারেন ‘আমার লিখতে-চাওয়ার ইতিহাস হয়তো চিরায়তের সঙ্গে সমকালীনের অন্তর্বয়নের সমাচার, কখনো সরাসরি কখনো-বা একান্তর আড়বুনুনিতে’। তাই তার শেষ কবিতার বইয়ের নাম হয় ‘বাস্তুহারার পাহাড়তলি’। যে সেতুপুরুষ নিজের কবিতায় রেখে যান জীবনবোধের আত্মসংঘাত, জগৎজোড়া শরণার্থী মানুষের মুখচ্ছবি আর এক অনশ্বর প্রত্যয়ের জাদুমন্ত্র যা দিয়ে চেনা যায় শিল্পিত স্বভাব। এই স্বভাবের সঙ্গে আজ আমাদের তারামৈত্রী হয়ে যাক।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
