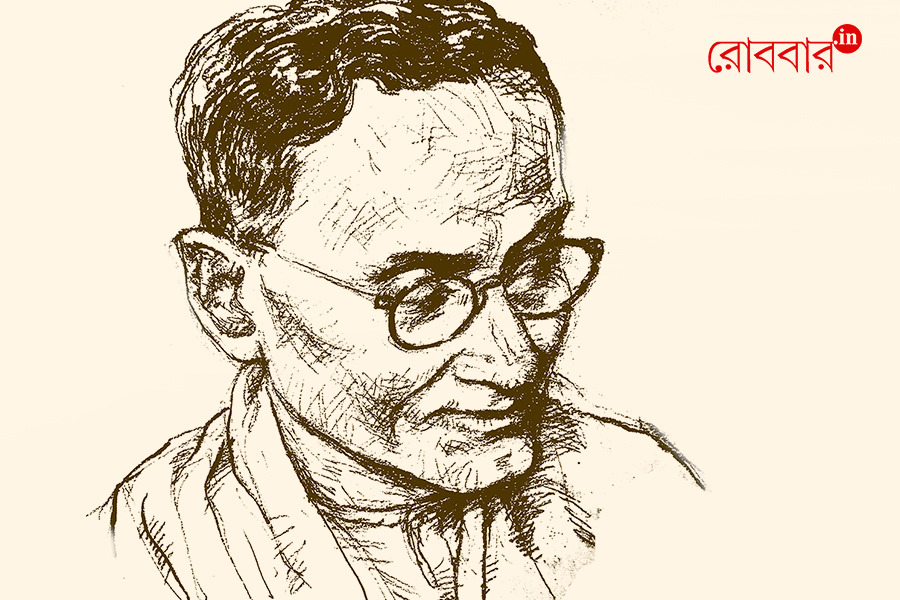
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বহু মানুষের আনাগোনা। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিভূতিভূষণের কলমে উঠে আসে ‘পৃথ্বীরাজ’ বা ‘কুইন অ্যান’ গল্পের রায়সাহেবদের তোষামোদি, ‘বি-এন ডব্লুর ব্রাঞ্চ লাইনে’ কি ‘কৈকালার দাদা’-র রেলকর্মী ও রেলযাত্রীদের ধরনধারণ, ‘গজভুক্ত’র মেস’বালক’দের বালখিল্য আচার আচরণ। ‘হার-জিত’ বা ‘যুগান্তর’-এর তরুণ রোমান্সই হোক কিংবা ‘পূর্ণ চাঁদের নষ্টামি’ বা ‘হোমিওপ্যাথি’ গল্পে দরকচা মেরে যাওয়া দাম্পত্যের রস-নীরস বার্তা, তাঁর পর্যবেক্ষণে ত্রুটি নেই। আজ, ২৪ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন।
প্রচ্ছদ: দীপঙ্কর ভৌমিক

বন্ধুর বিয়ে। তবে বিয়ে নিয়ে বরের যত আগ্রহ, বরযাত্রী যাওয়ার জন্য বরের বন্ধুদের উত্তেজনা বুঝি তাকেও ছাপিয়ে যায়। কারও সাজসজ্জার দিকে বাড়তি নজর, কারও নজর চপ-কাটলেট-মিষ্টি সরিয়ে রাখায়, আর সকলেরই মনে কৌতূহল বাসরঘরের তামাশা নিয়ে। আসলে কৌতূহল যৌবনের। আচমকা অপরিচিত তরুণীদের মুখোমুখি হয়ে পড়া, একটু আধটু সাহচর্য মেখে নেওয়ার দ্বিধাজড়িত আবেগ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে সময়ে ‘বরযাত্রী’ গল্প লিখছেন, সেই বিশ শতকের গোড়ার দিকে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে অচেনা নরনারীর অবাধ মেলামেশা নেহাতই কষ্টকল্পনা। তার দরুন এতটুকু ছোঁয়া আর এতটুকু কথার পুঁজি নিয়ে মনে মনে জাল বোনা চলে। সেখানে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানই সেই ছাড়পত্র, যা সেই মানস সফর পেরিয়ে রক্তমাংসের মানুষের স্পর্শ-গন্ধ নিয়ে আসে।

এই সামাজিক অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠানের সূত্রে মানুষের সঙ্গলাভ, একে নিজের জীবন দিয়ে আহরণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। প্রবাসের স্বজাতিবিহীন জীবন পেরিয়ে বাঙালি সমাজে পা রেখে পাওয়া মুখর জীবনকে তিনি যেন দু’চোখ ভরে দেখে গিয়েছেন। যে ‘বরযাত্রী’ গল্পের প্রসঙ্গে এ লেখার শুরু, সে গল্পের কে গুপ্ত-র সঙ্গে তাঁর মিল পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইন্টারমিডিয়েট-ইন-আর্টস পড়তে বিহার থেকে বাংলায় এসে দু’বছরের জন্য শিবপুরে থাকার সুযোগ মিলেছিল বিভূতিভূষণের। ১৯১২ সালে তিনি ভরতি হন রিপন কলেজে। রাজস্কুলে ৪০টা ছেলের মধ্যে যে ছিল পুরোভাগে, কলকাতার কলেজে বৃত্তি পাওয়া স্কলারদের ভিড়ে সুদূর বিহার থেকে আসা সেই ছাত্রকে ভেসে থাকার লড়াই করতে হয়েছিল বইকি। তবুও এই শিবপুর-বাস যেন তাঁর জীবনের অর্ধেকটাই জুড়ে আছে, পরে বলেছেন নিজেই। বাঙালিত্বকে যিনি মনে করতেন ‘একটা পাড়ার মধ্যে একটা বাড়ীর যে নিজস্বতা’, সেই আপন ঘরে তাঁকে টেনে নিয়েছিল শিবপুর। আর সেই তিনিই কে গুপ্ত-র বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে, ‘বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মহকুমার স্কুল হইতে পাস করিয়া কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এখনও কথায় পারিয়া উঠে না।’ প্রবাস থেকে বাংলায় আসা যে ছেলেটি সমবয়সি বাঙালি যুবকদের থেকে মাঝে মাঝেই খোঁচা বা ঠাট্টা উপহার পায়, তবুও বন্ধুত্বের টান ছেড়ে সরতে পারে না। হয়তো সে টান কেবল বাঙালি বন্ধুদের নয়, তার অচেনা বাংলাদেশ আর বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার টানও।

জন্মসূত্রে বিভূতিভূষণ যে মাটিতে বেড়ে উঠেছেন, তা বাঙালি সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে। ১৮৯৬ সালে প্রবাসেই তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠার একটা পর্বও কেটেছে সেখানেই। পণ্ডৌল নামে উত্তর বিহারের সেই অঞ্চল না শহর, না গ্রাম। নিস্তরঙ্গ এক গঞ্জজীবন। এক প্রান্তে নীলকুঠি, নতুন যুগের অভিজ্ঞান বলতে ওইটুকুই। গায়ে গায়ে লাগা দু’ঘর বাঙালি। সেকালের বাবুদের কোয়ার্টার হিসেবে মেটে বাড়ি, সেখানেই বসবাস। ‘শিক্ষা-সংকট’ গল্পের সেই অজ পাড়াগাঁ যেন, ‘চারিদিকে টানা মাঠ, মাঝখানটিতে স্টেশন আর গোটাকতক কোয়ার্টার্স। তারের বেড়ার বাহিরে এখানে ওখানে ছড়ানো দুইচারিটা দরিদ্র চালাঘর– থাকে দশাই, নবাবজান, বুধনী, তেতলী, দুখিয়ার মা। কেহ কুলীর কাজ করে, কেহ ইঞ্জিনের ছাই বাছিয়া বাবুদের কয়লা যোগায়, কেহ মালগুদাম ঝাঁট দিয়া ধান-দম বাছিয়া দিন গুজরান করে।’ এই পরিস্থিতিতে বাংলা থেকে দূরে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা বাঙালি পরিবারে জাঁকিয়ে বসে বিচ্ছিন্নতার বোধ। শিশুমনে হয়তো সে বিচ্ছিন্নতার ঢেউ লাগে না, কিন্তু পরোক্ষে তার বেড়ে ওঠাকে ঘিরে থাকে সেই পরিস্থিতিই। যে কথা পরবর্তীকালে বুঝেছেন লেখক। বুঝেছেন, পরবাসে দুই প্রজন্মে বাংলা ভাষা ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা বড় কঠিন। ঘরের কথাতেও যখন বড়কি ভৌজি (বড় বউদি), ছোটকি ভৌজি (ছোট বউদি), কটোরা (বাটি) চালু হয়ে যায়, তখন শিশুর সদ্য শেখা বাংলা ভাষাতেও মৈথিলি টান বসত পাতে। সন্তানের বাঙালি শিকড়ে সার জল দিতে তাই নিয়ম করে বাংলা পড়াতে বসান বাবা, আর অবশেষে চাতরা-শ্রীরামপুরের আদিবাড়িতেই ছেলেদের পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।
……………………………………………….
চাতরার পাঠশালায় পড়ার সময়েই বালকের মাথায় চেপে বসল ভবঘুরেবৃত্তি বা বাউন্ডুলেপনার ভূত। সেই ভূতের বরেই হয়তো, দিশা খুঁজে পেয়ে গেল উত্তরজীবন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির গোড়ায় ছিল ঘোরার এই নেশা– লেখকের ভাষায় ‘ব্যসন’। তাঁর আত্মকথায় সেকালের কলকাতা পায়ে হেঁটে ঘোরার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিনি বলতেন নেশা, ‘শিবপুর থেকে নিয়ে সর্বত্রই বাঙ্গালী টুকরা টাকরা কুড়িয়ে বেড়ানো’। শিবপুর ফেরিঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে হেঁটে কলেজ, সেই পথের পরিধিই ক্রমশ বাড়ে। নিজেই লিখেছেন, “বর্ষায়’ গল্পের নয়নতারার দ্বিপ্রাহরিক তাসের মজলিশে যে গেছি, তাও প্রায় নিরুদ্দেশভাবেই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে গিয়ে।’’
……………………………………………….
উপন্যাসের ছলে লেখা আত্মজীবনী ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’-তে সেই বিচ্ছিন্ন বাঙালিয়ানার আঁচ লেগেছে বটে। তবে বোঝা যায়, বিচ্ছিন্নতাকে দখল দেওয়ার চেয়ে আশপাশের মানুষকে চোখে চোখে জুড়ে নেওয়ার দিকেই ঝোঁক শৈলেনের। ভিড়ের মধ্যেও সে আলগা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতায় ভর করেই বুঝি ভিড়ের প্রতিটি মানুষের প্রতি তার চোখ পড়ে, কোনও একজনকে সে দৃষ্টি আঁকড়ে থাকে না। ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’-র এই শৈলেন যে বিভূতিভূষণের আত্মপ্রতিকৃতি, সে কথা অনেকেই বলেছেন। কেবল আত্মজৈবনিক উপন্যাসেই নয়, পথচলতি মানুষকে দেখার সে সাক্ষ্য মেলে বিভূতিভূষণের নিজের কথায়, ‘জীবন-তীর্থ’-এও। সেই ছেলেবেলাতেই যখন বিহার থেকে দেশের বাড়িতে ফিরছেন তাঁরা, বয়স মোটে বছর সাত-আট, রেলগাড়িতে ঘুম ভেঙে নজর করেছেন যাত্রী, ফেরিওয়ালা, সকলকে। বালক বিভূতিভূষণের পর্যবেক্ষণ, যাঁরা জিনিস বিক্রি করছেন, তাঁরা ছাড়া সবাই ‘আমাদের মতোই কথা বলছে’! অতএব প্রশ্ন, ‘এরা কারা বাবা?’
‘এরা বাঙ্গালী।’
‘আমরাও তো তাই।’
‘হ্যাঁ, তাছাড়া কী হব?’
‘তা এত কোথা থেকে এল বাবা?’
দাদা বলল, ‘এটা যে বাংলাদেশ রে। কী বোকা বিভূতিটা, বাবা।’

পরবাসে যা হয়নি, এই বাংলাদেশে এসেই তা হল। চাতরার পাঠশালায় পড়ার সময়েই বালকের মাথায় চেপে বসল ভবঘুরেবৃত্তি বা বাউন্ডুলেপনার ভূত। সেই ভূতের বরেই হয়তো, দিশা খুঁজে পেয়ে গেল উত্তরজীবন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির গোড়ায় ছিল ঘোরার এই নেশা– লেখকের ভাষায় ‘ব্যসন’। তাঁর আত্মকথায় সেকালের কলকাতা পায়ে হেঁটে ঘোরার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিনি বলতেন নেশা, ‘শিবপুর থেকে নিয়ে সর্বত্রই বাঙ্গালী টুকরা টাকরা কুড়িয়ে বেড়ানো’। শিবপুর ফেরিঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে হেঁটে কলেজ, সেই পথের পরিধিই ক্রমশ বাড়ে। নিজেই লিখেছেন, “বর্ষায়’ গল্পের নয়নতারার দ্বিপ্রাহরিক তাসের মজলিশে যে গেছি, তাও প্রায় নিরুদ্দেশভাবেই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে গিয়ে।’’ শিবপুরের বাঙালি সমাজে মেলামেশার সূত্রে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের ভোজে নিমন্ত্রণ, পঙ্ক্তির অপেক্ষা আর পঙ্ক্তিতে বসার মধ্যেই হয়ে যায় কত গল্পগাছা, সমালোচনা, পরনিন্দা, পরচর্চা, যাকে বলে ‘মজলিশ’। ১৯১৬ সালে কলেজ পাশের পর ১৯৪২-এ অবসর পর্যন্ত হরেক চাকরি করেছেন বিভূতিভূষণ। অনেক স্কুল, এবং দ্বারভাঙা-রাজের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনে বহু মানুষের আনাগোনা। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিভূতিভূষণের কলমে উঠে আসে ‘পৃথ্বীরাজ’ বা ‘কুইন অ্যান’ গল্পের রায়সাহেবদের তোষামোদি, ‘বি-এন ডব্লুর ব্রাঞ্চ লাইনে’ কি ‘কৈকালার দাদা’-র রেলকর্মী ও রেলযাত্রীদের ধরনধারণ, ‘গজভুক্ত’র মেস’বালক’দের বালখিল্য আচার আচরণ। ‘হার-জিত’ বা ‘যুগান্তর’-এর তরুণ রোমান্সই হোক কিংবা ‘পূর্ণ চাঁদের নষ্টামি’ বা ‘হোমিওপ্যাথি’ গল্পে দরকচা মেরে যাওয়া দাম্পত্যের রস-নীরস বার্তা, তাঁর পর্যবেক্ষণে ত্রুটি নেই।
দেখা না-দেখায় মেশা জীবনে রং-রসান চড়িয়েই হাত মকশো করেন সাহিত্যিক। সমনামী সাহিত্যিকের মতো না-দেখার দিকে বিশেষ দৃকপাত করেননি বিভূতিভূষণ। কিন্তু জীবনের পথচলায় যাদের দেখেছেন, সেই রক্তমাংসের জীবনকে তিনি ছুঁয়েছেনে দেখেছেন তাঁর লেখায়। চোখে-দেখার বাইরের দর্শনে তো বাংলা সাহিত্য ভরে আছে, তবে সাধারণ মানুষকে সাধারণ চোখে দেখার এই সহজ চোখটুকু যে জীবনের আঘ্রাণ দেয়, তা-ই বা কম কী!
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
