

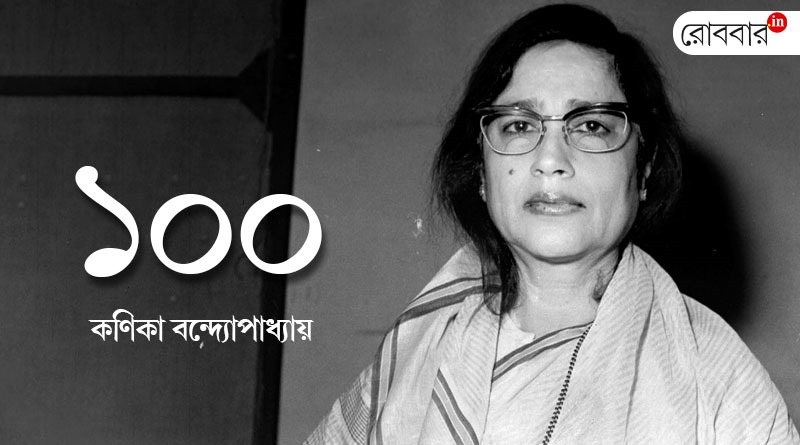
কোনও কোনও অনুষ্ঠানের মহড়ার জন্য ওঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সব গান যে তিনিই প্রত্যক্ষভাবে শিখিয়েছেন এমন নয়, কিন্তু উপস্থিত থেকেছেন। হয়তো শিখিয়েছেন গোরাদা বেশি। কিন্তু মোহরদির উপস্থিতি সামগ্রিকভাবে যে কোনও মহড়াকে অনেক বেশি দায়িত্ববান করে তুলত। সকলেই অনেক বেশি যত্নবান হতেন নিজ নিজ ভূমিকায়। কারণ তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই একটা স্বাভাবিক সম্ভ্রম আদায়ের ক্ষমতা ছিল। তা থেকে কেউই নিষ্কৃতি পেতে পারত না। সেটা শুধু মহড়ায় নয়, পথে-ঘাটে, রিকশায় হোক, গাড়িতে হোক– তাঁকে দেখে আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় হাত দুটো জড়ো হত।
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ‘রোববার.in’-এর পক্ষ থেকে আমার কাছে লেখার জন্য একটি অনুরোধ এসেছে। কেন আমার কাছে এই অনুরোধ, একটু বিস্মিত হয়ে ভেবে যে উত্তরগুলো খুঁজে পেলাম– প্রথমত, আমি দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনের অধিবাসী এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মোহরদিকে চোখে দেখার, কানে শোনার প্রত্যক্ষ সুযোগ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমি রবীন্দ্রনাথের গান ভালোবাসি। তৃতীয়ত, যোগ্যতর মানুষের অভাব হয়ে থাকতে পারে কোথাও। যার জন্য আমার মতো কিছুটা অযোগ্য মানুষের কাছে এমন জরুরি প্রয়োজন জানাতে হয়।
আমি যখন ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে এলাম, তার আগে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার সুযোগ হয়েছে। আমার জন্মস্থান দক্ষিণেশ্বর, বরানগর এলাকা, উত্তর কলকাতায়। তখন এই গান শোনা বেতার যন্ত্রে। অথবা গ্রামাফোন রেকর্ডে। কালো ডিস্ক। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান প্রধানত যে চারজনের গলায় শুনেছিলাম, তাঁরা হচ্ছেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এবং তখন ওই ‘থার্টিথ্রি’, মানে বড় রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, তার অডিও রেকর্ড ‘শাপমোচন’ বা ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘চণ্ডালিকা’ আসতে শুরু করেছে। সেখানেও এঁদের গান শুনেছি। এবং বলতে কোনও দ্বিধা নেই, সব থেকে কম ভালো লাগত যাঁর গান, তিনি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মোহরদি। কেমন যেন মনে হত, কীরকম কান্না কান্না করে গান করেন, ভালো লাগে না শুনতে। আজ এই পরিণত বয়সে আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মোহরদির গান যখন খুব ভালো লাগতে শুরু করে, বুঝি, সেটা শুধু বয়সের জন্য না। গান শোনার যে চর্চা, কান তৈরি হওয়া– সেটা ছিল না বলেই ওঁর গান তেমন লাগত না আগে। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি মেনে যে সুরের বিস্তারিত ব্যাঞ্জনা, নির্ভুলভাবে সেই সুরে বা স্বরে স্থিত থাকার যে ক্ষমতা ওঁর মধ্যে দেখেছি, সত্যি বলতে কী, ঠিক একইরকম অন্য কারও মধ্যে হয়তো পাইনি। আর নিজে গান গাইতে গিয়ে বুঝেছি, সেটা ‘শিল্পী’ হিসাবে নয়, একেবারেই একজন ‘গান ভালোবেসে গান’ করতে গিয়ে, যে, ওই নিখুঁতভাবে সুরে থাকা, আমার পক্ষে কতটা কঠিন! অথচ স্বরলিপি মাফিক ঠিক সুরে থাকলে আপনা-আপনি রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব কত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হতে পারে, সেই সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে পেরেছি মোহরদির গানের মধ্য দিয়ে।
পরে, আরেকটু যখন বড় হয়েছি, কোনও কোনও অনুষ্ঠানের মহড়ার জন্য ওঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সব গান যে তিনিই প্রত্যক্ষভাবে শিখিয়েছেন এমন নয়, কিন্তু উপস্থিত থেকেছেন। হয়তো শিখিয়েছেন গোরাদা বেশি। পরিচালনা করেছেন। কিন্তু মোহরদির উপস্থিতি সামগ্রিকভাবে যে কোনও মহড়াকে অনেক বেশি দায়িত্ববান করে তুলত। সকলেই অনেক বেশি যত্নবান হতেন নিজ নিজ ভূমিকায়। কারণ তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই একটা স্বাভাবিক সম্ভ্রম আদায়ের ক্ষমতা ছিল। তা থেকে কেউই নিষ্কৃতি পেতে পারত না। সেটা শুধু মহড়ায় নয়, পথে-ঘাটে, রিকশায় হোক, গাড়িতে হোক– তাঁকে দেখে আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় হাত দুটো জড়ো হত। সেই শ্রদ্ধার স্মৃতি খুব স্পষ্ট।
যে সময়টার কথা বলছি, সে সময়ে শান্তিনিকেতন আত্মসম্মানে অটুট। নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার প্রতিও ছিল প্রবল আস্থাশীল। খুব স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতনের বাইরের জগতের বাড়তি সমীহ অর্জন করত তা। আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। মাধ্যমিক পরীক্ষার একটা বিষয়ে ১০০ নম্বর থাকত, যাকে বলা হত ‘ফোর্থ সাবজেক্ট’। তার মধ্যে কাঠের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, তাঁতের কাজ, লোহার কাজ। ছিল নাচ– মণিপুরী, কথাকলি। এবং গানও– রবীন্দ্রসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত বা শাস্ত্রীয় সংগীত। এই বিষয়গুলোর পরীক্ষা নিতে আসতেন বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতনের বাইরের কেউ। রবীন্দ্রসংগীতের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছিল সংগীতভবনের একটি ঘরে। এক্সটার্নাল এগজামিনার কে, কোনও ধারণা নেই আগে থেকে। তা, আমার নামের আরম্ভে যেহেতু ‘এ’, আমিই প্রথম পরীক্ষার্থী। ঘরে ঢুকে দেখলাম, অবাক বিস্ময়ে যিনি বসে আছেন, এতদিন তাঁর ছবি দেখেছি বিভিন্ন রেকর্ডের কাভারে– সুচিত্রা মিত্র! তাঁরও শতবর্ষ চলছে এখন। আজকে ভাবি যে, তিনি এসেছিলেন মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষক হিসাবে, শুধুই কি বন্ধুত্বের খাতিরে, না কি শান্তিনিকেতনের প্রতি টানে? পরে অনেকবার শান্তিনিকেতনে দেখেছি তাঁকে। অনেকটা সময় ধরে থাকতেন, তা-ও জানি। কোথায় থাকতেন, তা-ও। কিন্তু ওই যে একটা প্রথম বিস্ময়, সেই ঘোরটা আজও রয়ে গেছে। এবং আজ বুঝি যে, শান্তিনিকেতনে মোহরদিদের উপস্থিতিটা কত বড় একটা সম্পদ বা ঐশ্বর্য।
সাতের দশকের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে আবাসিক ছাত্র হিসাবে যখন এসেছি, তখন পাঠভবনে আমাদের যাঁরা গান শেখাতেন, তাঁরা অনেকেই সংগীতভবনের অধ্যাপিকা। সীতাংশু রায় পরে সংগীতভবনের অধ্যাপক হয়েছেন। কিন্তু মঞ্জুদি, বাচ্চুদি, মানে মঞ্জু বন্দ্যেপাধ্যায়, নীলিমা সেন, আরতি বসু– এঁরা সংগীতভবনেরই অধ্যাপিকা ছিলেন। মোহরদির কাছে পাঠভবনে আমরা কোনও দিন ক্লাস করিনি। কিন্তু কোনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে, সেটা বিশেষ উপাসনা হোক বা বেতার অনুষ্ঠান– সমবেত গান শেখানোর সময় তাঁকে পেতাম। তাঁর উপস্থিতি আমাদের কাছে কতটা সৌভাগ্যের, তখনও বুঝিনি। নানারকম উৎসব, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, মহলা, নিয়মিত এই গুণীমানুষদের আন্তরিক সাগ্রহ উপস্থিতি সকলকে অনুপ্রাণিত করত। সকলকে নিজের যতটা সম্ভব ভালো উজাড় করে দিতে অনুপ্রাণিত করতেন মোহরদি। এই ব্যাপারে আমার অন্তত আজকে কোনও সন্দেহ নেই।
আমার নিজের কাছে ব্যক্তিগতভাবে মোহরদির কোনও ঘনিষ্ঠতা বা একা কোনও গান শেখার, শোনার সুযোগ হয়নি। আমার কাছে মোহরদির যে স্মৃতি, তা শুধু তাঁর একার স্মৃতি নয়। মোহরদি, শান্তিদা বা আরও অনেকের একটা সম্মিলিত উপস্থিতি, যেটা সেই সময় সংগীতভবন, এবং শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক জীবনকে খানিকটা পরিচালনাই করত, সেই সামগ্রিক স্মৃতিটাই মুখ্য। আজকের শান্তিনিকেতন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখি, তখন এইটুকু বুঝতে পারি, প্রতিদিনকার জীবনযাপনের মধ্যে যে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার স্পর্শ, তা অনেক স্পষ্ট ছিল সেকালে। আজকে কিছুটা অস্পষ্ট হয়েছে বলেই বোধহয় সেদিনকার স্পর্শ আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।