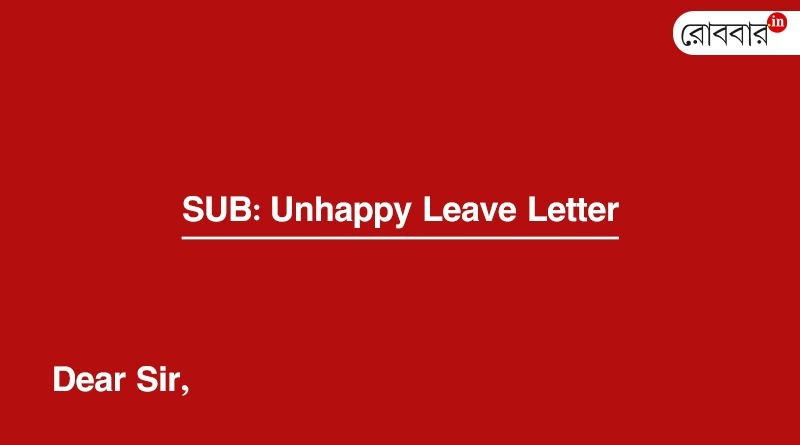টার্গেট সম্পূর্ণ করতে না পারলে ওপরওয়ালা বস-এর ‘খিস্তি’ খাওয়া যেখানে রেওয়াজ, চুরি করে ভিডিও করে সেটা সোশাল মিডিয়ায় না আসা পর্যন্ত সকলেই এ ব্যাপারে অন্যদিকে চেয়ে থাকতে পারেন– এটাই যেখানে চালু অভ্যাস, সেখানে আজকে আমার অফিস যেতে ভাল্লাগছে না বলে ‘সবেতন’ ছুটি নিলে সেটা আমার বিরুদ্ধে যাবে না, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য? মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়াটা যেখানে এখনও লুকিয়ে রাখতে হয়, সেখানে মনখারাপ নিয়ে এত সহজে কোনও আলাপচারিতা তৈরি হতে পারে?

রত্নাবলী রায়
‘‘ছোট ছেলেটা যখন পেটে, তখন হোটেলের কাজটা ছাড়তে হল। তিন বাড়ি কাজ করে পাঁচ হাজার টাকার মতন হত, কিন্তু মেজ ছেলেটার জ্বরের সময় দু’দিন যেতে পারিনি বলে সামন্ত গিন্নি কাজ ছাড়িয়ে দিলেন, মুখার্জ্জি বাড়ির মেয়েও ভারি কথা শোনাল। এখন এই কাগজ কুড়িয়ে আর রদ্দি মাল বেচে মাসে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা হয়। কিন্তু তাতে ছোট ছেলেটার খাবারের খরচ, বড় মেয়েদুটোর পড়াশুনোর খরচ– কোনওটাই হয় না। ওদের বাবা এখন ব্যাটারি রিকশা চালায়, তাতে রোজগার যত না বেড়েছে, খরচ বেড়েছে অনেক বেশি। সারাদিনে হাঁফ ছাড়ার ফুরসত হয় না, মনখারাপ টের পাওয়ার সময় কোথায়?’’ –মীনা, বাসন্তী কলোনি।
চিনের একটি সুপার মার্কেট চেন, ‘ফ্যাট দং লাই’ সম্প্রতি তাদের কর্মচারীদের জন্য বাৎসরিক দশ দিনের ‘মন-খারাপ’ ছুটির বন্দোবস্ত করেছে। এই ছুটি পেতে গেলে একজন কর্মচারীকে তার ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হবে না। রিপোর্টগুলিতে খুব পরিষ্কার করে কোথাও লেখা না হলেও যতদূর অনুমান করা যাচ্ছে, এটি ‘সবেতন’ ছুটির বন্দোবস্ত। যেহেতু মনখারাপ বিষয়টা ধরে নেওয়া হয় মনোবিদ বা মনোরোগ নিয়ে কাজ করেন এমন মানুষদের একচেটিয়া অধিকার, সেজন্যই সম্ভবত এই প্রসঙ্গে আমার মতামত চাওয়া হয়েছে। খুব নির্দিষ্ট করে বললে, প্রশ্নটা এরকম– এইরকম মনখারাপের ছুটি কি এদেশে সম্ভব?
দীর্ঘদিনের বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের এক কর্মীর কাছে শুনেছিলাম, আইটি সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়নের বোঝাপড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা। তাঁর বক্তব্য ছিল, আইটি সেক্টরের কর্মীরাই, আট ঘণ্টার কাজের নিয়মটাকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ মনে করেন। কারণ তাঁদের কাজে, শ্রমের একক হিসেবে ঘণ্টা মাপা দিনের বদলে, একটা প্রকল্পে তাঁদের যা কাজ সেটা সম্পন্ন করাটাকেই ‘একক’ বলে ভাবতে সুবিধে পান। আবার তিন দিন প্রায় ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করে এক বা দু’দিন বিশ্রামের সুযোগ থাকলে তাঁদের হয়তো সুবিধে হয়। কিন্তু সেটা সম্ভব কি না, তা আবার নির্ভর করে পরবর্তী প্রকল্প কতটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তার ওপর। বা সেই প্রোজেক্ট টিমের ম্যানেজার কতটা তাঁর দলের সদস্যদের প্রতি সহানূভূতিশীল, তিনি তাঁর ওপরওলার সঙ্গে কতটা দর-কষাকষি করতে পারেন– এই সমস্ত বিষয়ের ওপর।
আইটি বা আইটি নির্ভর সার্ভিস সেক্টরের শ্রমসময়ের একক বিষয়টা নিয়ে কোনও সর্বসম্মত বোঝাপড়া তৈরি না হওয়ার কারণে, আজকে এরকম আকছার দেখা যায়– একজন ভারতীয় আইটি কর্মী, যিনি ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও প্রজেক্টে কাজ করছেন, তিনি, ভারতীয় সময়ে অফিস করছেন আবার মক্কেলের দেশের যে অফিসের সময় সেই সময়ও অফিস করছেন। বিশেষ করে থার্ড পার্টি কোম্পানিগুলোতে এন্ট্রি লেভেল কাজে যাঁরা ঢুকছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বেশি হয়। ‘ভাল্লাগছে না’ বলে ছুটি পাওয়াটা সেখানে দুষ্কর। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায়, এরকম একটা ছুটির বন্দোবস্ত হল, তাহলে, কোম্পানি এটা খেয়াল রাখছে না যে, কে বেশি মনখারাপের ছুটি নেয়, সেটা ভাবাটা আরও কঠিন। মানে, একটা ছুটি যদি চালুও হয়, তাহলে, সেই ছুটিটা নেওয়ার জন্য আমাকে পেনালাইজ করা হবে না– কোম্পানির ওপর এমন আস্থা আছে, এমন কর্মী আর কোম্পানি দুটোই খুঁজে পাওয়া সম্ভবত বেশ কঠিন হবে।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
মনখারাপ-কে শুধুই ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটির সঙ্গে জুড়ে দিলে ব্যাপারটাকে অকারণ সাইকোলাইজ করা হয়। এবং এই অহেতুক সাইকোলাইজেশন একটা প্রবণতা যেটা ঘুরেফিরে আর পাঁচটা বাজারি পণ্যের ক্রেতা তৈরি করে। এবং জটিল করে দেখানোর এই যে অতিসরলীকরণ মনখারাপের জ্যান্ত কারণগুলোকে, দারিদ্র, অনটন, ঠিকঠাক খেতে না পাওয়া, পারিবারিক অশান্তি, কাছের মানুষের অসুস্থতায় যথাযথ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে না পারা এরকম আরও হাজারটা কারণ দেওয়া যায়– সেগুলোকে অবান্তর, খাটো করে দেয়, দুঃখকে নেহাতই ‘ব্যক্তিকেন্দ্রিক’ বলে ব্যখ্যা করে এবং দুঃখমোচনের দায়টাও ব্যক্তির ওপরেই চাপায়।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
কিন্তু মূল প্রশ্নটা অন্যত্র। শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য মানুষের অধিকারের প্রশ্ন কি ক্রমশ আইটি, সার্ভিস সেক্টর, রিটেল চেন-এর কর্মচারী এঁদের কাছে এসে মুখ লুকোচ্ছে? মাঠের কৃষিমজুর, কারখানার শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমের বাজার যার বেশিরভাগটাই মহিলারা, ক্রমশ বাড়তে থাকা গিগ-শ্রমিকের দল, এঁরা কেন এই সমস্ত আলোচনার আওতায় এসে পৌঁছন না, এ এক বেজায় ধাঁধা!
একটি চিনা সুপারমার্কেট চেন মনখারাপের ছুটি চালু করলে যতটা সাড়া পড়ে, তার সিকিভাগও টের পাওয়া যায় না আশা কর্মী বা মিড ডে মিল কর্মীদের দাবিদাওয়া নিয়ে। আইটি সেক্টরে চোদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজের বাধ্যবাধকতা নিয়ে কথা হয় না অথচ বছরে দশটা দিন আজকে আমার অফিস যেতে ভাল্লাগছে না বলে ছুটি পাওয়া উচিত কি না, তা চর্চায় এলে একটু অদ্ভূতই লাগে।
এমনিতে চিন সম্পর্কে সাধারণভাবে তথ্য এত কম পাওয়া যায়, সেই তথ্য যাচাই করার সুযোগ আরও এত কম থাকে যে, বিষয়টি আসলে কী, কেন ঘটছে, এটা নিয়ে খুব নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তাও, যেটুকু জানা যাচ্ছে, এই সুপার মার্কেট চেনটি, ‘ফ্যাট দং লাই’, নয়ের দশকের মাঝামাঝি তাদের শুরুর সময় থেকেই একরকম ব্যতিক্রমী ইমেজের জন্য পরিচিত। ইউ দং লাই, ইউ দং মিং আর লিউ হংজুন– এই তিনজন মিলে হেনান রাজ্যের একটা জেলাশহর জ্যুচ্যাং-এ যেটা চালু করেছিলেন, সেটা আমাদের চেনাশুনো বড় মুদির দোকান বলা যায়, যেখানে তামাক এবং মদ-ও পাওয়া যেত। ১৯৯৬-এ তৃতীয় তাইওয়ান প্রণালী সংকটের সময়, ব্যবসার এক বছরের গোটা রোজগার, ২০ হাজার ইউয়ান দেশের জন্য দান করেন। এঁরা এতটাই সাধারণ ঘর থেকে এসেছিলেন যে বেইজিং-এ পৌঁছে ঠিক কোথায় গেলে চিনা বিমান তৈরির জন্য এই টাকাটা দান করা যাবে সেটা বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। ১৯৯৮-এ তাঁদের দোকানে আগুন লেগে আটজন কর্মচারী মারা যান, যেটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের সন্দেহর কথা শোনা যায়। তারপরেও, শুধুমাত্র অর্জিত সুনামের ওপর ভর করে, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব এমনকী, খদ্দেরদের সহযোগিতায় ফের ব্যবসা চালু করেন তিন বন্ধু।

এরপরে, ‘ফ্যাট দং লাই’-এর ব্যবসা বেড়েছে, একাধিক জায়গায় তাঁদের রিটেল শপ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিতে যা জানা যাচ্ছে, ‘ফ্যাট দং লাই’-এর বিভিন্ন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ অনেক দিন ধরেই এদেরকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ‘আউট অফ স্টক’ পণ্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি শিশুকে তার পছন্দের বিস্কুট উপহার দেওয়া, ডিসকাউন্ট না পেয়ে খেপে গালিগালাজ করা ক্রেতার থেকে ক্ষমা চেয়ে উপহার পাঠানো, গালি খাওয়া কর্মীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া, স্টোরে কেনাকাটা করতে আসুন বা না আসুন, ফ্রি পার্কিং স্পেস-এর সুবিধে দেওয়া, সপ্তাহে চোরাগোপ্তা ভাবে ৭২ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়ার রেওয়াজটাই যেখানে চালু, সেখানে পাঁচদিন সাত ঘণ্টা (সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা ) শিফট চালু করা, বছরে ৪০ দিন পর্যন্ত ছুটি এবং কর্মচারীদের জন্য বিদেশ ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা– এই ধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ক্রমশ ‘ফ্যাট দং লাই’-এর ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়াতে সাহায্য করেছে। অথচ প্রতিযোগিরা কেউই এই সমস্ত নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেনি। ২০০৩ সালে সার্স-এর সময় আট মিলিয়ন ইউয়ান, ২০০৮ সালে ওয়েনচুয়ান ভূমিকম্পের সময় ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ মিলিয়ে দশ মিলিয়ন ইউয়ান, ২০২০ সালে কোভিড দুর্যোগের সময় পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউয়ান, ২০২১ সালে জেংঝাউ-এর বন্যায় উদ্ধারকার্যে কর্মচারীদের শামিল করার সঙ্গে আরও দশ মিলিয়ন ইউয়ানের দান– রাষ্ট্রীয় দুর্যোগগুলোতে এই ধারাবাহিক ভূমিকা ফ্যাট দং লাই-কে আরও জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছে। এই মনখারাপের দশ দিনের (সবেতন) ছুটিকে এই ব্যতিক্রমের ধারাবাহিকতাতেই দেখা উচিত– নিয়ম হিসেবে দেখতে গেলে অন্য অনেক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তার আগে চলে আসবে।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
আমাদের দেশে, সরকারি ক্ষেত্রেই একটা ঠিকঠাক মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে যে গড়িমসি দেখা যায়, সেখানে এরকম বেসরকারি ব্যতিক্রম কতটা সম্ভব? টার্গেট সম্পূর্ণ করতে না পারলে ওপরওয়ালা বস-এর ‘খিস্তি’ খাওয়া যেখানে রেওয়াজ, চুরি করে ভিডিও করে সেটা সোশাল মিডিয়ায় না আসা পর্যন্ত সকলেই এ ব্যাপারে অন্য দিকে চেয়ে থাকতে পারেন– এটাই যেখানে চালু অভ্যাস, সেখানে আজকে আমার অফিস যেতে ভাল্লাগছে না বলে ‘সবেতন’ ছুটি নিলে সেটা আমার বিরুদ্ধে যাবে না, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য? মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়াটা যেখানে এখনও লুকিয়ে রাখতে হয়, সেখানে মনখারাপ নিয়ে এত সহজে কোনও আলাপচারিতা তৈরি হতে পারে? মনখারাপ-কে শুধুই ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটির সঙ্গে জুড়ে দিলে ব্যাপারটাকে অকারণ সাইকোলাইজ করা হয়। এবং এই অহেতুক সাইকোলাইজেশন একটা প্রবণতা যেটা ঘুরে ফিরে আর পাঁচটা বাজারি পণ্যের ক্রেতা তৈরি করে। এবং জটিল করে দেখানোর এই যে অতিসরলীকরণ মনখারাপের জ্যান্ত কারণগুলোকে, দারিদ্র, অনটন, ঠিকঠাক খেতে না পাওয়া, পারিবারিক অশান্তি, কাছের মানুষের অসুস্থতায় যথাযথ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে না পারা এরকম আরও হাজারটা কারণ দেওয়া যায়– সেগুলোকে অবান্তর, খাটো করে দেয়, দুঃখকে নেহাতই ‘ব্যক্তিকেন্দ্রিক’ বলে ব্যখ্যা করে এবং দুঃখমোচনের দায়টাও ব্যক্তির ওপরেই চাপায়। দশ দিনের দুঃখযাপনের সবেতন ছুটি ভারতে সম্ভব কি না, এই প্রশ্নটার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, দুঃখের দায়টা কি শুধু দুঃখী মানুষেরই? প্রতিটা দুঃখকে এরকম ব্যক্তিগত আলাদা আলাদা দুঃখ হিসেবে দেখতে গিয়ে, দুঃখমোচনের সামাজিক দায় এবং উদ্যোগগুলো হারিয়ে ফেলব না তো?
‘এসব হলে আমরা দুঃখীরা দেবতাদের পুজো দিই।’ লীলা মজুমদার। অহিদিদির বন্ধুরা।