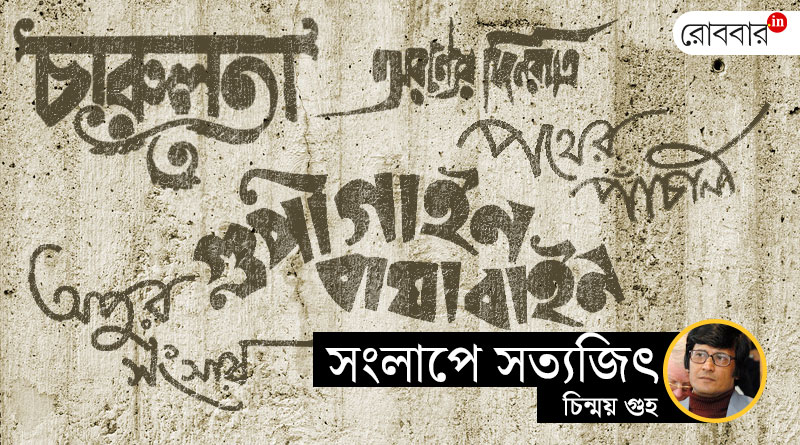
‘দেবী’ ছবিতে দয়াময়ী যখন অপ্রত্যাশিত দেবীত্ব আরোপে ক্রমশ এক সংশয়ের মধ্যে ডুবে আছে, তখন বলটি তার ঘরে চলে এলেও বাচ্চাটি ঘরে ঢুকতে ভয় পায়, প্রিয় পাখিটি ডেকে ওঠে– ‘দয়াময়ী! দয়াময়ী!’ পাখির ডাকের এই আশ্চর্য প্রয়োগের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সত্যজিৎ ভেবেছেন ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম জীবন্ত মানুষ উঠে এসেছে পর্দায়, তার বহিরাবয়ব, তার পশ্চাৎপট, তার পোশাক, তার কথা, কথা বলার স্বাভাবিকতা নিয়ে চলচ্চিত্র খুঁজে পাচ্ছে তার আপন প্রাণ। কী করে গভীর অভিনিবেশে ও প্রত্যয়ে সত্যজিৎ রায় অনুধাবন করতে পারেন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মুড, কথা, অনুরণন– বাঙালি দর্শক কি বুঝতে চেয়েছে কখনও? মনে হয় না সে-চেষ্টা তেমন করে হয়েছে।
যেমন, ধরা যাক, ‘পথের পাঁচালী’-র কথা। এক তরুণ যুবক কত বড় একটা বিপ্লব করে ফেললেন শুধু দৃষ্টি আর আলোই নয়, সংলাপ দিয়ে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে পথ দেখালেন বটে, কিন্তু সেই পথ নিবিষ্ট ভাবে অনুসরণ করার যোগ্যতা অর্জন কি সহজ কথা? যা ক্রমশ প্রসারিত হবে সমস্ত ধরনের মানুষের কণ্ঠস্বরে।
আমরা দেখছি, অপু বই-স্লেট ঘরে রেখে রান্নাঘরে দাওয়ায় মায়ের কাছে যায়। সর্বজয়া বাটনা বাটছিল।
সর্বজয়া: অ্যাই, ছুঁসনি ছুঁসনি!
কিন্তু অপু ততক্ষণে মায়ের আঁচল ধরে ফেলেছে।
সর্বজয়া: দিলি তো ছুঁয়ে!
অপু (মৃদু গলায়): মা, খিদে পেয়েছে।
সর্বজয়া: সত্যি? এত শিগগির? কেন রে! মুড়ি খাসনি?
অপু: হ্যাঁ–
সর্বজয়া: তাহলে?
নেপথ্যে দুর্গার গলা।
দুর্গা: অপু, এদিকে আয়!
(অপু ছোটে)
সর্বজয়া: হাঁড়িতে মুড়কি আছে! দুর্গাকে বল দিতে–
(অপু-দুর্গার আচার খাওয়া)
ইন্দির: অ হরি– হাতটা ধরে একটু তোল বাবা!
হরিহর: কী হল?
(হরিহর হেসে ইন্দিরের হাত ধরে তাকে দাওয়ায় তুলে দেয়।)
ইন্দির: মাথাটা ধরে গেছে–
হরিহর: কেমন বোধ করছ আজকাল?
ইন্দির: অ বাবা, বুড়ো মানুষকে আর কে দেখে বল!
হরিহর: হল কী?
ইন্দির: এই দ্যাখ না–
(ইন্দির তার চাদরটা নিয়ে একটা বিরাট ফুটোর মধ্য দিয়ে নিজের মাথা বের করে দেখায়।)
ইন্দির: দ্যাখ!
হরিহর: ওটা কী!
ইন্দির: এই চাদরখানা সন্ধ্যাবেলা গায়ে দিয়ে বসি।
হরিহর: বেশ তো, পুজোয় একটা নতুন চাদর কিনে দেব!
ইন্দির: দিবি তো?
হরিহর: দেব দেব–
ইন্দির: দিবি তো, অ হরি!
হরিহর: বলচি তো দেব!
(সর্বজয়া শুনেছে, তার মুখ ভার)
হরিহর: কই, আগুনটা দেবে?

(সর্বজয়া নিঃশব্দে কলকেটা নেয়, তারপর রান্নাঘরে ঢুকে আগুন ভরে দেয়।)
সর্বজয়া (তিক্তস্বরে): গাড়ি গাড়ি তামুক খাবার আগুন জোগাব কোত্থেকে তোমায়? সুঁদুরি কাঠের ব্যবস্থা আছে কি না!
নিঃশব্দ কথাও বারবার অপরূপ বাঙ্ময় করেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে। যেমন, ‘অপরাজিত’-তে।
অপু: মা… মা…
(উঠোনে দেখতে না পেয়ে বাইরে আসে। দাদু কমণ্ডলু হাতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। অপু গাছতলায় বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে)
ভবতারণ: কান্দিস না অপু… বাপ মা, চিরদিন কারও থাকে না। যা হবার হয়ে গেছে। এখন শ্রাদ্ধটা কোনও রকমে কর—জজমানি করলে তোর ভালো রকম চলে যাবে।
(অপু গাছতলায় বসে কাঁদছে। পরনে উত্তরীয়। অপু মাথা গুঁজে বসে আছে। হঠাৎ সামনের পুকুরের জলে চোখ গেল। জলে কালপুরুষের ছায়া পড়েছে)
অপু: কালপুরুষ!
(পরদিন সে জিনিসপত্র গোছগাছ করে। দাদুকে বলে, সে কলকাতায় যাচ্ছে। মায়ের কাজ কলকাতায় করবে– কালীঘাটে। কাপড়ের পুঁটুলি হাতে সে আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে যায়। ভবতারণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। সে দরজা পেরিয়ে, গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলেছে। দূরের পথ ধরে মিলিয়ে যায়। মেঘের গর্জন)
যেমন ‘অপুর সংসার’ ছবিতে অপু-অপর্ণার প্রেম। অপু শুয়ে অপর্ণাকে দেখে। সিগারেট খাওয়া নিয়ে স্ত্রীর নির্দেশ। স্বয়ং জাঁ রনোয়ার সত্যজিৎকে ওই দৃশ্যের ব্যঞ্জনায় অভিভূত হওয়ার কথা বলেন। নৈঃশব্দ্যের শক্তি ও ইঙ্গিতময়তা।
কিন্তু একটি পাখি কী করে মানুষের কথার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে?

‘দেবী’ ছবিতে দয়াময়ী যখন অপ্রত্যাশিত দেবীত্ব আরোপে ক্রমশ এক সংশয়ের মধ্যে ডুবে আছে, তখন বলটি তার ঘরে চলে এলেও বাচ্চাটি ঘরে ঢুকতে ভয় পায়, প্রিয় পাখিটি ডেকে ওঠে– ‘দয়াময়ী! দয়াময়ী!’ পাখির ডাকের এই আশ্চর্য প্রয়োগের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সত্যজিৎ ভেবেছেন ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।
অথবা স্বামী উমাপ্রসাদের সঙ্গে ওই নরক থেকে পালাতে সেই ভয়ার্ত আতঙ্কিত আত্মপ্রশ্ন, যা চলচ্চিত্রের পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলে: ‘আমি যদি দেবী হই! আমি যদি দেবী হই!’ সে ফিরে আসে! গায়ে কাঁটা দিয়ে সে এবার মাঠে হারিয়ে যাবে। শর্মিলা ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ছবি।
পাখির ব্যঞ্জনা আমরা ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-তে দেখেছি। দেখেছি কীভাবে একটি পাখির ডাক হয়ে উঠেছে একটি ছবির প্রধান ভাবসূত্র।
তপু: দাদা, কীরকম একটা পাখি ডাকছে শোন।
সিদ্ধার্থ: শ…
সেই পাখির ডাক ফিরে আসে শেষ দৃশ্যের মায়ায়।
অথবা ‘সীমাবদ্ধ’ ছবির শেষ দৃশ্যে একটি পাখা নিঃশব্দ ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময়।
‘কাপুরুষ’-এর শেষ দৃশ্যে অপেক্ষারত অমিতাভ ট্রেনের হুইসলের শব্দে তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে। চোখ মেলতেই সামনে করুণা দাঁড়িয়ে। পিছনে ট্রেনের হেডলাইট এগিয়ে আসছে।
অমিতাভ: করুণা!
(করুণা কি যাওয়ার জন্যই এসেছে?)
করুণা: ঘুমের ওষুধটা কি তোমার কাছে?
অমিতাভ (ক্ষুব্ধস্বরে): করুণা!
করুণা: ওটা দেবে? দরকার আছে। এখানে পেলাম না। দাও না, লক্ষ্মীটি!
(করুণা শিশিটা নেয়)
করুণা: চলি!
(করুণা চলে যায়। ট্রেনের গর্জন বেড়ে যায়। করুণা হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়)
নৈঃশব্দ্য সব সংলাপকে অতিক্রম করে যায়। হয়ে ওঠে অধরা এক যন্ত্রণা।
‘চারুলতা’। শেষ চিত্রাংশের সেই ভুবনবিখ্যাত মুহূর্ত। ভালোবাসাহীন যান্ত্রিক দাম্পত্য জীবনের অন্তহীন শূন্যতা।
চারু: এসো–
হাত বাড়িয়ে দেয়।
চারু: এসো।
(হাত দুটো পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে যায়।)
ফ্রিজ।
(গলা ভেসে আসে)
ভূপতি: চারু–
চারু: বলো।
ভূপতি: তোমার বড্ড একা লাগে…
(ফ্রিজ। আরও এগিয়ে আসে)
চারু: ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।
(ভূপতির ফ্রিজ শট। তার ওপর ভূপতির গলা)
ভূপতি: আমার চারুলতা আছে… নাটক নভেল কাব্য– আর কিস্যুর দরকার নেই।
(বাতি হাতে ভৃত্য ব্রজ ফ্রিজ হয়ে আছে। চারুর কণ্ঠস্বর)
চারু: ব্রজ, কানে শোনো না নাকি? চারটে বেজে গেছে। অফিসে চা দিয়ে এসো।
(চারু ও ভূপতির ফ্রিজ শট। দূরে আলো হাতে ব্রজ। তিনজনে একসঙ্গে স্থিরচিত্র। অমলের গলার আওয়াজ।)
অমল: জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদ…
(হরে মূরারে, মধুকৈটভারে–)
চারু-ভূপতির হাত না মেলার অবিস্মরণীয় লং-শট– এত দূর অন্ধকার যে, চেনা যাচ্ছে না। তখন চারু আর ভূপতি পৃথিবীর সব হতভাগ্য চারুরা আর ভূপতিরা হয়ে গেছে!

কথা, না কথা, নৈঃশব্দ্য মিলে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র-স্থাপত্য জীবনের কঙ্কাল থেকে উৎসারিত হয়।
(চলবে)
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
