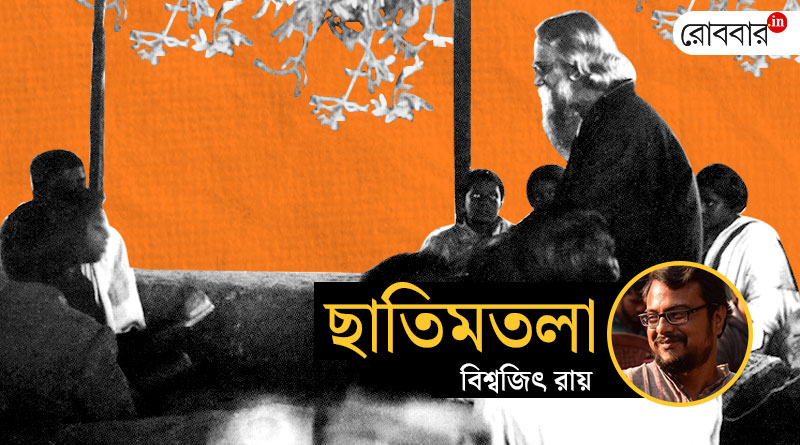
‘মুক্তধারা’ নাটকে যে ‘প্যাট্রিয়টিজ্ম্’-এর কথা বলা হয়েছে তা অন্ধতা। শিক্ষক তার প্রচারক। এই অন্ধতা শিখিয়ে সামরিক প্রভুদের হাতে সেই পড়ুয়াদের সমর্পণ করা হবে। এ ধর্মীয় অন্ধতার সঙ্গে তুল্য। এভাবেই ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় দেশকে, কৌশলে। এর বিরুদ্ধেই ছাত্র অরবিন্দমোহনকে সচেতন করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখছিলেন এই manliness-এর আদর্শ, খাটো দেশপ্রেমের অভিমত আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখেছি।

শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে প্রথম যুগে যাঁরা পড়তে আসতেন তাঁরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের পরিচিত পরিবারের সন্তান। বন্ধুস্থানীয়রা কবির বিদ্যালয়ে পাঠাতেন তাঁদের। জগদীশচন্দ্রর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর বন্ধুত্ব– বিজ্ঞানীবন্ধুকে কবি তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ বিষয়ে চিঠি লিখতেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথের মনে ব্রহ্মচর্য ও তপোবনের আদর্শ বড় হয়ে উঠেছিল। পরে অবশ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও তপোবনের পুনর্নির্মাণের ঘোর অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়কে নানা দিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের ভাগনে অরবিন্দমোহন বসু শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম দিকের ছাত্র, ১৯০২-১৯০৭ পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন।
জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ হয়েছিল, অরবিন্দমোহন তখন আশ্রমের ছাত্র। এমন অভিজ্ঞতা অবশ্য নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠিয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন এমন অভিভাবক কেবল অবলা বসু-ই নন, আরও কেউ কেউ। আবার অভিভাবকদের বিরক্তি কেবল আদর্শ নিয়ে নয়– পড়ুয়াদের থাকা-খাওয়াকে ঘিরেও অনেক সময় তাঁদের অভিযোগ মাথা তুলত। সবাই তো আর ইন্দিরা গান্ধীর পিতা নেহরুর মতো নন। কন্যা ইন্দু পিতা জহরলালকে শান্তিনিকেতনের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে নিয়ে চিঠি লিখলেও জহরলাল তাতে কর্ণপাত করছেন না। এটুকু তো মানিয়ে নিতেই হবে। নিজের ছেলে রথীন্দ্র আর শমীন্দ্রর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের মোটা ভাত-কাপড়ের বরাদ্দ মঞ্জুর করতেন। তবে আশ্রম তখন ছোট ছিল বলে তাঁদের সহাধ্যায়ীরা অনেক সময় মৃণালিনীর শরণ নিতেন। মৃণালিনীর ভাণ্ডারে সকলের জন্যই কিছু না কিছু বৈচিত্রের ব্যবস্থা থাকত। তবে তা বাহুল্যময় বিপুল আয়োজন নয়।
গত পর্ব: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও
অবলা বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ অবশ্য বাহ্যিক খাওয়া-পরা নিয়ে নয়। সে মতভেদ আদর্শগত। অরবিন্দমোহনকে রবীন্দ্রনাথ ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে চিঠিতে লিখছেন প্যাট্রিয়টিজ্ম্অকে চরম করে তোলা ঘোরতর অন্ধতা। এই অন্ধতা কেমন অন্ধতা? রবীন্দ্রনাথের অভিমত, ‘সে প্যাট্রিয়টিজ্ম্ একটা ঘোরতর অন্ধতা; আমাদের দেশের ওলাবিবি ঘেঁটু পূজার মতই অন্ধতা।’ অরবিন্দমোহনের মামি অবলা বসু রবীন্দ্রনাথের এই মতামত পুরোটা বুঝতে পারেননি। আর বিরোধের কারণ সেখানেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দমোহনকে জানিয়েছেন, ‘তিনি[অবলা বসু] আমার সম্বন্ধে এতটা বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে আমার মত কি তা ভাল করে পড়েও দেখেন নি।’ হয়তো অবলা বসুরা ভাবছেন যে বিদ্যালয়ের আচার্য ‘প্যাট্রিয়টিজ্ম্’কে অন্ধ বলেন তিনি দেশকে ভালোবাসেন না। সে বিদ্যালয়ে পড়ানোও উচিত নয়। ভাল বিদ্যালয় তো দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করবে।
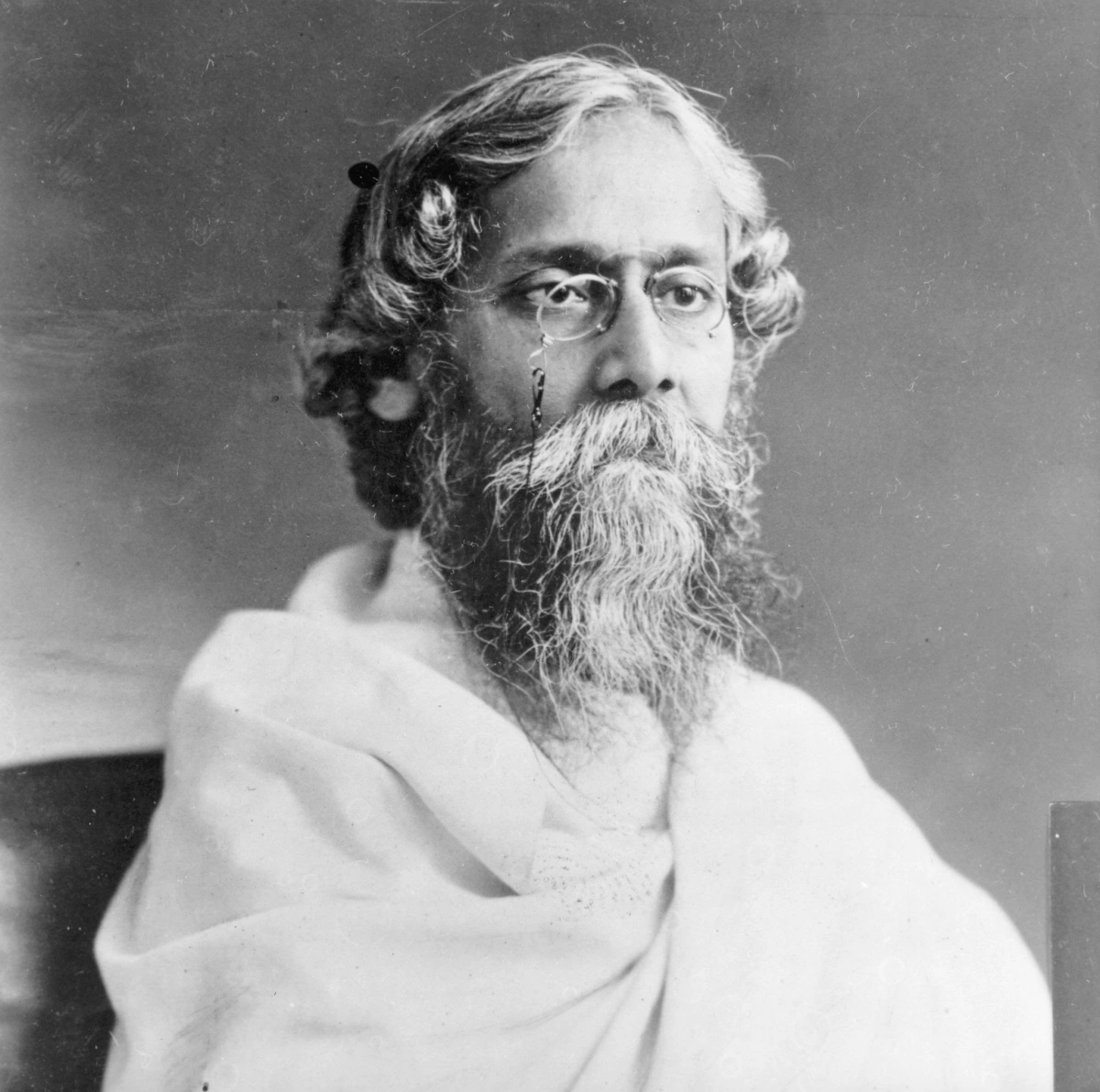
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মুক্তধারা’ নাটকে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করার স্কুলের কথা লিখেছিলেন। সে বড় ভয়ংকর স্কুল। সেখানে অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ শেখানো হয়। এমন বিদ্যালয় নির্মাণের কথা এখন একালে এদেশেও কেউ কেউ হয়তো ভাবেন।
“গুরু। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।
রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?
ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।
রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?
ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।
রণজিৎ। কেন জব্দ করা?
ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।
রণজিৎ। কেন খারাপ?
ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।
রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?
গুরু। জানে বৈকি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িস নি— বইয়ে পড়িস নি— ওদের ধর্ম খুব খারাপ—
ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
গুরু। আর ওরা আমাদের মতো— কী বল্-না— (নাক দেখাইয়া)
ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।
গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন— নাক উঁচু থাকলে কী হয়?
ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।
গুরু। তারা কী করে? বল্-না— পৃথিবীতে— বল্— তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?
ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।
গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?
ছেলেরা। কোনোদিনই না।
গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্জিৎ দুশো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?
ছেলেরা। হাঁ, দিয়েছিলেন।
গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।”
এ নাটকে যে ‘প্যাট্রিয়টিজ্ম্’-এর কথা বলা হয়েছে তা অন্ধতা। শিক্ষক তার প্রচারক। এই অন্ধতা শিখিয়ে সামরিক প্রভুদের হাতে সেই পড়ুয়াদের সমর্পণ করা হবে। এ ধর্মীয় অন্ধতার সঙ্গে তুল্য। এভাবেই ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় দেশকে, কৌশলে। এর বিরুদ্ধেই ছাত্র অরবিন্দমোহনকে সচেতন করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখছিলেন এই manliness-এর আদর্শ, খাটো দেশপ্রেমের অভিমত আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখেছি। লিখেছেন, ‘তোমার মামী যে আমার উপরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন সেটা কেবল বর্তমান সময়ের উত্তেজনা বশত।’ আমাদের দেশীয় রাজনীতি এখন বর্তমান সময়ের উত্তেজনায় ফুটছে। দেশপ্রেমের নামে দিকে দিকে ছোটখাট দেবতা মাথা তুলছে। পৌরুষের নামে মানবতাকে বাতিল করার সদা তৎপরতা। বিদ্যালয়ে ও বিদ্যায়তনে এই অন্ধতাকে নির্বিচারে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উল্টো বিচার করছেন যাঁরা, তাঁদের প্রতি সবাই খড়্গহস্ত। অবলা বসুর বিরক্তি এখন অন্যরূপে বহুগুণিত। বিরক্তির পরিবর্তে অপর স্বরকে আটকে দেওয়ার জন্য নিপুণ প্রস্তুতি। মনে মনে রাষ্ট্রপোষিত অন্ধতার ধারকেরা বলছেন, ‘উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে।’
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
