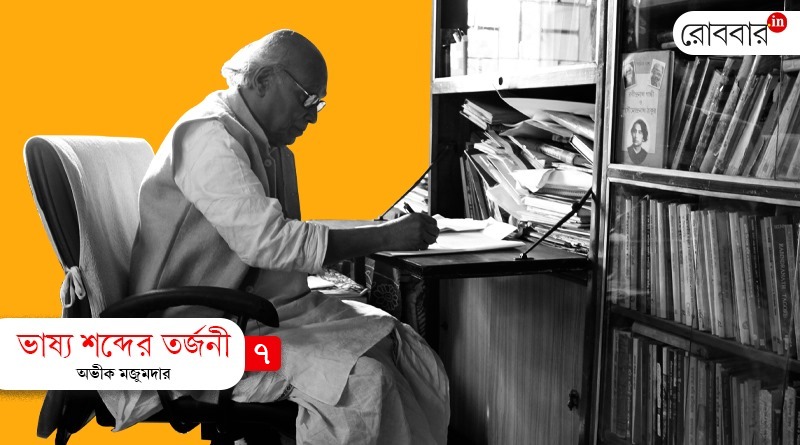
‘এই সময় ও জীবনানন্দ’ বইয়ের একেবারে শেষাংশে রয়েছে ‘উৎসনির্দেশ’ অংশ। সেই পর্বে খুব যত্ন করে প্রতিটি পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিগুলির ক্রমসংখ্যা এবং তার উৎস পাশাপাশি নির্ণয় করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রাসঙ্গিক ছত্রসংখ্যাও। খুব সহজেই বোঝা যায়, পুরো তালিকাটি কতদূর শ্রমসাধ্য। আড়াইশোর কাছাকাছি পঙ্ক্তি এবং উৎসের এই তালিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, প্রস্তুতকর্তা জীবনানন্দের যাবতীয় লেখালেখি, গদ্য-কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বর্গের লেখা একেবারে তন্ন তন্ন করে পূর্বাপর পড়েছেন।

৭.
রবীন্দ্রনাথের থেকে আমরা এবার এগিয়ে যাচ্ছি জীবনানন্দ দাশের কাব্যকৃতির প্রসঙ্গের দিকে। ওই প্রবন্ধ সংকলনটি সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের সম্পাদকীয় নানা মন্তব্য হয়তো অন্তঃশীলভাবে জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর নানা অবলোকনকেও পরিবেশন করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, শঙ্খ ঘোষ নানা গ্রন্থ একক বা যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন বটে কিন্তু এই দুই কবির ক্ষেত্রে তাঁর অভিমুখ ছিল সবথেকে স্পষ্ট এবং সুমিত। বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনার সময়, আগেই বলেছি, আমার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর কাছাকাছি থাকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বইগুলিই দেখেছি। যেমন, ‘সতীনাথ গ্রন্থাবলী’ বা ‘সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত’ (প্রথম সংস্করণ)। ফলে, যৌথ প্রযত্নে সম্পাদিত বইগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে শঙ্খ ঘোষের সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোনও নিশ্চিত মন্তব্য করা ঠিক হবে না। দু’টি-একটি কথা তুলে রাখছি মাত্র। ‘সতীনাথ গ্রন্থাবলী’ প্রকাশনা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, অরুণা প্রকাশনী থেকে। সম্পাদক ছিলেন শঙ্খ ঘোষ এবং নির্মাল্য আচার্য। সম্পাদক হিসেবে নির্মাল্য আচার্য আজ এক অতি সম্মানিত নাম। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘এক্ষণ’ পত্রিকা বর্তমানকালে কিংবদন্তির মতো। এই দুই মহাসম্পাদক যখন সতীনাথ ভাদুড়ী-র মতো মহালেখকের গ্রন্থাবলী গ্রন্থনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন বোঝাই যায়, এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। প্রথম খণ্ডের গোড়ায় ‘সতীনাথ ভাদুড়ী: প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা’ এবং গ্রন্থ প্রসঙ্গ অংশ দু’টি যেমন চমৎকার তথ্য সন্নিবেশে শুধু মূল্যবান নয়, বহু গবেষণার বীজগর্ভ।

দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতেই ‘স্বীকৃতি’ অংশ। সেই অংশে বলা হয়েছে, ‘শ্রী ভূতনাথ ভাদুড়ীর সংগ্রহ থেকে সতীনাথের ব্যবহৃত নটি ডায়েরিখাতা আমরা দেখতে পেয়েছি। এই ডায়েরিগুলির মধ্যে ছড়ানো টুকরো টুকরো কিছু মন্তব্য সংকলন করে নিয়ে এই খণ্ডের ভূমিকা সাজানো হলো।…’ ভূমিকার নাম ছিল ‘সতীনাথ ভাদুড়ী: নিঃসঙ্গ দীক্ষা’। এই প্রাক্কথন অংশটি ডায়েরির অগ্নিভ দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত সময়কালে সতীনাথ ভাদুড়ীর চিন্তার নানা দ্যুতি মন্তব্যে, উপলব্ধিতে, উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে সতীনাথ ভাদুড়ীর নিজস্ব সন্ধান এবং মনোভঙ্গি গড়ে ওঠার ধারাবিবরণী এই ডায়েরিগুলি। তাঁর কথাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত, দর্শন এবং ভাবমণ্ডলের জায়মান অন্তরাত্মার মূল্যবান কয়েকটি দিক উন্মোচিত করে ডায়েরিগুলি। স্যরের মুখে শুনেছি এই অত্যাশ্চর্য ডায়েরিগুলির সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন নেহাতই আপতিকভাবে। বাতিল কাগজপত্রর মধ্যে ডায়েরিগুলি অতি অযত্নে পড়েছিল, ধুলোয় ঢাকা! আজ ভাবতে ভালো লাগে সম্পাদকদ্বয়ের অমলিন দায়বদ্ধতা এবং গভীর অনুসন্ধিৎসাকে স্বীকৃতি দিতেই যেন ডায়েরিগুলি নিজে ধরা দিল এবং প্রকাশিত হল সতীনাথের লেখালেখির সম্পূর্ণ অচেনা এক জগৎ!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
সাত-আট-নয়ের দশকের বহু কবির, ‘কবিতা-পাঠক’ বা বলা ভালো ‘প্রথম পাঠক’ হিসেবে সম্পাদনা করতেন তিনি। বহু মান্য কবির কাব্যগ্রন্থে নির্বাচন থেকে বিন্যাস, হরফ থেকে বানান/ ছন্দ সংশোধন এবং শেষে প্রুফ দেখা সবটাই শঙ্খ ঘোষ করে দিতেন। আমার বইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রুফ দেখতে দিইনি কখনও। এইসব কাজের নানা দিক নিয়েও কিন্তু তাঁর সম্পাদকসত্তার সমগ্রতার সন্ধান করতে হবে। তাঁর সংশোধিত চিহ্নগুলি এবং স্মৃতিগুলি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
২.
এই ধরনের আরও কয়েকটি সম্পাদনার প্রসঙ্গ আলোচনায় আনা যেতেই পারে। তার মধ্যে ‘সুভাষ মুখোপাধ্যায়: কথা ও কবিতা’ বইটির কথাও মনে রাখব। এই বইটির প্রস্তুতির সময়ও স্যরের সঙ্গী হিসেবে বেশ কয়েক দিন কাজ করেছিলাম। তার মধ্যে প্রধান দায়িত্ব ছিল মনোযোগ সহকারে প্রুফ দেখা। কতজন জানেন আমি বলতে পারব না, শঙ্খ ঘোষ প্রচুর প্রুফ দেখতেন। আরও আশ্চর্য কথা হলো, সম্পাদনা এবং গ্রন্থনার প্রুফ সেখানে প্রাধান্য পেত, নিজের বইগুলির প্রুফ দেখতেন না পারতপক্ষে। সেসব কাজ অন্যের হাতে ছেড়ে দিতেন, ভুলভ্রান্তি নিয়ে খুব চিন্তিত হতেন না। অন্যের বই তৈরি করতে তাঁর অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম। সেখানে তিনি পাতার পর পাতা প্রুফ দেখতেন জম্পেশ উৎসাহে। একাধিক বইয়ের ক্ষেত্রে এমনকী, আমার মতো অপটু প্রুফ রিডার তাঁর বই এবং গদ্য সংগ্রহের প্রুফ দেখেছি। তিনি এত উদারভাবে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন কেন কে-জানে!
সেই সূত্রেই মনে পড়ল, আমার তো বটেই, সাত-আট-নয়ের দশকের বহু কবির, ‘কবিতা-পাঠক’ বা বলা ভালো ‘প্রথম পাঠক’ হিসেবে সম্পাদনা করতেন তিনি। বহু মান্য কবির কাব্যগ্রন্থে নির্বাচন থেকে বিন্যাস, হরফ থেকে বানান/ ছন্দ সংশোধন এবং শেষে প্রুফ দেখা সবটাই শঙ্খ ঘোষ করে দিতেন। আমার বইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রুফ দেখতে দিইনি কখনও। এইসব কাজের নানা দিক নিয়েও কিন্তু তাঁর সম্পাদকসত্তার সমগ্রতার সন্ধান করতে হবে। তাঁর সংশোধিত চিহ্নগুলি এবং স্মৃতিগুলি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। খাতায় তিনি বিন্দু-বিন্দু দাগ দিতেন, এবং সেগুলি নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করতেন। সে সময় বাংলা ছন্দ, পঙ্ক্তি বিন্যাসের কাব্যিক তাৎপর্য কিংবা এমনকী, চিত্রকল্প নির্মাণের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলতেন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত টেনে আনতেন যেগুলি অশেষ কার্যকর ছিল সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে। একবার যেমন কথায়-কথায় বুঝিয়েছিলেন ‘স্বপ্ন’ (কল্পনা) কবিতায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প– ‘সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি/ আমার দক্ষিণ করে, কুলায় প্রত্যাশী/ সন্ধ্যার পাখির মতো…’ আর ‘বনলতা সেন’ কবিতায় বহুউদ্যাপিত ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন’– কীভাবে পরস্পর সংলাপ-সংকেতন চালায়। সে মিল-অমিলের দ্বন্দ্বের সূত্রে উঠে এসেছিল প্রতিমা গঠনের নিজস্বতা সন্ধানের কথা। সেসব কথাও কিন্তু গ্রন্থনা সম্পাদনারই অংশ বিশেষ।

যাই হোক, ফিরে যাব, ‘এই সময় ও জীবনানন্দ’ গ্রন্থের দিকে। সেই বইয়ের ‘সূচনাকথা’ অংশে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। দেখা যাক সেই অতুলনীয় বাক্যটি। ‘‘জীবনানন্দের কবিতা বা গদ্য থেকে বহুল পরিমাণে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন আলোচকেরা, কিন্তু লেখার মধ্যে বা পাদটীকায় অনেকেই তার কোনো সূত্র জানাননি। পাঠকের কখনো কখনো কৌতূহল হতে পারে মনে করে এ-বইয়ের শেষাংশে সেজন্য একটি ‘উৎসনির্দেশ’ সাজিয়ে দেওয়া হলো।’’
৩.
‘এই সময় ও জীবনানন্দ’ বইয়ের একেবারে শেষাংশে রয়েছে ‘উৎসনির্দেশ’ অংশ। সেই পর্বে খুব যত্ন করে প্রতিটি পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিগুলির ক্রমসংখ্যা এবং তার উৎস পাশাপাশি নির্ণয় করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রাসঙ্গিক ছত্রসংখ্যাও। খুব সহজেই বোঝা যায়, পুরো তালিকাটি কতদূর শ্রমসাধ্য। আড়াইশোর কাছাকাছি পঙ্ক্তি এবং উৎসের এই তালিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, প্রস্তুতকর্তা জীবনানন্দের যাবতীয় লেখালেখি, গদ্য-কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বর্গের লেখা একেবারে তন্ন তন্ন করে পূর্বাপর পড়েছেন। উৎসের ক্ষেত্রেও সম্পাদক জানাচ্ছেন, ‘দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত’ ‘জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ’-কে ‘সং’ এবং দেবেশ রায় সম্পাদিত ‘জীবনানন্দ সমগ্র’-কে ‘স’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্রের খণ্ডসংখ্যা বোঝানোর জন্য ‘স’-এর সঙ্গে ১, ২, ৩ ইত্যাদি যুক্ত আছে। কেবল ‘ক’ থাকলে বুঝতে হবে জীবনানন্দের প্রবন্ধ-সংকলন ‘কবিতার কথা’, ১৩৬২ সালে মুদ্রিত তার প্রথম সংস্করণ।
‘বাঁদিকে রইল এ-বইয়ের পৃষ্ঠা আর পঙ্ক্তি-সংখ্যা। ডাইনে উৎস সূত্র। রচনা, গ্রন্থ বা/এবং গ্রন্থসংকলন, পৃষ্ঠাসংখ্যা এই ক্রমে।…’
সম্পাদনার এই পদ্ধতি ঈর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয়। এত অনুপুঙ্খে এবং এত স্বচ্ছ সারণীর মাধ্যমে এই তথ্যগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সেই তথ্যপঞ্জি দেখে যে-কেউ করতালি দেবেন।
এছাড়াও, গ্রন্থে জাগরূক আছেন সম্পাদক, কখনও কখনও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন তোলার জন্য। এই প্রশ্নগুলি ঠিক জীবনানন্দের রচনারীতি বা তাঁর সন্ধান বিষয়ে নয়, বরং লেখকদের ‘পাঠ’ আর ‘পরিভষা’, ‘পরিভাষার পরিপ্রেক্ষিত’ এবং ‘পরিভাষার প্রয়োগ যথার্থ্য’ বিষয়ে। এই প্রশ্ন উত্থাপনের সূত্রে বোঝা যায়, সম্পাদক বিভিন্ন নব্য সমালোচনা, সমকালীন তত্ত্ব এবং উত্তর গঠনবাদী দৃষ্টিকোণ বিষয়ে কতখানি অবহিত। যেমন ধরা যাক, ওই গ্রন্থে ত্রিদিব সেনগুপ্তের দীর্ঘ নিবন্ধ ‘মাল্যবান: একটি না উপন্যাস’-এর একটি পাদটীকায় সম্পাদক শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন, “প্রতিসরণ কথাটিকে বাংলায় একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি ‘রিফ্র্যাকশন’ শব্দের অনুবাদ হিসেবে সেটা সংগত। ফুকোর ব্যবহৃত ‘raré faction’-এর সঙ্গে তাকে মেলানো ঠিক হবে কি না, বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক এই সংশয় জানাবার পর লেখক এখানে নতুন একটি পাদটীকা যুক্ত করেছেন। সম্পাদক অবশ্য মনে করেন না তাতেও সমস্যাটার সম্পূর্ণ নিরসন হয়।” অকরুণ এই মন্তব্যের সঙ্গে লেখকের ‘নতুন’ পাদটীকাটিও সযত্নে মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষ করতে হবে, এক্ষেত্রে সম্পাদকের সজীব উপস্থিতি সারস্বত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করছে। প্রশ্নগুলি জীবনানন্দচর্চার সঙ্গে জড়িত এবং স্পর্শকের মতো উত্তর আধুনিক নানা কনসেপ্ট-কে ছুঁয়ে থাকে। এখানে বলা চলে, সম্পাদক উসকে দিলেন পশ্চিমা তত্ত্বভাষ্যের বঙ্গীকরণে কনসেপ্টকে প্রাধান্য দেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্ন। ত্রিদিব সেনগুপ্তের ব্যবহার করা ‘নতুন’ শব্দ ‘দুঃসরণ’ নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর টীকায় তেমন ইঙ্গিতও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, শব্দ নিয়ে এ ধরনের নানা কাটাছেঁড়া এবং জোড়কলম তৈরি করার ধাত আছে জাঁক দেরিদারও। তাঁর তৈরি করা শব্দ এবং কনসেপ্ট Différ ance নিয়েও বাংলা অনুবাদে গভীর সংকট। এ ধরনের শব্দ সরাসরি বাংলায় আনা প্রায় অসম্ভব। অনুবাদ, ভাষাতত্ত্ব এবং উত্তর আধুনিক দর্শন সংক্রান্ত এইসব প্রশ্ন নিয়েই হাজির হলেন সম্পাদক। লেখকের সঙ্গে দ্বিরালাপ প্রকৃতপক্ষে পাঠকের সঙ্গেও কথাবার্তা। একটা প্রাসঙ্গিক সমস্যার রূপরেখা এবং বিতর্ক নিয়ে তাঁর উপস্থিতি গ্রন্থনার আরও একটি মাত্রা খুলে দিল। সম্পাদনা এবং সম্পাদকের এই আকস্মিক মঞ্চে আবির্ভাবও শঙ্খ ঘোষ, বা বলা ভালো সম্পাদক শঙ্খ ঘোষের নয়া সংযোজন! আড়াল রেখেও তিনি সম্পাদককে তত্ত্বকেন্দ্রে দৃশ্যমান করলেন!
(চলবে)
…পড়ুন ভাষ্য শব্দের তর্জনী-র অন্যান্য লেখা…
পর্ব ১. কত কম বলতে হবে, মুখের কথায়, সভায়, কবিতায় কিংবা ক্রোধে– সে এক সম্পাদনারই ভাষ্য
পর্ব ২. তথ্যমূলক তথাকথিত নীরস কাজে শঙ্খ ঘোষের ফুর্তির অন্ত ছিল না
পর্ব ৩. কোনও সংকলনই গ্রন্থনার পূর্ণচ্ছেদ হতে পারে না, ভাবতেন শঙ্খ ঘোষ
পর্ব ৪. শঙ্খ ঘোষ বলতেন, অদৃশ্যে কেউ একজন আছেন, যিনি লক্ষ রাখেন এবং মূল্যায়ন করেন প্রতিটি কাজের
পর্ব ৫: অনিশ্চয়তার কারণেই কি রবীন্দ্রনাথের গানে ও পাণ্ডুলিপিতে এত পাঠান্তর?
পর্ব ৬. সহজ পাঠের ‘বংশী সেন’ আসলে ‘বশী সেন’, দেখিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
