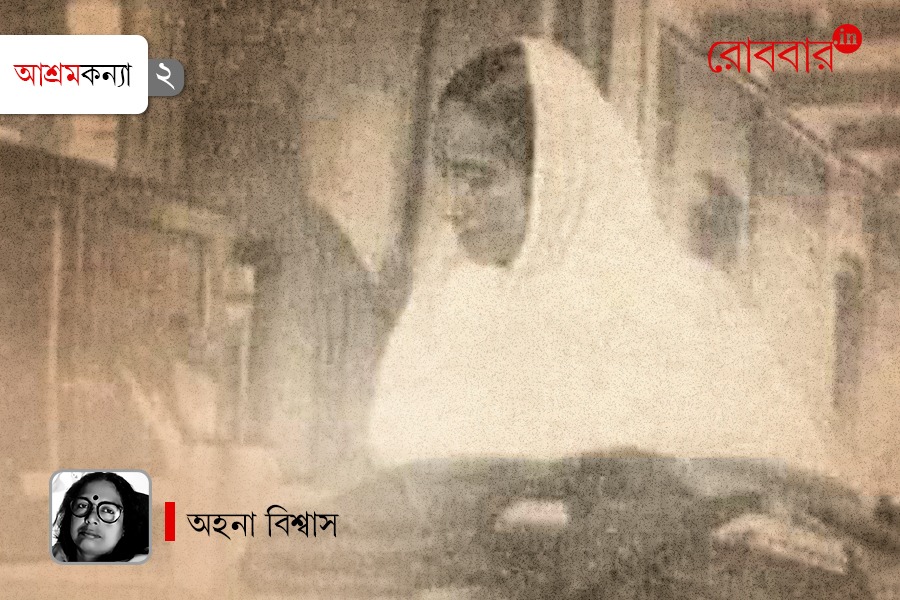
সুকুমারী দেবী ছিলেন স্বভাবশিল্পী। যিনি গ্রাম ঘরে দেশি সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করতেন, তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনের ভাণ্ডার থেকে নানা ধরনের সূচিশিল্পের নমুনা দেখে দেখে নিজেই নানাপ্রকার অপূর্ব ফোঁড়ের জন্ম দিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যারা নতুন সেলাই সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠলেন। লখনউয়ের স্টিচ, কাঠিয়াওয়ারার স্টিচ, কাচ বসানো স্টিচ, বাংলাদেশের কাঁথার ফোঁড়– সব মিলিয়ে অসাধারণ সীবনশিল্পে মেতে উঠল আশ্রমেরকন্যারা। সে-সব দেখার মতো সেলাই ব্লাউজের হাতায়, শালের নকশায়, টেবিলক্লথে, শাড়ির পাড়ে স্থান পেল। সেইসব অসামান্য কারুকাজ চিরকালীন শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল।

২.
শান্তিনিকেতনের অঙ্গনের শ্রী ফোটাতে যে আশ্রমকন্যারা অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গৌরী-যমুনা-চিত্রনিভার নাম প্রথমেই উঠে আসে। এছাড়াও আর একজনের কথা বিশেষভাবে আসে। তাঁর নাম সুকুমারী দেবী– যাঁকে সকলে ‘মাসিমা’ বলে ডাকতেন। সেকালের শান্তিনিকেতনের আত্মীয়সমাজের পরিবেশকে শ্রীমণ্ডিত করার সাধনা বিশেষ গুরুত্ব পেত। সুকুমারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কাছের মানুষ কর্মযোগী কালীমোহন ঘোষের স্ত্রী মনোরমা দেবীর মাসি। বরিশালের গ্রামে বসে তিনি খুব সুন্দর আলপনা দেন শুনে একদিন শান্তিনিকেতনে তাঁর ডাক পড়ল। ১৪ বছর বয়সে বাল্যবিধবা, সূচিশিল্প ও আলপনায় পারদর্শী মেয়েটি ঈদুলপুরের গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে পা দিয়ে হয়ে উঠলেন যথার্থই আশ্রমকন্যা। গ্রামীণ শিল্পকলা শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতিতে ডুবে, মাজাঘষা পেয়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পেল সুকুমারীর হাতে।
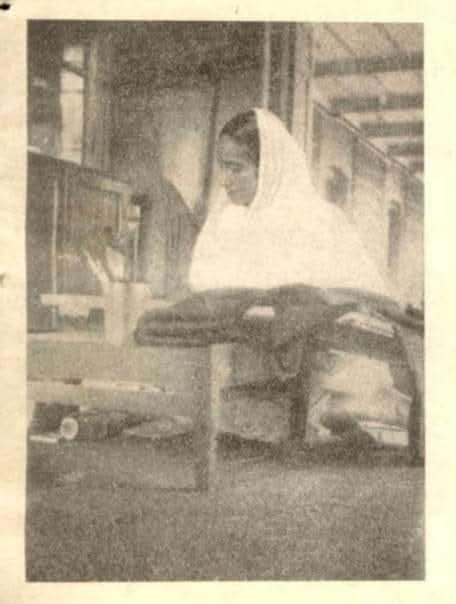
শুধু কি গ্রামের মেয়ের শান্তিনিকেতনে পদার্পণ! রবীন্দ্রনাথ গুণের মর্যাদা দিতে জানতেন। তাঁর জহুরির চোখ গুণীকে মুহূর্তে চিনে নিতে পারত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কমলাদেবীর একটি শালের এমব্রয়ডারি করেছিলেন সুকুমারী। সেই শিল্পকাজটি দেখে মুগ্ধ হয়ে সুকুমারীকে তৎক্ষণাৎ কলাভবনের শিল্পশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করে দেন স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।
কী আশ্চর্য সেই সময়! কী আশ্চর্য সে-সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা! বিকেলবেলায় সুকুমারী নিজে নন্দলাল বসুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন মনোযোগ দিয়ে, শিল্পকলার যাবতীয় আঙ্গিক আত্তীকরণ করেন। আর সকালে ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমারী নিজে আলপনা দিতে শেখান। তাঁর গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল খুবই বেশি। তাঁর দেওয়া আলপনা বা মণ্ডনশিল্প এবং সূচিশিল্প এত সুন্দর ছিল যে, পরবর্তীকালে সে-সবের অনুকরণে একটি বিশেষ ঘরানা তৈরি হয়ে যায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমে। পরবর্তীকালে যতজন শান্তিনিকেতনে আলপনা শিখেছেন সুকুমারী ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের গুরু।

সৌন্দর্যের অন্যতম অঙ্গ হল পারিপাট্য। সহজ গার্হস্থ সৌন্দর্যের রূপায়ণে সেই গ্রামীণ মণ্ডনকলা সুকুমারীর হাত দিয়ে নবীনরূপে আত্মপ্রকাশ করল। আশ্রমবিদ্যালয়ে অন্য সব কাজের মধ্যে কন্যাদের সেলাইও শিখতে হত। নিজেদের ও ছোট ছেলেমেয়েদের ছিঁড়ে যাওয়া জামাকাপড় সেলাই করা এবং বোতাম লাগানোর কাজ শিক্ষার্থীদের শিখতেই হত। প্রতিদিনের কাজকে কত নিপুণভাবে, কত শ্রীমণ্ডিতভাবে প্রকাশ করা যায়, ছোট ছোট পদক্ষেপে সেই কাজেরও দীক্ষা ছিল আশ্রমবিদ্যালয়ে।
সুকুমারী দেবী ছিলেন স্বভাবশিল্পী। যিনি গ্রাম ঘরে দেশি সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করতেন, তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনের ভাণ্ডার থেকে নানা ধরনের সূচিশিল্পের নমুনা দেখে দেখে নিজেই নানাপ্রকার অপূর্ব ফোঁড়ের জন্ম দিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যারা নতুন সেলাই সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠলেন। লখনউয়ের স্টিচ, কাঠিয়াওয়ারার স্টিচ, কাচ বসানো স্টিচ, বাংলাদেশের কাঁথার ফোঁড়– সব মিলিয়ে অসাধারণ সীবনশিল্পে মেতে উঠল আশ্রমেরকন্যারা। সে-সব দেখার মতো সেলাই ব্লাউজের হাতায়, শালের নকশায়, টেবিলক্লথে, শাড়ির পাড়ে স্থান পেল। সেইসব অসামান্য কারুকাজ চিরকালীন শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল।
গুরুদেব এবং তাঁর তৈরি সেদিনের শান্তিনিকেতন এমন এক পরশপাথর ছিল যে তার সংস্পর্শে নিতান্ত গ্রামের মেয়েও সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আলপনার দীক্ষা দিতে পারতেন। আমরা দেখলাম সেই পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে সীবন শিল্পের গুরু হিসেবে সুকুমারী দেবীর স্থান বঙ্গসংস্কৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে রইল।
এভাবে একটি বাল্যবিধবা অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা হিসেবে সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে ওঠেন। কলাভবনের মণ্ডনশিল্পী এবং সূচিশিল্পের গোড়াপত্তনে তাঁর অবদানকে আজ কেউ অস্বীকার করবেন না। সুকুমারী ছবি আঁকতেন সে-সময়ের রীতি অনুযায়ী, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে। এইসব ছবি আঁকা ছাড়া শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আলপনা তো দিতেনই। যাঁরা তাঁর কাজ দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, সুকুমারী যখন পদ্মের আলপনা দিতেন তখন তা সত্যিকারের পদ্মের মতোই দেখতে হত।
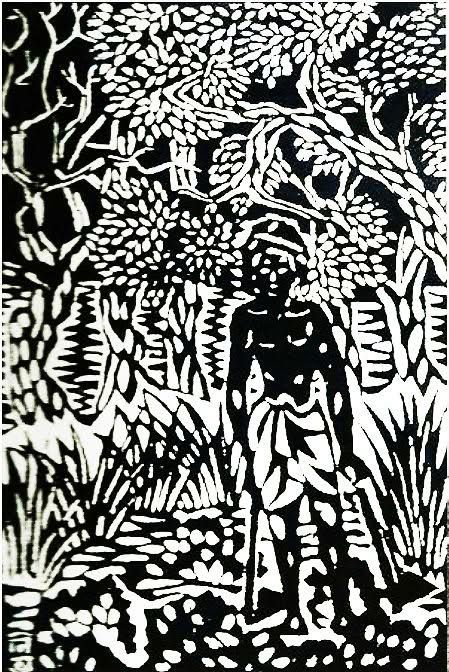
১৯৩৬ সালে এই আশ্রমকন্যা ধরাধাম ছেড়ে বিদায় নেন। তখন সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা ‘প্রবাসী’তে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। ‘প্রবাসী’ লেখে– ‘আলপনা ও অন্য নানান গৃহশিল্পে তিনি নিপুণ ছিলেন। নূতন আলপনার পরিকল্পনায় তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন পৌরাণিক অন্যবিধ ছবি আঁকিতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন।’ বাংলার ব্রত প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, ‘না শেখার লেখা আর্ট স্কুলের পাকা হাতের লেখাকে হার মানিয়েছে।’ সুকুমারীর কথা ভাবলে তেমনটি মনে হয়। শান্তিনিকেতনে আলপনা যে আজ ইতিহাস হয়ে উঠেছে, তাতে যে ক’জন আশ্রমকন্যার অবদান আছে সুকুমারী হয়তো তাঁদের প্রথমেই থাকবেন।
সুকুমারীর কথা বলতে বলতে আর একজন শিল্পী আশ্রমকন্যার কথা মনে হয়। তিনি চিত্রনিভা– চিত্রনিভা চৌধুরী। চিত্রনিভার আসল নাম ছিল নিভাননী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রশিল্পে আগ্রহ দেখে তাঁর নামটি পরিবর্তন করে ‘চিত্রনিভা’ রাখেন।
চিত্রনিভা সেই যুগে এক বিরল সৌভাগ্যের অধিকারিণী। ১৪ বছর বয়সে যাঁর আঁকা ছবি দেখে, নোয়াখালীর লামচোরের অত্যন্ত সংস্কৃতিবান জমিদার মনোরঞ্জন চৌধুরী তাঁর ছোট ভাই নিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রনিভার বিবাহ দেন। শুধু বিয়েই দেন না, ১৯২৮ সালে চিত্রনিভার শ্বশুর তাঁকে কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রকলা এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সংগীত শিখতে পাঠান।

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি যেন চিত্রনিভাকে বরণ করে নিল চিত্রনিভা লিখেছে, ‘তখন ছিল শরৎকাল। প্রকৃতি দেবী তার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছড়িয়ে রেখেছিলেন সারা আশ্রমে। সমস্ত মাঠঘাট অপূর্ব রূপে সজ্জিত হয়ে ছিল। শিউলি ফুলের গন্ধে সারা আশ্রম মধুময় হয়ে উঠেছিল।
সন্ধ্যার সময় আমি আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। তখন গুরুপল্লীর কুটিরে কুটিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠল। দিনান্তের ক্লান্ত রবি তার শেষ আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে গেল সমস্ত ধরণীকে। গোয়ালপাড়ার রাঙা পথ সিন্দুরের মতো রঞ্জিত হয়ে উঠল। তারপর শ্রীরবীন্দ্রনাথকে দর্শন করে আমার জীবন ধন্য হল।’
প্রকৃতির মধ্যে আত্মভোলা হয়ে থাকা এমন শিল্পী যে তাঁর ছবিতে, মিউরালে, আলপনায় প্রকৃতিকে ছড়িয়ে দেবেন– এটাই স্বাভাবিক। চিত্রনিভা ঠিক তাই করেছেন। তাঁর ছবি দেখে যেন প্রকৃতিকে নতুন রূপে আবিষ্কার করি আমরা। খুব সুন্দর লিখতেন চিত্রনিভা। তার রবীন্দ্রস্মৃতি পড়লে সেই স্বর্ণযুগে আমরা ফিরে যাই। সেই গ্রন্থে সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের আর গুরুদেবের কত যে অসাধারণ সব চিত্রমালা পাই!

একবার চিত্রনিভা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আঁকা ডিজাইন দেখাতে নিয়ে গেছেন। ডিজাইনের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা আছে। সেই জায়গায় কিছু লেখার জন্য গুরুদেবের হাত সুড়সুড় করছে বুঝতে পেরে তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন সেখানে কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। পরদিন চিত্রনিভা দেখেন, ডিজাইনের সেই ফাঁকা জায়গায় কবি একটি নতুন কবিতা লিখে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে যাকে আমরা গান হিসেবে পেয়েছি। ওই যে–
‘যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ।’
রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমবিদ্যালয়ের আশ্রমকন্যাদের অগাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সেখানে আলাদা করে কোনও প্রহরী রাখতেও দেননি। মেয়েদের স্বাধীন সত্তাকে এতটাই মূল্য দিতেন তিনি। তাই চিত্রনিভার স্কেচ করতে যাওয়ার জন্য তিনি কোনও সীমানা নির্দেশ করেননি, ছবি আঁকার জন্য তিনি যতদূর খুশি যেতে পারতেন। কোনও বাধা ছিল না কোনওখানে।

তেমনই যখন আরও বড় ক্ষেত্রে, স্বদেশি আন্দোলনের সময় বন্ধু ফিরোজা বারিকে নিয়ে গ্রামের কাজে যোগ দিলেন চিত্রনিভা– তখনও এই আশ্রমবালিকাকে গুরুদেব দেশের কাজের, আশ্রমের বাইরে মানুষের কাজের জন্য অনুমতি দিতে দ্বিধা করলেন না। গুরুদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, বাঁধগোড়া গ্রাম থেকে শুরু করে মাইলের পর মাইল খালি পায়ে হেঁটে, অশেষ পরিশ্রম করে সে সময় চিত্রনিভারা কাজ করেছেন। আশ্রমের কাজ তো শুধু ভৌগোলিক সামান্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আশ্রমকন্যাদের রবীন্দ্রনাথ বিশ্বক্ষেত্রে বিচরণ করার জন্য তৈরি করেছিলেন। তাঁরাও তেমনই তৈরি হয়েছিলেন ।

এই আশ্রমদুহিতা নন্দলাল বসুর অধীনে শিল্পকলা শিক্ষা করেন। কালো বাড়ির নির্মাণের সময় তিনি রামকিঙ্করদের সঙ্গে হাত লাগান। চিত্রনিভা শ্রীসদনের দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করেন। সে আমলে তাঁর নিজস্ব ক্যামেরা থাকলেও তিনি শান্তিনিকেতনে আগত অতিথিদের পোর্ট্রেট আঁকতে থাকেন। মহাত্মা গান্ধী, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বিখ্যাত মানুষজনের মুখ তিনি আঁকেন। সেইসব ছবি একে একে ‘জয়শ্রী’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় তিনি প্রথম মহিলা অধ্যাপক হিসেবে কলাভবনে যোগ দিলেন।
নন্দলালের কাছে চিত্রনিভা শিখেছিলেন চাল, ডাল প্রভৃতি শস্য দিয়ে আলপনা দিতে। শুধু শান্তিনিকেতনে নয়, তিনি তাঁর মণ্ডনকলাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আশ্রমের বাইরেও। তিনি ফ্রেস্কো করেছেন, ভাস্কর্য করেছেন, কাদামাটি ঘেঁটে উঁচু ভারাতে উঠে অক্লেশে কাজ করেছেন। তারপর নোয়াখালীর লামচোর গ্রামে ফিরে তিনি বাড়িতে সংগীত ও শিল্পকলা সংস্কৃতি কেন্দ্র খুলে সকলকে চামড়ার কাজ, সেলাই, গান-বাজনা, বাটিকের কাজ শিখিয়ে গেছেন। এমনকী, চিত্রনিভা সেখানে সাহিত্যের আসরও বসাতেন। এভাবে আশ্রমের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে তিনি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আশ্রমের শিক্ষার পরিপূর্ণ রূপ তাঁর মধ্যে বাস্তব প্রকাশ পেয়েছিল।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
