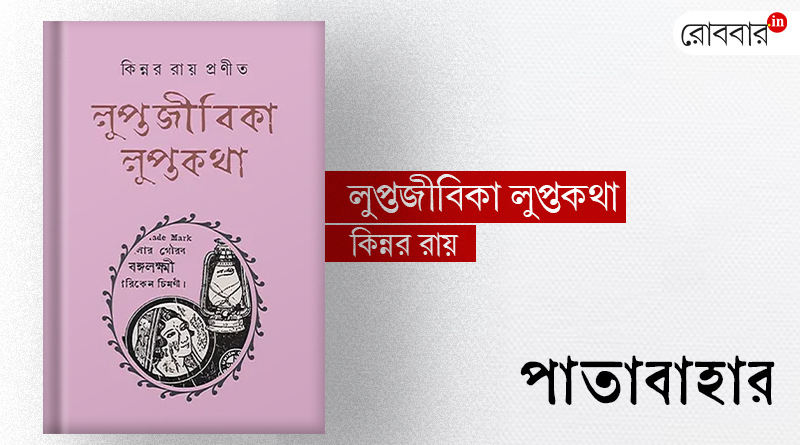
যে সমস্ত জীবিকা বেপাত্তা, তাদের স্মৃতিরোমন্থন, যে-স্মৃতিরোমন্থন আসলে ইতিহাসই, আক্ষরিক তথ্যচিত্র। লিখছেন রিংকা চক্রবর্তী।

কত কিছুই তো হারিয়ে যায় জীবন থেকে। বই, খাতা, পেনসিল, রুমাল, ছেলেবেলা, প্রেম, খেলার মাঠ, এমনকী, মানুষের জীবনও। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মুহূর্তে পড়ে থাকে শুধু স্মৃতি। কোনওটাই খুব প্রত্যাশিত নয়। ‘সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।’ বাঁকে পড়ে অন্যদিকে ঘুরে যায় যেমন নদীর গতিমুখ, তেমনই স্রোতের ধারা তার দু’-প্রান্তে রেখে যায় ভাঙাগড়ার চিহ্ন। সময়ের ছাঁচে সব কিছু আবার নতুন রূপে গড়ে ওঠে। এই বদলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চলতে এগোনো, এভাবেই নিরন্তর প্রবাহ। খানিক রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ার মতো। আজকে যা প্রয়োজনীয়, কাল তা কাজে নাও লাগতে পারে। আসতে পারে বিকল্প। এটাই স্বাভাবিক।
কালের নিয়মেই পাল্টেছে যুগের হাওয়া, পাল্টেছে সামাজিক রীতিনীতি, বদল এসেছে নানা ক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয়। সেখানে পেশার ক্ষেত্রই বা বাদ যায় কেন! বিগত কয়েক বছরে আমাদের দৈনন্দিনের সঙ্গে জড়িত অনেক পেশা এখন ‘লুপ্ত’। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা হাপিশ। আবার কিছু ফিরে এসেছে নবরূপে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের কাজ। তারপর সেই পেশাও একদিন পুরনো হয়েছে। তার জায়গায় এসেছে আধুনিক ছোঁয়া, অথবা একেবারে বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছে প্রায়। কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায়ের এই বিষয়ে রয়েছে চমৎকার একটি বই– ‘লুপ্তজীবিকা লুপ্তকথা’, যার ট্যাগলাইন বলা যেতে পারে– ‘কিছু জীবিকা, কিছু কথা, কিছু লুপ্ত, বাকিরা লুপ্তপ্রায়…।’
কথাকার হবেন, এ-ভাবনা তাঁর কখনওই ছিল না। তবু দেখা না-দেখায় মেশা এই জীবনে কিছু বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন এই বইতে। জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সব জীবিকার অণুকথা তিনি মেলে ধরেছেন বইয়ের পাতায় পাতায়।
আরও পড়ুন: সেন্সরের কাঁচি কি ব্যতিব্যস্ত করেছিল রায়সাহেবকেও? উত্তর দিচ্ছে ‘সুবর্ণ সাক্ষাৎ সংগ্রহ’
প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরেই মূলত বিলুপ্ত হয়েছে পেশাগুলো। যেরকম চিঠির গুরুত্ব অনেকটাই কমে এসেছিল টেলিফোন আসার পর। বিদেশে পাঠানো চিঠির জায়গা নিল প্রথমে ফ্যাক্স, তারপর ইন্টারনেট পরিষেবা আসার পর ই-মেল। একটা সময় ছিল রানারদের রমরমা। বরশার মাথায় ঘুঙুর লাগিয়ে ছুটত তারা। রানার যে কার চিঠি বা কার টাকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তা জানা যেত না। বহুযুগ হল বেপাত্তা হয়েছে রানাররা। তারা শুধু কবিতায়, গানে, গল্পে।
আমাদের ছোটবেলায় বহুরূপীদের অনেক দেখেছি। মা কালী-সহ আরও নানা চরিত্রে সেজে ঘুরে বেড়াত গ্রাম-মফস্সলের এদিক-সেদিক। দুপুরবেলা, নয়তো বিকেল-সন্ধেয় বহুরূপী চলে আসত। তাদের হঠাৎ আগমনে বাচ্চারা ভয়ে পেয়ে যেত অনেক সময়। বংশপরম্পরায় চলে আসত এই পেশা। কেউ কেউ মুখোশ পরত, কেউ বা শুধুমাত্র মেক-আপের সাহায্যেই ফুটিয়ে তুলত নিজেকে। শহরের মানুষ তাদের বলত ‘সং’। এখন তো ঘরে ঘরে, পথে পথে, কাজের জায়গায় সব অন্য বহুরূপী। নিজের আসল মুখটি আড়াল করে, বারে বারে মুখোশ-বদল।
আরও একটি পেশা, যা লুপ্তপ্রায়, কম্পাউন্ডার। তাদেরকে বলা হত, ‘হাফ ডাক্তার’। ডাক্তারদের দুর্বোধ্য হাতের লেখা উদ্ধার করে মিক্সচারের ফরমুলা বুঝে নিয়ে তারাই বানিয়ে ফেলত ওষুধের মিক্সচার। ফোড়া কাটা থেকে বোরিক কমপ্রেস, কাটা-পোড়া-ঘা-অপারেশনের জায়গা ড্রেসিং করা, গজ-ব্যান্ডেজ বদলে দেওয়া, কাটা জায়গা সেলাই করা– এসব কাজ ছিল তাদের কাছে বাঁয়ে হাত কা খেল। কখনও এরা হত পাশ করা, কখনও না-পাশ করাও। তাই বলে আধা-শহর, গ্রামে এদের গুরুত্ব একজন ডাক্তারের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। এখনও বেশ কিছু জায়গায় ‘কম্পাউন্ডার’ শব্দটির চল আছে, তবে এখন বেশিরভাগই ‘ফার্মাসিস্ট’ বলতেই স্বচ্ছন্দ। তাই এই পেশাটিও ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে চলেছে, এ-কথা বলাই যায়।
হারিয়ে গিয়েছে মহিলাদের বেশ কিছু সাবেকি পেশাও। আগেকার সময় মহিলারা পর্দানশিন থাকলেও তথাকথিত নিম্নবিত্ত শ্রেণির মহিলারা কয়েকটি পেশায় যুক্ত থাকত, মূলত উচ্চবিত্তদের অন্দরমহলেই। যার মধ্যে অন্যতম ছিল আলতা পরানো নাপিতানি। নাপিতের স্ত্রী, যাদের চলতি বাংলায় বলা হত নাপতে-বউ, তারা জমিদার বাড়িতে, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তর বাড়িতে আসত বাড়ির মেয়ে-বউদের আলতা পরাতে। আলতা দিয়ে নানারকমের নকশাও করে দিত। এখন অবশ্য বিয়ে বা পুজোপার্বণে আলতা পরার রেওয়াজটাই টিকে রয়েছে। আলাদা করে নাপিতানি ডাকিয়ে তাকে পয়সা দিয়ে আলতা পরানোর চল গত হয়েছে অনেকদিন।
এই পেশার মতোই বিলুপ্তপ্রায় ধাই-মা বা দাই-মা এবং দুধ মা। ধাই কথাটা এসেছে ধাত্রী থেকে; ‘ধাই’ থেকে অপভ্রংশ হয়ে ‘দাই’। সেকালে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রসব হত বাড়িতেই। বাড়ির একটি অংশে তৈরি হত আঁতুড়ঘর, সেখানেই নির্দিষ্ট দিনে ধাই এসে প্রসব করাত।
দুধ-মায়েদের কাজও ছিল সদ্যোজাত শিশুদের নিয়েই। একজন নারী অর্থের বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে আসত। ধাই-মায়েদের মতোই তাদের সম্মান ছিল যথেষ্ট। এই বিষয় নিয়েই মহাশ্বেতা দেবী একটি অসামান্য গল্প লিখেছিলেন– ‘স্তন্যদায়িনী’। দুধ-মা কনসেপ্টটি জীবিকা হিসাবে এখন আর নেই। রয়েছে ‘সারোগেট মাদার’। তবুও স্মৃতি হয়ে যাওয়া এইসব দুধ-মায়ের ভূমিকা নিয়ে কিন্নর রায়ের লেখা আবেগপ্রবণ করে তোলে।
এছাড়া আরও কত জীবিকাই না বিলুপ্তির পথে, অথবা পুরোপুরিই হারিয়ে গিয়েছে, যেরকম– ‘পুকুর-ডুবুরি’, ‘সাজো ধোপা’, ‘ক্যাচার’, ‘কুয়োর ঘটি তোলা’, ‘অগ্রদানী’, ‘পালকির বেহারা’, ‘সহিস, কোচোয়ান’– এরকম আরও কত! লুপ্তকথায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘নেমন্তন্ন বাড়ির মেনু বদল’, ‘হারিয়ে যাওয়া ডাক’, ‘কত যে নতুন শব্দ’, ‘মশারি’, ‘চোদ্দপিদিম, চোদ্দশাক’। এখনও কিছু বাড়িতে চোদ্দো প্রদীপ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু বাজার গরম করেছে এলইডি। আর লেখক যথার্থই বলেছেন, বাজারে এখন চোদ্দো শাক বলে যা বিক্রি হয়, সেই শাকে চোদ্দোরকম আছে কি না, কে জানে!
কী সুন্দর গল্পচ্ছলে লিখে গিয়েছেন কিন্নর রায়! পড়তে কোথাও একঘেয়েমি আসে না। আগেকার দিনের সমাজ-ভাবনাকে একালের সঙ্গে তুলনা করে উপস্থাপন করেছেন এক-একটি বিবরণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই হারিয়ে যায়। কিছু ফিরে আসে নতুন মোড়কে। ওই যেমন বলে, পুরনো বোতলে নতুন মদ। আজ যা ঝলমল করছে, কয়েক বছর বাদেই হয়তো তা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। কিন্তু সবকিছুর রিপ্লেসমেন্ট হয় কি? কিন্ডল বা অডিও বুক আসার পরেও হাতে নিয়ে বই পড়ার আনন্দ কি মুছে গিয়েছে একবারও? না কি, AI যতদূরই এগোক, যে তাকে বানিয়েছে, সেই হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিকে সে কখনও অস্বীকার করতে পারবে? সময়ই উত্তর দেবে।
লুপ্তজীবিকা লুপ্তকথা
কিন্নর রায়
প্রতিক্ষণ। ৩০০ টাকা
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
