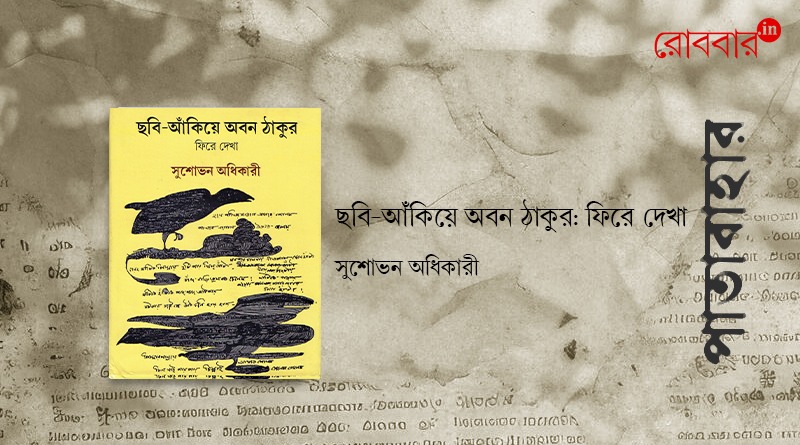
একটি বই, যা দিয়ে অবন ঠাকুরকে ফিরে পাওয়া যায়। ভারত কী ছিল ও কী হইয়াছে, সম্ভবত সে-ও টের পাওয়া যায়। শিল্পীর চিন্তা কোন পথে ধরে অগ্রসর হল, কী দেখাল ও কী দেখাল না, তাও এই বইয়ের কালো অক্ষরে বলা। রয়েছে বহু ছবিও। ছবি-লেখার অবন ঠাকুর, ছবি-আঁকার অবন ঠাকুরের পাশাপাশি– তাঁকে ও তাঁর কাজকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়াও এই বই পড়ার ফুর্তি।

স্বদেশি হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এক শিল্পীর নাম। সময়টা আরও খতিয়ে দেখলে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনাপর্বে। ভারতীয় শিল্প ঘরানা তখন তাঁকে প্রায় স্বীকার করেই নিয়েছে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের সিংহাসনে। সেই শিল্পীর হাতে ফুটে উঠছে এই ভারতেরই নানা রূপ। অনেকটা নাট্যাভিনয়ের মতো তাঁর ছবির চরিত্ররা। সংলাপ বলতে উদ্যত, মুখর হয়ে আছে সেসব চরিত্র। কী আঁকছেন সেই শিল্পী? প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভারতীয় পুরাণ। তিনি রাজা রবি বর্মা। ব্রিটিশ বিরোধিতার যে আবহাওয়া, সেই আবহে এই ছবিগুলি– একের পর সাধারণের মনে জায়গা করে নিচ্ছে। চিত্রের ভাষায় যেন অনূদিত হচ্ছে স্বদেশি আন্দোলন। ছবির পরিধি থেকে এ হল দেশজ উপাদানের দিকে ঝোঁকা, স্বাদেশিকতায় শিল্পিত ঝাঁপ দেওয়া।

কিন্তু, ‘কিন্তু’ রয়ে গিয়েছে একটা। সেই কিন্তুর জোর ক্রমে টের পাওয়া যাবে। সময়ের দূরত্বে তা আরও জোরালো। রাজা রবি বর্মা যে ছবির দেশ তৈরি করছেন, তা ভারতীয়। দেশজ উপাদানে ভরপুর, কিন্তু তাঁর আঙ্গিকে রয়ে গিয়েছে পশ্চিমি তেলরঙের দৃঢ় ছাপ। ফলে ছবির বিষয়টি ‘ভারতীয়’ হলেও, আঙ্গিকে তা বিলিতি। স্বদেশি আন্দোলনের রূপান্তরটি সম্পূর্ণ ‘স্বদেশি’ নয়।
……………………………………………………..
অবনীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেই রয়েছে, এই সময়ে ওঁর ছাত্র নন্দলাল বসু বলেছিলেন, ‘পাখি?’। ‘না, পাখি উড়ে গেছে, দাঁড়টি থাক।’ ‘ডাকঘর’ নাটকের ভেতরে থাকা যে শূন্যতার আবহ, তা যেন ওই দাঁড়ে দোল খাওয়ালেন অবনীন্দ্রনাথ। সুশোভন অধিকারী, ধরিয়ে দিয়েছেন সেই চিন্তামূল– ‘মঞ্চের অসংখ্য উপকরণের পাশে ওই পাখিহীন শূন্য একটি দাঁড় টাঙিয়ে কাহিনির মূল সুরটি ছুঁয়ে দিলেন। সব ছাপিয়ে ওই শূন্য দাঁড় যেন অমলের জীবনের নীরব প্রতীক হয়ে উঠলো।’
……………………………………………………..
এই পরিবহেই জরুরি হয়ে উঠেছেন অবন ঠাকুর। সে-কথা খানিক শুনে নিই, সুশোভন অধিকারীর কাছ তিনি। তিনি লিখছেন, ‘আজ নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করতে হয় যে, ভারতীয় ছবির আধুনিকতা অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে এসেছে। আমাদের শিল্পকলায় তিনিই প্রথম পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এমন এক সেতু বাঁধতে এগিয়ে এসেছিলেন।’ যে কারণে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ‘ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী’ বিশেষণ অভিহিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে। তাহলে কি অবন ঠাকুরকে শুধুই এই বিশেষণে সীমায়িত করব? এর উত্তরও দিয়েছেন সুশোভন অধিকারী, বলেছেন, ‘তাঁর চিত্রকে ভারত শিল্পের একান্ত নিদর্শন বলে গ্রহণ করাও চলে না। সেদিক থেকে তাঁর ছবি স্বদেশ স্বকালের সীমানা ছাড়িয়ে শিল্পীর নিজস্ব নন্দন-আদর্শের দ্বারা জড়িত।’

কিন্তু শুধু এটুকু দিয়েও অবনীন্দ্রনাথকে মাপা যায় না। মঞ্চসজ্জার শিল্পী হিসেবে কী করছেন অবন ঠাকুর? ‘ডাকঘর’ নাটকে পাড়াগেঁয়ে ঘর তৈরি হচ্ছে বাহারি পটচিত্র দিয়ে। সেটাকে নেপথ্যে রেখে, একটি দাঁড় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেই রয়েছে, এই সময়ে ওঁর ছাত্র নন্দলাল বসু বলেছিলেন, ‘পাখি?’। ‘না, পাখি উড়ে গেছে, দাঁড়টি থাক।’ ‘ডাকঘর’ নাটকের ভেতরে থাকা যে শূন্যতার আবহ, তা যেন ওই দাঁড়ে দোল খাওয়ালেন অবনীন্দ্রনাথ। সুশোভন অধিকারী, ধরিয়ে দিয়েছেন সেই চিন্তামূল– ‘মঞ্চের অসংখ্য উপকরণের পাশে ওই পাখিহীন শূন্য একটি দাঁড় টাঙিয়ে কাহিনির মূল সুরটি ছুঁয়ে দিলেন। সব ছাপিয়ে ওই শূন্য দাঁড় যেন অমলের জীবনের নীরব প্রতীক হয়ে উঠলো।’
……………………………………………………..
আরও পড়ুন সরোজ দরবার-এর লেখা: রবি-আলোকে চেনার অভ্যাসে প্রতিমা দেবী আজও অপরিচিত
……………………………………………………..
যে বই পড়ছিলাম, তা কিছুদিন হল প্রকাশিত হয়েছে। ‘ছবি-আঁকিয়ে অবন ঠাকুর: ফিরে দেখা’। সুশোভন অধিকারীর এই বই সত্যিই ফিরে দেখার, ফিরে তাকানোর। দেড়শো বছর আগে এই শিল্পীর জন্ম, অথচ এখনও তাঁর ছবি-লেখা ও চিত্রশিল্পকে সময়ের কাঁচি ছেঁটে ফেলতে পারেনি। আজকে, এদেশে এক বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্রমশ ‘দেশ’-এর ধারণায় ঘা মারতে চায়, ‘দেশপ্রেম’ প্রতিষ্ঠা করতে চায় সুবিধাবাদী ছকে– এই ষড়যন্ত্রের মুখে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দর্শনই যথাযথ বর্ম। অবনীন্দ্রনাথকে জানা-পড়ার ছল আসলে ভারতের বিরাটত্বকে স্বীকার করাই। ভারতশিল্প পুনরুদ্ধার যেমন করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, আজ সম্ভবত সেই অতীত ভারতের আত্মাটিকেও পুনরুদ্ধার করা জরুরি বলে প্রয়োজন বোধ হচ্ছে।
ছবি-আঁকিয়ে অবন ঠাকুর: ফিরে দেখা
সুশোভন অধিকারী
দোসর
৭৫০
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
