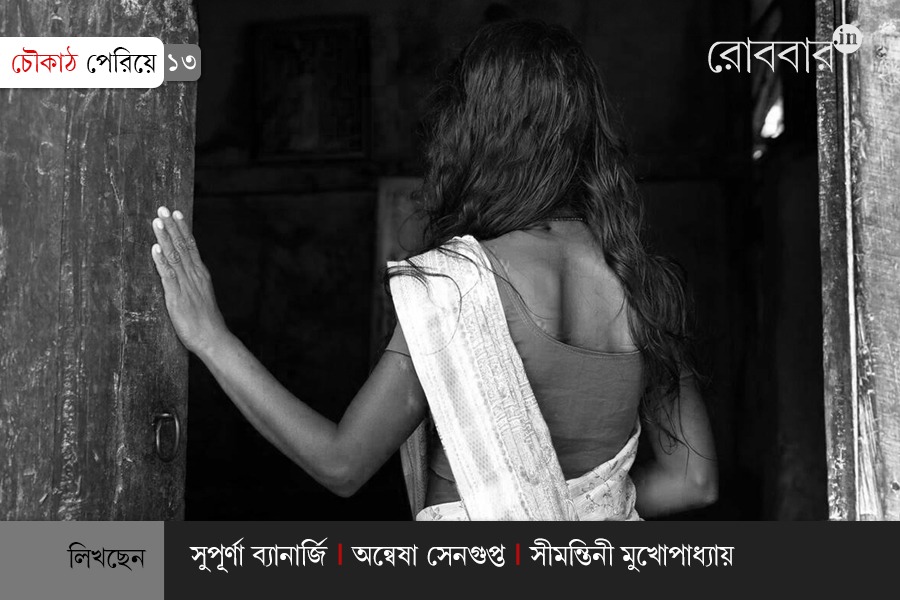
মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ৭১’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘দেহমন’ বা সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘রোদন ভরা বসন্ত’ সিনেমা অবশ্য যৌনকর্মী মেয়েদের প্রতি সহমর্মী। নিদারুণ দারিদ্র আর অসাম্যের কারণে তথাকথিত ‘ভদ্র’ পেশায় সুযোগ পেতেন না যে মেয়েরা, তাঁরা কখনও কখনও জীবিকা হিসাবে বেছে নিতেন যৌনকর্মকেও। প্রচ্ছদের ছবিটি প্রতীকী।



পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের ভিড়ে শহরে পা ফেলবার যো নেই, শহরে তাদের স্থান দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির পুনর্বসতি সাব কমিটি স্থির করেছেন, এই পতিতা পল্লীটিকে শহরের মাঝখান থেকে যদি উপড়ে ফেলা যায়, অনেক জায়গা বেরুবে। বহু ভদ্র গৃহস্থ ঘর-সংসার পাততে পারবে এখানে। বস্তিবাড়িগুলির মালিক প্রাণগোপাল মল্লিক প্রথমে এক আধটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি জোর চাপ দিয়েছেন। তাছাড়া প্রাণগোপালকে একথাও কমিটি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এতে তার লাভ ছাড়া লোকসান নেই। বস্তির ঘরগুলির জন্য ওরা যা ভাড়া দেয়, বিপাকে পড়ে বাঙালরা তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম ভাড়া দেবে না। ফলে প্রাণগোপালেরও কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।
বিদ্যুৎলতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বাড়িওয়ালি সুখদা অবশ্য সে নোটিসের কথা প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ২৫ বছর ধরে দেখে দেখে পুরুষ চিনতে তার আর বাকি নেই। তাদের তুলে দিয়ে বাবুরাই থাকতে পারবে না। দিনের বেলা যারা নাক সিঁটকায়, রাত্রে এসে তারাই পায়ে ধরে সাধাসাধি করে। তুলে দেওয়া অমনি চাট্টিখানি কথা কিনা! তুলে দিয়ে ওরা নিজেরাই কি একতিল সুস্থ থাকতে পারবে নাকি? মেয়েদের আশ্বাস দিয়েছিল, ‘এবেলায় তুলে দিলে ওবেলায় ফের সেধে ভজে নিয়ে আসবে দেখে নিস।’

লোকালয়ের ভিতরে পতিতাদের থাকতে দেওয়া হবে কি না, পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ করে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হবে কি না– এ সব নিয়ে সে আমলে বিতর্কও হয় অনেক। ১৯৫৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখছি, পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদে বিডন স্কোয়ারের একটি সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোককুমার সেন (২ জুন)। যৌনকর্ম যে শুধু নিষিদ্ধপল্লির ঘেরাটোপেই চলত তা কিন্তু নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যাঁরা ছিলেন উদ্বাস্তু যুবক, তাঁরা অনেকেই বলেছেন, অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা অনেক সময়ে ‘দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাত।’ মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ৭১’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘দেহমন’ বা সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘রোদন ভরা বসন্ত’ সিনেমা অবশ্য এই মেয়েদের প্রতি সহমর্মী। নিদারুণ দারিদ্র আর অসাম্যের কারণে তথাকথিত ‘ভদ্র’ পেশায় সুযোগ পেতেন না যে মেয়েরা, তাঁরা কখনও কখনও জীবিকা হিসাবে বেছে নিতেন যৌনকর্মকেও।
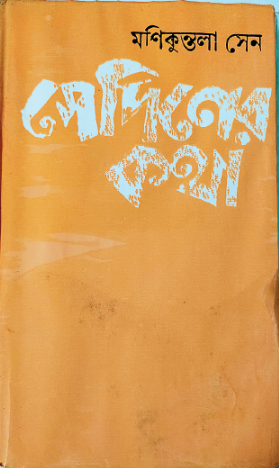
মহিলা ভোট প্রার্থী হিসাবে কালীঘাটের যৌনপল্লির প্রতিটি ঘরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল মণিকুন্তলা সেনের। নিজের আত্মজীবনী ‘সেদিনের কথা’-য় মণিকুন্তলা লিখছেন, ‘ওদের অভিযোগ ছিল পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ওদের বক্তব্য ছিল: অন্য সব ব্যবসার মতো এটাও ওদের জীবিকার জন্য ব্যবসা। অন্য ব্যবসায় যখন পুলিস আসে না তখন এদের উপরেই বা উপদ্রব হবে কেন? আর থানায় নিয়ে গিয়ে টাকা পেলেই তো পুলিস এদের ছেড়ে দেয়।’ মণিকুন্তলা লিখছেন, এ সমস্যার সমাধান তাঁর জানা ছিল না। গান্ধীজির মিটিংয়ের কথা ভেবে তিনি বলতেন, ‘তোমরা কি জানো কেন তোমাদের পেটের ভাতের জন্য নিজেকে এমন বিক্রি করে দিতে হয়?’ বক্তব্যকে যথাসাধ্য মর্মস্পর্শী করে বলার চেষ্টা করেও দেখতেন, পল্লির মেয়েরা এসব কথায় আমল দিত না। দালালরা আবার বিরক্তও হত। যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে তিনি ততটা উৎসাহী ছিলেন না, যতটা ছিলেন সমাজের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে পেশাটির বিলোপে। মণিকুন্তলা হোটেলের ক্যাবারেগার্লদের কথাও বলেছেন, ‘এদেরই উপার্জনে হয়তো পিতৃ-পরিবার বা স্বামীর সংসার বাঁচে। কিন্তু এসবের মধ্যে এখন আর কেউ অন্যায় বা অসামাজিক কিছু দেখে না। বরং আমোদ-প্রমোদের অনিবার্য অঙ্গ হিসাবেই এগুলো স্বীকৃত।’
সে সময়ের খবরের কাগজের শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কলামে প্রায়ই দেখতে পাই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মহিলা ও পুরুষ চাওয়া হচ্ছে। ১৯৫০-এর যুগান্তরে কর্মখালি কলামে যেমন দেখি ‘আমোদ-প্রমোদীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সুশ্রী নৃত্যগীতজ্ঞ মহিলা কর্মী’ চাওয়া হচ্ছে (১০ মে)। অভিনয়ের পেশায় আসা সকলের পক্ষে সহজ ছিল না। মনে পড়ে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘নায়ক’ ছবির (১৯৬৬) মলি চরিত্রটির কথা। অন্য পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে অসৎভাবে উপার্জন করতে আটকায় না তার স্বামীর, তবু মলিকে অভিনয়ে ‘নামতে’ দিতে আপত্তি করে সে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘রূপ’ গল্পে অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী হলেও ভালই রোজগার করত কাজল মিত্র। দুই সুন্দরী দিদির পরে ‘অসুন্দর’ কাজলকে নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না মায়ের। উঠতে বসতে গঞ্জনাও সহ্য করতে হত তাকে।
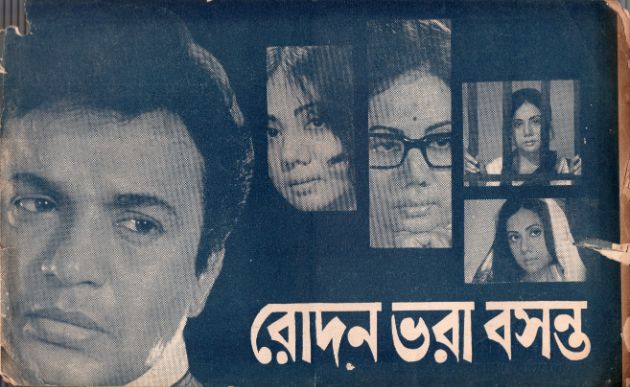
‘রোদন ভরা বসন্ত’ সিনেমায় (১৯৭৪) শুক্লা তার রুগ্ন মাকে বলে সে চাকরির চেষ্টায় বেরোচ্ছে। মা জানতে চান কী কাজ। সে বলে, ‘আমার দ্বারা যা সম্ভব, নীচু ক্লাসে পড়ানো বা অ্যাংমেচার থিয়েটারে টিয়েটার…।’ মা বলেন থিয়েটারের কথা শুনলে তাদের মাথার উপরের পুরুষমানুষ হারুকাকা অমত করবেন। শুক্লা বলে হারুকাকার মতামতের কোনও মূল্য নেই তার কাছে। আবার শুধুমাত্র জীবিকার সন্ধানে নয়, শিল্পের নেশাতেই নানা জায়গা থেকে ‘নাটক-পাগল ছেলেমেয়েরা’ এসে জড়ো হয়ে একত্রে দল করত, সেই দলের মধ্যেই গড়ে উঠত ‘স্নেহ-ভালবাসা-ঈর্ষা-হিংসায় জড়িয়ে তাদের পরিবার’। সাধারণ অর্থে পারিবারিক জীবন থাকত না অনসূয়া বা জয়ার মতো মেয়েদের, যেমন লিখেছিলেন ঋত্বিককুমার ঘটক, কোমল গান্ধার (১৯৬১) ছবির মুখবন্ধে।

এছাড়া সেলাই দিদিমণি, নাচ-গানের শিক্ষিকা, প্রাইভেট টিউটর বা কারখানার মজুর হিসাবে কাজ করে স্বাধীনভাবে রোজগার করতেন বহু মেয়ে। সিনেমা, সাহিত্য, স্মৃতিচারণা, কাগজের বিজ্ঞাপন তার সাক্ষ্য দেয়। ১৯৪৯-এর যুগান্তরে কর্মপ্রার্থী কলামে দেখছি এক ‘উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা গৃহস্থবধূ বা ছোট ছেলেমেয়েকে সকল রকম শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক’ (৪ ডিসেম্বর)। সে সময়ের খবরের কাগজের পাতায় পাতায় মেলে টেলারিং-কাটিং শেখানোর প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার উপরেও জোর দেওয়া হয়।
স্বাধীনতার পরে যে বাঙালি মেয়েরা বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরিতে ঢুকলেন, এই সিরিজে আমরা এত দিন তাঁদের কথা বলেছি। এঁরা বেশিরভাগই উচ্চবর্ণ, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের, অনেকেই উদ্বাস্তু হিসাবে ওপারের ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছেন এপারে। মূলত এঁদের নিয়েই আমাদের গবেষণা। তবে যেসব মেয়ে অনেক চেষ্টা করেও সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি পেলেন না, বা যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না অফিসে চাকরি পাওয়ার, তাঁরা কী করতেন? নিম্নবিত্ত মেয়েদের একটা বড় অংশ করতেন পরিচারিকার কাজ। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, দেশভাগের ফলে গৃহশ্রমিক হিসাবে পুরুষদের জায়গায় অনেক বেশি মেয়ে আসতে শুরু করেন। উচ্চবর্ণ পরিবারের অনেক উদ্বাস্তু মেয়ে থাকার জায়গা পাবেন বলে গৃহস্থ বাড়িতে কাজ নিতেন। বস্তুত, ১৯৫১ সালের সেন্সাসে দেখছি, কলকাতা শিল্পাঞ্চলে টাকার বিনিময়ে গৃহশ্রমের কাজে যুক্ত ছিলেন ৪৫,৪২২ জন মহিলা। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে অ-কৃষিক্ষেত্রে যত জন মেয়ে উপার্জন করতেন, গৃহশ্রমিকেরা ছিলেন তার ৩০ শতাংশ।

আমরা সে সময়ের চাকরিজীবী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি উচ্চবিত্ত পরিবারে অনেক ক্ষেত্রেই থাকতেন সর্বক্ষণের কাজের লোক বা ‘খাওয়াপরা লোক’। যাঁদের সেই ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই রাখতেন ঠিকে কাজের লোক। এই লোক পাওয়ার অসুবিধে নিয়ে মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে সময়ের সিনেমা সাহিত্যে অনেক রসিকতাও চোখে পড়ে। তপন সিংহের ‘গল্প হলেও সত্যি’ সিনেমায় (১৯৬৬) বাড়ির বড় বউ (ছায়াদেবী) রান্না করতে করতে বলেন, ‘‘ঝি-মুখপুড়ির মেজাজে প্রাণ যাবার দাখিল!’’ গৃহিনী এবং গৃহপরিচারিকার কথোপকথন:
–আবার ঝিকে কাঠি দিচ্চ কেন? ঝি তোমাদের কী পাকা ধানে মই দিলে?
–পাকা ধানে আবার কে কার মই দেয়! একটা বাড়তি কাজ বললে মুখনাড়া দাও কিনা, তাই বলছি।
–একটা বাড়তি পয়সা চাইলে কি হেসে কথা কও? সেটা আগে বল!
–শুনছিস কথা! পয়সা যেন গাছে ঝুলছে!
–পয়সা যে গাছে ঝোলে না, গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হয়, তা জানি। জ্ঞান আর দিওনি বাপু!

এই ছায়াদেবীই তপন সিংহের ‘আপনজন’ ছবিতে (১৯৬৮) নিঃসন্তান বিধবা বাণী দেবীর ভূমিকায় সুবিধাভোগী বাঙালি মধ্যবিত্তের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দেন। দূর সম্পর্কের ভাগনে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ‘রাঙামামিমা’ বলে ডেকে ওঠে। বিনা মাইনের কাজের লোক হিসাবে তাঁকে শহরে নিয়ে আসে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে। ভাগনে এবং তাঁর স্ত্রী, দু’জনেই চাকরি করে। বউমা অর্থনীতির এমএ, ৪০০ টাকা মাইনে পায়। ভাগনে সংসারের সারা দিনের কাজ, বাচ্চা দেখা সবই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে। বাড়ির ঠিকে লোকের কথায় অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন তাঁর সঙ্গে কতখানি অন্যায় হচ্ছে। সে তাঁকে জানায় ছেলে দেখার লোকের খাওয়া পরা ছাড়াও নিদেনপক্ষে ৩০ টাকা মাইনে প্রাপ্য হয় বাজারদর অনুযায়ী। খোলাখুলি ভাগনেকে গিয়ে মাইনে চাইলে তার বউ বলে কুড়ি টাকা দেবে, তবে মাইনে নয়, প্রণামী হিসাবে। তিনি বলেন প্রণামী, সেলামি, বেনামি, তারা যা খুশি বলুক, তিনি মাইনে হিসাবেই নেবেন টাকাটা। তা ছাড়া গরমকালে দই আর শীতকালে রাবড়ির ব্যবস্থা চাই। একই ফন্দি নিয়ে এক দিন হাজির হয় তাঁর খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ‘সোনাজ্যেঠিমা’ বলে ডাকায় এবার আর গলে যান না তিনি। বলেন, কলকাতার জল খেয়ে আপন-পর ভালই বুঝতে শিখেছেন তিনি। সরাসরি জিজ্ঞাসা বলেন, ‘তুমি আমার কত আপন জন… মাইনে কত?’ তারপরে বলেন রাতে বউয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আরেক দিন দুপুরবেলা আসতে। চোখ গোল গোল করে বলেন, ছুটির দিন না আসতে কারণ এ বাড়ির আপনজন সেদিন বাড়িতে থাকবে।
তথ্যসূত্র
Banerjee, S. (2003). Displacement within Displacement: The Crisis of Old Age in the Refugee Colonies of Calcutta. Studies in History, 19(2), 199-220.
Bagchi, Jasodhara and Subhoranjan Dasgupta (Eds) (2003). The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India, Stree,. Kolkata
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
