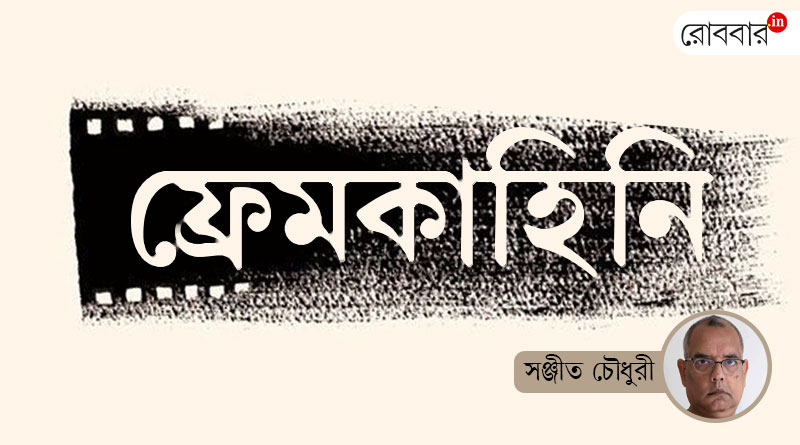
সুব্রতদা একটা সময় শুরু করলেন ছবি আঁকা। একেবারে নিজের মতো করে। এবং শুধু ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হতেন না। সেই ছবি আঁকার ছবিও তুলে রাখতেন। ছবিগুলো যেহেতু রঙিন, সুব্রতদাও রঙিন ছবি তুলতেন। ছবির সঙ্গে রাখতেন নানা রঙের নানা রকমের প্যাকেট। যাতে প্রিন্ট হওয়া ছবিতে রংটাকে ভালো করে বোঝা যায়। এসব জেনেশুনেই একবার রঙিন ছবি তুলেছিলাম সুব্রতদার। সুব্রতদা আমাকে ছবি তুলতে দিতেন, সবাইকে দিতেন এমন নয়। ক্যামেরা বের করলেই বলতেন, ‘কী ফিল্ম রয়েছে?’ যদি বলি, কোড্যাক, তাহলে কত স্পিডের ফিল্ম– সবটা জানতে চাইতেন। আমি রঙিন ছবি একটু অবাকই হয়েছিলেন।

১০.
আজাদ হিন্দ হোটেল আর সুব্রত মিত্রর বাড়ির মধ্যে মিল কোথায়?
উত্তর– এম. এফ হুসেনের ম্যুরাল।
হুসেন বন্ধু ছিলেন সুব্রত মিত্রর। সুব্রতদার বাড়ি ছিল ল্যান্ডসডাউনে। মোটরভিকেলস-এর অফিসের কাছে। আমি যেহেতু থাকতাম টালিগঞ্জে, ফলে যাতায়াতের পথেই পড়ত ওঁর বাড়ি। নানা কারণে-অকারণে ডেকে পাঠাতেন। আলাপ ছিল আগেই, তবে যোগাযোগ ঘন হয় ওই কলেজবেলা নাগাদ। ছোট থেকেই কলকাতায় এক টি-ব্যাগের বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে সুব্রতদার একটা কিস্সা শুনে আসছি। বাগে পেয়ে সেকথা একদিন সরাসরি জানতে চাই– ঠিক করে বলুন তো, কী হয়েছিল আপনার টি-ব্যাগের শুটে?
সুব্রতদা বললেন, ভালো হল তুমি প্রশ্নটা করলে। শুটিংটা হচ্ছিল বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে। ওরা টি-ব্যাগ ডোবানোর জন্য ড্রেনের জল দিয়েছিল। সেই জলে কি টি-ব্যাগের শুট হয় বলো!
আমি বুঝতে পারছিলাম, সুব্রতদার বক্তব্য ওই জল আসলে অপরিষ্কার, ড্রেনের জল যে, তা নয়। তখন যদিও বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে বড় ড্রেন ছিল। কিন্তু নির্ঘাত ড্রেনের জল দেওয়া হয়নি।
বললাম, কী করলেন তখন আপনি?
–জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম পরিষ্কার জল নেই। অতএব আমি এবং বাচ্চু (সুব্রতদার ভাই, যে মানসিকভাবে ছিল একেবারে সুব্রতদার মতোই)– কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে ইকুইপমেন্ট কিনলাম যা দিয়ে পরিষ্কার জল তৈরি করা যায়। তারপর বাড়ি ফিরে জল ভেপারাইজ করে একেবারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুদ্ধ দু’জগ পরিষ্কার জল তৈরি করলাম। সেদিনের শুট হল না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গ্র্যান্ড হোটেলে ক’দিন বাড়তি রাখা হল। শুট হল তার পরের দিন।
এই হল সুব্রতদা! এমনই আশ্চর্য!

সুব্রতদা নিয়ে কথা বলছি বটে, তবে আমরা অনেকেই ওঁর কাজ বলতে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে করা ছবিগুলোর কথাই বুঝি। জীবনে প্রথমবার ক্যামেরা হাতে নেওয়া সুব্রত মিত্র ‘পথের পাঁচালী’তে সেই কামাল করেছিলেন তো বটেই, মনে রাখতে হয় বিশেষ করে ‘অপু ট্রিলজি’ এবং অবশ্যই ‘চারুলতা’র ম্যাজিক। সে কারণেই হয়তো জেমস আইভরি নির্দেশিত ‘দ্য হাউজহোল্ডার’ (১৯৬৩), ‘শেক্সপিয়রওয়ালাহ’ (১৯৬৫), ‘দ্য গুরু’ (১৯৬৯) কিংবা ‘বম্বে টকি’(১৯৭০)-র মতো কাজ আড়ালে থেকে গিয়েছে।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ফোন করে প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন, ‘তোমার বাড়িতে কি টোস্টার আছে?’ যদি উত্তর ‘না’ হয়, উনি সটান ফোন রেখে দিতেন। মানে, আর কোনও কথা নয়, কেন এই টোস্টারের জন্য ফোন, সেসবের কোনও উত্তর তিনি দেবেন না। এবং সম্ভাব্য পরের জনকে ডায়াল করবেন। টোস্টার যদি থাকে, তাহলে গোটা ২০ প্রশ্ন। কোন কোম্পানির টোস্টার, কী রং, মডেল কী, কতগুলো করে টোস্ট করা যায়, কতক্ষণে গরম হয়– ইত্যাদি। কয়েকমাস এই প্রবল তদন্তের পর এক দোকানে সকালবেলা প্রবেশ করে দীর্ঘ ছানবিনের পর বিকেলবেলা টোস্টার হাতে বেরিয়েছিলেন সুব্রত মিত্র।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
এহেন সুব্রতদারই একবার মশারি কেনা কিছুতেই ফুরোচ্ছিল না। তার মানে এই নয় যে, অনেক মশারি কিনে বাড়িতে জড়ো করেছেন তিনি। আসলে যে মশারিটা কিনেছেন, তা রাতের অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে দেখতেন যে, প্রতিটা চৌকোয় কতগুলো গিঁট রয়েছে। আসলে তখন যন্ত্রে নয়, মশারি তৈরি হত হাতে। সেই হাতে-তৈরি মশারিতে থাকত অনেক গিঁট। গিঁটের সংখ্যা বেশি, এই অছিলায় সুব্রতদা বারেবারেই মশারি বদলে বদলে নিয়ে আসছিলেন দোকান থেকে। এরকম বার পাঁচেক হওয়ার পর সেই মশারি বিক্রেতা খেপে বোম! বলে দেন যে, যা কিনে নিয়ে গিয়েছেন সেটা টাঙিয়ে ঘুমোন, এরপর এই দোকানে আর ঢুকবেন না!
বেচারা সুব্রতদা, কী আর করবেন। সে যাত্রায় মশারি অভিযান ছিল সেই পর্যন্তই। আরও একবার সুব্রতদা একটা লম্বা লিস্ট বানালেন– ওঁর চেনাশোনা লোকেদের, কাদের কাদের বাড়িতে টোস্টার থাকতে পারে। ফোন করে প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন, ‘তোমার বাড়িতে কি টোস্টার আছে?’ যদি উত্তর ‘না’ হয়, উনি সটান ফোন রেখে দিতেন। মানে, আর কোনও কথা নয়, কেন এই টোস্টারের জন্য ফোন, সেসবের কোনও উত্তর তিনি দেবেন না। এবং সম্ভাব্য পরের জনকে ডায়াল করবেন। টোস্টার যদি থাকে, তাহলে গোটা ২০ প্রশ্ন। কোন কোম্পানির টোস্টার, কী রং, মডেল কী, কতগুলো করে টোস্ট করা যায়, কতক্ষণে গরম হয়– ইত্যাদি। কয়েকমাস এই প্রবল তদন্তের পর এক দোকানে সকালবেলা প্রবেশ করে দীর্ঘ ছানবিনের পর বিকেলবেলা টোস্টার হাতে বেরিয়েছিলেন সুব্রত মিত্র।
টোস্টার তো হল। কিন্তু কোন পাঁউরুটি এই টোস্টারে সবথেকে ভালো টোস্ট হয়? বাড়ি ফেরার পথে প্রায় ১০-১২ পাউন্ড পাঁউরুটি কিনে ফেললেন তিনি। এবং বাড়ি ফিরে সেই পাঁউরুটিদের পরীক্ষায় বসতে হল– সবথেকে কড়কড়ে ও চমৎকার পাঁউরুটি কোন ব্যান্ডের? পুরো কাণ্ডটা শেষ হল যখন বিকেল-সন্ধে গড়িয়ে তখন অনেকটাই রাত। হাতে রইল ১০-১২ পাউন্ড টোস্ট করা পাঁউরুটির চাঁই। তা আর কী করবেন? বাড়ির বাইরে ফেলে দেন সুব্রতদা।
আজ্ঞে না, গল্পটা এখানেই শেষ নয়। পাড়া-বেপাড়ার যত রাজ্যের কুকুর এসে সারারাত হল্লা করায় তাঁর একেবারেই ঘুম হয়নি।
এহেন সুব্রতদার বাড়ি গিয়েছি একদিন। সুব্রতদা বললেন, ‘তুমি কিছু খাবে? চা খাবে?’ একথা মনে আছে, কারণ সুব্রতদা এর আগে কখনও চায়ের সুপারিশ করেননি। আমি ভাবলাম কে জানে কী ব্যাপার। বললাম, ‘হ্যাঁ।’ একটা ছেলে এল, সে তখন প্রায় আমারই বয়সি। কুড়ির ঘরেই বয়স হবে। সুব্রতদা তাকে বলে দিলেন, ‘জলে যখন প্রথম বাবল হবে, তখন তুমি আমায় বলবে।’ আমাদের সেই বসার ঘর থেকে রান্নাঘরটা খানিক দূরে, আজকালকার ফ্ল্যাটবাড়ির মতো লাগোয়া নয়। খানিক পর ছেলেটি জানায়, সুব্রতদা তখন আবারও নির্দেশ দেন। বলেন, ‘এইবার চা পাতাটা দাও।’ সুব্রতদার এই কড়া নিয়মাবলি মেনে চা বানানো চলল প্রায় মিনিট ৪০। এর মধ্যেই সুব্রতদা গোটা ৩০ প্রশ্ন করেছেন ওই ছেলেটিকে। এবং ছেলেটিও বারবার রান্নাঘর থেকে বসার ঘরে যাতায়াত করছে। তারপর সত্যিই চা এল। এবং তা, খুবই সাধারণ মাপের একপাত্তর চা। আমার মনেই হল এ-ছেলে এ বাড়িতে বেশিদিন টেকার নয়। পরের সপ্তাহে সুব্রতদার কাছে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই! মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সুব্রতদা, ওই ছেলেটার কী হল?’ সুব্রতদা খুবই হেলা ভরে বললেন, ‘ও অকারণে হঠাৎ একদিন চলে গেল।’
সুব্রতদা একটা সময় শুরু করলেন ছবি আঁকা। একেবারে নিজের মতো করে। এবং শুধু ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হতেন না। সেই ছবি আঁকার ছবিও তুলে রাখতেন। ছবিগুলো যেহেতু রঙিন, সুব্রতদাও রঙিন ছবি তুলতেন। ছবির সঙ্গে রাখতেন নানা রঙের নানা রকমের প্যাকেট। যাতে প্রিন্ট হওয়া ছবিতে রংটাকে ভালো করে বোঝা যায়। এসব জেনেশুনেই একবার রঙিন ছবি তুলেছিলাম সুব্রতদার। সুব্রতদা আমাকে ছবি তুলতে দিতেন, সবাইকে দিতেন এমন নয়। ক্যামেরা বের করলেই বলতেন, ‘কী ফিল্ম রয়েছে?’ যদি বলি, কোড্যাক, তাহলে কত স্পিডের ফিল্ম– সবটা জানতে চাইতেন। আমি সেইদিন রঙিন ছবি তুলছি বলে একটু অবাকই হয়েছিলেন।
আমাকে একদিন খুব সকালবেলা অভীক মুখোপাধ্যায় ফোন করে খবরটা দিয়েছিল। সে খবর, সুব্রতদার মৃত্যুর। বললাম, ‘কোথা থেকে জানলে?’ ও বলল, ‘ঋতু ফোন করে জানিয়েছে। ঋতুকে ফোন করে জানিয়েছেন মৃণাল সেন।’
অভীকের পকেটে ওয়ালেট ছিল, ও মর্নিং ওয়াক থেকে সরাসরি চলে গিয়েছে ল্যান্ডসডাউনে, সুব্রতদার বাড়িতে। গিয়ে দেখে, সুব্রতদার দেহ শোয়ানো রয়েছে। আমার যেতে খানিক দেরি হল। দেখলাম সুব্রতদার ভাই বাচ্চুদাও রয়েছেন আশপাশেই। মৃণালদাও এসে পড়েছেন, মৃণালদার সঙ্গেও দীর্ঘদিনের আলাপ ছিল সুব্রতদার।
একসময় মৃণালদা, কৌতূহলবশে বাচ্চুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছিল?’ যে কোনও মৃত্যুর খবরেই যে-প্রশ্ন প্রায় অনিবার্য। এ প্রশ্নের উত্তরে বাচ্চুদা চলে গিয়েছিল বডি-ফিজিক্সে। হৃদ্যন্ত্রে ঠিক কত শতাংশ অক্সিজেন পৌঁছলে শরীর ঠিক থাকে, আর কতটা কম থাকলে শরীর গড়বড় করে এবং শ্বাস নিতে অসুবিধে হয় ইত্যাদি, প্রভৃতি মিলিয়ে একটা দীর্ঘ বর্ণনামূলক উত্তর।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
