
প্রচলিত যে উদ্দেশ্যে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়, তাকে তোয়াক্কা করেননি জীবনানন্দ দাশ। ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা…’ ও ‘…তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে’ যে একটিমাত্র সেমিকোলনের সহায়তায় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারল, তার কারণও বুঝি ‘অন্ধকার’। তাই শেষে ইন্দিয় গ্রাহ্যতাকে অতিক্রম করে যখন লেখেন ‘শিশিরের শব্দ’ ও ‘ডানার গন্ধ’ তখনও তাদের মধ্যে নির্জন একটি সেমিকোলন থেকে যায়। সেমিকোলন থেকে যায়, একদিকে ‘পাণ্ডুলিপি’-র আয়োজন ও অন্যদিকে নদীর ঘরে ফেরার মতো অবাস্তবতায়। আর তখন অন্ধকারে মুখোমুখি বসবার জন্য থাকে শুধু বনলতা সেন। আমাদের মনে হয়, বনলতা সেন নিজেও যেন এক অন্ধকার। এবং তা সেমিকোলনের ঠারঠোর ইঙ্গিত ও বিপর্যাসে সম্ভব হয়।

যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রায় তিন হাজার বছরের পুরোনো হলেও, সেমিকোলনের জন্ম ৫৩০ বছর আগে। কোলনের দু’টি বিন্দু থেকে একটি বিন্দু চিহ্ন ও কমা থেকে কমার চিহ্নটি নিয়ে ১৪৯৪ সালে পিয়েরো বেম্বো তাঁর ‘ডি অ্যাটনা’ গ্রন্থে প্রথম সেমিকোলন যতিচিহ্নটি ব্যবহার করেন। যদিও খুব একটা কণ্টকমুক্ত নয়, সেমিকোলনের এই যাত্রাপথ। যুগে যুগে এর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল রবিনসনের এমনটাও মনে হয়েছে যে সেমিকোলন চিহ্নটি শুধু ‘ঘৃণ্য’-ই নয়, এটির ব্যবহারে ‘নৈতিক আপোশ’ করতে হয়।
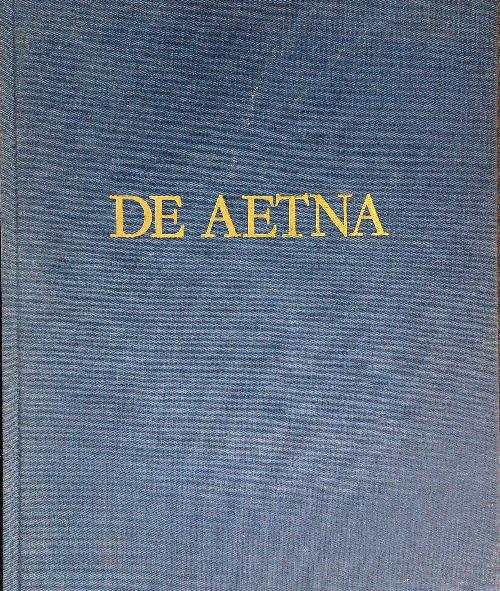
আমরা সেমিকোলনের সংজ্ঞা হিসেবে জানি, দাঁড়ির চেয়ে কম এবং কমার চেয়ে বেশি বিরামের জন্য যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকেই সেমিকোলন বলে। যখন আপাত সম্পূর্ণ দু’টি বাক্যকে অর্থগত কারণে দাঁড়ি বসিয়ে একেবারে আলাদা করা যাচ্ছে না, আবার মাঝখানে কমা বসিয়েও একটি বাক্যে পরিণত করা যাচ্ছে না, তখন সেমিকোলন ব্যবহার করে দু’টি বাক্যের মধ্যকার টানাপোড়েনকে মান্যতা দেওয়া হয়।
জীবনানন্দ দাশের লেখায় যেকোনও যতিচিহ্ন ব্যাকরণের জাঁতাকলে পিষ্ট নিছক কোনও চিহ্ন মাত্র নয়, বরং তা স্বতন্ত্র এক অনুধ্যানের বিষয়। যতিচিহ্ন সেখানে ব্যাকরণের বিধিনিষেধ পেরিয়ে জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়, স্ববিরোধ অস্তিত্বের পরিত্রাণহীন অসহায়তার কথা বলে, সদা সতর্ক থেকেও ভয়াবহ কোনও খাদের কিনারায় পৌঁছে দেয়। আসলে জীবনানন্দের লেখার ধাতের সঙ্গে যতিচিহ্ন মিশে আছে। তিন ধরনের লেখকের কথা বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। স্টাইল-সর্বস্ব কলমবীজ, মেধ-সর্বস্ব ঘিলুবীজ ও সত্তা-সর্বস্ব রক্তবীজ। জীবনানন্দ নিজে রক্তবীজের জাত। যে অনিশ্চয়তা, নিরভিসন্ধি ও বিপন্ন বিস্ময় জীবনানন্দ দাশের লেখার ধমনিতে প্রাণ সঞ্চার করে, তা তাঁর যতিচিহ্ন প্রয়োগেও চারিয়ে যায়। তখন তা আর শুধুই চিহ্ন থাকে না, অক্ষরের মতো বিরামচিহ্নেও প্রাণসঞ্চার হয়।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
সন্দীপ রায়ের সাক্ষাৎকার: সন্দেশে লেখকদের পারিশ্রমিক ছিল লেখার সঙ্গে বাবার অলংকরণ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
‘কবিতা’ পত্রিকায় চৈত্র, ১৩৪২ সালে প্রকাশিত ও ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থে ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে সংকলিত একটি কবিতা ‘আমি যদি হতাম’। ২৮ পঙক্তির এই কবিতাটিতে আমরা দেখি, শুরুর চারটি পঙক্তি ও শেষের চারটি পঙক্তি প্রায় এক।
কবিতাটির শুরুতে ছিল:
‘আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে’
আর শেষ হচ্ছে:
‘আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।’

এখানে দু’টি মাত্র তফাত লক্ষ করি। শুরুর ‘আমি যদি হতাম বনহংস’ শেষে এসে ‘আমি যদি বনহংস হতাম’ হয়েছে। হয়েছে, কারণ শুরুর ‘যদি’-র অনিশ্চয়তা ও অনির্দিষ্ট অভিঘাত শেষে এসে সম্পূর্ণ দূর না হলেও কোথাও যেন তার বেগ একটু বেশি বিরাম চায়। আর সেই আশ্রয় তাকে দেয়, শুরুর কমা নয়, সেমিকোলন। ‘বনহংসী হতে যদি তুমি’, শেষে পৌঁছে ‘বনহংসী হতে যদি তুমি;’ হয়ে যায়। একটি কমার থেকে একটি সেমিকোলনের ওজনের তারতম্য, শ্বাসাঘাতের রসায়ন ও প্রয়োগের দর্শন একটি কবিতাকে আমাদের কাছে অর্থবহ করে তোলে। এখানে সেমিকোলন শুধুমাত্র আর একটি কেজো যতিচিহ্ন হয়ে থাকল না, তা কবিতার অস্থিমজ্জায় মিশে বাঙ্ময় হল।
‘আমি যদি হতাম’ কবিতাটি যেমন সম্ভাবনার আবার অসম্ভবেরও। শুরুর ‘যদি’ যে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, আমরা যত কবিতাটির গভীরে প্রবেশ করব,দেখব ‘তা হলে’ ও ‘হয়তো’ শব্দ দু’টি আমাদের স্থিত হতে দেয় না বরং এক আততি বলয় সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে চার বছর পর, এমন একটা সময় কবিতাটি লেখা। তাই তোমার পাখনায় আমার পালক, আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দেওয়া বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। গুলির শব্দ আমাদেরও স্তব্ধ করে। যে ‘তির্যক গতিস্রোত’-এর কথা কবি অতঃপর বলেন তা যেন উল্লেখিত শেষের সেমিকোলনটিতে গিয়ে বিলীন হয়, কবিতাটির ম্যাজিক মোমেন্ট বা প্রস্থানবিন্দু তৈরি করে।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
জীবনানন্দ দাশের লেখায় যেকোনও যতিচিহ্ন ব্যাকরণের জাঁতাকলে পিষ্ট নিছক কোনও চিহ্ন মাত্র নয়, বরং তা স্বতন্ত্র এক অনুধ্যানের বিষয়। যতিচিহ্ন সেখানে ব্যাকরণের বিধিনিষেধ পেরিয়ে জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়, স্ববিরোধ অস্তিত্বের পরিত্রাণহীন অসহায়তার কথা বলে, সদা সতর্ক থেকেও ভয়াবহ কোনও খাদের কিনারায় পৌঁছে দেয়। আসলে জীবনানন্দের লেখার ধাতের সঙ্গে যতিচিহ্ন মিশে আছে। তিন ধরনের লেখকের কথা বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। স্টাইল-সর্বস্ব কলমবীজ, মেধ-সর্বস্ব ঘিলুবীজ ও সত্তা-সর্বস্ব রক্তবীজ। জীবনানন্দ নিজে রক্তবীজের জাত।
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
কবি যে এমন একটা প্রত্যয়ে পৌঁছন, জীবনের টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকবে না, থাকবে না জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার, তা এই একটি সেমিকোলন, সেমিকোলনের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শই ধারণ করে।
ওই একই কাব্যগ্রন্থের ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি যদি দেখি, ১৮ পঙক্তির কবিতাটিতে সেমিকোলন ব্যবহার হয়েছে ৮ বার। প্রথম ৬টি পঙক্তিতে ৩টি কমা, ৩টি সেমিকোলন ও একটি দাঁড়ি। এই ৬টি লাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ কবিতাটির মোহনায় পৌঁছনোর জন্য। সাধারণত মনে হয়, জীবনানন্দ দাশ এই প্রথম ৬টি লাইনে ৬টি সেমিকোলনই ব্যবহার করতে পারতেন। যে পদ্ধতি বা যুক্তিক্রমে কমা ও সেমিকোলন একটি বাক্য ছেদ করার জন্য যুগপৎ ব্যবহার হয়, তা এখানে মান্য করা হয়নি। ‘নিশীথের অন্ধকার’, ‘ধূসর জগৎ’ ও ‘দূর অন্ধকার’-এর যে একমাত্রিক অভিমুখ, তা কমার চেয়ে বেশি বিরতিতে পাঠকমনে এমন স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয় যে, শেষের ‘থাকে শুধু অন্ধকার’-এর ‘অন্ধকার’ যে কবিতাটির চাবিকাঠি, তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।
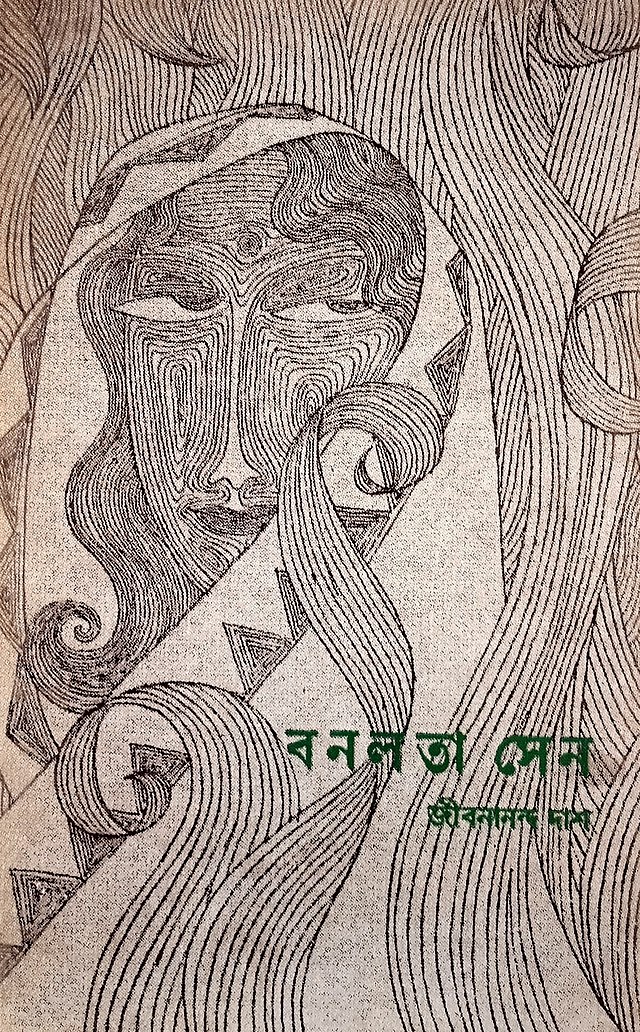
প্রচলিত যে উদ্দেশ্যে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়, তাকে তোয়াক্কা করেননি জীবনানন্দ দাশ। ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা…’ ও ‘…তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে’ যে একটিমাত্র সেমিকোলনের সহায়তায় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারল, তার কারণও বুঝি ‘অন্ধকার’। তাই শেষে ইন্দিয় গ্রাহ্যতাকে অতিক্রম করে যখন লেখেন ‘শিশিরের শব্দ’ ও ‘ডানার গন্ধ’ তখনও তাদের মধ্যে নির্জন একটি সেমিকোলন থেকে যায়। সেমিকোলন থেকে যায়, একদিকে ‘পাণ্ডুলিপি’-র আয়োজন ও অন্যদিকে নদীর ঘরে ফেরার মতো অবাস্তবতায়। আর তখন অন্ধকারে মুখোমুখি বসবার জন্য থাকে শুধু বনলতা সেন।আমাদের মনে হয়, বনলতা সেন নিজেও যেন এক অন্ধকার। এবং তা সেমিকোলনের ঠারঠোর ইঙ্গিত ও বিপর্যাসে সম্ভব হয়। তরঙ্গে তরঙ্গে ছোট ছোট অন্ধকারকে বড় অন্ধকার করে তোলে সেমিকোলন। বৌদ্ধ অনুষঙ্গ তো আছেই ‘বনলতা সেন’ কবিতা জুড়ে, শেষে আমরা বৌদ্ধ দর্শনের মৌল অন্ধকারে পৌঁছে যাই– যা বলে এই অন্ধকারের আড়ালেই লুকিয়ে আছে জীবনের সত্য, সত্তার স্বরূপ ও চিরপদার্থ।
জীবনানন্দ দাশ যেখানে যেখানে যতিচিহ্ন তথা সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন, নিজের শর্তে করেছেন, নিজের যুক্তিক্রমে ব্যাকরণের শৃঙ্খল ভেঙেছেন, চিহ্নকে করে তুলেছেন অক্ষরের মতো শব্দের মতো বাঙ্ময়।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
