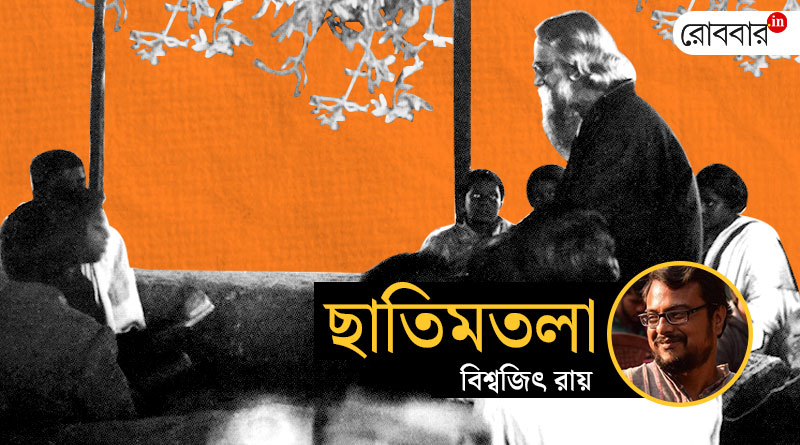
বাঙালি লেখক আঁকছেন, রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালে জমিদারি দেখতে এসে পেগের পর পেগ পান করছেন। চোখ তরল হয়ে উঠছে। তারপর জানালা দিয়ে কোনও গ্রামদেশের দেহপল্লব সিঞ্চিতা রমণীকে দেখছেন। সে রমণীর অঙ্গবস্ত্রখানির বিবরণ দিতে গিয়ে বাঙালি লেখক নিজের চিত্তাবেগ অনুযায়ী খোলা-মেলার কথা লিখছেন। এই হল রবীন্দ্রনাথের ‘গুরুদেব’ মূর্তির বিপরীতে ‘গুরুদেব’ হয়ে ওঠার আগে বাস্তববাদী বাঙালি লেখকের কাছে ‘আসল রবীন্দ্রনাথ’।

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চেনার জন্য মাঝে মাঝেই বাঙালি লেখকদের মনে বেশ উৎসাহ জাগে। তবে উৎসাহের সঙ্গে শ্রমের ও মনের যোগ বড় একটা ঘটে না। খামচা মেরে রবীন্দ্রজীবনের হঠাৎ পাওয়া তথ্যকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁরা কাজে লাগান। তাজা-টাটকা একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে চেনার এমনিতে সবচেয়ে সহজ উপায় রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়া। ধরা যাক, জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাপনের ছবি আঁকতে চাইছেন কেউ। এ ছবি আঁকতে গিয়ে লেখকেরা বোটের ওপর রবীন্দ্রনাথকে বসান, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগের ছবি আঁকেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মুহূর্ত তুলে ধরেন। তবু অনেক সময়েই মনে হয় আরও কিছু দরকার– আরও কিছু বাস্তবের কারুকার্য, মানুষটি ধরা দিয়েও যেন ধরা দিলেন না।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি এই ফাঁক ভরাট করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তখন ‘গুরুদেব’ হননি। শিলাইদহ থেকে ৬ জুলাই ১৮৯৪ তারিখের চিঠিতে গগনকে জমিদারিতে দিনযাপনের নানা খবর দিচ্ছেন। জুলাই মানে আষাঢ় মাস। বর্ষা নেমেছে ধরে নেওয়া যায়। চিঠির শুরুতেই আছে খাদ্যাখাদ্য সংবাদ। ‘আমার অতিথিরা দুদিন ধরে বিস্তর মুরগি, টিনের মাছ, সসেজ, শ্যাম্পেন ক্লারেট এবং হুইস্কি সমাপ্ত করে গেছেন। ভেবেছিলুম সাহাজাদপুরে যদি দৈবাৎ কোন অভ্যাগত উপস্থিত হয় তাদের জন্য শ্যাম্পেনজাতীয় দুই একটা তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাকবে– কিঞ্চিৎ আছে কিন্তু সে একেবারেই যৎকিঞ্চিৎ।’ সন্দেহ নেই অতিথি সৎকারের জন্য বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদারের উপযুক্ত খাদ্যতালিকা। মদ্যের রুচি দেখার মতো– শ্যাম্পেন, ক্লারেট এবং হুইস্কি। মনে পড়ে যাবে তাঁর ‘চিরকুমার সভা’-র গান।
অভয় দাও তো বলি আমার
wish কী–
একটি ছটাক সোডার জলে
পাকী তিন পোয়া হুইস্কি॥
এ পর্যন্ত লিখে একটি টিপ্পনী যোগ অনিবার্য। অবদমিত চিত্ত বাঙালি লেখকদের স্বভাব একটি মূর্তি ভাঙার জন্য অন্য একটি মূর্তির নির্মাণ। ‘মহাপুরুষ’ কিংবা ‘গুরুদেব’ বানিয়ে তোলা চিন্তাশীল উনিশ-বিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালিদের জীবনযাপনের নানারকম অভ্যাসকে নিরাসক্ত সহজ ভঙ্গিতে তুলে ধরতে পারেন না তাঁরা। ফলে চিঠির এই উল্লেখ দেখেই হয়তো তাঁরা আঁকতে বসলেন বর্ষাকাতর রবীন্দ্রনাথের একটি দিন। ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ৩৩ বছরের কাছাকাছি যুবক। বাঙালি লেখক আঁকছেন, রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালে জমিদারি দেখতে এসে পেগের পর পেগ পান করছেন। চোখ তরল হয়ে উঠছে। তারপর জানালা দিয়ে কোনও গ্রামদেশের দেহপল্লব সিঞ্চিতা রমণীকে দেখছেন। সে রমণীর অঙ্গবস্ত্রখানির বিবরণ দিতে গিয়ে বাঙালি লেখক নিজের চিত্তাবেগ অনুযায়ী খোলা-মেলার কথা লিখছেন। রমণীর স্তন, বিভাজিকা ইত্যাদি এল। কারণ তাঁর মাথায় রবীন্দ্রনাথের রচিত ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থটির অনুষঙ্গ ক্রিয়াশীল। সে বইতে রবীন্দ্রনাথ ‘স্তন’ নামে কবিতা লিখেছেন। সুতরাং জমিদারির সেরেস্তায় অতিথিদের সঙ্গে দু’পাত্তর হুইস্কি খেয়ে সজল চোখে বৃষ্টি বিধৌত গ্রামবাংলার উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে খাটো শাড়িতে বৃষ্টিস্নাত দিনে যুবক রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করছিলেন। এই হল রবীন্দ্রনাথের ‘গুরুদেব’ মূর্তির বিপরীতে ‘গুরুদেব’ হয়ে ওঠার আগে বাস্তববাদী বাঙালি লেখকের কাছে ‘আসল রবীন্দ্রনাথ’। প্রমাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের ৬ জুলাই ১৮৯৪ তারিখের চিঠি ও সই মিলিয়ে নিতে হবে। এই তো গগনকে লেখা চিঠির তলায় সই করেছেন রবিকাকা। অতঃপর প্রমাণ পাকা।

এজন্যই রবীন্দ্রনাথ দশচক্রে ভগবান কিংবা ভূত হন, কিছুতেই স্বাভাবিক একজন মানুষ হিসাবে ধরা দেন না। কেবল খামচে খামচে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়লেই হবে না। মন দিয়ে পুরোটা পড়তে হবে। এ চিঠিতেই এরপর আছে ‘পুণ্যাহের টাকা গুজস্তামত আদায় হবে কিনা সন্দেহ।… সাজাদপুরের জন্য একটি ভাল গোছ লোক ভাবী পেশ্কার যোগাড় করেছি– লোকটি বিরাহিমপুরের নায়েবশ্রেণীর লোক– ইংরাজি বেশ জানে– জমিদারী হিসাবপত্র ও মোকদ্দমামামলার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। …জমাওয়াশিলের কাগজ সহজ করবার জন্যে আমি সব যোগাড় করচি। পুণ্যাহের পর এখানকার তহশিলদারদেরও কতক পরিবর্ত্তন হবে।’ বোঝাই যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে জমিদারি প্রশাসন চালাতেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ মার্কা যুবকদের অরণ্যযাপনের মতো গ্রামযাপনের সময় ও অভিলাষ তাঁর ছিল না। জমিদারি চালাতে গিয়ে বুঝেছিলেন প্রশাসনে উপযুক্ত কর্মী চাই। আইন জানতে হবে আবার সংবেদনশীল হওয়া দরকার। প্রজাদের অধিকার আদায়ের জন্য অনেক সময় মামলা লড়তে হত। গগনকে আরেকটি চিঠিতে লিখছেন দ্বারী বিশ্বাসের কথা। দ্বারী বিশ্বাস মানে দ্বারকানাথ বিশ্বাস। ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার তাঁকে আইনের প্যাঁচে ফেলে শেষ করে দিয়েছিল। দ্বারী মারা গেলেন। তাঁর ছেলে রবীন্দ্রনাথকে এসে জানায় ম্যানেজারবাবু ধনে-প্রাণে পিতাকে মেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন দ্বারকানাথ সৎ প্রজা। তিনি ম্যানেজারকে আদেশ দেন বোয়ালদহের খাস করা জমি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে, রক্ত-মাংসের রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে, বাঙালি লেখকদের পরিশ্রম করতে হবে। যেভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ও দেখাতে চাইছেন, সেভাবে খামচা মেরে রবীন্দ্রজীবনের উপাদান ব্যবহার করা অনুচিত। অথচ তাই তো হচ্ছে। একসময় রবীন্দ্রনাথকে ‘গুরুদেব’ সাজানো হল বলে তারপরেই সেই ‘গুরুদেব’কে ভাঙার নানা আয়োজন হল সেকালে, একালে। রবীন্দ্রনাথের ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে’ এই গানের সাংঘাতিক মনোবিকলনকারী ব্যাখ্যা করেছিলেন একদল উঠতি মনোবিদ। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত বাউলাঙ্গের এই গান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী, কল্লোল যুগের ঘোর লাগা আধুনিক মনোবিদদের ব্যাখ্যায় হয়ে উঠল গোপন মনোবাসনার পথ। রাঙা পথ কি আর এমনি পথ? রাঙা পথ কি আর বাইরের পথ? রাঙা মাটির পথের তলায় গোপন মনে নাকি উঁকি দিচ্ছে রক্তরঞ্জিত রমণপথ! শিহরিত হতে হয়। শিউরে ওঠার আরও অনেক উপাদান একালের লেখাতেও মেলে– রক্তমাংসের রবীন্দ্রনাথের নামে কী সমস্ত রবীন্দ্রনাথ যে আমরা পাই! পাই এবং খাই।
ধন্য বাঙালি, ধন্য বাঙালি পাঠক।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
