

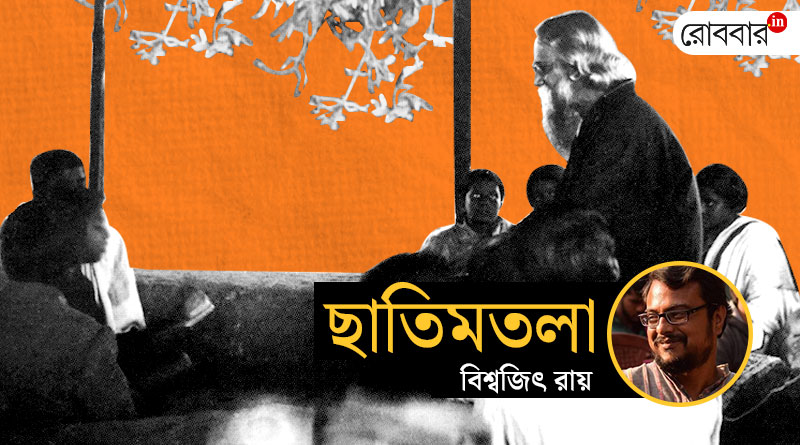
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক হিসেবে কখনও পড়ুয়াদের অসম্মান করতেন না, তাঁদের সঙ্গে সমবয়সির মতো মিশতেন– ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি তো বিজ্ঞান শিক্ষক নয়, ভাষা শিক্ষক। ইংরেজি পড়ানোর সময় যাতে বিদেশি ভাষা পড়তে গিয়ে ‘গ্রামার’-এর কচকচিতে মন ভার না হয়, সেদিকে নজর রাখতেন। তাঁর ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতিটি ছিল প্রত্যক্ষ ও মনোগ্রাহী। ব্যাকরণের গরাদ দিয়ে ভাষায় প্রবেশ না করে ছোট ছোট সহজ বাক্য দিয়ে ভাষার উঠোনে দাঁড়াতেন। তাঁর বই ‘ইংরেজি সহজ শিক্ষা’-র দু’টি ভাগ সেই নিদর্শন বহন করছে।
কেমন বিদ্যালয়-শিক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ? নিজে যখন এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে পড়ুয়া হিসেবে গিয়েছেন, তখন শিক্ষকদের আচরণের প্রতি, পড়ানোর পদ্ধতির প্রতি, তাঁর নানা অসন্তোষ ছিল। সেসব অসন্তোষের কথা ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখেছিলেন। নর্মাল স্কুলের হরনাথ পণ্ডিত, কুৎসিত ভাষায় ছাত্রদের আক্রমণ করতেন। তখন বালক রবি কী করত? ‘তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসা চেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল।’
মনোবিদ বলবেন, শত্রুটি আসলে হরনাথ পণ্ডিতই। তাঁকে তো কিছু বলা যাচ্ছে না, তাই অন্য শত্রু কল্পনা করে, মনে মনে যুদ্ধজয়ের আয়োজন। পড়ুয়ার হাতে অস্ত্র নেই, কল্পযুদ্ধে হারিয়ে দেওয়াই, তাই লক্ষ্য। যে শিক্ষক পড়ুয়াদের অসম্মান করেন, সেই শিক্ষকের সঙ্গে পড়ুয়াদের সংযোগ তৈরি হয় না।

পড়ুয়াদের মন পেতে, শিক্ষকদের তাহলে কী করতে হয়? সে কথার উল্লেখও আছে। বাড়িতে আসতেন সতীনাথ দত্ত। কেমন তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি? ‘যন্ত্রতন্ত্র যোগে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল।’ অর্থাৎ, পড়ুয়াদের মনের আগ্রহ ও কৌতূহল উসকে দিতে পারলে কিন্তু কাজ হয়। সতীনাথ দত্ত যা পারতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবু অবশ্য পরিশ্রম করেও তা পারতেন না। তাঁর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সততা, তুলনাহীন। তবে শুধু যন্ত্রবৎ পরিশ্রমে বালকদের মন ভিজত না। ছুটি চাই। তিনিও পড়াতে রবিদের বাড়িতে আসতেন, তাঁর আসা এতই নিয়মিত যে, ছুটি মিলত না কোনও দিনই। এমন একদিনের কথা আছে ‘জীবনস্মৃতি’তে। ‘সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু’-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না।’ সেদিনও জল ভেঙে সশরীরে অঘোরবাবু উপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক হিসেবে কখনও পড়ুয়াদের অসম্মান করতেন না, তাঁদের সঙ্গে সমবয়সির মতো মিশতেন– ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি তো বিজ্ঞান শিক্ষক নয়, ভাষা শিক্ষক। ইংরেজি পড়ানোর সময় যাতে বিদেশি ভাষা পড়তে গিয়ে ‘গ্রামার’-এর কচকচিতে মন ভার না হয়, সেদিকে নজর রাখতেন। তাঁর ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতিটি ছিল, প্রত্যক্ষ ও মনোগ্রাহী। ব্যাকরণের গরাদ দিয়ে ভাষায় প্রবেশ না করে, ছোট ছোট সহজ বাক্য দিয়ে ভাষার উঠোনে দাঁড়াতেন। তাঁর বই, ‘ইংরেজি সহজ শিক্ষা’-র দু’টি ভাগ সেই নিদর্শন বহন করছে। সেখানে শিক্ষককে নির্দেশ দিয়েছেন, ‘মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাক্যগুলি নানা প্রকারে বারবার ব্যবহার দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে, ইহাই লেখকের অভিপ্রায়।’ এই বারবার ব্যবহারের মাধ্যমেই ছেলেদের কৌতূহল উসকে তুলতে হবে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, কখনও অঘোরবাবুর মতো ছুটিহীন পড়ার আয়োজন করেননি। পড়ুয়াদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতেন, চাঁদের আলোয় গান গাইতেন।

এ-সবের সূত্রে তিনি কেমন শিক্ষক, তার একরকম পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয় প্রত্যক্ষ। যেখানে তিনি শিক্ষা-প্রশাসক, সেখানেও তিনি বেশ অন্যরকম। প্রমথনাথ বিশী অঙ্কে কাঁচা, বাংলায় পাকা। তাই প্রমথনাথ যে শ্রেণির ছাত্র, তার থেকে উঁচু শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে বাংলা পড়তেন। আর যেহেতু অঙ্কে কাঁচা, সেহেতু অঙ্ক কষতেন নিচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে। এ-ব্যবস্থা শুনতে ভালো, তবে এ-ব্যবস্থা বাস্তবে চালিয়ে যাওয়া কঠিন। পরীক্ষা নিতে অসুবিধে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থাপনা বেশিদিন বজায় রাখতে পারলেন না। পরীক্ষা পদ্ধতিতে একটা সমতা বিধান তো করতেই হয়।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
যেখানে তিনি শিক্ষা-প্রশাসক, সেখানেও তিনি বেশ অন্যরকম। প্রমথনাথ বিশী অঙ্কে কাঁচা, বাংলায় পাকা। তাই প্রমথনাথ যে শ্রেণির ছাত্র, তার থেকে উঁচু শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে বাংলা পড়তেন। আর যেহেতু অঙ্কে কাঁচা, সেহেতু অঙ্ক কষতেন নিচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
পরীক্ষক হিসেবে কেমন প্রশ্ন করতেন তিনি? প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষক বা শিক্ষা-প্রশাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন না। তবে তাঁর প্রশ্নগুলি তাঁর শিক্ষাভাবনার পরিচয় বহন করছে। বাংলার আদ্য পরীক্ষায়, রবীন্দ্রনাথ ‘বীরপুরুষ’ কবিতা থেকে প্রশ্ন দিয়েছেন, ‘বালক তার মাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করবার যে গল্প মনে মনে বানিয়ে তুলেছে সেটি রস দিয়ে ফলিয়ে লেখো।’ কবিতাটি পড়তে পড়তে বালকের কল্পনা অনুসরণ করে পড়ুয়া-পাঠকও যাতে নিজের কল্পনাকে সম্প্রসারিত করতে পারেন, তাই চাইছেন রবীন্দ্রনাথ। ম্যাথু আর্নল্ডের ইংরেজি কবিতা ক্লাসে পড়ানোর সময় একই পদ্ধতি নিতেন তিনি। প্রথমে সহজ বাংলায় কবিতাটির গল্প বলতেন। তারপর ইংরেজি কবিতাটি পড়তেন। ইংরেজি কবিতার বাক্যগুলি গ্রহণ করে, পড়ুয়াদের তারই অনুসরণে নিজেদের কল্পনা ফলিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলতেন। লেখা-পড়ার কাজটি যেন কল্পনার আনন্দে হয়, এই ছিল লক্ষ্য। আরেকটি প্রশ্নের পরিচয় দেওয়া যাক। ‘বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর দয়ার বিশেষত্ব কী? সামাজিক কী কারণে এইরূপ দয়া আমাদের দেশে দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দেখাও।’ ‘বিদ্যাসাগর জননী’ পাঠ্য। দয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দেশ ও সমাজের দিকে ফিরলেন। উদ্দেশ্য একটাই– পড়ুয়ারা যেন পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার যোগ সাধন করতে পারে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথের কাজের ক্ষেত্র বড় হয়েছিল। ১৯১২ সাল পর্যন্ত আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাজেকর্মে যতটা মন দিতে পারতেন, পরে সেই মনোযোগ প্রদানের সময় পেতেন না। তবে মন পড়ে থাকত পড়ুয়াদের দিকে। নির্দেশ দিতেন, ইতিহাসের ক্লাসে যেন প্রয়োজনে ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ অভিনয় করে দেখানো হয়। বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার উপকরণ দেখলেই বিদ্যালয়ের জন্য নিয়ে আসতেন। নাটক ছিল তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা ও ভাবনা বিস্তারের উপায়। শুধু যে আশ্রম-বিদ্যালয়ের জন্য বাংলা নাটক লিখতেন তাই নয়, ইংরেজি যাতে বলতে শেখে, তারই জন্য লিখেছিলেন ‘কিং অ্যান্ড দ্য রেবেল’-এর মতো নাটক।
তিনি জানতেন বিদ্যালয়ে পড়াতে গেলে কেবল জ্ঞানী বা পণ্ডিত হলেই চলবে না, এমন মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে, যাঁরা পড়ুয়াদের সঙ্গে স্নেহ পারবশ্যে ও প্রসন্নতায় মিশে যেতে পারবেন। তাঁরা যেন ছেলেমানুষির মনটিকে জাগিয়ে রাখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাই সকলেই ছিলেন অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে, যে বিদেশিরা এদেশে এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনের স্কুলের কাজে তাল মিলিয়ে ছিলেন, সেই পিয়ার্সন, অ্যান্ড্রুজও ছিলেন এমনই খোলামনের ছাত্রবৎসল মানুষ। পিয়ার্সন তো বিদেশে ফিরে গিয়েও ভুলতে পারেননি এই বিদ্যালয়টিকে। হরনাথ পণ্ডিতদের অসম্মানের জগতের বাইরে পড়ুয়াদের ভালোবাসা আর সম্মান দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয়-শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ।
…………………ছাতিমতলা অন্যান্য পর্ব……………………..
ছাতিমতলা পর্ব ২০: সুভাষচন্দ্র বসুকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!
ছাতিমতলা পর্ব ১৯: আবেগসর্বস্ব ধর্ম ও রাজনীতির বিরোধিতা করে অপ্রিয় হয়েছিলেন
ছাতিমতলা পর্ব ১৮: রবীন্দ্রনাথ কখনও গীতাকে যুদ্ধের প্রচারগ্রন্থ হিসেবে বিচার করেননি
ছাতিমতলা পর্ব ১৭: ক্রিকেটের রাজনীতি ও সমাজনীতি, দু’টি বিষয়েই তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ১৬: রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন?
ছাতিমতলা পর্ব ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?
ছাতিমতলা পর্ব ১৩: পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা রেণুকার স্বাধীন মনের দাম দেননি
ছাতিমতলা পর্ব ১২: এদেশে ধর্ম যে চমৎকার অস্ত্রাগার, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি
ছাতিমতলা পর্ব ১১: কাদম্বরীকে বঙ্গজ লেখকরা মুখরোচক করে তুলেছেন বলেই মৃণালিনীকে বাঙালি জানতে চায়নি
ছাতিমতলা পর্ব ১০: পাশ্চাত্যের ‘ফ্যাসিবাদ’ এদেশেরই সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির প্রতিরূপ, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ
ছাতিমতলা পর্ব ৯: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান
ছাতিমতলা পর্ব ৮: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও
ছাতিমতলা পর্ব ৭: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না
ছাতিমতলা পর্ব ৬: যে ভূমিকায় দেখা পাওয়া যায় কঠোর রবীন্দ্রনাথের
ছাতিমতলা পর্ব ৫: চানঘরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও আপত্তি ছিল না রবীন্দ্রনাথের
ছাতিমতলা পর্ব ৪: যে রবীন্দ্র-উপন্যাস ম্যারিটাল রেপের ইঙ্গিতবাহী
ছাতিমতলা পর্ব ৩: ‘রক্তকরবী’র চশমার দূরদৃষ্টি কিংবা সিসিটিভি
ছাতিমতলা পর্ব ২: ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ বনাম ‘রবীন্দ্র-কৌতুক’
ছাতিমতলা পর্ব ১: ‘ডাকঘর’-এর অমলের মতো শেষশয্যা রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু পাননি

নতুন লেখককে এড়িয়ে গিয়ে পুরনো লেখকদেরই বই ক্রমাগত করে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের চিন্তার স্থবিরতা আছে বলে আমার মনে হয়। একটু গভীরে গেলে মনে হয়, রয়্যালটি যুক্ত বই-ই প্রকাশকের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, সুবিধে অনেকগুলো। একই বইয়ের দশ-পনেরো রকম সংস্করণ বাজারে থাকবে না। বইটা আপনি নির্ভয়ে প্রচার করতে পারবেন।