
মহেন্দ্রলাল দত্তের স্মৃতিকথায় দেখি কলকাতা শহরে ভোরবেলায় একটা চেনা ডাক ছিল– ‘কু-য়ো-র ঘ-ও-ও-টি তোলা-আ আ’। এরা নানারকমের বড়শি দিয়ে কুয়োতে পড়ে যাওয়া ঘটি-কলসি-বালতি তুলে দিত। কলের জল এসে কুয়োর ব্যবহার বন্ধ করে দিল, আর ওই ডাকটাও হারিয়ে গেল। এরকম একটা ডাক ছিল– ‘ভিস্তি, ভিস্তি আছি…’। ওদের ছিল বেল্ট ঝোলানো চামড়ার পাত্র। অনেকটা জল ধরত তাতে। বাইরে থেকে জল ভরে এনে বাড়িতে ঢালত। সবার ঘরেই মাসকাবারি ভিস্তি থাকত। তবুও কেউ কাজ না পেলে এমন ধারা হাঁকত। বিকেলের দিকে ‘চাই তপসে মাছ’ হাঁকটা ছিল গঙ্গা তীরবর্তী কলকাতায়। গঙ্গায় তখন প্রচুর তপসে মাছ ধরা পড়ত।
গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক
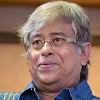
৩.
লকডাউন পর্বে ফেরিওয়ালাদের ফিরে পেলাম ফের। ফেরিওয়ালাদের হাঁক একেবারেই কমে গিয়েছিল কলকাতা শহরে। বাসনওলাদের ঠং ঠং শব্দ শোনা যেত না, মাছের ফেরিওয়ালা, ফলের ফেরিওয়ালাদের ডাকও শোনা যেত না। কিছু সবজিওলারা চারচাকার ভ্যান ঠেলে ‘তাজা শাক, তাজা সবজি’ হাঁকছিল। হিন্দিভাষী অধ্যুষিত এলাকায় ওরা ‘টমেটর’, ‘লাউকি’, ‘গোবি’ বলত। ফেরিওয়ালারা বাঙালিই, ওদের হাঁকেই বোঝা যেত এলাকায় হিন্দিভাষীর প্রাধান্য কতটা হয়েছে। কাগজ বিক্রিওয়ালারা আছে এখনও, কিন্তু ওরাও একটা ভ্যান চালিয়ে আসে ‘পুরানা কাগজ ভাঙা লোহা বিক্রি’-র সঙ্গে সঙ্গে বলে ‘বাতিল কম্পুটার, ইউপিএস, পিকচার টিউব’। পনেরো-কুড়ি বছর আগে ভাবা যেত এমন হাঁক?
‘পুরনো কাগজ’ না বলে ‘পুরানা কাগজ’ই বলতে শুনি। আসলে আগে এই ফেরিওয়ালারা মূলত হিন্দিভাষী ছিল। ওরা ওই ধরনটাই অনুসরণ করে। আর একটা আওয়াজের কথা মনে পড়ছে। লোহার চাটুতে খুনতি বাজানোর ঠং ঠং শব্দ। এরা দোসাওয়ালা, বাড়ির সামনে গরম দোসা বানিয়ে দেয়। এই ফেরিওয়ালাদের কুড়ি বছর আগে দেখিনি। আসলে ফেরিওয়ালারাও সামাজিক উৎপাদন। জীবনযাপনের প্রয়োজন এবং বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এরাও পাল্টে যায়।
শৈশবের ফেরিওয়াদের কথা মনে পড়ে। ‘পুরানা কাগজ বিককিরি, লোহা ভাঙা বিককিরি’ যারা হাঁকত, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা পিতল তামা কাঁসা বিককিরিও হাঁকত। কারণ তখন স্টিলের বাসনের চল হয়নি। স্টিলের বাসনের দাম ছয়ের দশকেও তুলনায় বেশিই ছিল। সাতের দশক থেকে দাম কমতে শুরু করে। পিরিং পিরিং আওয়াজ করতে করতে ধুনকররা আসত। তখন শীতও বেশি ছিল, বাড়িঘরগুলোও এমন নিশ্ছিদ্র ছিল না। রাতে ঠান্ডা ঢুকতে পারত, ফলে লেপ দরকার হত। যাঁরা ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে পাথরের শিল ঠুকে ঠুকে খরখরে করে, ওরা একটা অদ্ভুত ধরনের সুরেলা শব্দ করত– ‘শি-ই-ইল কাটাও’। এদের ডাকও প্রায় হারিয়ে গেছে। কারণ অনেক গেরস্ত বাড়িতেই এখন শিলে মশলা বাটা হয় না। মশলার গুঁড়ো বাজারে এসে গেছে ব্যাপক, আর মিক্সি মেশিনও তো আছে। আদা, পেঁয়াজ, লঙ্কা এসব মিক্সিতে বাটা নয়, পেস্ট হয়।
…………………………………………
সিনেমায় চানাচুরওয়ালাদের হাঁক শুনেছি, চানাচুরওয়ালাদের গানও শুনেছি সিনেমায়– ‘হরিদাসের বুলবুল ভাজা’। তবে ছোটবেলায় বয়স্ক মানুষদের কাছে শুনেছি ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা নিয়ে যাও’ হেঁকে ডালমুট বিক্রি হত। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ওঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, কলকাতার রাস্তায় নানা ধরনের মুখোরোচক খাবারের ফেরিওয়ালারা আসত। যেমন অবাক জলপান, চটপটি আলুকুচালু, নকুলদানা, ঘুগনিওয়ালা, মুড়িওয়ালাদের দল। একজন ফেরিওয়ালা আসত যে গান গেয়ে বিক্রি করত মনমোহিনী চপ।
…………………………………………
বসন্তের দখিনা বাতাস শুরু হতেই মাথায় ঝুড়ি, কিংবা টিনের বাক্স পিঠে ফেরিওয়ালাদের আগমন হত। সুরেলা স্বরে ‘মা-লাই বরওফ’। মালাই বরফওয়ালাদের বাক্সে একটু সিদ্ধির মণ্ডও থাকত। একটু বয়স্করা মৃদুস্বরে বলত সবুজটা মিশিয়ে দিও। বেলফুলওয়ালা একজনকে দেখেছি আমার স্কুল জীবনে। ‘চাই বেলফুল… চাই ইস্টিক ফুল…’। ইস্টিক ফুল মানে বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। মানে রজনীগন্ধার স্টিক। বিকেল বিকেল একজন টিনের বাক্স বাজিয়ে বলত– ‘ঘুঘনিআলুদ্দম… আলুদ্দমঘুগনি’। টিনের বাক্সের ভিতরে দুটো গোল টিন। সম্ভবত ডালডার। একটায় ছোট আলুর দম থাকত, ঝোল কম, অন্যটায় ঘন ক্ষীরের মতো ঘুগনি। ঘুগনির ওপরে নারকোল পাতি দিয়ে সাজিয়ে দিত। ডালডার কৌটোয় ভরা জাদু মশলা ছিটিয়ে দিত ঘুগনির ওপরে। আমরা একটা হাত পেতে দিতাম– দাও না, একটু মশলা দাও না…। জিভের ডগা লাগিয়ে সেই মশলা সারা মুখে লাগিয়ে জারিয়ে নিতাম। আলুর দম, ঘুগনি সবই শালপাতার পাত্রে। আলুর দমের ওপরে একটা কাঠি দেওয়া থাকত। কাঠি দিয়ে আলুর দম খাওয়া যে কী সুখের ছিল! কোনও রোগা ছেলের বড় মাথা থাকলে ওকে বলা হত ‘খ্যাংড়া কাঠি আলুর দম’। ডাবের ফেরিওলা দেখেছি। মাথায় ঝুড়ি করে ডাব ডাব হাঁকত। এখন অবশ্য সাইকেলের সারা গায়ে ডাব ঝুলিয়ে চলমান ডাবিং হয়। কাঠের বাক্সের দুটো কাঠের হ্যান্ডেল ঠেলতে ঠেলতে ‘আ ই স-কিরিম’ হাঁক কতদিন শুনিনি। এখনকার আইসক্রিমের বাক্সও প্রায় একই রকম আছে। কিন্তু ওরা এখন আর হাঁকে না। এক জায়গা থেকেই বিক্রি হয়ে যায়। আর আমাদের সময়ের দু’-পয়সা দামের স্যাকারিন দেওয়া রঙিন বরফের আইসক্রিম আর নেই। এক শনপাপড়িওলাকে দেখতাম। ওরও টিনের বাক্স। ওর হাঁক ছিল ভারি মজার– ‘এসো, এসো গো নন্দের দুলাল। আমি এসে গেছি। কোথা গো বামী, খেপি, ললিতা, বিশাখা, রাধিকা। গোপীগণ চলে এসো। আমি এসে গেছি। বেশিক্ষণ রইবোনা সই। তাড়াতাড়ি এসো।’

সিনেমায় চানাচুরওয়ালাদের হাঁক শুনেছি, চানাচুরওয়ালাদের গানও শুনেছি সিনেমায়– ‘হরিদাসের বুলবুল ভাজা’। তবে ছোটবেলায় বয়স্ক মানুষদের কাছে শুনেছি ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা নিয়ে যাও’ হেঁকে ডালমুট বিক্রি হত। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ওঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, কলকাতার রাস্তায় নানা ধরনের মুখরোচক খাবারের ফেরিওয়ালারা আসত। যেমন অবাক জলপান, চটপটি আলুকুচালু, নকুলদানা, ঘুগনিওয়ালা, মুড়িওয়ালাদের দল। একজন ফেরিওয়ালা আসত যে গান গেয়ে বিক্রি করত মনমোহিনী চপ। সেই গানটি হল–
মাছ মাংস ডিম্ব ছাড়া
শুদ্ধভাবে তৈরি করা
মনমোহিনী চপ।
সাড়ে বত্রিশ ভাজায় থাকত নানারকমের ডাল, বাদাম, চিঁড়ে ইত্যাদি। প্রথমে এর নাম ছিল ‘আঠেরো ভাজা’।
মহেন্দ্রলাল দত্তের স্মৃতিকথায় দেখি কলকাতা শহরে ভোরবেলায় একটা চেনা ডাক ছিল– ‘কু-য়ো-র ঘ-ও-ও-টি তোলা-আ আ’। এরা নানারকমের বড়শি দিয়ে কুয়োতে পড়ে যাওয়া ঘটি-কলসি-বালতি তুলে দিত। কলের জল এসে কুয়োর ব্যবহার বন্ধ করে দিল, আর ওই ডাকটাও হারিয়ে গেল। এরকম একটা ডাক ছিল– ‘ভিস্তি, ভিস্তি আছি…’। ওদের ছিল বেল্ট ঝোলানো চামড়ার পাত্র। অনেকটা জল ধরত তাতে। বাইরে থেকে জল ভরে এনে বাড়িতে ঢালত। সবার ঘরেই মাসকাবারি ভিস্তি থাকত। তবুও কেউ কাজ না পেলে এমন ধারা হাঁকত। বিকেলের দিকে ‘চাই তপসে মাছ’ হাঁকটা ছিল গঙ্গা তীরবর্তী কলকাতায়। গঙ্গায় তখন প্রচুর তপসে মাছ ধরা পড়ত। মাথায় জরির টুপি পরা, প্যান্টালুনে জামা গুঁজে পরা অদ্ভুত পোশাকের মানুষ ‘দেস্লাই, দে-স্-লা ই’ হাঁক পাড়ত। এরা দেশলাই কাঠি বিক্রি করত। দিয়াশলাই আসে ১৮৫৭ সালে। এর আগে টিকের আগুন বা কাঠকয়লার আগুন সংরক্ষণ করতে হত। ‘সতী ঠাকুরাণীর সতীত্ব বেচি গো…’ এরকম ডাক শুনলে আজকাল সতী-অসতী সবাই ভিরমি খাবেন। আসলে এরা আলতা-সিঁদুর কুমকুম বেচত। আর ‘মাজন মিশি মাথাঘষা’ বিক্রি করত মুসলমান ফেরিওয়ালারা। ওরা সুর্মাও বিক্রি করত। মাথাঘষা ছিল একধরনের গুঁড়ো, যা কিনা শ্যাম্পুর পূর্বপুরুষ। ‘রিফু কর্ম’ হাঁকের কথাও লিখেছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। বেদেনীরাও আসত। ‘বাত ভালা করি, দাঁতের পোকা বের করি গো…’।
বেদেনীরা সাপের খেলাও দেখাত। ভালো ভালো নয়া সাপ দেখ গো…।
ডুগডুগি বাজিয়ে বাজিয়ে বাঁদর নিয়েও আসত বাঁদর খেলাওয়ালা। ‘ভাঙ্গা বাসুন সারাতে আছে… পিলসুজ সারাতে আছে… টেরাঙ্ক সারাতে আছে…’।
যারা জয়নগর অঞ্চল থেকে আসত, ওরা পুতুল খেলাও দেখাত। পুতুলের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পুতুল নাচাত। আমি শৈশবে দেখেছি। সঙ্গে গান-রসের বিনো দিয়ে ভালো নাচবি খেঁদি। ধামা তৈরি হত বেত দিয়ে। ধামা খুলে যেত। সেই ধামা সারাই করার লোকও আসত।
এরকম নানা ফেরিওয়ালারা নানাভাবে গেরস্ত জীবনে সহায়তা করত। কিন্তু একটা জিনিস কোথাও দেখিনি যে, মদ ফেরি হচ্ছে। আদিবাসী এলাকাতেও নয়, যেখানে হাঁড়িয়া ঘরে ঘরে খায়। হাঁড়িয়াও গিয়ে খেতে হয়, ঘরের সামনে আসে না। কবীর সেই কবে বলে গিয়েছিলেন–
“সাংচা কো মারে লাঠা ঝুট জগৎ পিতায়
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বিকায়।”
ভালোর কদর নেই। গোয়ালা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দুধ বিক্রি করে, মদ এক জায়গায় বসেই বিক্রি করে। যেমন আর ফিরে আসবে না সিনেমাওয়ালারা। কাঠের বাক্স, ঢাকনা দেওয়া কাচ, ওখানে চোখ রেখে দেখতাম রাজ কাপুর-মধুবালা-সায়রা বানু। দেখতাম তাজমহল-কুতুবমিনার। ফিরে আসবে না চলমান খাটাল। সামনে দুধ দুইয়ে দেওয়া। গরু নিয়ে চলে আসত ভোজপুরি গোয়ালা। বাড়ির সামনে দুইয়ে দিত দুধ। ঘটিতে গরম দুধ নিয়ে ঘরে ফিরতাম। দুধের বালতিতে ফেনা।
‘ঝালাই করাবেন… ঝা-লা-ই’ শুনি না আর। রাং দিয়ে ফুটো হয়ে যাওয়া বালতি, ঘটি, কাঁসার বাসন ঝালাই করে দিত। এখন ইউজ এন্ড থ্রো-র যুগ। একটা সময় আমরা তালিবান ছিলাম সবাই। শতরঞ্চিতে, ছাতায়, জুতোয় তালি লাগাতাম তালিমারা ছাতা দেখতে পাই না বহুদিন।
বেদেনীদের দেখি না বহুকাল। ওই টানা চোখ, খাড়া নাক বেদেনীরা, ওদেরই একটা অংশ জিপসি। ওরা সারা পৃথিবীতে নানা নামে খ্যাত। ওদের নিয়েই অভিজিৎ সেনের উপন্যাস ‘রুহু চন্ডালের হাড়’। ওরা দাঁতের পোকা বের করত। বাতের তেলও বিক্রি করত ওরা। অনেক আগে তামাক খাবার চল ছিল। তামাক বা হুঁকো ধরাতে টিকে লাগত। আমি শুনিনি, গবেষক হরিপদ ভৌমিক জানিয়েছেন ওরা হাঁক দিত ‘টি-কে-লেও, ভালো জ্বলবে’।
এরা ছিল ফুটো সারানোর কারিগর। ঝালা দিয়ে সারাই করত। এখন ইউজ অ্যান্ড থ্রো-এর যুগে এত সারাই করে ব্যবহার করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকে দইওয়ালাকে দেখেছি। ‘দই চা-আ-ই দই, ভালো দই….’। আমি অবশ্য কলকাতা শহরে বাঁকে করে দই বিক্রি করার ফেরিওয়ালা দেখিনি। ওড়িশাতে দেখেছি। অমৃতলালের নাটকে চুড়িওয়ালাদের পেয়েছি। একদল ফেরিওয়ালা ‘খোস-পাচড়া-দাদ-হাজা’ বলতে বলতে যেত। ওরা মলম বেচত।
রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালাতে দেখেছি ‘হিং ভালো হিং, মেওয়া পেস্তা’ বলতে বলতে ফেরি করছে। ‘ছা-আ-তা, ছাত্তা সারাই’ ডাক এখনও শোনা যায়। ওরা বেশিরভাগই ফরিদপুরের লোক। ফুচকাওয়ালারা কোনও হাঁক দেয় না কেন জানি না।
আলুকাবলিওলারাও হাঁকে না। ওরা নিঃশব্দে বিক্রি করে রাস্তায় বা পার্কে দাঁড়িয়ে। এই হাঁক দুটো আর শুনি না– ‘বোম্বাইওয়ালা, বোম্বাইআলা’ আর ‘মেমসাহেবের চুল’। বোম্বাইআলা হল চিনির একরকম রঙিন খাবার। থকথকে চিনির নরম পাত একটা লাঠির মাথায় জড়িয়ে আনত, এবং ফুল, ঘড়ি, প্রজাপতি ইত্যাদি আকৃতি দিত। আর মেমসাহেবের চুলও চিনির রঙিন খাবার। চুলের মতোই ফিনফিনে, মুখে দিলে গলে যায়। এখন এ জিনিস বড় বড় শপিংমলে বেশ ভালো দামে বিক্রি হতে দেখেছি, অন্য কিছু নাম হয়েছে নিশ্চয়ই।
এতক্ষণ তো শহুরে ফেরিওয়ালাদের কথা বললাম। গ্রামেও ছিল বা আছে। সুপুরি পাড়ানোর লোক, ডাব পাড়ানোর লোক আসে। ফকিরমোহন সেনাপতির আত্মজীবনীতে পড়েছি ‘অবধান’ নামের একধরনের মানুষ আসত, যারা গাছের ফল দেখে সম্ভাব্য কত সের বা কত টন/মণ হবে বলে দিত। এটা জানতে পারলে পাইকারদের সঙ্গে দরাদরি করতে গৃহস্থের সুবিধা হত। গ্রামের দিকে সাইকেলে করে টিপ, সেফটিপিন, ন্যাপথালিন ইত্যাদি ফেরি করতে দেখেছি। রাঢ় অঞ্চলের গ্রামে মহল্লা হয়। পরপর ঘর। পূর্ববাংলার গ্রামে ঘরগুলি ছাড়া-ছাড়া। ফলে পূর্ববাংলার গ্রামে ফেরিওয়ালাদের খুব একটা সুবিধা হয় না। ফলে পূর্ববাংলার গ্রামের ভিতরে ফেরিওয়ালাদের খুব একটা দেখা যায়নি।
যে ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনার জন্য ভোরবেলার ট্রেনে অপেক্ষা করি সেটা হল– ‘চা-আ-য় গরম, গরম চা-য়’। ইদানীং স্টেশনে চাওয়ালারাও কমে এসেছে। কামরার ভিতরে বড় ফ্লাক্স আর কাগজের কাপ নিয়ে চলে আসছে। হাঁকের সুর ও পাল্টে গেছে। ফেরিওয়ালা শব্দটা ফার্সি ‘ফির’ থেকে এসেছে। ফির… আবার। বারবার।
কিন্তু কিছু ফেরিওয়ালা হারিয়ে গেল। আর আসবে না।
……………………………………
ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল
……………………………………
…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্বও…
২. নাইলন শাড়ি পাইলট পেন/ উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন
১. যে গান ট্রেনের ভিখারি গায়কদের গলায় চলে আসে, বুঝতে হবে সেই গানই কালজয়ী
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
