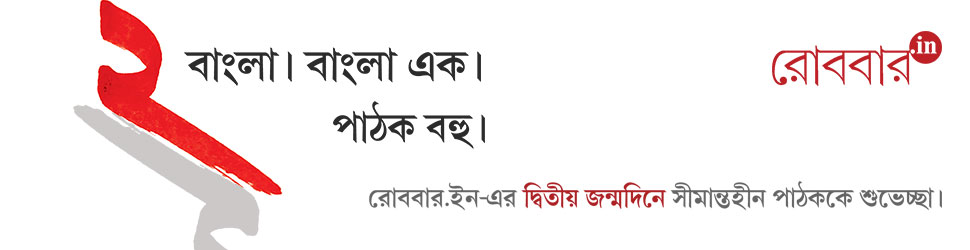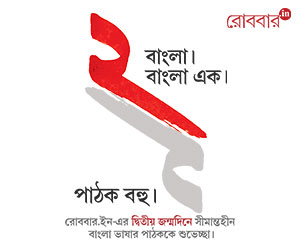উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে, মসূয়ায়। আদিতে অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ জেলার অংশ ছিল মসূয়া। বর্তমানে ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার একটি গ্রাম মসূয়া। মসূয়ার পত্তন হওয়ার আগে নাম ছিল ‘খুকুরপাড়া’। ব্রহ্মপুত্র নদ আগে উপেন্দ্রকিশোরের বসত বাড়ির গা ঘেঁষে বইত। এখন কাছে এসেছে আড়িয়াল খাঁ নদী। দূর দিয়ে বয়ে চলে ব্রহ্মপুত্র। মসূয়ার বাড়ির কিছু অংশ এখনও অক্ষত রয়েছে।

১৫.
‘‘প্রতি বৎসর ছুটির সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম পাহাড়ে, পশ্চিমে, কিম্বা আমাদের ‘দেশে’। ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকায়, অবশেষে হাতি এবং পাল্কিতে চড়ে পূর্ব-বাংলায় আমাদের সেই গ্রামে যাওয়াটা আমাদের কাছে যেন মস্ত একটা এডভেঞ্চার ছিল।
রাত্রে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে চড়ে সকাল বেলায় গোয়ালন্দে স্টিমার ধরতাম। মস্ত মস্ত জাহাজ, তাদের নাম ছিল এলিগেটর, ক্রোকোডাইল, পরপয়জ; আবার একদল ছিল ঈগল, কণ্ডর, ভালচার। আমরা কেবিনের ভিতরে থাকতেই চাইতাম না, সারাদিন ডেকে দাঁড়িয়ে দুধারের দৃশ্য দেখতাম। একেক জায়গায় নদী এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপার ভাল করে দেখাই যায় না। বর্ষাকালে পদ্মা নদীর স্রোতের এত জোর হয় যে, অনেক সময় দুই তীর ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কত ক্ষেত-গ্রাম ঘরবাড়ি, পুরনো দিনের কত কীর্তিচিহ্ন যে পদ্মা নাশ করেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। সেজন্যে তার আরেকটা নাম ‘কীর্তিনাশা’। এক জায়গায় মা দেখাতেন এইখানে তাঁর মামাবাড়ি ছিল– পদ্মার ভাঙনে গ্রামসুদ্ধ কোথায় তলিয়ে গিয়েছে।

বিকালের দিকে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে ট্রেনে উঠতাম। রাতদুপুরে কাওরাইদ স্টেশনে নেমে নৌকায় চড়তে হত। কাছাকাছি গভীর জঙ্গল, স্টেশন থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় শুনতাম নাকি ‘ভয় আছে’। আলো নিয়ে, লম্বা লম্বা লাঠি হাতে, অনেক লোকজন সঙ্গে থাকত– ঘুমচোখে গিয়ে আবার নৌকোর মধ্যে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়তাম।
…………………………………
স্নান করে, খেয়ে দেয়ে, আবার দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতাম, সারাদিন খেলা, গল্প ইত্যাদি হত।… নৌকো যখন গিয়ে ঘাটে লাগত, তখনও বাড়ি অনেক দূর। ঘাটে হাতি, পাল্কি-ডুলী অপেক্ষা করত। একটা বড় হাতি ছিল, সে ‘পাগলা’ বলে তার পিঠে কেউ চড়ত না, মালপত্র সব তার পিঠে চাপানো হত। ছোট হাতীটা খুব শান্ত, বাবা-কাকারা তার পিঠে চড়তেন, আমরা ডুলী-পাল্কিতে ভাগাভাগি করে চড়তাম।
…………………………………..
সকালে উঠে দেখতাম এবার পদ্মা নয়, অনেক ছোট নদী দিয়ে চলেছি। বেলা হলে এক জায়গায় নৌকো বেঁধে সঙ্গের লোকজন রান্না করত, আমরা নৌকোর আড়ালে নদীতে নেমে স্নান করতাম। নদীর ঢালু পাড়ে মাটির মধ্যে ছোট ছোট গোল গোল গর্ত, তার মুখের কাছে অনেক মাছের কাঁটা বসানো– শুনলাম ওগুলো নাকি মাছরাঙা পাখির বাসা। ইঁদুর প্রভৃতি যাতে ঢুকতে না পারে, তাই মাছরাঙা পাখি মাছ খেয়ে তার কাঁটাগুলো দিয়ে গর্তের মুখে ‘কাঁটা তারের বেড়া’ বানিয়ে দেয়। লম্বা ঠোঁটওয়ালা সুন্দর নীল মাছরাঙা পাখিকেও দেখলাম, জলের ধারে গাছের ডালে চুপ করে বসে আছে– মাছ দেখতে পেলেই তীরের মত ছোঁ মারছে।
স্নান করে, খেয়ে দেয়ে, আবার দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতাম, সারাদিন খেলা, গল্প ইত্যাদি হত।… নৌকো যখন গিয়ে ঘাটে লাগত, তখনও বাড়ি অনেক দূর। ঘাটে হাতি, পাল্কি-ডুলী অপেক্ষা করত। একটা বড় হাতি ছিল, সে ‘পাগলা’ বলে তার পিঠে কেউ চড়ত না, মালপত্র সব তার পিঠে চাপানো হত। ছোট হাতীটা খুব শান্ত, বাবা-কাকারা তার পিঠে চড়তেন, আমরা ডুলী-পাল্কিতে ভাগাভাগি করে চড়তাম। মনে পড়ে, একবার মা টুনী মণিকে নিয়ে পাল্কিতে চড়লেন, সুরমা মাসী আর দিদি উঠল একটা সুন্দর চূড়োওয়ালা ‘মহাপায়া’-তে (চতুর্দোলার মত), দাদার আর আমার, ভাগ্যে জুটল একটা বাঁশের ডুলী। আমি কেঁদে-কেটে জোর করে দিদি আর সুরমা মাসীর মাঝখানে ঠেসে দোলায় চেপে বসলাম, দাদা (সুকুমার রায়) লক্ষ্মী ছেলের মত একাই ডুলীতে গেল। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হত, কারা যেন শাঁখ বাজাত, ঠাকুরমা, পিসীমারা এগিয়ে এসে আমাদের আদর করে ঘরে নিয়ে যেতেন।…’’

ওপরের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটুকু পুণ্যলতা চক্রবর্তীর আত্মজীবনী ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এখানে রয়েছে ছুটিতে রায়বাড়ির সদস্যদের কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি মসূয়ায় ফেরার বর্ণনা। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। মাতা বিধুমুখী। দাদা সুকুমার রায়। দিদি সুখলতা রাও। ছোট ভাই সুবিনয় ও সুবিমল। ছোট বোন শান্তিলতা। ‘বাংলা শিশু সাহিত্য’ যাঁদের হাতে সৃষ্টি, তাঁদের সবাইকে এক ফ্রেমে এই বনাকীর্ণ জলাভূমির যাত্রাপথে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের এই রায় পরিবারের সবার মধ্যে ভাষার যে আশ্চর্য সরলতা বা প্রসাদগুণ, তার শিকড় ময়মনসিংহের মসূয়ার মাটিতে পোঁতা রয়েছে।
পুণ্যলতার দুই কন্যা নলিনী ও কল্যাণী। নলিনী (পরবর্তীকালে দাশ) যুক্ত ছিলেন ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল। জীবনানন্দ দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের সঙ্গে বিবাহ হয় নলিনীর।
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে, মসূয়ায়। আদিতে অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ জেলার অংশ ছিল মসূয়া। বর্তমানে ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার একটি গ্রাম মসূয়া। মসূয়ার পত্তন হওয়ার আগে নাম ছিল ‘খুকুরপাড়া’। ব্রহ্মপুত্র নদ আগে উপেন্দ্রকিশোরের বসতবাড়ির গা ঘেঁষে বইত। এখন কাছে এসেছে আড়িয়াল খাঁ নদী। দূর দিয়ে বয়ে চলে ব্রহ্মপুত্র। মসূয়ার বাড়ির কিছু অংশ এখনও অক্ষত রয়েছে। একটা ভবনে ‘মসূয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস’ হয়েছে। আরেকটা ভবনকে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায় এনে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়। বাড়ি সামনের ঘাট বাঁধানো বিশাল দিঘি, বাড়ির পিছনে ছোট পুকুর। এ বাদে মসূয়ায় রায়বাড়ির আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র সুকুমার রায় এবং পৌত্র সত্যজিৎ রায়। মসূয়ার রায়বাড়ির এই তিনজন অধিক পরিচিত। কিন্তু এই তিনজন ছাড়া আগে-পরে চৌদ্দো পুরুষ ধরে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তর মতো প্রতিভা প্রাপ্ত এই পরিবারের প্রায় সকলেই।
উপেন্দ্রকিশোরের পিতামহ লোকনাথ রায় ছিলেন একজন তান্ত্রিক। উপেন্দ্রকিশোরের জন্মদাতা পিতার নাম কালীনাথ রায় ওরফে মুন্সী শ্যামসুন্দর। তিনি ছিলেন আরবি, ফারসি, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। ময়মনসিংহ ও মসূয়ার মানুষের কাছে শ্যামসুন্দর মুন্সী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। জন্মদাত্রী মাতা জয়তারা দেবী। দত্তক পিতার নাম হরিকিশোর রায়চৌধুরী। পালিকা মাতা রাজলক্ষ্মী দেবী। জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী পেশায় ছিলেন একজন আইনজীবী। শিক্ষা ও পেশাগত কারণে রায়বাড়ির সকলেই মসূয়া ছেড়ে প্রথমে ময়মনসিংহ, ঢাকা ও শেষে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মাতা জয়তারা দেবী স্বামীর ভিটে মসূয়ার বাড়ি কখনও ত্যাগ করেননি।

উপেন্দ্রকিশোররা পাঁচ ভাই, তিন বোন। সকলেরই জন্ম মসূয়ায়। দাদা সারদারঞ্জন, দিদি গিরিবালা, এরপর উপেন্দ্রকিশোর (কামদারঞ্জন), ষোড়শীবালা, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন ও কনিষ্ঠ বোন মৃণালিনী। এরা ব্রহ্মপুত্রের সন্তান। মনে হয় যেন এঁরা সবাই ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দস্যু কেনারাম ও কাজলরেখার একেকটা চরিত্র। কত কত গুণীজন জন্ম নিয়েছেন এই রায়বাড়িতে। বাংলাকে এঁরা ধারণ করছেন যেভাবে, তেমন করে বাংলাকে এঁরা বহন করেছেন যুগ যুগ ধরে। উপেন্দ্রকিশোরের অনুমতি সাপেক্ষে স্বদেশিযুগে মসূয়ার বাড়িতে বেশ কিছু তাঁত বসিয়েছিলেন দত্তক ভাই জমিদার নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জীবনের প্রথম ১৬ বছর কাটে মসূয়া ও ময়মনসিংহ শহরে। মসূয়ার বাড়ির মতোই বিশাল বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ শহরে। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরের বাড়িটি বিলীন হয়ে সেখানে শহরের সবচেয়ে উঁচু ভবন হয়েছে। কিন্তু বাড়ির সামনের রাস্তার নামকরণ রয়ে গেছে ‘হরিকিশোর রোড’ নামে। মজার বিষয় হচ্ছে ময়মনসিংহ বা মসূয়া যেখানেই উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির খোঁজ করতে গিয়েছি, লোকজন সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছেন।
ময়মনসিংহ জেলার প্রথম সংবাদপত্র ও প্রথম ছাপাখানা ‘বিজ্ঞাপনী’-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন মসূয়ার জমিদারি হরিকিশোর রায়চৌধুরী। ১৮৬৬ সনে ‘বিজ্ঞাপনী’ যন্ত্র ময়মনসিংহ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন ময়মনসিংহ হিন্দু মহাসভার সভাপতি। আর পুত্র উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহ থাকাকালীন সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী জীবনে ছোটদের জন্য লেখা বাদেও বড়দের জন্য ব্রাহ্মসংগীত রচনা করেন।

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে উপেন্দ্রকিশোরের পড়াশোনা শুরু হয়। পড়াকালীন সময়ে প্রথমে বেহালা বাজানো শুরু করেন। এবং ছবি আঁকায় মেতে উঠেন। এতে করে স্কুলের হেডমাস্টার রতনমণি গুপ্ত উপেন্দ্রকিশোরের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এই স্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি-সহ উত্তীর্ণ হন। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন সংগীত পিপাসু। উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পের মহৎ সমন্বয় ঘটেছিল। উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পুত্র সুকুমার রায় কেউই আঁকা শেখেননি। কিন্তু তাঁদের ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অফুরন্ত কল্পনাশক্তি।
একদিন ময়মনসিংহ জিলা স্কুল পরিদর্শনে আসেন বাংলার ছোটলাট স্যর অ্যাসলি ইডেন। অ্যাসলি উপেন্দ্রকিশোরের ক্লাসে যখন ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন। তাৎক্ষণিক উপেন্দ্রকিশোর তাঁর লেখার খাতায় স্যর অ্যাসলি ইডেনের একটি পোট্রের্ট আঁকেন। উপেন্দ্রকিশোরের খাতায় নিজের প্রতিকৃতি দেখে ইডেন-সহ পরিদর্শক দলের সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হন।
প্রবেশিকা পরীক্ষার পর মসূয়া থেকে উচ্চশিক্ষার্থে উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় যান এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ এবং মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট থেকে বি.এ পাস করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন ও ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় প্রমদারঞ্জন রায়ের সার্ভেয়ার জীবন নিয়ে লেখা ‘বনের খবর’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বনের খবরে জানা যায় আমাদের প্রাকৃতিক অতীত কেমন ছিল। আমরা কোন অরণ্য ধ্বংস করে আজকের এই নগর গড়ে তুলেছি। শিশুসাহিত্যক লীলা মজুমদারের লেখা ‘হলদে পাখির পালক’ কোন অরণ্যের হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে সেই সূত্র পাওয়া যায় তাঁর পিতা প্রমদারঞ্জন রায়ের লেখা বনের খবরে।
উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় স্থায়ী হওয়ার পর ইংরেজি ১৮৯৮ সালের দিকে কলকাতায় ‘প্লেগ’ মহামারী দেখা দিলে উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে মসূয়ায় ফিরে আসেন এবং টানা কয়েক মাস মসূয়ায় কাটান। এর মধ্যে কোনও একসময় ময়মনসিংহ আদালতে দত্তক ভাই নরেন্দ্রকিশোর একটি মিথ্যা খুনের মামলার প্রধান আসামী হওয়ায় কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ ছুটে আসেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন সেই সময়ের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসুকে মামলা লড়ার জন্য। এরপর ১৯০৬ সালের দিকে মসূয়ার জমিদারির বিষয়সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার জন্য আত্মীয়স্বজন-সহ সকলেই মসূয়ায় আসেন। আর শেষবারের মতো মসূয়া ও ময়মনসিংহে ঘুরে যান ১৯১১ সালে।
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ময়মনসিংহের খাঁটি গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় ছিল বাঙাল টান। পূর্ববঙ্গের জনপদ এসেছে তাঁর রেখায় ও লেখায়। উপেন্দ্রকিশোরের নিজের লেখা নিজের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশুতোষ গ্রন্থ ‘টুনটুনির বই’। এই বইয়ের ভূমিকাতে উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন– ‘সন্ধ্যার সময় শিশুরা আহার না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন।’ এখনও বাংলার শিশুরা উপেন্দ্রকিশোরের গল্প শুনে জেগে থাকে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বেহালা শুনে ঘুমিয়ে পড়েন।
ছবি: কামরুল হাসান মিথুন
… দ্যাশের বাড়ি-র অন্যান্য পর্ব …
পর্ব ১৪: পাবনার হলে জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছিলেন সুচিত্রা সেন
পর্ব ১৩: নদীমাতৃক দেশকে শরীরে বহন করেছিলেন বলেই নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমৃত্যু সজীব ছিলেন
পর্ব ১২: শচীন দেববর্মনের সংগীত শিক্ষার শুরু হয়েছিল কুমিল্লার বাড়ি থেকেই
পর্ব ১১: বাহান্ন বছর পর ফিরে তপন রায়চৌধুরী খুঁজেছিলেন শৈশবের কীর্তনখোলাকে
পর্ব ১০: মৃণাল সেনের ফরিদপুরের বাড়িতে নেতাজির নিয়মিত যাতায়াত থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার জীবন শুরু
পর্ব ৯: শেষবার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে জানলায় নিজের আঁকা দুটো ছবি সেঁটে দিয়েছিলেন গণেশ হালুই
পর্ব ৮: শীর্ষেন্দুর শৈশবের ভিটেবাড়ি ‘দূরবীন’ ছাড়াও দেখা যায়
পর্ব ৭: হাতে লেখা বা ছাপা ‘প্রগতি’র ঠিকানাই ছিল বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের বাড়ি
পর্ব ৬ : জীবনের কালি-কলম-তুলিতে জিন্দাবাহারের পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন পরিতোষ সেন
পর্ব ৫ : কলাতিয়ার প্রবীণরা এখনও নবেন্দু ঘোষকে ‘উকিল বাড়ির মুকুল’ হিসেবেই চেনেন
পর্ব ৪ : পুকুর আর বাঁধানো ঘাটই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির একমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন
পর্ব ৩ : ‘আরতি দাস’কে দেশভাগ নাম দিয়েছিল ‘মিস শেফালি’
পর্ব ২: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈশবের স্মৃতির নন্দা দিঘি চিরতরে হারিয়ে গেছে হাজীগঞ্জ থেকে
পর্ব ১: যোগেন চৌধুরীর প্রথম দিকের ছবিতে যে মাছ-গাছ-মুখ– তা বাংলাদেশের ভিটেমাটির
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved