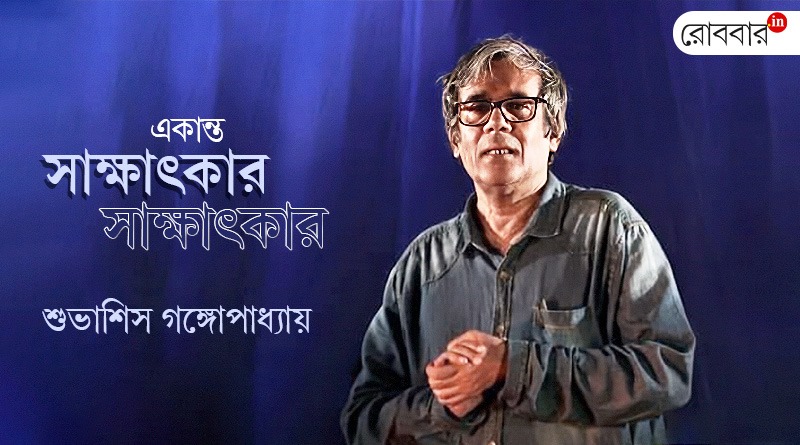
আজ বিশ্ব নাট্য দিবস। নাট্যচর্চা এবং থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত মানুষদের জন্য বিশেষ দিন। সেই পঙক্তিভুক্ত থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত দৃষ্টিহীন নাট্যকর্মীরাও। মূলস্রোতের নাট্যচর্চার পাশাপাশি দৃষ্টিহীনদের থিয়েটার চর্চার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কীভাবে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তাঁরা এই নাট্যসাধনায় ব্রতী হন? কীভাবে তাঁরা অনুভব করেন দর্শকদের স্পন্দন? সেই অভিজ্ঞতাই তুলে ধরলেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ‘ব্লাইন্ড অপেরা’ নিয়ে যিনি কাজ করছেন দীর্ঘসময় ধরে। রোববার.ইন-এর তরফে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার নিলেন প্রিয়ক মিত্র।

আপনি দীর্ঘদিন ধরে দৃষ্টিহীনদের নিয়ে নাট্যচর্চা করে চলেছেন, ‘ব্লাইন্ড অপেরা’ দিয়ে যে–কাজ শুরু। এই কাজটার শুরু কীভাবে? এই ভাবনাটা এল কীভাবে?
‘ব্লাইন্ড অপেরা’-র সঙ্গে কাজ শুরু করলেও এখন আমি কাজ করি ‘শ্যামবাজার অন্যদেশ’ দলে। ১৯৯৪ সালে ‘ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল’-এর ১০০ বছর উপলক্ষে একটি থিয়েটার করানোর দায়িত্ব পড়েছিল আমাদের ওপর। সেই স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল পেরিয়ে কলেজে যাওয়ার সময় চাইল, নিজেদের একটি থিয়েটার গ্রুপ খুলতে, নিয়মিত, পেশাদারি থিয়েটার করতে। তখন ভাবলাম, দেখাই যাক না, কী হয়! মূলত তাদের চাওয়াতেই এই নাট্যচর্যার শুরু। তারপর থেকে তিন দশক ধরে এই থিয়েটারের যাত্রাপথ চলছে।
আপনি মূলস্রোতের নাট্যচর্চার সঙ্গেও যুক্ত থেকেছেন। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে থিয়েটার করতে এসে নাটক তৈরির, রিহার্সাল থেকে মঞ্চে ওঠার পদ্ধতিতে বা প্রক্রিয়ায় কোনও পার্থক্য অনুভব করেছিলেন?
থিয়েটার আর বেঁচে থাকার মধ্যে আসলে কিন্তু খুব একটা দূরত্ব নেই। যে-কোনও মানুষের বেঁচে থাকা, যাপনই থিয়েটারের আয়নায় প্রতিফলিত হয়, শিল্পের অমোঘ নিয়মে। যে চোখে দেখতে পায় না, সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, শুনে শুনে দেখে। এই পথেই তার নিজস্ব দৃষ্টি তৈরি হয়। সেই অন্য দৃষ্টিই ব্লাইন্ড থিয়েটারের পাথেয়। দু’টো মানুষের মধ্যে তফাত করে তো এই দেখার দৃষ্টিই। দেখা মানেই আলো, আলো মানেই জ্ঞান– এমন একটা ধারণা তো আমরা তৈরি করে রেখেছি। কিন্তু সবসময়ই তা সত্যি নয়। আলো মানেই জ্ঞান, আর অন্ধকার মানেই অজ্ঞান, এই বাইনারি বা দ্বিস্থানিক কথাগুলো জ্যান্ত মানুষের ক্ষেত্রে মোটেই খাটে না, পাল্টে যায়। ‘অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে’- একথা কাব্যে একভাবে পড়ি, কিন্তু অন্ধ মানুষ তো কোনও ইমেজ বা প্রতীক নয়, সে একজন জীবন্ত মানুষ। এই জীবন্ত মানুষ যখন থিয়েটার করছে, তখন তার ধরন তো আলাদা হয়ে যাবেই।

যদি প্রসেনিয়াম মঞ্চের কথাই বলি, একজন দৃষ্টিহীন অভিনেতা যখন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ান, তখন তিনি দর্শকের উপস্থিতি অনুভব করেন কী করে?
যে দৃষ্টিহীন মানুষ বেঁচে আছে, সে তার আশপাশের অন্য বেঁচে থাকা মানুষের অস্তিত্বটা অনুভব করে কী করে? সে তো দেখতে পাচ্ছে না তাদের। সে বুঝে নেয় শব্দে, বা স্পন্দনে। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে একজন দৃষ্টিহীন অভিনেতাও তাই দর্শকের স্পন্দন টের পায়, দেখতে না পেলেও। রাস্তা পার হওয়ার সময়, বা বাড়িতে সে যেভাবে অন্য মানুষকে টের পায়, অনেকদিনের শোনা-জানার অভ্যাসে, সেই অভ্যাসেই দৃষ্টিহীন অভিনেতা চিনে নেয় দর্শককে। অভিনেতা যখন মঞ্চে উঠছে, তখন সে দর্শক কেন, নিজের চরিত্রকেও তো দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে না সে কীভাবে সেজেছে, কীভাবে সে মেক আপ করেছে। কিন্তু তার সমস্ত শরীর দিয়ে সে কমিউনিকেট করছে। যা তার সামনে আছে, বা তার যে প্রিয় চরিত্রের আধারে সে মঞ্চে আসছে, তাকে সে চিনছে। সে যে চরিত্র সেজেছে, সেই চরিত্র আর সে তো এক ব্যক্তি নয়। কিন্তু তাও সে কিন্তু সেই অন্য চরিত্রটাকে দেখতে পায়। কোনও কোনও অভিনেতা আমাকে এমনও বলেছেন, তিনি যখন অভিনয় করেন, তখনই কেবল দেখতে পান। সে অন্য একটা চরিত্রের কথা শুনছে, সেই চরিত্রকে সে অন্তরে দেখতে পাচ্ছে। সেই চরিত্র রামের হোক, বা সিরাজ-উদ-দৌল্লার-দৌল্লার, বা পতিতপাবনের।
আপনার এমন কোনও অভিজ্ঞতা ঘটেছে এই নাট্যপ্রক্রিয়ায়, যা একদম অন্যতর?
‘ব্লাইন্ড অপেরা’ বা ‘শ্যামবাজার অন্যদেশ’– এই দুই দলের হয়েই আমি নাট্য নির্দেশনা করেছি। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্দেশনার সময় আমি যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে চিনেছি, তা হয়তো সাদা চোখে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। যেহেতু বারেবারেই রবীন্দ্রনাথে অন্ধকারের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে, তাই আরও বেশি করে এক অন্য প্রতীতি নির্মিত হয়েছে বারবার। যেমন, ‘রাজা’ নাটকের শুরুতেই একজন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ, সুদর্শনার সংলাপ, ‘আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না’– এই সংলাপ যখন এক দৃষ্টিহীন অভিনেত্রী দিচ্ছেন, তখন তার দ্যোতনা পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর আলোর সন্ধান তো অন্যরকম! অথবা কেউ যখন গাইছেন, ‘আরো আলো আরো আলো’, তখন এক অন্য ব্যঞ্জনায় আলো এসে পৌঁছচ্ছে আমার কাছেও। ‘রাজা’ নাটকের নির্দেশনা তাই আমাকেও রবীন্দ্রনাথকে অন্যভাবে চিনতে শিখিয়েছে।

বাংলা নাটকে শরীরী অভিনয়ের দিকটা অনেকদিন ধরেই খুব জরুরি হয়ে উঠছে। দৃষ্টিহীনদের থিয়েটারে সেই শারীরিক ভাষাটা কীভাবে তৈরি হয়?
‘রক্তকরবী’ করেছেন ওঁরা, ‘তাসের দেশ’-ও করেছেন, ‘তাসের দেশ’ তার মধ্যে নৃত্যনাট্য। যেখানে নৃত্য আছে, সেখানে শরীরের ভাষা তো অবশ্যই আছে। তাছাড়াও, এই শরীরী ভাষা তৈরির পদ্ধতি অবশ্যই রয়েছে। একটি মূর্তি যদি তৈরি করে কোনও চোখে দেখতে পাওয়া মানুষের সামনে রাখা হয়, এবং তার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়, সে যেমন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চিনে নেবে সেই মূর্তির কারুকাজ; সেভাবেই অন্য মানুষ, অন্য অভিনেতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একজন দৃষ্টিহীন অভিনেতার শরীরের ভাষা তৈরি হচ্ছে। দৃষ্টিহীনদের স্বাভাবিক শারীরিক ভাষা থাকে না, কারণ তারা চোখে দেখে না। কিন্তু মূর্তি তৈরির মতোই, মাটির তালের মতো বহু চেনার অভ্যাস জুড়ে জুড়ে দৃষ্টিহীনদের শরীরের ভাষা তৈরি হয়। চোখে যারা দেখতে পায়, তারাও তো অন্যের শরীরের ভাষা দেখে, নকল করতে করতেই নিজের শরীরের ভাষা তৈরি করে, একজন দৃষ্টিহীনও তার চেনাজানার ভিত্তিতে, নকল করতে করতে তার নিজস্ব শরীরের ভাষা তৈরি করবে। সেই নকল করার কাজ হয়তো অভিনয়ের মতো শিল্পকলায় এসে হয়তো রসোত্তীর্ণ হচ্ছে। এখন, ছৌ-নাচের মতো বিভিন্ন বিভঙ্গ তো যে দেখতে পায়, সেও প্রভূত অভ্যাস ছাড়া আয়ত্ত করতে পারবে না, দৃষ্টিহীনদের ক্ষেত্রেও তাই।

‘বিশ্ব নাট্য দিবস’ আজ। দৃষ্টিহীনদের এই থিয়েটার চর্চার সূত্র ধরে মূলস্রোতের থিয়েটারকে কোনও বার্তা কি আপনি দেবেন?
না, ওভাবে বার্তা দেওয়ার তো কিছু নেই। একটা কথাই বলব, ভারতে বা এশিয়ায় হয়তো অন্যত্র এই দৃষ্টিহীনদের নিয়মিত ও পেশাদার থিয়েটার চর্চা খুব একটা সহজে চোখে পড়বে না। তাই নিয়ে উৎসাহ একটু বাড়লে ভালো হয়। এই দেশে প্রায় ১৫ মিলিয়ন দৃষ্টিহীন রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি। মূলস্রোতের বাঁচার বাইরে আরও অনেকরকম বাঁচা রয়েছে, সেই বাঁচার দিকে না তাকানোও এক ধরনের দৃষ্টিহীনতা, যা রাজনীতির মতোই ছড়িয়ে পড়ছে এখন দেশ জুড়ে। তাই বিশ্ব নাট্য দিবসে এটুকুই বলার, কেবলই মধ্যবিত্তর সংকটের বাইরে বেরিয়ে থিয়েটার এই অন্যধরনের জীবনধারাগুলোর দিকেও ফিরে তাকাক।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
