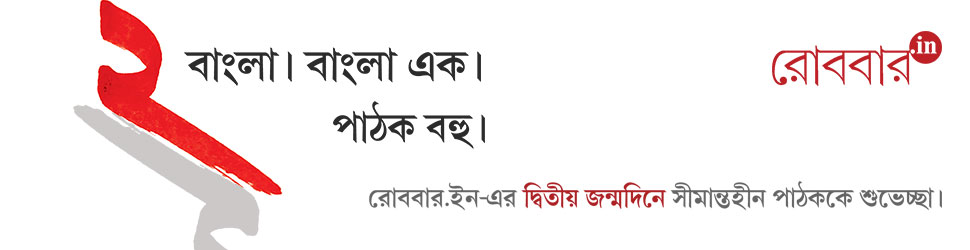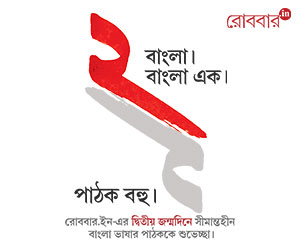বিশেষত পুজো এলেই কীরকম অতীন্দ্রিয় যোগসাজশে যেন আজকের ছিন্নভিন্ন এই ভূমণ্ডলের বহুধাবিভক্ত ভাষা ও ধর্ম, এমনকী পরস্পরকে জেনে-না-নেওয়ার কৃত্রিম প্রয়াস থেকে বিমুক্ত হয়ে শারদোৎসবের উপযোগী ভবিষ্য সমাজের দিকে এগিয়ে যায়। আমার কাছে এই নান্দনিক কুসংস্কারই বুঝি-বা-দুর্গাপূজার রহস্য।

বয়সের সুবাদে যখন কৌশোরমদির পল্লিগ্রাম এবং বহির্বিশ্বের তরঙ্গসংকুল নগরপুঞ্জ একাকার হয়ে যায়, স্থান-কাল হয়ে ওঠে আপেক্ষিক, মা-র পুজোটা কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেদিকে তেমন হুঁশ থাকে না, আসল এষণাটা হয়ে ওঠে, যেভাবেই হোক এবারেও দশভূজার পূজা প্রণীত হয়েছে কি না। এরকমই একটি সন্ধিক্ষণে মহালয়ার মুখে সুদূর ভিয়েনা থেকে শরণার্থীরা তাদের আরদ্ধ পূজার উদ্বোধনের মর্মে আমাকে যখন ডাক পাঠান, বিমানবন্দরের লাউঞ্জে কয়েকটা লাইন কোত্থেকে উঠে এসে আমায় যেন ছোবল মারল:
এমন মাটি আকাশ এবং আকাশ মাটি,
ঘাসের ভিতর ঘুপটি মেরে বিমানঘাঁটি।
সন্ধিপূজা বলতে পারো, কিশোরদশায়
মহাষ্টমীর রাত্রে যখন পুরুৎমশায়
তর্জনীটা ঘুরিয়ে ধ’রে অর্ধমাত্রা
‘এই মুহূর্তে দীপ জ্বেলে দে একশো আটটা’
বলে উঠতেই মা আর আমি থরথরিয়ে
দীয়া জ্বালতাম এবং তিনি খড়্গ নিয়ে
চেয়ে দেখতেন সলতে কিছু কমতি হলে
মা আর আমার আঙুলগুলো উঠত জ্বলে;
বহ্নুৎসব ঘিরে তখন জোনাক-আঙার,
রিখিয়া এক উপগ্রহ ভুবনডাঙার।
আর এখুনি বিশ্বলোকে যাবার আগে
মুখে ঘষছি গুগ্গুল ইউক্যালিপটাসের
ভাবছি শেষে পৌঁছে যেতে পারব তো ঠিক
একটু পরেই ভূমধ্য ওই সাগরান্তিক
উদ্বাস্তুর দুর্গাপূজায়? দশভূজা
আমার কাছে যাচে আবার সন্ধিপূজা!
পথ চলতি চটজলদি এই ত্বরগ্রাম কোনও একটি কবিপত্রে বেরনোর পর আমার বহু ভাষাবিশারদ বন্ধু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, কোনও একটি তথ্যচিত্রের জন্য ইংরেজিতে সেটি ভাষান্তরিত করার মুহূর্তে, ভারি সুন্দর একটি দোলাচলে পড়ে গিয়েছিলেন যেন। বিশেষত, ‘রিখিয়া এক উপগ্রহ ভুবনডাঙার’ জায়গাটায়। কেননা আবার সংবেদী সতীর্থ হিসেবে তিনি তো জানতেনই, ‘ভুবনডাঙা’ বলতে আমি আবিশ্ব চরাচরকেই বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেই জায়গায় ‘ভুবনডাঙা’ শব্দটাকে তার অবিচল কৌমতায় অক্ষুণ্ণ রেখে দিলেন: বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথের সেই সংজ্ঞাতীত অথচ স্থানিক পরিসর। অনুবাদ-কালে শমীকের ওই অন্তিম নির্ধারণ আজ আমার নিদারুণ মনঃপূত, যেহেতু আজ আমার কাছে ইহজগতের প্রতিটি অঞ্চলই আন্তর্জাতিক, তাকে বোঝানোর জন্য কোনও অতিরিক্ত টিপ্পনীর দরকারই পড়ে না। বিশেষত পুজো এলেই কীরকম অতীন্দ্রিয় যোগসাজশে যেন আজকের ছিন্নভিন্ন এই ভূমণ্ডলের বহুধাবিভক্ত ভাষা ও ধর্ম, এমনকী পরস্পরকে জেনে-না-নেওয়ার কৃত্রিম প্রয়াস থেকে বিমুক্ত হয়ে শারদোৎসবের উপযোগী ভবিষ্য সমাজের দিকে এগিয়ে যায়। আমার কাছে এই নান্দনিক কুসংস্কারই বুঝি-বা-দুর্গাপূজার রহস্য।
২.
সত্যের খাতিরে কবুল করতেই হয়, আজন্মপ্রবাসী বাঙালি যখন তার ভিটে ছেড়ে চলে যায়, তখনও তার সঙ্গে অনপনেয়ভাবে অনুস্যূত থাকে তার কিছু কিছু মজ্জাগত স্বভাবদোষ। তার এরকম একটি অন্যতম বিখ্যাত বিশেষত্ব– শতদল ভেঙে শতদল গড়া। পূজার বোধনলগ্নেই এভাবে, যেমন কিনা জার্মানিতে, কতবার যে কত হীনযানী মৈত্রীচক্র চুরমার হয়ে গিয়েছে তার উয়েত্তা নেই। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আমার নিজস্ব কয়েকজন ঐশ্বরিক গোয়েন্দার কাছে অবশ্যই এই সমাচারও পেয়েছি, এক-এক সময় কোনও শিখ সাধক আদিগ্রন্থ সম্বল করে বিভাদভঞ্জন করতে অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছেন, কিংবা কোনও ইমাম জায়নামাজ নিয়ে হাজির, বারোজন শিষ্য সামন্ত নিয়ে ‘শালাৎ’ অর্থাৎ সমবেত উপাসনায় মগ্ন তখন। ফলত তখনকার মতো বারোয়ারি পুজোর আয়োজনে জোড়াতালি লেগেছে ঠিকই, কিন্তু বিজয়ার কোলাকুলির পরেই পাশের মহল্লায় নির্মীয়মাণ পরের বারের উৎসবের মর্মে আসন্ন একটি পূজাকমিটি। আবার, আমার অভিজ্ঞতায় এমনও দেখেছি, ফ্রাঙ্কফুর্টে দু’টি পূজাপ্রতিষ্ঠান– একটি ঘরোয়া, আরেকটি কিছু জড়োয়া– বিনিময়ের ছন্দে পুজোর ক’দিন রাত্রি-দিন সানন্দ পরিশ্রমে বুঁদ হয়ে আছে। একটি দল, রাইন আর মাইন নদীর মোহনার মিলিত রূপকের কাছে উৎসর্গিত, দিগ্বিদিক থেকে নানাদেশি মানুষজন জড়ো করে আনার জন্য প্রায় প্রতিদিনই একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে কীরকম ব্যাপৃত।
আরও পড়ুন: আমার তো বাবা সেই ছয়ের দশকের রামকৃষ্ণ মিশনের পুজোর জন্যই মনকেমন করে
১৯৮৬-তে ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব-বইমেলায় (বিষয়: ভারতবর্ষ) তাদের এই প্রয়াস যেন তুঙ্গে সার্থকতায় পৌঁছে গিয়েছিল। কোনও এক নিখিল প্রবর্তনায় ওই সময়েই পূজার কালক্রম সাব্যস্ত হওয়ার দরুন অতিথি শিল্পীর অনটন পড়েনি। এত অনায়াসে স্বতঃপ্রণোদিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একের-পর-এক কবিতাপাঠ শোনা, মহাশ্বেতা দেবী কিংবা কবিতা সিংহের আড্ডায় পুরুষদের সিংহভাগ, এত পারমিতা অর্জন করার দিব্য সুযোগ পেয়ে অভ্যাগত দর্শকেরা এক সময় ভুলেই গিয়েছিলেন যে, তাঁদের স্বপ্নের শিল্পীদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নিতে হবে। হঠাৎ কে যেন হাওয়ায় রটিয়ে দিল, লেখকদের মধ্যে সেরা গায়ক বুদ্ধদেব গুহ প্রাঙ্গণে, প্রকাশ্যে গোপনতা অবলম্বন করে বসে আছেন। তাঁকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে হয়নি, তিনি নিজেই মঞ্চে উঠে এসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা গজল ও টপ্পা শোনালেন। মনে রাখতে হবে, স্থানীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য ‘মায়াবীর মতো জাদুবলে’ প্রাক্-প্রস্তুতি ছাড়াই জনায়কেয় দোভাষী তাৎজ্ঞণিক ভাষান্তরণের দুরূহ দায়িত্বে বৃত হয়েছিলেন। আসরের শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পালা এলে তাঁরা কোথায় অন্তর্হিত।
মনে রাখতে হবে, বইমেলার বিপুল কার্যক্রম সত্ত্বেও আমাদের দেশের সর্বাগ্রণী লেখকরা বারংবার পুজোর প্রাঙ্গণে ছুটে এসেছেন– অজ্ঞেয়, মুল্ক রাজ আনন্দ, রঘুবীর সহায়, নির্মল ভার্মা, অনন্তমূর্তি, দিলীপ চিত্রে, কমলা দাস এবং আরও অনেক দুর্মর ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে অনন্তমূর্তি-ই বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দে প্রাণিত বলে সবচেয়ে বেশি বাংলা-ঘেঁষা। নবমীর সন্ধ্যায় তিনি উত্তেজিত হয়ে আমাদের বললেন: ‘আমি যতটুকু বুঝেছি, মা দুর্গা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐহিক একটি শক্তি, যা মহিষাসুর অর্থাৎ ধর্মান্ধ মৌলবাদকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে সক্ষম। সেদিক থেকে দেখলে তিনিই আমাদের একমাত্র নব্য-ভারতীয় দেবতা।’ আমি মৃদু অনুনয়ের সুরে বলি: ‘কিন্তু দুর্গা ওরফে হৈমবতী উমার উৎসপ্রতিমা তো সেই কবেকার কোনোপনিষদ-এর যুগের, কী করে তাঁকে আমাদের সময়ে অত সহজে কালান্তরিত করি?’ তিনি তখন: ‘তা হতে পারে, কিন্তু এখন, এখনই, তাঁকে আমাদের এই দ্বিধাদীর্ণ ভুখণ্ডে বড় প্রয়োজন। এভাবেই কি মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের দেবী শরণাগত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য জন্ম নেননি?’ অনন্তমূর্তির এই বাঙালিয়ানা আমায় কেমন যেন আচ্ছন্ন করে তোলে। তিনি তখন আতিপাতি করে কাগজ কলম খুঁজছিলেন। হিন্দিভাষী কবি বিষ্ণু খারে আর আমি তাঁকে ধরে-ধরে নিয়ে যাই স্টেশনের সমীপবর্তী একটি বিস্ত্রোয়। কালো কফির গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে তিনি বিড়বিড় করতে-করতে কী যেন লিখতে থাকলেন। একসময় আমাদের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ ভ্রূকুঞ্চনে বললেন: ‘আমি এক কন্নড় অর্থাৎ আমার মাতৃভাষায় লিখে চলেছি একটি দুর্গাস্তোত্র।’ এখন আমার মনে হয়, বহির্বিশ্বে যাপিত দুর্গোৎসব এই মুহূর্তে শরৎকালে বাংলাভাষিত চৌহদ্দির তৃপ্ত আত্ম-উদ্যাপনের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিশ্রুতিময়, অন্তত সৃজনী ভারতীয়তার শর্তে।
আমি এখানে দেশ-বিদেশে তথাকথিত প্রবাসী-বাঙালির পুজোআচ্চার প্রতিবেদন দিতে বসিনি। শুধু অনুষঙ্গত এটুকু বলছি, ফ্রাঙ্কফুর্টের ওই সংগঠনের শিকড় ছিল বার্লিনে, যখন দুই জার্মানি সমীকৃত হয়নি। মাতৃমণ্ডপের বেদি কলকাতা থেকে আসা মাত্তরই শুল্ক সংস্থা ছেড়ে কথা বলত না; অথচ, কী আশ্চর্য, পুরোহিতের অভাব পড়লে পুব থেকে পশ্চিমে এসে দুর্গাপূজায় পৌরোহিত্যের সৌজন্যে সংস্কৃতজ্ঞ যাকজ-ঋত্বিকদের জন্য সত্বর ভিসা জুগিয়ে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি কট্টর ছদ্ম-মার্কসীয় পূর্বাঞ্চল। এই চ্যালেঞ্জসঞ্চারী টানাপোড়েনের মধ্য থেকেই নির্গত হলেন প্রাচীন এবং নবীন ভারতের মধ্যে সেতুসঞ্চারী আচার্য গৌরীশ্বর ভট্টাচার্যের মতো কয়েকজন দিশারী মনীষা, যাঁরা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন দুর্গার্চনা কোনও স্বদেশিক পার্বণ নয়, বরং তার ঝোঁক সারা জগতে, এমনকী আজকের আত্মবিস্মৃত গৌড়বঙ্গের নবায়নের পক্ষেও যা একান্ত জরুরি। এঁদেরই সাধনা ও চর্যার ফলে বার্লিনে জন্ম নিল ‘ভারত মজলিশ’, যার অন্যতম অবদান কিনা পূজার দিনরাত্রি জুড়ে সর্বভারতীয় জনসমাগমের ব্যাকুলতা। শুধু ভারতীয়রাই-বা কেন, জার্মানির আবালবৃদ্ধবনিতা স্নিগ্ধ কৌতূহলে মণ্ডপে এসে আঁচল ভরে ভোগ নিয়ে যায়। একটি অনতিউনিশ তরুণকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম: ‘এদেশে তো গ্রিক, তুর্কি তথা কত নানা জাতির পূজাপার্বণ হয়, সেখানে তোমরা বড়-একটা যাও না কেন, যেমন এখানে এসে মজা করো’ তার উত্তরে সে আমায় ভারি সুন্দর একটি কথা বলেছিল: ‘আপনি বুঝি জানেন না, আমাদের এই দেশেই একদা ভারতবিদ্যা বা ইন্ডোলজি জন্ম নিয়েছিল?’
বার্লিনের ছাঁচেই ক্যোল্ন-স্টুটগার্ট-হামবুর্গ এবং আরও কত-না শহরে আজও যাপিত হয় দুর্গতিনাশিনীর আবির্ভাবের অর্চনা, সংলগ্ন কিয়স্কে শোভা পায় এক একটি ছত্রাকপ্রতিম পূজাসংখ্যা, হঠাৎই-বা মঞ্চায়িত হয় ‘ভানুসিংহের পদাবলী’। আমি কিন্তু ভিতরে ঢুকি না। গর-ঠিকানিয়ার ভূমিকায় অটুট থাকি। কেননা আমার শিরায়-শিরায় যে মিশে রয়ে গিয়েছে আমার সেই কিশোরদশা, সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত সেই লিলাপরিসর, যার নাম রিখিয়া, যেখানে আমার পিতামহ, আমার যখন বড়জোর চোদ্দো বছর বয়স, আমার কাঁধে গোটা বাড়ির দুর্গাপূজার ভার ন্যস্ত করে দিয়ে অনির্দেশ্য ইথারজগতে প্রস্থানোদ্যত। সেই দুর্গোৎসব কোনও পারিবারিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল পড়শিপল্লির দেহাতি সাঁওতালিদের মজ্জায়-মজ্জায়, পূজার পরতে-পরতে তাঁদেরই কৌম-অংশগ্রহণের করুণায় দেখতে পেয়েছি, পুরোহিতকে একঝটকায় সরিয়ে দিয়ে মা দুর্গার নথ নেড়ে দিয়ে আদিবাসী এক কন্যাকুমারিকার অপূর্ণ কামনার উদ্ঘাটন, এসব দেখার পর কলকাতা হোক আর ক্যোল্নই-হোক, কোনও বারোয়ারি পূজায় আমার যেন মন সরে না।
তবু যাঁরা কথায়-কথায় পরবাসী বাঙালির বাৎসরিক মাতৃচর্যায় বিরূপাক্ষ হয়ে ওঠেন, তাঁদের আমি দু’-চক্ষে দেখতে পারি না। আমি এক ধূর্ত ভ্রমণবিলাসীকে জানি, যিনি সারা চরাচর ঘুরে এখানে-ওখানে সংঘটিত দুর্গাপূজার সরেজমিন ময়নাতদন্ত করে বেড়ান! মরুবিধুর আরিজোনা অঞ্চলে অমাবস্যা তিথিতে একদিনের মধ্যেই মার্কিনি-বাঙালিদের সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-বিজয়া চুকিয়ে দেওয়ার দৃশ্য দেখে এসে থরথর করে কাঁপছিলেন তিনি। ফুটনোটে শেষে সংযোজন করে দিলেন: ‘দুঃখের কথা, প্রবাসী বাঙালিরা জানে না, রাতের দিকে অষ্টমী থেকে মহানবমীর বাঁকেই সন্ধিপূজার লগ্ন; কিন্তু, ভাড়াটে পুরোহিতকে ঘুষ দিয়ে বিকেল-বিকেল সেই পাট চুকিয়ে ওরা কোথায় যে চলে যায়!’
২০১৫ সালের ১৮ অক্টোবরের ‘রোববার’-এর ‘প্রবাস পুজো’ সংখ্যাটি থেকে এ লেখাটি পুনর্মুদ্রিত
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved