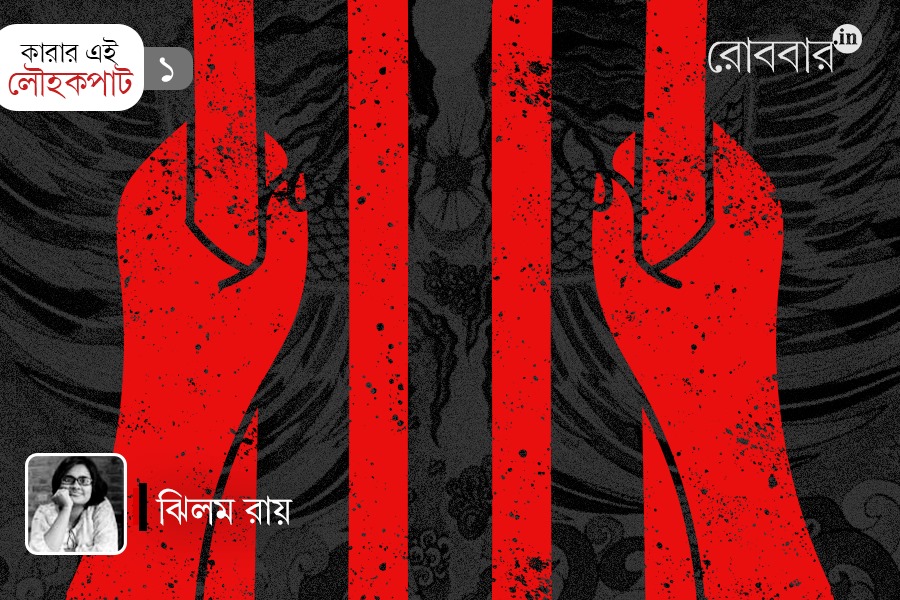
রাজবন্দিদের অনাত্মীয় করে তোলার চক্রান্তকে ব্যর্থ করতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে হাতে হাত ধরে মর্যাদাপূর্ণ যাপনের দাবিতে অনশন করেছিলেন ননীবালা, দুকড়িবালা। সেই লড়াইয়ের উত্তরাধিকার বহন করেই ১৯৩৯-এ বাংলার বুকে রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন অমিয়া, লতিকা, গীতা, প্রতিভা। জীবন দিয়ে জাহির করেছিলেন বন্দি কমরেডদের প্রতি আত্মীয়তা। সেই ঐতিহ্য বুকে নিয়েই উত্তাল সত্তরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্বরূপ উন্মোচন করে মিনাক্ষী, রাজশ্রী, কৃষ্ণা, কল্পনা, পিয়াসা, কুনি, জয়ারা রেখে যান তাঁদের বন্ধুত্বের বয়ান। সেই লড়াইয়ের আগুন বুকে নিয়েই শত অবমাননা সহ্য করেও টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যান জয়িতা দাস, কল্পনা মাইতি, ঠাকুরমণি মুর্মু, শোভা মুন্ডা, জ্যোতি জাগতপ, গুলফিশা ফাতিমা, শীলা মারান্ডি, বেল্লালা পদ্মারা।

আমাকে ঘিরে রাখা দেওয়াল
এই যে চার দেওয়াল
কবে থেকে নিঃশব্দে
দাঁড়িয়ে আছে…
তিহার জেল থেকে গুলফিশা ফাতিমার কবিতা। অনুবাদ: স্বপ্না
চার দেওয়াল। জন্ম থেকেই মেয়েদের জীবন একভাবে কারাবাসের প্রস্তুতি। কী বলবে, কী পড়বে, কোথায় যাবে, কখন যাবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে– সবই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তাই ছোট থেকে বেড়ে ওঠা আসলে এই চার দেওয়ালের সঙ্গে লড়াই-সমঝোতা করে। বিভিন্ন পরতে পরতে টেনে দেওয়া লক্ষণরেখার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে। বারবার বলে দেওয়া হয় তার নিজস্ব মত থাকতে নেই, নিজস্ব পরিচয় থাকতে নেই, নিজস্ব সত্তা থাকতে নেই। থাকতে হবে বাধ্য, শান্ত, অদৃশ্য হয়ে। মেনে নিয়ে, মানিয়ে নিয়ে। কিন্তু যে মেয়েরা সেই নিঃশব্দে চার দেওয়ালের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ধৈর্য্যর বাঁধ ভেঙে একদিন সশব্দে ফেটে পরে চৌকাঠ পেরোয়? এই পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান জাহির করে, দিন বদলের স্বপ্ন চোখে জোট বাঁধে? ঘরে, বাইরে, কর্মক্ষেত্রে, সংগঠনে, আড্ডায়, মিটিংয়ে, মিছিলে প্রতিটা ব্যাঙ্কে লড়াই চালিয়ে যারা জাহির করে নিজেদের রাজনৈতিক সত্তাকে? প্রশ্নের মুখে ফেলে পরিবেশ, গণপরিসরে, রাজনৈতিক পরিসরের লিঙ্গায়িত কাঠামোকে? যে সমাজে মেয়েদের ওঠা-বসা, শ্রম, প্রেম, যাপন– সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেখানে কারা ভাঙার স্বপ্ন দেখাই রাজদ্রোহিতা। বিপজ্জনক, নিষিদ্ধ, অসম্ভব। এই সমস্ত নিয়মকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে, এই সমস্ত পাহাড় ডিঙিয়ে যখন মেয়েরা ক্ষমতার আস্ফালনের বিরুদ্ধে, এই শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ডেটে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে এই কারা ভাঙতে উদ্যত হয়েছে– তখনই রাষ্ট্রযন্ত্র সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছে যে সে মেয়ে। নিকেশ করতে চেয়েছে বহু সংগ্রামে তিলতিল করে বেড়ে ওঠা স্পর্ধাকে। তাঁদের বাতিল করতে। তাঁদের ‘বিপজ্জনক’ দাগিয়ে দিতে।
এই বিপজ্জনক দাগিয়ে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনৈতিক বন্দিদের কাজের, ভাবনার, আদর্শের যে ভিত, যা এই শোষণ ব্যবস্থার স্থিতাবস্থায় আঘাত হানে, সেই রাজনৈতিক সত্তার অপরাধীকরণ করা। কারণ সেই সত্তা আসলে যে এই সমাজব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার তাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় জেলবন্দির সেই সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করা। গারদের ওপারে গেলেই তুমি তাই আর মানুষ নও। তুমি শুধুই একটি কেস নং, একটি সেল নং। বিচার হোক না হোক গারদের ওপারে পৌঁছলেই তুমি অপরাধী। এই অপরাধীকরণ জনমানসে নিয়ে যেতেও তাই প্রয়োজন– কারার ওপারের জীবনকে সাধারণ জনমানসের কাছে এক রহস্য করে রাখা। সাধারণ মানুষের থেকে এই বিপজ্জনক মেয়েদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা। তাদের অনাত্মীয় করে রাখা। যা কিছু একজন মানুষকে মানুষ করে তোলে, যা কিছু কোনও ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি করে তোলে– সেই সমস্ত কিছুকে মুছে দেওয়া, সেই সমস্ত কিছুকে একটু একটু করে মেরে দেওয়া। জেল পরিচালনার একদম মূলেই তাই থাকে বন্দিদের জেল-যাপনকে যথাসম্ভব অমর্যাদাকর করে রাখা। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে অসম্মানজনক, দুর্বিসহ করে তোলা। রাজবন্দি মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অপরাধ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় কারণ তাঁদের রাজনৈতিক সত্তা রাষ্ট্রের পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রকেও উন্মোচিত করে। উন্মোচিত করে এই ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রকে। তাই জেলের মধ্যেও তাঁদের শবক শেখানো চলতে থাকে। চলতে থাকে হেফাজতে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন। একই সঙ্গে চলতে থাকে জেলের বাইরে তাঁদের চরিত্র হনন। সংবাদমাধ্যম জুড়ে চলতে থাকে তাঁদের নিয়ে নানা রসালো গল্প, তাঁদের নিয়ে কুৎসা। যাতে তাঁদের এই দৈনন্দিন অবমাননার কথা, এই নিপীড়নের কথা আমাদের সুরক্ষিত নাগরিক জীবনে দাগ না কাটে। যাতে গারদের ওপারের জীবন আমাদের থেকে অনেক দূরের মনে হয়। যাতে গারদের ওপারের মানুষদের টিকে থাকার সংগ্রামে আমাদের কিছু যায় আসে না। যাতে গারদের ওপারের মানুষেরা আমাদের অনাত্মীয় হয়েই থাকে।

তবে মেয়েদের যে গোটা জীবনই আসলে কারাবাসের অনুশীলনে কাটে। জীবন জুড়েই চলতে থাকে কারাভাঙার লড়াই। যাঁদের এমনিতেই সমাজ শুধু স্বীকৃতি দেয় তার পারিবারিক কিংবা বৈবাহিক পরিচয়, যাঁদের সমাজ কখনওই স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে নিজেকে প্রকাশ করতে শেখায় না, যাঁদের আত্মীয়তাও সমাজ নিয়ন্ত্রিত– জেল-জীবন একদিক দিয়ে যেমন তাঁদের স্বজনহারা করে তোলে; তেমনই এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-স্বীকৃত, এই সমাজ-নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের বাইরে নতুন কোনও নিজেকে খোঁজা, নতুন করে আত্মীয়তা গড়ার এক সুযোগও করে দেয়। জেল খাটার অপরাধে তাঁর পরিবার-পরিজন ত্যাগ করলেও, জেল-যাপন অনেক সময়ই নতুন বন্ধুত্ব, নতুন যৌথতার সম্ভাবনা তৈরি করে। যে বন্ধুত্ব, যে যৌথতা এই বিচারব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই এক নতুন প্রতিরোধের জন্ম দেয়। যে প্রতিরোধে মেয়েরা একজোট হয়ে আবার লেখাপড়ার ক্লাস শুরু করে; যে প্রতিরোধে ব্যারাকে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালন করার তোড়জোড় চলতে থাকে; যে প্রতিরোধে এক কমরেডকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার ডাক এলে অন্যরা নিজেদের শাড়ি ধার দিয়ে পুলিশি নির্যাতন রুখতে মোটা জামার বর্ম তৈরি করে দেন; যে প্রতিরোধে এক বন্দির অমর্যাদার প্রতিবাদে বাকি বন্দিরাও অনশন শুরু করে; যে প্রতিরোধ ঘুচিয়ে দেয় গারদের এপার-ওপারের দূরত্ব, উঁচু প্রাচীর ভেদ করে গারদের ওপারের মানুষদের মুক্তির ডাকে মুখর হয় এপারেও।
এই আত্মীয়তা, এই সংহতি, বন্ধুত্বের রাজনীতিকেই ভয় করে শাসক। তাই জনমানসে কারাগার, কারাজীবনকে বরাবর এক অপরাধ সম্পৃক্ত বিপজ্জনক পরিসর হিসেবে চিহ্নিত করতে লাগে। বন্দিদের অপরাধ প্রমাণের আগেই তাঁদের অপরাধী করে তুলতে লাগে, বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই সাজা চলতে থাকে। মেয়েদের রাজনৈতিক সত্তাকে অস্বীকার করলেও, মেয়েদের রাজদ্রোহিতা তাই শাস্তিযোগ্য। রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাথে সাথেই, এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ‘ভালো মেয়ে’ হয়ে ওঠার গাইডলাইনকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলাও সমান অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। তবু, রাষ্ট্রের এই নীল নকশাকে প্রতিহত করেই আমাদের স্মৃতি-বিস্মৃতি ভেদ করে এই বিপজ্জনক, বেপরোয়া, অবাধ্য মেয়েরা নিজেদের কথা বলে গেছে। বলে গেছে কারাযাপনের কথা, রেখে গেছে তাঁদের শরীরে-মননে বিভিন্ন ক্ষতের বয়ান। আমাদের পরিচয় করিয়ে গেছে অন্য অসংখ্য নামহীন, পরিচয়হীন হারিয়ে যাওয়া বাতিল মেয়েদের সঙ্গে। সজোরে প্রশ্ন করেছে: যে রাষ্ট্র, যে সমাজ মেয়েদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা, মুক্ত আকাশে শ্বাস নেওয়াকেই অপরাধ ঘোষণা করে গেছে; যাঁদের প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত নানা ভাবে নানা কারণে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়; যে রাষ্ট্র জাত, ধর্ম, রাজনৈতিক অনুসারে কিছু মানুষের অস্তিত্বকেই বেআইনি করে দেয়; যে রাষ্ট্র প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে ‘সন্ত্রাসবাদের’ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে– সেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় গারদের ওপারের জীবন কী সত্যিই আমাদের নাগরিক জীবনের থেকে খুব আলাদা?

রাজবন্দিদের এই অনাত্মীয় করে তোলার চক্রান্তকে ব্যর্থ করতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে হাতে হাত ধরে মর্যাদাপূর্ণ যাপনের দাবিতে অনশন করেছিলেন ননীবালা, দুকড়িবালা। সেই লড়াইয়ের উত্তরাধিকার বহন করেই ১৯৩৯-এ বাংলার বুকে রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন অমিয়া, লতিকা, গীতা, প্রতিভা। জীবন দিয়ে জাহির করেছিলেন বন্দি কমরেডদের প্রতি আত্মীয়তা। সেই ঐতিহ্য বুকে নিয়েই উত্তাল সত্তরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্বরূপ উন্মোচন করে মিনাক্ষী, রাজশ্রী, কৃষ্ণা, কল্পনা, পিয়াসা, কুনি, জয়ারা রেখে যান তাঁদের বন্ধুত্বের বয়ান। সেই লড়াইয়ের আগুন বুকে নিয়েই শত অবমাননা সহ্য করেও টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যান জয়িতা দাস, কল্পনা মাইতি, ঠাকুরমণি মুর্মু, শোভা মুন্ডা, জ্যোতি জাগতপ, গুলফিশা ফাতিমা, শীলা মারান্ডি, বেল্লালা পদ্মারা। শত নিপীড়ন সহ্য করেও ছবি আঁকে, কবিতা লেখে গুলফিশা। জেলখানার উঁচু পাঁচিল টপকে সেই কবিতা উচ্চারিত হয় দেশজুড়ে শত মানুষের কণ্ঠে। এই বহু প্রাজন্মিক লড়াইয়ের আগুনেই শানিত হতে থাকে অন্য আত্মীয়তার কথন। যে আত্মীয়তাই আগলে রাখে কারাবন্দিদের মর্যাদাকে, যত্নে রাখে তাঁদের মনুষ্যত্বকে, এবং সর্বোপরি, বাঁচিয়ে রাখে গারদের দুই পারেরই কারা ভাঙার স্বপ্নকে।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
