
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আটটি স্তম্ভের ওপরেই ভারতীয় বিদ্যাচর্চার অন্তরযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তার প্রধান কারণ বিদ্যার্থীর গ্রহণযোগ্যতা তার মানসিক শারীরিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে। আত্মবিশ্বাস, জীবন আদর্শ, মূল্যবোধ ভারতীয় যে কোনও শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন ধরা যাক, একজন স্থপতি কেমন হবেন? প্রাচীন পুস্তক অনুসারে তাঁর প্রথম লক্ষণ হবে তিনি সৎ, শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল, দয়াবান, হিংসা-নিন্দা থেকে মুক্ত, বিনয়ী ও দয়ালু। তিনি সর্বদা সুখী এবং সংযমী।

২.
ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি– একটি ধারণা
প্রথম ভাগ
ব্রিটিশরা ভারতের মাটিতে নতুন শিক্ষাব্যব্যবস্থা শুরু করার আগে ভারতীয়রা কি অশিক্ষিত ছিল?
এই প্রশ্ন অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে কি সত্যিই সঠিক ধারণা আছে যে, কীরকম ছিল, এবং কতকগুলো পাঠশালা ও বিদ্যালয় চালু ছিল, কী শেখানো হত সেখানে? কারণ আমরা ভাবি যে, ভারতের কিছু সংখ্যক মানুষরাই শিক্ষিত ছিল। আর বাকি ভারতীয়রা ছিল অশিক্ষার অন্ধকারে। আরেকটি সাধারণ ধারণা যে, উচ্চবর্ণের মানুষদেরই শুধু এই শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার ছিল এবং বাকিরা– নারীরাও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। পাঠশালাগুলো যে শিক্ষার বিশেষ কেন্দ্র ছিল, সে ধারণার বদলে আমরা টোল, গুরুকুল এবং পাঠশালাগুলোকে সামাজিক নিপীড়নের একটা মাধ্যম মনে করে এসেছি। এই সমস্ত কারণে ব্রিটিশদের আনা কলোনিয়াল বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষার থেকে বেশি আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। এবং ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখতে তারা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ভারতীয়দের চোখে অবিশ্বাসযোগ্য ও দুর্বল বলে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। একদিকে তারা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ‘অন্ধকার’ আর ‘কুসংস্কারে আচ্ছন্ন’ ও ব্রিটিশ কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘সভ্যতার আলো’ বলে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল।
আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে খানিক ধারণা করব। কী কী পদ্ধতিতে এই শিক্ষা প্রদান করা হত? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ভারতীয় শিক্ষা দুটো ভাগে বিভক্ত। একটি ব্যবহারিক, অপরটি ব্রহ্মবিদ্যা।

কিন্তু যদি সমগ্র ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিকে একত্রিত করে দেখা হয়, তাহলে দু’টি বিষয় যা দুই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা হল– ১. গুরু-শিষ্য পরম্পরা ২.অন্তরযোগ। ব্যবহারিক ও ব্রহ্মবিদ্যার বুনিয়াদ গুরু-শিষ্য পরম্পরা ও অন্তরযোগের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিল।
গুরু-শিষ্য পরম্পরা
আমাদের পারম্পারিক শিক্ষা গুঢ় ও সময়সাপেক্ষ। তা একেবারে বুঝে নেওয়ার বিষয় নয়। এই বিদ্যাকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে গুরু উপদেশ অনুযায়ী নিয়মিত অনুশীলন করলে তবেই বিদ্যার্জন সম্ভবপর হবে।
বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষা-জ্ঞান মৌখিকভাবে গুরু-শিষ্যকে প্রদান করে থাকেন। গুরুর সঙ্গে সরাসরি আদানপ্রদান পড়ুয়ার মধ্যে এক গভীর প্রভাব ফেলে, যা তার পাঠ্য বিষয়টিকে একটি অনুভবের মাত্রায় নিয়ে যায়, যা একটি বই পড়ে বা একটি ভিডিও বা রিল দেখে সম্ভব নয়। গুরু-শিষ্য পরম্পরার ভিত্তিতে যেভাবে একটি বিদ্যাচর্চার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব, তা নকল বা অনুকরণ করে সে গভীরতায় আসা কোনও রকমেই সম্ভবপর নয়।
তাই ভারতীয় বিদ্যাচর্চা পুরোপুরি গুরু-শিষ্য কেন্দ্রিক। যার নিয়ম হল গুরুকে একাগ্রতার সঙ্গে শোনা, পূর্ণভাবে সমর্পণ, গুরু উপদেশে পূর্ণ বিশ্বাস, আর গুরুদত্ত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা। এই ভাবেই ধীরে ধীরে বিদ্যার্থী মনের চেতন ও অবচেতন স্তরগুলোকে অতিক্রম করে বিদ্যার যথার্থ রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়। গুরুর মাধ্যমে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান বাস্তবে মূর্ত হয়। তাই আধুনিক সময়ে যখন সব কিছুই লিখিত বা অডিও-ভিডিও মাধ্যমে নথিবদ্ধ করা সম্ভব, এখনও পারম্পারিক বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বা গুরুকুল/পাঠশালাগুলো মৌখিক গুরু-শিষ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চার পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করে। এই পদ্ধতিতে পাঠাভ্যাস হয়ে থাকে। এর মূল কারণ হল একজন সম্পন্ন গুরুর বাকশক্তি, বিদ্যাপ্রদান শক্তি, বিদ্যার্থীর বিদ্যাশক্তিকে পুরোপুরি অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অপরিহার্য।
অন্তরযোগ
আমাদের প্রাচীন পুস্তক তৈত্তরীয় উপনিষদ অথবা পতঞ্জলি যোগসূত্র– মন-বুদ্ধি-চিত্তকে পরিণত ও পরিপক্ব করার একটি পূর্ণ প্রক্রিয়া। যে কোনও ভারতীয় বিদ্যাই– তা ব্যবহারিক হোক বা ব্রহ্মবিদ্যা এই অন্তরযোগের ওপরে আধারিত।
পতঞ্জলি যোগসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সাধনাপাদে অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আটটি স্তম্ভের ওপরেই ভারতীয় বিদ্যাচর্চার অন্তরযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তার প্রধান কারণ বিদ্যার্থীর গ্রহণযোগ্যতা তার মানসিক শারীরিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে। আত্মবিশ্বাস, জীবন আদর্শ, মূল্যবোধ ভারতীয় যে কোনও শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন ধরা যাক, একজন স্থপতি কেমন হবেন? প্রাচীন পুস্তক অনুসারে তাঁর প্রথম লক্ষণ হবে তিনি সৎ, শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল, দয়াবান, হিংসা-নিন্দা থেকে মুক্ত, বিনয়ী ও দয়ালু। তিনি সর্বদা সুখী এবং সংযমী। সাধারণ বেশভূষা, ধৈর্য্যবান, নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করেন, চিত্তশুদ্ধ, জীবন বোধ ও জ্ঞান, প্রকৃতি, মাটি, আবহাওয়া, পরিবেশ জ্ঞান, রক্ষী ও প্রাণীদের প্রতি সম্মান ও তাদের তাৎপর্য জ্ঞান। জ্যোতিষ ও বাস্তুজ্ঞান। এইসব মূল্যবোধগুলিই অষ্টাঙ্গের ‘যম’ অঙ্গে রয়েছে।
অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য়াপরিগ্রহা যমাঃ। দ্বিতীয় অধ্যায় ৩০। যোগসূত্র
অহিংসা সত্য অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহকে যম বলে।
পূর্ণ যোগীর স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। আত্মা পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই মিলনের সৃষ্টি। চুরি করা যেমন অসৎ কাজ, ঠিক সেরকমই পরিগ্রহ, অপরের ওপর নির্ভরশীল বা গ্রহণ করাটাও আমাদের দুর্বল করে দেয়।
জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম। ৩১। দ্বিতীয় অধ্যায় । যোগসূত্র
এই সংযম জাতি দেশ কাল সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বজনের মহাব্রত।
আবার ‘নিয়মে’ বলা হচ্ছে
শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানাদি নিয়মাঃ। ৩২। দ্বিতীয় অধ্যায়। যোগসূত্র
বাহ্য ও ভেতরের শৌচ, সর্ব সন্তোষ, অভঙ্গ তপস্যা, স্বাধ্যায় বা আত্মতত্ত্বকে চিন্তা করা এবং ঈশ্বর প্রণিধান বা পূর্ণ সমর্পণ এই প্রত্যেকটি নিয়মই শিক্ষার অন্তর্গত।
যোগের এই অষ্টাঙ্গ অনুসরণ করলে চিত্তশুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের আলো প্রকাশ পায়। যা যে কোনও বিষয়ে চিকিৎসা বা বিজ্ঞান, নীতি, ন্যায়, মার্শাল আর্ট বা কলা স্থাপত্য শিল্প ও সংগীতে পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা আনতে হলে অন্তরযোগ অপরিহার্য।
ভারতীয় অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা বা কোনও বিষয়ের আভাস অনুমানের তর্ক-বিতর্ক নয়, ডিগ্রি বা সময়বদ্ধ গতানুগতিক শিক্ষা নয়, একজন মানুষ হিসেবে তার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করার এক প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া।
পরম পুরুষ
পরম পুরুষ বাউলের ভাষায় বলা হচ্ছে মনের মানুষ। পরম পুরুষ তিনি তাঁকে ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে হাজার মস্তক, হাজার চক্ষু, হাজার পদ, বিশ্বকে জড়িয়ে আছেন যিনি। দশ আঙুল প্রস্থে এই মানুষের এই সার। যিনি পূর্ব বা উত্তরকালে সমান। চিরন্তন সনাতন, গোলকের অধিপতি। তিনি অন্নময় কোষে প্রবেশ করে আকৃতি ধারণ করেন। সব চরাচর তার এক চতুর্থাংশ। বাকি তিন চতুর্থাংশ তিনি অব্যক্ত। অবাঙমানসগোচর। বাউলের শিক্ষা আলোচনায় এই বিষয়ে আরও গভীরে যাওয়ার প্রচেষ্টা করব।
ব্যবহারিক বিদ্যা
ব্যবহারিক শিক্ষা যেমন গণিত, ভাষা শিক্ষা, লেখা ও পড়া, হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি। এই পাঠ্যস্থানগুলো আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামের বাচ্চারা কয়েক ঘণ্টার জন্য আসত। যা টোল বা পাঠশালা নামে জানা যেত। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই টোল বা পাঠশালা ছিল। আমার গুরু সনাতন দাস বাউল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা টোলেই সম্পন্ন করেছেন।
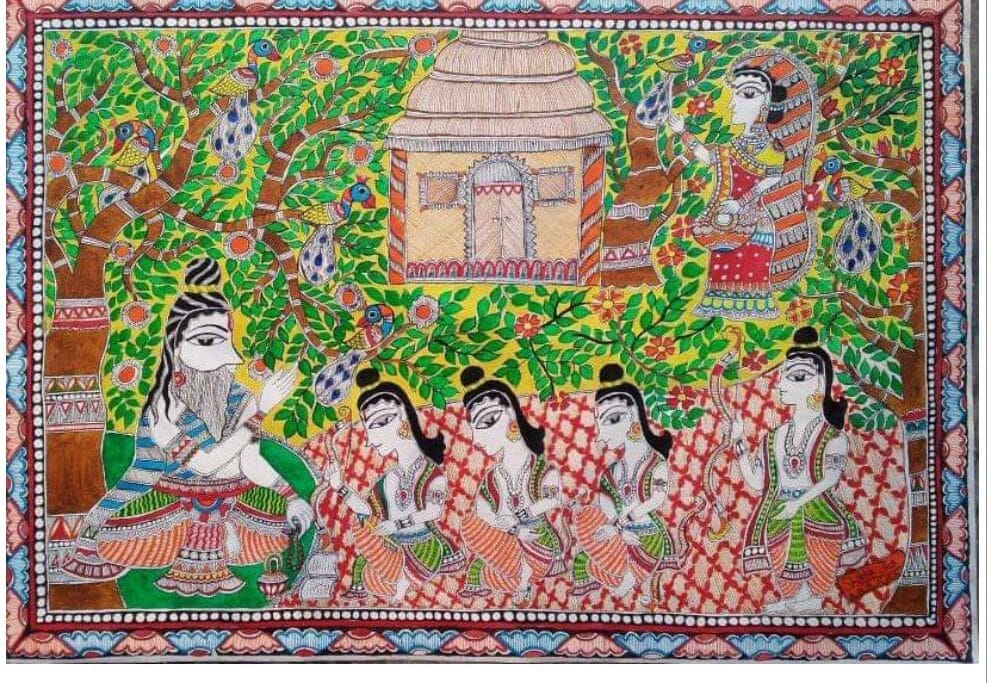
টোলে প্রাথমিক শিক্ষার পরে ছাত্ররা তাদের পাঠ্য বিষয় নিয়ে বহু বছর চর্চা করতেন। এবং যিনি গুরু তিনি সেই বিষয়টিই শেখাতেন যে-বিষয়ে তিনি চর্চা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই পড়ুয়ারা তাঁদের গুরু গৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। এই পদ্ধতিতে শিষ্যকে বহু বছর গুরুর কাছে শিক্ষণীয় বিষয়কে অধ্যয়ন করতে হত শুধুমাত্র শিক্ষা নয় তারা গুরু সেবার মাধ্যমে গুরুর আচার ও নিয়ম আচরণও শিক্ষা করতেন।
ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৪টি বিদ্যাস্থান ও ৬৪টি কলায় বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও অনেক বিস্তৃত শিক্ষা পদ্ধতি ছিল। গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে এই শিক্ষাপ্রদান করা হত। গুরু-শিষ্য পরম্পরার একটি প্রাতিষ্ঠানিক গঠনও ছিল। যেমন ঘরানা, সম্প্রদায় ও বাণী। কলা বিদ্যা, স্থাপত্য শিল্পচর্চার ও ধাতু শিল্পের জন্য বিভিন্ন সমবায়িকা সংঘ ছিল, যা কারখানা, স্থপতি, শিল্পকুডাম নামে পরিচিত ছিল। এখানে বিদ্যার্থী কাজ শিখে তৎক্ষণাৎ উৎপাদন করতেও সমর্থ ছিলেন।
ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠশালা, টোল, গুরুকুল, আশ্রম, বিহার,পীঠ ও মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত, তাদের পাঠ্যচর্চার বিষয় অনুযায়ী। প্রাচীন মন্দিরগুলিও এক একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। পরের ভাগে, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব।
ব্রহ্মবিদ্যা
মান্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্মবিদ্যা দুই প্রকার পরা এবং অপরা। অপরা হল ঋগ্বেদ, সামবেদ,অথর্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ। পরা বিদ্যা হল যা দিয়ে ব্রহ্মকে অধিকার করা যায়। এই ব্রহ্মবিদ্যায় আগ্রহী ব্যক্তি চার প্রকার। আর্ত অথার্থী ভক্ত ও জিজ্ঞাসু। যে আর্ত অর্থাৎ বিপদে পড়ে পরম পুরুষকে চিন্তা করে বিপদে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে। অথার্থী অর্থাৎ যার কোনও বিপদ ঘটেনি, কিন্তু সে কোনও প্রকার আশাকে পরিপূর্ণ করার জন্য পরম পুরুষের চিন্তা করেন। ভক্ত আরও উচ্চস্তরের, তার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুগ্রহে ও ভালোবাসায় পরমপুরুষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। জিজ্ঞাসু সে, পরম পুরুষ কে, জানতে ইচ্ছা করে।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
