
দেবীদের থাকে স্ববিরোধ। আশাপূর্ণা দেবীর একটি গল্পে পড়ি, বর্ষিয়সী স্বর্ণপ্রভা শৈশবে তাঁর ঠাকুমার কাছে শেখা তুলসীর প্রণামমন্ত্র শিখিয়েছেন নাতনিকে। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর আধুনিক পুত্রবধূ, বলছেন ‘নাতনিকে একটি কুসংস্কারের ডিপো বানাতে চাইছেন’, ‘আর ওকে এইরকম গাঁইয়ামি শেখাবেন না।’ কিন্তু তারপরেই দেখা যাচ্ছে, পুত্রবধূ নিজে রাখছেন সন্তোষী মা’র ব্রত– প্রসাদী ছোলা-গুড় কলাপাতায় মুড়ে গরু খুঁজতে বেরচ্ছেন, কারণ গরুর মুখে প্রসাদ দিয়ে তবে ব্রতভঙ্গের নিয়ম। অর্থাৎ, সে সংস্কারকে ঘৃণা করছেন তিনি, নিজেও সেই একই সংস্কারের দাস– শুধু সেটুকু তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

দেবীপক্ষে স্মৃতির সমুদ্র থেকে উঠে আসেন সার বাঁধা দেবীমূর্তি। কারও মুখ অবগুণ্ঠিত, কেউ রৌদ্রকরোজ্জ্বল। কারও হাতে কঙ্কন, কারও হাতা-খুন্তি। কারও পুষ্পভার, কেউ বা কীটদষ্ট মলিনবসনা। কলমবনবাসিনী এক দেবীর প্রতি অর্ঘ্য রইল আজ। আশাপূর্ণা দেবী।
প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষা ছিল না। যে জীবন কাটিয়েছেন, তা মূলত অন্তঃপুরের– তার মধ্যে দুঃসাহসিক, বৈপ্লবিক ছিল না কিছুই। বিপ্লব তবু ঘটিয়েছেন তিনি, নিজের লেখায়। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে উঠে এসেছে একের পর এক সমাজচিত্র, উঠে এসেছেন দৃপ্তকণ্ঠের নারীরা। অন্তঃপুরের সাতকাহনকেই উপাদান করে নিয়েছেন তিনি, আর সেই মাটি ছেনেই গড়েছেন একের পর এক আশ্চর্য প্রতিমা।

মনে আছে, স্কুলে ‘দোরোখা একাদশী’ বলে একটি কবিতা পাঠ্য ছিল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর। তাতে ছিল বাল্যবিধবার যন্ত্রণার কথা। সেই কবিতা প্রসঙ্গেই সে যুগের মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট-সংগ্রাম বোঝাতে গিয়ে উমাদিদিমণি বলেছিলেন ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র কথা। পড়তে গিয়ে দেখলাম, এ পুরো অন্য ভুবন। বাংলা সাহিত্যের অন্য অনেক মণিমুক্তোর সঙ্গে তার অনেক আগেই পরিচয় ঘটে গিয়েছে– কিন্তু বুঝলাম, আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র ভূমিকাতেই যেমন আশাপূর্ণা দেবী সেকথা লিখেছেন, ‘রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙা-গড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।’
সত্যবতী তেজস্বিনী মেয়ে। ব্রীড়াবনতা নয় আদৌ। সে মাছ ধরতে চায়, ত্রিপদীতে কবিতা লিখতে পারে। পিতা ছাড়া পিত্রালয়েও কারও কাছে প্রশ্রয় পায়নি, তার এইসব আগ্রহ বেহায়াপনা হিসেবেই দেখেছেন তার জেঠি-পিসি-মামিমারা। শ্বশুরালয়ে গিয়েও তার সংগ্রাম চলতে থাকে– কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে। সমাজের কদর্য পঙ্কগর্ভ থেকে নিজেকে আর নিজের আশপাশের মানুষগুলিকে তুলে আনার সেই লড়াইতে সঙ্গী হয়তো পায় না কাউকে। তবু সত্যবতীর চেষ্টায় স্বামী-পুত্র-কন্যারা কিছু কিছু নিগড় ভাঙতে শেখে, কোথাও কোথাও আটকেও যায় ফের। পল্লিজীবন ছেড়ে কলকাতানিবাসী হয় তারা, সরকারি চাকরিতে যোগ দেয় সত্যবতীর স্বামী, সন্তানরা ভর্তি হয় ভালো স্কুলে। সত্যবতী ভাবে, ‘স্বাধীনতার সুখ মানে তাহলে এই? মাথার ওপর সর্বদা উদ্যত খাঁড়ার বদলে অনেক উঁচুতে আলো– ঝকঝকে আকাশ থাকা?’

এবং তারপরেও শেষরক্ষা হয় না। পড়াশোনায় ইতি টেনে জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয় সত্যবতীদুহিতা সুবর্ণলতা। প্রতিবাদে গৃহত্যাগিনী হয় সত্যবতী। তার লড়াইয়ের ব্যাটন উঠে যায় সুবর্ণলতার হাতে। বধূ হয়ে যেখানে আসে, সেখানে বৃহৎ সংসার, যাদের টাকা আছে কিন্তু রুচিবোধ নেই, সেখানে একটা বারান্দা, একফালি খোলা ছাদের জন্য সুবর্ণলতা আজন্মের তৃষ্ণা বহন করে চলে। তিল তিল করে সমাজ পাল্টায়। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষ্যে ‘সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনীর মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।’
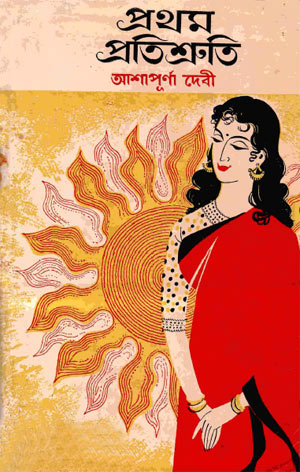
পরবর্তী প্রজন্ম, সুবর্ণলতার কন্যা বকুল– যার পোশাকি নাম অনামিকা দেবী। তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখিকা, পাঠকবর্গের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী। ঘটনাপ্রবাহ অন্যরকম, তবু আশাপূর্ণা দেবীর নিজের জীবনের ছায়া কি অনামিকার মধ্যে নেই খানিক? সত্যবতী-সুবর্ণলতা, অর্থাৎ মা-দিদিমার বিদ্যোৎসাহ শেষ পর্যন্ত পরিণতি পেয়েছে এই বকুলের কলমে। তাঁর জীবন কি নিতান্ত মসৃণ? তা নয়। কিন্তু আলোর পথে উত্তরণ যে ঘটেছে, তা তো অস্বীকার করার জায়গা নেই।
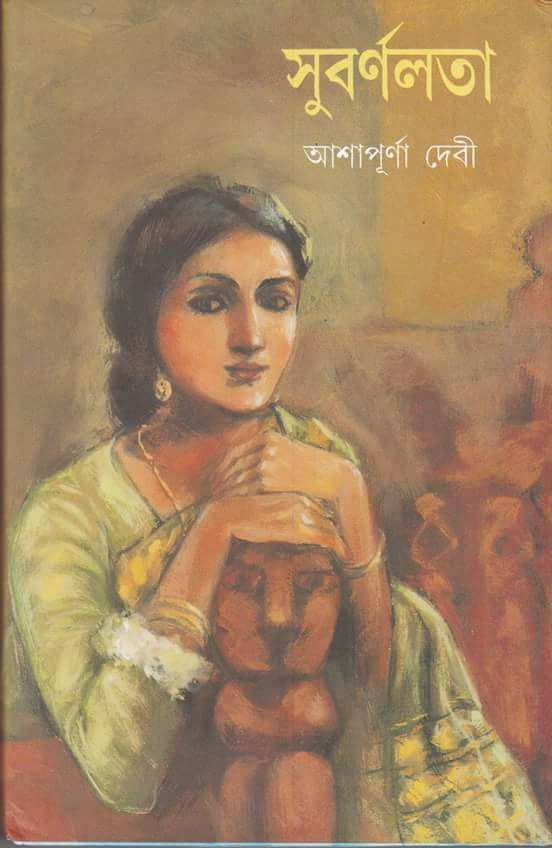
সত্যবতী-সুবর্ণলতা-বকুল, এই দেবীত্রয়ীর মধ্যে ধরা আছে বাঙালি নারীর আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার এক সম্পূর্ণ উপাখ্যান। সময়ের নিখুঁত দলিল।
আর প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা এই ট্রিলজির বাইরে? অসংখ্য ছোটগল্পে আশাপূর্ণা গেঁথে তুলেছেন অজস্র এমন নারীমুখ, যাদের সঙ্গে একবার আলাপ হলে ভুলতে পারা শক্ত।
যেমন ‘অভিযোগ’ গল্পের ছোট খুকুটি। তার নাম পর্যন্ত জানা নেই পাঠকের। সে তার বাবার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে ফুটপাতে বিছানো মনোহারি দোকানের সামনে, চাইছে একটা নীল কাচের মালা কিনতে। সে-মালার দাম বাবার দাম বাবার সাধ্যের বাইরে– তাই একবার তিনি দোকানির সঙ্গে দরদাম করছেন, আবার একবার নানাভাবে মেয়েকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা। তারপর হঠাৎ ঝড় উঠল। সবকিছু এলোমেলো, লণ্ডভণ্ড। তার মধ্যে সেই একরত্তি মেয়ে চিৎকার করছে, ‘ও বাবা, মালার দাম দিলে না?’ বোঝা যাচ্ছে, বাবা আসলে দাম-না দিয়ে মালাটা নিয়ে পালাচ্ছিলেন। মেয়ে ক্রোধে, ঘৃণায় মালা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয় রাস্তায়।
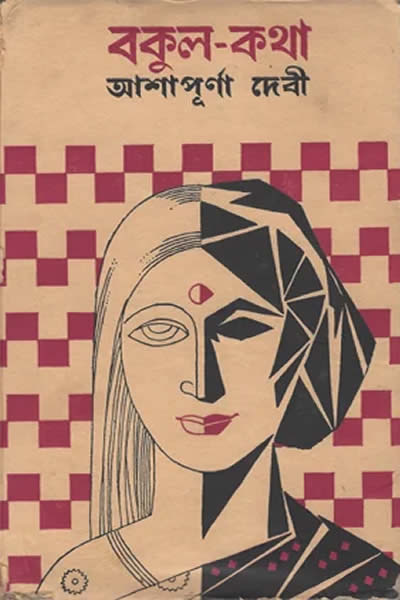
এ গল্পে দুটো মুখই বড় মর্মভেদী। অসহায় বাবা, মেয়ের আবদার রাখার ক্ষমতা যাঁর নেই, অথচ না-রাখতে পারার তীব্র যন্ত্রণাবোধ আছে, তিনি চুরির পরেও স্বীকার না করে উল্টে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে মেয়ের মন ঘুরিয়ে দিতে চান অন্যদিকে। এর বিপ্রতীপে বছর ছয়েকের বালিকা– যে প্রতিরোধে অটল, মালার প্রতি আকর্ষণ আছে অথচ দাম-না-দিয়ে সে মালা নিতে তীব্রভাবে অস্বীকৃত সে। বালিকা এ দেবী, রুদ্রতেজা প্রচণ্ডা।

কিংবা ধরা যাক, ‘সাফ-জবাব’ গল্পের নববধূটিকে। তার দুধের মতো রং, মেঘের মতো চুল, বাঁশির মতো নাক, চাঁপাকলি আঙুল দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সপরিবার নবাঙ্কুর। তারপর বিবাহের পর ফুলশয্যার রাতে যা ঘটল, তার অসম্ভব হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন আশাপূর্ণা। নবাঙ্কুরের আদর-আবেগের আতিশয্যে তার স্ত্রীর মাড়ি থেকে ছিটকে পড়ল মুক্তার মতো দন্তপংক্তি, বধূ হাহাকার করে উঠল– ‘কত খরচ করে বম্বে থেকে আনানো হয়েছিল।’ তারপর আশাপূর্ণার নিটোল ভাষ্যে, মেয়েটি ‘খুলে রাখে মেঘের মতো কেশপাশে গড়া ঝুড়ির মতো কবরী, খুলে রাখে খাঁদা নাকের উপর বসানো নাইলন নির্মিত সুগঠিত নাসিকা, টেনে টেনে খোলে আঠা দিয়ে আঁটা ফুলধনু মার্কা বাঁকানো ভ্রূযুগল’ ইত্যাদি। নবাঙ্কুর যখন ক্ষিপ্ত, বলে, ‘তুমি আমায় ঠকিয়েছ’, মেয়েটি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে, ‘মেয়েদের রূপচর্চার ইতিহাস তো আবহমান কালের। রবীন্দ্রনাথ পড়োনি বুঝি? পড়োনি– ‘শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।’ নিতান্ত হাস্যরসের গল্প, কিন্তু তার মধ্যেও মিশে আছে একরকমের চিনচিনে কষ্ট। রূপের তুলাদণ্ডে প্রত্যহ মেয়েদের যে উঠে দাঁড়াতে হয়, মূল্যায়িত হতে হয়, সেই অবমাননা, আর একটি মেয়ের নিজের শর্তে নিজের মূল্যমান স্থির করে নেওয়ার প্রচেষ্টা, মিশে আছে তাও।
সব দেবী কি সত্যি জেতেন?

সোনাই যেমন। ‘ভুল লগ্নে-ভুল জায়গায়’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শুরুতেই তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে ‘চিরবঞ্চিতই রয়ে গেল। সারাজীবনে তার কোনও ইচ্ছে-বাসনাই পূরণ হল না।’ এইটুকু পড়ে কেউ যদি ভাবেন, এ-ও অন্তরালবর্তিনী মেয়েদের বঞ্চনাগাথা, তিনি ভুল করবেন। কারণ সোনাই উচ্চমধ্যবিত্ত দম্পতির দুহিতা, স্কুলে ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রি পড়া কন্যা। তবু তার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হয় না। কেমন সেসব ইচ্ছে? ব্রেকফাস্টে ডিম-কলা-টোস্টের বদলে কাজের মেয়েটির মতো বাসি-রুটি গুড় খাওয়ার ইচ্ছে, নামী স্কুলের বদলে মাথায় লাল রিবন বেঁধে পাড়ার সাধারণ ইশকুলে যাওয়ার ইচ্ছে, কাদামাটি নিয়ে মূর্তি গড়ার ইচ্ছে। বাবা-মা প্রশ্রয় দেন না এমন আবদারে। এমনকী, মাসির বাড়ি গিয়ে মেসোর ছিমছাম বাহুল্যবর্জিত কোয়ার্টার তার মনে ধরেছিল– স্বপ্ন দেখত অমন এক ঘর বাঁধার। কিন্তু বিয়ে হল তার ঐশ্বর্যে মোড়া প্রাসাদোপম বাড়িতে। দারিদ্র নেই, সংসারের ঘানির শ্রম নেই, তবু সোনাইয়ের জীবন হয়ে থাকে শুধু সাধ-না-মেটার উপাখ্যান। এ গল্প বর্ণনায়, বিষয়বৈচিত্রে আজও কী তীব্র সমকালীন, ভাবি! আর ভাবি, মেয়েদের কষ্টের উৎস যে আসলে অভাব-অনটন-পরিশ্রম নয়, তার উৎস স্রেফ দৈহিক-মানসিক পরাধীনতা; এবং সে কুটিরবাসিনী হোক বা রাজেন্দ্রাণী, তাতে কিছু যায়-আসে না– এমনটা আশাপূর্ণার মতো করে বুঝেছিলেন আর বুঝিয়েছিলেন কে?

দেবীদের আরও থাকে। স্ববিরোধ। একটি গল্পে পড়ি, বর্ষিয়সী স্বর্ণপ্রভা শৈশবে তাঁর ঠাকুমার কাছে শেখা তুলসীর প্রণামমন্ত্র শিখিয়েছেন নাতনিকে। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর আধুনিক পুত্রবধূ, বলছেন ‘নাতনিকে একটি কুসংস্কারের ডিপো বানাতে চাইছেন’, ‘আর ওকে এইরকম গাঁইয়ামি শেখাবেন না।’ কিন্তু তারপরেই দেখা যাচ্ছে, পুত্রবধূ নিজে রাখছেন সন্তোষী মা’র ব্রত– প্রসাদী ছোলা-গুড় কলাপাতায় মুড়ে গরু খুঁজতে বেরচ্ছেন, কারণ গরুর মুখে প্রসাদ দিয়ে তবে ব্রতভঙ্গের নিয়ম। অর্থাৎ, সে সংস্কারকে ঘৃণা করছেন তিনি, নিজেও সেই একই সংস্কারের দাস– শুধু সেটুকু তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।
বস্তুত যা কিছু পুরনো তা-ই বর্জনযোগ্য, যা কিছু নতুন তা-ই বরেণ্য, এমনটা ভাবেননি আশাপূর্ণা। আধুনিকতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ভাবনার প্রসারতা দিয়েই শুধু। তাই সত্যবতী বা সুবর্ণলতার লড়াই যেমন সমাজের জগদ্দল পাথর সরানোর, তেমনই, বদলে যাওয়া সময়ে দাঁড়িয়ে বকুল তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দেখেছে, উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা ভাবার বিষ-পরিণাম। বকুল আর তার অগ্রজা পারুল, এরা তখন উল্টে ভেবেছে, ‘এইটাই কি চেয়েছিলাম আমরা? আমি, তুমি, আমাদের মা দিদিমা, দেশের অসংখ্য বন্দিনী মেয়ে?’ আশাপূর্ণার গল্পেও তাই ভূমিকাবদল হয়েছে কোথাও কোথাও, প্রাচীনে ও নবীনে। কোনও গল্পে দেখি সম্পন্নঘরের শিক্ষিতা গৃহিণী সবার জন্য দামি জামাকাপড় কিনলেও কাজের মেয়েটির জন্য কিনতে তাঁর হাত সরে না। আবার অন্য গল্পে দেখি, সংস্কারাচ্ছন্না কটুভাষিণী ভটচাজগিন্নি তাঁর বাসনমাজুনির ছেলের অসুখে হত্যে দিতে তারকেশ্বরে যান।

আসলে সমাজ, সম্পর্ক কোনও কিছুই একরৈখিক নয়। আশাপূর্ণা সেই জটিলতার বিষকে সানন্দে ধারণ করেছেন স্বকণ্ঠে, স্ব-কলমে। তাঁর হাতে গড়া প্রতিমারাও তেমনই, দোষে-গুণে, ক্রোধে-প্রেমে সার্থক রক্তমাংসের মূর্তি।
যে দেবীদের আবাহন কিংবা বিসর্জন নেই, তাঁরা চিরায়ত।
……………………….
রোববার.ইন-এ পড়ুন রাকা দাশগুপ্ত-র অন্যান্য লেখা
……………………….
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
