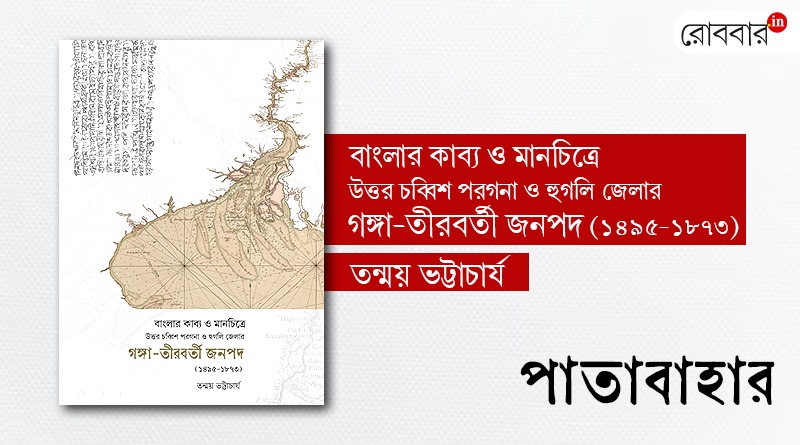
আত্মপরিচয় থেকে দূরত্ব যে শতবর্ষের নিঃসঙ্গতার ভিতর নিয়ে গিয়ে ফেলছে মানুষকে, তা থেকেই হয়তো জন্ম নিচ্ছে নানা বিকৃতি। অথচ একটু মায়া– নিজেকে আর নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার আকুতি থাকলে, সেই দূরত্ব অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে না।

মৃতের কঙ্কাল নয়। ইতিহাস, বর্তমানের মতোই জীবন্ত এবং সত্য। সেই সত্যের সন্ধানে রত হওয়ার জ্বালানি হিসেবে, বাঙালির ইতিহাস প্রণেতা নীহাররঞ্জন রায় জ্ঞানস্পৃহাকে একক কৃতিত্ব দেননি। বরং তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল প্রাণের আবেগ। স্বভূমি-স্বদেশকে ভালোবাসাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল জ্ঞানের পথে। বাঙালির ইতিহাসের যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামো নির্মাণ করতে নেমে, তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত যুক্তিই যাচাই করেছিলেন, এবং যোগ করেছিলেন তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং মন্তব্য; তবে, সেখানেই বন্ধনী শেষ করে তিনি ইতিহাসের পথ রুদ্ধ করে দেননি। অর্থাৎ, শেষ কথা বলে যে কিছু নেই, তাই-ই আসলে খুলে দেয় ভবিষ্যৎ গবেষকদের চলার পথ, জোগায় পাথেয়। নীহাররঞ্জন তাঁর সেই ব্যাপ্ত কর্মের উদ্দেশ্যটিকে স্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এই সন্ধান ‘দেশকে আরও গভীর আরও নিবিড় করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে’। ইতিহাসের চর্চা তাই এক অর্থে স্বদেশব্রত। সমসময়ের কোনও লেখক যখন একই রকম আগ্রহে তাঁর ইতিহাস, জনপদের দিকে ফিরে তাকান, তখন বোঝা যায় তিনিও বুঝে নিতে চাইছেন তাঁর দেশ, জন্মভূমিকে। তন্ময় ভট্টাচার্যের ‘বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ’ সেই অর্থে দেশচর্চার একটি নতুন বই, নতুন আঙ্গিকের বই।
সভ্যতা নদীমাতৃক। সুতরাং, নদীকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের ঘনিয়ে ওঠা। দেশের টানেই লেখক তাই ফিরে গিয়েছেন সেই নদীর কাছে। ত্রিবেণী থেকে শুরু হচ্ছে যাত্রাপথ। শেষ হবে গিয়ে কলকাতায়। হুগলি নদী ধরে ভেসে চলবে অনুসন্ধিৎসু মন। প্রাথমিক একটা উদ্দেশ্য আছে। যে-ধারার একদিকে হুগলি আর অন্যদিকে চব্বিশ পরগনা, তার তীরবর্তী জনপদগুলির অতীত খুঁজে বের করা। সেগুলির অতীত নাম কী ছিল, তার যথাসম্ভব অনুসন্ধান চালানো। প্রচলিত-কথায় কিছু ভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। আবার লোকমুখে বিবর্তিত হতে হতে জনপদগুলির যে-নাম দাঁড়িয়েছে, তাতে এক রকমের অর্থ অনুমান করে নেওয়া হয় ইদানীং। তাই-ই সত্যি কি না, তা খতিয়ে দেখেছেন লেখক। তথ্যের চালাচালিতে মোটের উপর সত্যের একটা কাঠামো পাওয়া যায়, যেমনটা লৌকিক বয়ানের রূপভেদ থেকে মেলে সমাজবাস্তবতার আঁচ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………
বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে কাব্য। এবং সেই কাব্যের ভিতরও তো এই নদীরই দেখা মিলছে। কখনও বাণিজ্যের পসরা ভেসে যাচ্ছে, তো কখনও ভক্তির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এই সব জনপদ ধরেই। ফলত, দ্বিতীয় পর্বে লেখক কাব্য ধরে ধরে এই জনপদ চিনে নেওয়ার ও চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঠিক এই জায়গাতে এসেই লেখকের অনুসন্ধান অন্য মাত্রা পায়।
………………………………………………………………………………………………………………………………………
তবে, এরপর লেখক যে ডুব দেন তা একেবারে গহীনে। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে কাব্য। এবং সেই কাব্যের ভিতরও তো এই নদীরই দেখা মিলছে। কখনও বাণিজ্যের পসরা ভেসে যাচ্ছে, তো কখনও ভক্তির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এই সব জনপদ ধরেই। ফলত, দ্বিতীয় পর্বে লেখক কাব্য ধরে ধরে এই জনপদ চিনে নেওয়ার ও চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঠিক এই জায়গাতে এসেই লেখকের অনুসন্ধান অন্য মাত্রা পায়। এমন নয় যে, তাঁর আগের তথ্য-তালাশের তেমন গুরুত্ব নেই। তবে, কাব্য তো ইতিহাস নয়, আবার তা একেবারে ইতিহাসবিমুখও নয়। আজকের ভারতবর্ষে কাব্য আর ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়ার বেজায় চেষ্টা। একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ মনই এই দুয়ের পৃথক করতে পারে, এবং সেখান থেকে আহরণ করতে পারে প্রয়োজনীয় উপাদান; যা ইতিহাসচর্চার জন্য তো একান্ত জরুরি বটেই, আরও বেশি জরুরি ইতিহাসচেতনার নিরিখে। বাংলার কাব্যে কাব্যে জড়িয়ে আছে বাংলার সমাজ, মন এবং মানুষ। ইতিহাসালোচনায় তাই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি যেমন পুষ্টি জোগায়, একটা জাতিকে তার সমগ্রে বুঝে নিতে সাহায্য করে, তেমনই এই কাব্যের মন্থনেও সমাজ বিবর্তনের ধারা থেকে যে-ছবি ফুটে ওঠে, যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করতে পারলে তা ইতিহাসের সহায়কই হয়ে ওঠে। প্রয়োজন শুধু মতপ্রতিষ্ঠার গোঁড়ামি ছেড়ে খোলা মনে, খোলা চোখে দেখার নিবিড় অনুশীলন। বিশ্বাসে বস্তুকে না মিলতে দিয়ে যদি একটির চিহ্ন ধরে অন্যটির কাছে যাওয়া যায়, তাহলেই একটা তুলমূল্য বাস্তবতার নাগাল মেলে। কাব্যে নিহিত সমাজের বহুবিধ কথা। সেই সমাজ বাদ দিয়ে ইতিহাস রচিত হয় না। কোশাম্বী যেমন ভারতের ইতিহাস সন্ধানে জনগোষ্ঠীর সংগঠন এবং ক্ষয়কেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাজার থেকেও তাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাঙলের ওজন। আবার বাংলার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নীহারঞ্জনও বলেন, ‘মানুষের সমাজই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস, এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাসই দেশকালধৃত মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে।’ ফলত কাব্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কাজে না লাগিয়ে, সদর্থেই ব্যবহার করা যায়। তাতে ইতিহাস, বর্তমান কোন ক্ষেত্রেই অশান্তি বাধে না। অনুসন্ধানে এবার বাকি থাকে একেবারে হাতে-কলমে মিলিয়ে নেওয়ার পালা, অর্থাৎ মানচিত্রে চোখ রাখা। এ-কাজেও বিরত হননি লেখক। বাংলার প্রথম নির্ভরযোগ্য জ্যাও ডি ব্যারোজের মানচিত্র থেকেই সে-কাজ শুরু করেছেন, এবং আলোচ্য জনপদগুলি শ-চারেক বছরে মানচিত্রে কীভাবে ধরা দিয়েছে তার নকশা খুঁজে বের করেছেন।
………………………………………………………………………………………………………………………………………
আরও পড়ুন: মুখোমুখি জীবন আর জীবনের মর্ম, ভিতরপানে চাওয়ারই আখ্যান ‘উজানযাত্রা’
………………………………………………………………………………………………………………………………………
সন্দেহ নেই, এ-কাজ শ্রমসাধ্য। শুধুমাত্র জ্ঞানস্পৃহা দিয়ে গবেষণা হয়তো চালানো যায়, তবে ওই প্রাণের আবেগ আর দেশকে ভালবাসার চালিকাশক্তি না থাকলে অনুসন্ধান স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে না। জনপদগুলির অতীত সত্যে পৌঁছতে গিয়ে লেখক পুথি ঘেঁটেছেন, মানচিত্র দেখছেন। এই ধরনের গবেষণা কাজে যেরকম নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় লাগে, এই বইয়ের সর্বত্র সে-ছাপ স্পষ্ট। তবে, জরুরি একটি প্রসঙ্গ এই বইয়ের ভূমিকায় ধরিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়, তা হল– আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান। সেখানে ‘কৌতূহল যেমন থাকে, তেমন থাকে মায়া।’ এরকম একটি গবেষণামূলক কাজ বিদ্যায়তনিক পরিসরেই হয়তো যথাযোগ্য সমাদর পাবে। আর পাঠক সাধারণভাবে স্থান-নামের ইতিহাস আপন গরজে জেনে নিয়ে কৌতূহল মেটাবেন। সে-সবের বাইরেও এই বইয়ের একটি গুরুত্ব থেকে যায়। যা রাখা আছে ওই আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান আর মায়ার ভিতর। মনে রাখতে হবে, যে-সময়ে দাঁড়িয়ে এই কাজ করছেন লেখক সেই সময়ে সবথেকে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইতিহাস এবং পরিচয়কেই। আত্মপরিচয় থেকে দূরত্ব যে শতবর্ষের নিঃসঙ্গতার ভিতর নিয়ে গিয়ে ফেলছে মানুষকে, তা থেকেই হয়তো জন্ম নিচ্ছে নানা বিকৃতি। অথচ একটু মায়া– নিজেকে আর নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার আকুতি থাকলে, সেই দূরত্ব অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে না। তাহলে আর কেউ দূরত্বের সুযোগ নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতিটাও বিষিয়ে তুলতে পারে না। ইতিহাসকে ঠিকভাবে জানা, নানা উপায়ে অতীত সত্যের কাছে পৌঁছনো, কাব্য আর ইতিহাসকে গুলিয়ে না ফেলেও সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া– এসবই সমসময়ের জরুরি এবং আবশ্যিক অনুশীলন। এই বই নিবিষ্টভাবে জনপদের ইতিহাস সন্ধানীই বটে, তবে একই সঙ্গে সময়ের চরিত্র বুঝেই তার চাহিদাগুলোকে পূরণ করেছে। সেই নিরিখে বইয়ের অন্তরতম সত্যটি যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক; ইতিহাসের বিকৃতির যুগে ইতিহাসের কাছে পৌঁছনোই স্বদেশব্রত। এ-বই তার বিপুল সম্ভার নিয়ে সে-কথা পাঠককে বলতে দ্বিধা করে না।
আর যে-কথা বলতেই হয়, তা হল বইটি নির্মাণের পারদর্শিতা। পুথির নমুনা থেকে আস্ত মানচিত্র বইয়ের ভিতর রেখে দেওয়া– যা ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়ক হবে। আসলে লেখা শুধু নয়, একটা বই হয়ে ওঠে তার সমগ্রে এবং ভাবনায়। আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ সেই মেজাজ গোড়াতেই বেঁধে দেয়। এমনকী পুস্তানিও এ বইয়ের বাহুল্য বা কেজো প্রয়োজন মেটানোর দায় নিয়ে হাজির হয়নি, জরুরি অংশই হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সবার আগে ধন্যবাদ দিতে হয় প্রকাশক ‘মাস্তুল’-কে। এরকম একটি বইয়ের স্বপ্ন তাঁরা শুধু দেখেছেন তাই-ই নয়, যে যত্ন ও নিষ্ঠায় বইটিকে গড়ে তুলেছেন, তা অজস্র হতশ্রী নির্মাণে জর্জরিত বাংলা প্রকাশনাকে আদতে স্বস্তিই দেবে।
বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে
উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার
গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ
তন্ময় ভট্টাচার্য
মাস্তুল
১৩৯৯ টাকা
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
