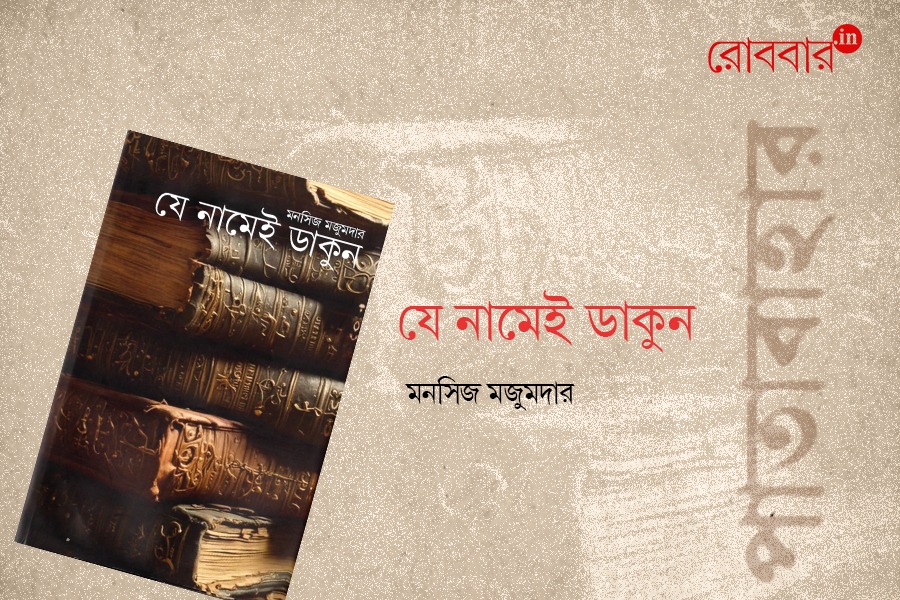
এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য চকমকি পাথর। যা পথ দেখায়। দিগভ্রষ্ট হতে দেয় না। চিন্তার জাল, যুক্তির নানা প্রকরণ ভাবনার উদ্রেক ঘটাতে থাকে। অথচ আগাগোড়া মজলিসি ঢঙে বলা কথার চলন যেন এক কথোপকথনের মতোই এগোয়। লেখক বক্তা। আমাদের মনে জন্ম নেওয়া অস্ফূট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে দিতে তিনি লেখাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। রেখে যান নানা স্মারক।

‘সময় এক দর্পণ। ঘড়ির মতো। আবার কখনও তা সময়ের চেয়েও এগিয়ে।’ বক্তার নাম ফ্রানৎস কাফকা। ১৯২৪ সালে প্রাগে পিকাসোর প্রথম কিউবিস্ট ছবির প্রদর্শনীতে এসে কোনও নিন্দুকের মুখ বন্ধ করতে এই সপাট উক্তি করেছিলেন তিনি। ১০০ বছর পরের পৃথিবীতে প্রকাশিত এক বাংলা বই শেষ হচ্ছে এই ঘটনার উল্লেখে। যেন গোটা বইটির সারাৎসার ধরা রয়েছে এখানেই।
মনসিজ মজুমদারের ‘সময়ের ফসল’ নামের রচনাটি ২০০৫ সালে লিখিত হলেও তা সংকলিত হয়েছে ‘যে নামেই ডাকুন’ নামের যে বইয়ে, তা এবছরের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে। চিন্তার চকমকি পাথরে সাজানো এক পথ নির্দেশিকা যেন এই বই। স্ট্রাকচারালিজম থেকে ক্রমেই পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের অমোঘ সরণিতে নিয়ে যায় আমাদের।
মনস্বী বাঙালির কাছে মনসিজ মজুমদারের পরিচিতি দেওয়ার কোনও অর্থই হয় না। জনপ্রিয় ও বহুল পরিচিত সংবাদপত্র, পত্রিকায় তাঁর কলাসমালোচনা বহু বছর পাঠকদের ঋদ্ধ করেছে, ভাবিয়েছে। তাঁরই আটটি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁর বলার কথায় ফিচারের লঘুতা নেই, কেননা এগুলি আক্ষরিক অর্থেই প্রবন্ধ। কাজেই নানা কাজের ফাঁকে পড়ার নয়, এই বই নিরালা অবসরের সঙ্গী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি ধীরে ধীরে বিষয়ে ঢোকেন। প্রথমে বেশ সহজ। তারপর প্রসঙ্গ বদলে আরও গভীরে নিয়ে চলেন। প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নকে ভাঙেন অন্য প্রশ্ন দিয়ে। আর এই সময় পাঠককে তাঁর হাত ধরেই এগোতে হবে। তাহলেই চোখের সামনে খুলে যাবে বিশ্লেষণ-নান্দনিকতার অনুপম জগৎ।
যেমন বইয়ের প্রথম রচনা ‘পোর্টফোলিও ব্যাগের হারানো-প্রাপ্তি সংবাদ’। যার শুরুতে বলা হচ্ছে, একটি পোর্টফোলিও ব্যাগেই আজ ধরে যায় মানুষের পরিচিতির বহুবিধ অভিজ্ঞান। অর্থাৎ ‘আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের পরিচিতি কতগুলি চোথা কাগজে এসে ঠেকেছে।’ কিন্তু যত লেখা এগোয় তিনি প্রসঙ্গান্তরে সরে আসেন। প্রশ্ন তোলেন ‘ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের স্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্বভাষা বা ডিসকোর্সের মধ্যে আমরা যদি এই আলোচনাকে নিয়ে আসি তা হলে কি বলা যাবে যে ওই ব্যাগটি একটি চিহ্নকারী (signifier) এবং ওই ব্যক্তি চিহ্নিত (signified)? ব্যাগটি যদি বলে দেয় ব্যক্তিটি কে, তার পরিচয় কী, তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে বলতে পারি চিহ্নকারী বা signifier এবং ব্যক্তির পরিচয় signified। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই ব্যক্তি ও তার পরিচয়, অন্তত ওই ব্যাগটি যা দিচ্ছে, তা কি এক এবং অভিন্ন?’ আবার কিছুটা পরে তিনি বলছেন ‘প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত; সাহিত্যের কাজ চিহ্নকরণ এবং সেই চিহ্নকরণের লক্ষ্য অস্তিত্ব নয়, অস্তিত্বের ধারণা বা ব্যাপকভাবে মানুষি বাস্তবতার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের অভিজ্ঞতা।’ এভাবেই যে ডিসকোর্সে আমরা ঢুকে পড়ি তা আমাদের পিরানদেল্লো, সোফোক্লিসের নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ ছুঁয়ে মানুষের পরিচিতির ‘নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ’-কে তুলে ধরতে থাকে। লেখাটি শেষ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দিয়েই। “লক্ষ করার বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাকে ‘ভারতীয়’ করেননি… গোরা আজ সকল ধর্মসংস্কার থেকে মুক্ত। তার পরিচয় হিন্দু নয়, আবার অন্য ধর্মাশ্রয়ী অহিন্দুও নয়। এই দুই পরস্পরবিরোধী signifier থেকে রবীন্দ্রনাথ তাকে উত্তীর্ণ করেন ‘ভারতবর্ষীয়’– এই নতুন পরিচিতিতে।” সাম্প্রতিক সময়ে এই উচ্চারণের এক ভিন্নতর অভিঘাত হয় ঠিকই। তবু ১৯৯৭ সালে লিখিত প্রবন্ধটির আসল ফোকাস যদিও তা নয়।

একই ভাবে নামরচনায় শিল্প-সাহিত্যে নামকরণই হয়ে ওঠে তাঁর বিষয়। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে সুগন্ধই ছড়াবে, ক্লিশে হয়ে যাওয়া এই প্রসঙ্গ দিয়েই রচনাটির সূচনা। এসে পড়ে গ্যারট্রুড স্টাইনের বিখ্যাত পঙক্তি: ‘Rose is a rose is a rose is a rose’-ও। মনে হতে থাকে খুব সচেতন ভাবেই পরিচিত, সহজ প্রসঙ্গকেই কি তিনি বেছে নিলেন পাঠকের হাত ধরার জন্য? ভুল ভাঙে যখন ক্রমশ শিল্পকলা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সিঁড়িতে তিনি ঢুকতে থাকেন। বোঝা যায় তাঁর অভীষ্ট এইটুকু মাত্র নয়। বরং তা এক ভিন্নপথে যাওয়ার আগে সুকৌশলী প্রস্তাবনা মাত্র। কখনও ভিলেনডর্ফের ভিনাস তার কুরূপা, গর্ভিনী নগ্ন নারীমূর্তি নিয়ে ভেসে ওঠে। কখনও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশে নির্মিত ইতালির পম্পেইয়ের এক রহস্যভিলার অপূর্ব রঙিন দেওয়ালচিত্র। প্রস্তের উপন্যাস থেকে জেমস জয়েসের ‘ইউলিসিস’ (লেখক অবশ্য অন্য বানান লিখেছেন) এবং আরও নানা রচনা, সৃষ্টিকে ছুঁয়ে নানা কূট প্রশ্নের সন্ধান করেছেন মনসিজ। তবে একেবারে শেষে উমবের্তো একোর ‘দ্য নেম অফ দ্য রোজ’ নিয়ে তাঁর চমৎকার বিশ্লেষণ লেখাটির সেরা অংশ নিঃসন্দেহে। উপন্যাসটির মধ্যে যে ‘এক গভীর বহুমাত্রিক উচ্চমার্গীয় তাৎপর্যের স্তর’ রয়েছে তার ‘চাবিকাঠি’র সন্ধান করতে নেমে লেখক খুঁজে পেয়েছেন উপন্যাসের শিরোনামকেই। যা বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন ‘সেই জন্যে গোলাপ নয়, গোলাপের নামই সত্য।’

এমনই নানা রচনা। এই স্বল্প পরিসরে যার কেবল ‘হিমশৈলের চূড়া’টুকুকেই ভাসিয়ে রাখা গেল। এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য চকমকি পাথর। যা পথ দেখায়। দিগভ্রষ্ট হতে দেয় না। চিন্তার জাল, যুক্তির নানা প্রকরণ ভাবনার উদ্রেক ঘটাতে থাকে। অথচ আগাগোড়া মজলিসি ঢঙে বলা কথার চলন যেন এক কথোপকথনের মতোই এগোয়। লেখক বক্তা। আমাদের মনে জন্ম নেওয়া অস্ফূট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে দিতে তিনি লেখাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। রেখে যান নানা স্মারক। যেমন ‘… কালজয়ী শব্দটিতে মরচে পড়ে গেছে। নিজের সময়কে যিনি জয় করেছেন, তাঁর কালজয়ী না হলে কিছু এসে যায় না।’ কিংবা ‘কবিতা-প্রসূত ছবি বা ছবি-প্রণোদিত কবিতায় বীজের সঙ্গে বনস্পতির অনেক সময় কোনও সাদৃশ্য থাকে না। বিশেষ করে ছবি থেকে যে কবিতার জন্ম, তা আরও অনেক বাহ্য ঘটনা থেকে ছিটকে-পড়া প্রেরণাস্ফুলিঙ্গে জ্বলে ওঠা কবিতার মতোই।’ এই টুকরো টুকরো বাক্যনিচয় মনের ভিতরে নাগাড়ে চিন্তার বুদবুদকে ফুটিয়ে তুলতে থাকে। এই বইয়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এটাই। পাঠ ও পুনঃপাঠের ইচ্ছের জন্ম দিতে থাকা বইটি বইয়ের সেলফে বরাবরের মতো থাকার জন্যই হাতে এসেছে, একথা বুঝতে পাঠকের বেশি সময় লাগে না।
যে নামেই ডাকুন
মনসিজ মজুমদার
রাবণ
৩৫০্
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
