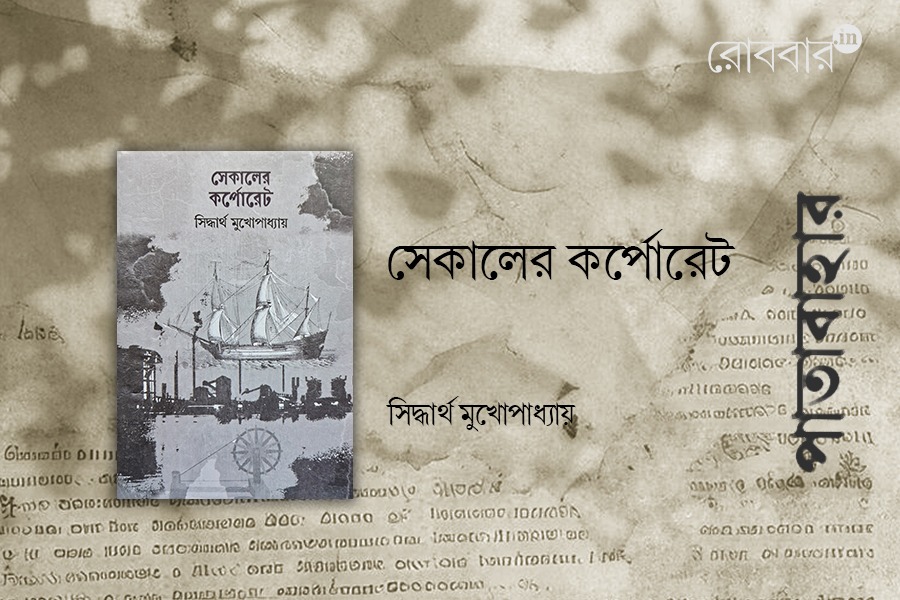
জীর্ণ আর অজীর্ণ ছাড়া বাঙালির কিছু নেই বলে সবথেকে বেশি আক্ষেপ বাঙালিরই। আছে বলতে তার এক সিন্দুক স্মৃতি। আত্মপরিচয়ের আখ্যান। এই স্মৃতি, যা কিনা বাঙালির জনজীবনেরই ইতিহাস, স্বভাবতই উজ্জ্বল। বাঙালির বাজুবন্ধ যতবার খুলে খুলে যায়, ততবার এই ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ‘সেকালের কর্পোরেট’ বইতে বাংলা ও বাঙালির ব্যবসার ইতিহাসকে গল্পে-গল্পে এই অন্তর্ভুক্তিকরণ এক সময়োপযোগী প্রতিরোধেরই বয়ান।

জীর্ণ আর অজীর্ণ ছাড়া বাঙালির কিছু নেই বলে সবথেকে বেশি আক্ষেপ বাঙালিরই। আছে বলতে তার এক সিন্দুক স্মৃতি। আত্মপরিচয়ের আখ্যান। এই স্মৃতি, যা কি না বাঙালির জনজীবনেরই ইতিহাস, স্বভাবতই উজ্জ্বল।
বাঙালির বাজুবন্ধ যতবার খুলে খুলে যায়, ততবার এই ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। মোটামুটি উনিশ শতক অবধি পৌঁছে তবে স্বস্তি, যেখান থেকে বাঙালির আত্মপরিচয়ের আধুনিকতা। বিনয়কুমার সরকার যে ‘বেঙ্গলিসিজম’ চেতনার কথা বলেন, তার সাধারণ চরিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যায়, ধর্ম নয় ভাষাই এখানে ভিত্তি। এই ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালির চেতনাকে একটা সার্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা উনিশ শতকেই, এবং বঙ্কিম সেখানে পুরোধা। একই সঙ্গে বাঙালি রাজনৈতিক চেতনাও এসময় পরিণতি পাচ্ছে, যার স্পষ্ট এক রূপ দেখা যাবে স্বদেশি আন্দোলনে।
সমাজসংস্কার থেকে এই রাজনীতি-চেতনা পর্যন্ত পৌঁছনো বাঙালির জাতিসত্তার বুনিয়াদ। উনিশ থেকে বিশের এই যাত্রায় সুতরাং যে পাঁচটি কর্মক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করবেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যা কি না আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণের অন্যতম উপাদান, তা হল– সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মসংস্কার, সাহিত্যচর্চা আর রাজনীতি। বিজ্ঞানচর্চা, সাংবাদিকতার মতো ধারাও এই পর্বে ক্রমে স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু যা পাবে না, তা হল ব্যবসা। অথচ জেমসনীয় ঐতিহাসিকতার সূত্রে দেখতে গেলে, উনিশের এই আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্ম-আবিষ্কার ইতিহাসবর্জিত হতে পারে না। বরং সেই আত্মবিশ্বাসের অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল বাঙালি ব্যবসায়ীদেরও। আমরা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহনকে যেমন খতিয়ে দেখি, ঠিক তেমনই গুরুত্ব-সহকারেই দেখা উচিত রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর এমনকী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও।
রামদুলাল দে হাজার চোদ্দো টাকায় জাহাজ কিনে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন ইংরেজ বণিককে, এ ঘটনা হয়তো অনেকেরই জানা। তবে শুধু ব্যবসায় মাত দেওয়া হিসাবে একে দেখলে চলে না। নেটিভ খরিদ্দারের এত বড় সাহস বরদাস্ত হয়নি। অতএব জাত ঔপনিবেশিক প্রভুর ‘থ্রেট কালচার’ জারি রইল। কিন্তু রামদুলাল দমেননি। এই অদম্য রামদুলাল কি উনিশ শতকের ইতিহাসকে পুষ্ট করেননি? দ্বারকানাথের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে যে বৈষ্ণব শেঠের হদিশ মেলে, যিনি খুব সফল ভাবে নির্ভেজাল গঙ্গাজল হাঁড়িতে করে দেশে নির্গাঙ্গেয় অংশে পাঠিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তা আমাদের অবাকই করে। গঙ্গাজলের কারবার নতুন নয়। বৈষ্ণব শেঠ যেভাবে তাঁর ব্র্যান্ড ভ্যালু নির্মাণ করেছিলেন, তা অতুলনীয়। এই শেঠের আনুকূল্য ছিল যে পরিবারের ওপর, সেই পরিবার থেকেই এলেন দ্বারকানাথ। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে যেভাবে তিনি গণ্ডির বাইরে এনে জনমুখী করতে চাইলেন, তা ভারতবর্ষের অর্থনীতির ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ব্যবসায় তাঁর দক্ষতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছিল যে, বাঙালির আত্মবিশ্বাস নতুন মাত্রা খুঁজে পেয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।
………………………………………………
সময়ের সূত্রে ধারাবাহিক আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চলছিলই। যার ভরকেন্দ্রে ছিল বাঙালির ব্যবসার ইতিহাসও। এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে এই পরম্পরা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। সমাজসংস্কার, ভাষা-সংস্কৃতি ও সেই থেকে রাজনৈতিক গণচেতনায় বাঙালির যে পরিপূর্ণ জাগরণ, যে ইতিহাসের মুখাপেক্ষী আমরা আজও, সেই ঐতিহাসিকতার সূত্রেই ব্যবসায়ী বাঙালির দিকেও আমাদের সমমর্যাদায় তাকানো উচিত, যেমনটা দৃষ্টিপাত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। নইলে সমাজেতিহাসের পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।
………………………………………………
দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পত্তি সেভাবে রাখতে পারেননি। তবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যাঁর ব্যবসা ও নানা রকমের কাজকর্ম নিয়ে সময় সময় খানিক কৌতুক-ই করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বাণিজ্য-প্রয়াসেও থেকে গিয়েছিল স্বদেশি-ভাবনার বীজ। একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের মতো করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ফলত ‘এ জাহাজ স্বদেশবাসীর’– এই উক্তি তার যেমন আবেগের, তেমনই গভীর ভাবনাপ্রসূত। অচিরেই যে ভারতীয়দের সমমর্যাদার জন্য ক্যালকাটা ক্লাবের জন্ম হবে, তা বিচ্ছিন্ন দ্রোহের বশে নয়। সময়ের সূত্রে ধারাবাহিক আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চলছিলই। যার ভরকেন্দ্রে ছিল বাঙালির ব্যবসার ইতিহাসও। এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে এই পরম্পরা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। সমাজসংস্কার, ভাষা-সংস্কৃতি ও সেই থেকে রাজনৈতিক গণচেতনায় বাঙালির যে পরিপূর্ণ জাগরণ, যে ইতিহাসের মুখাপেক্ষী আমরা আজও, সেই ঐতিহাসিকতার সূত্রেই ব্যবসায়ী বাঙালির দিকেও আমাদের সমমর্যাদায় তাকানো উচিত, যেমনটা দৃষ্টিপাত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। নইলে সমাজেতিহাসের পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের ‘সেকালের কর্পোরেট’ বইটির গুরুত্ব এখানেই। বই জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বহু গল্প থেকে এই চেতনার ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। সাম্প্রতিকের ইতিহাসে এর মাত্রা অন্য। উনিশ শতক থেকেই যে চাকুরীজীবী বাঙালির উদ্ভব, তার ক্লান্তি-অবসাদ-হীনম্মন্যতা, সেখান থেকে নতুন ধর্মবোধের দিকে গড়িয়ে যাওয়া– এসবের ভিতর দিয়ে বিত্তমধ্য শ্রেণির এক আদল আমরা পেয়ে থাকি। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোয় এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবার এই শ্রেণি নানা কারণে কাঠগড়াতেও ওঠে। তার অন্যতম হল যে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। স্বার্থবিঘ্নিত না হতে দেওয়া এবং সেই সূত্রে শক্তি-ক্ষমতার সঙ্গে এক সমঝোতার দিকে এগনো। গণতন্ত্রের ফাঁকফোকর খুঁজতে গিয়েও সমাজতত্ত্ববিদদের এই মৌলিক সমঝোতার বিন্দুতেই তাই পৌঁছতে হয়।
আজ বাঙালি যখন বিপর্যস্ত গণতন্ত্রে বেসামাল, তখন সে খুঁজে দেখতেই পারে তার অতীত। এবং দেখা যাবে, সেখানে কেবল সমর্পণ নেই, সমঝোতা নেই, অসহায়ত্ব নেই; আছে প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও। আত্মমর্যাদার সূত্রেই তার যাবতীয় প্রতিরোধ এবং প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসে বিপর্যয় থাকবে না, তা হয় না। সপ্তডিঙা মধুকর ডুবেও যেতে পারে। তা বলে চাঁদবণিকের পালা তো আর ফুরোয় না! ফলত এক সিন্দুক স্মৃতি দুর্যোগের দিনে আর মেদুর আবেশ নিয়ে হাজির হয় না। আসে আগামীর বীজধান হয়ে। বাঙালির ইতিহাসে, বাংলা ও বাঙালির ব্যবসার ইতিহাসকে গল্পে-গল্পে এই অন্তর্ভুক্তিকরণ এক সময়োপযোগী প্রতিরোধেরই বয়ান। তা ফিরিয়ে আনার জন্য, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লেখক-প্রকাশক উভয়কেই সাধুবাদ দেবে সমসময়। তা তাঁদের প্রাপ্য।
সেকালের কর্পোরেট
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
মান্দাস
৩০০ টাকা
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
