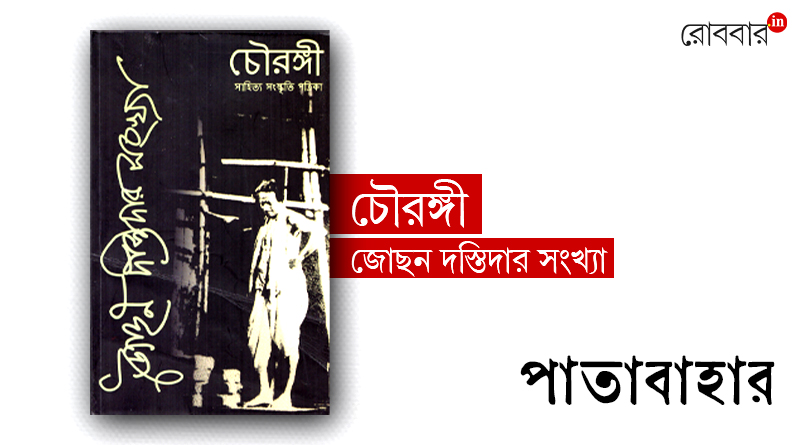
‘চৌরঙ্গী’ পত্রিকা যে বিন্যাসে ও বিস্তারে জোছন দস্তিদারের জীবন আর কাজকে ধরতে চেয়েছে, তা ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকের সংলাপ-সম্ভাবনাকেই জায়মান করে তোলে। তাঁর নিজের লেখালিখি ও বিভিন্ন সময়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারগুলি সংকলিত হয়েছে ‘স্বগতোক্তি’ এবং ‘থিয়েটার প্রসঙ্গ’ পর্বে, যা আদতে বাংলা নাটকের ক্রমবিবর্তনের পদছাপটিকে স্পষ্ট করে দেয়। মার্কসবাদী বীক্ষা চৈতন্যে নিয়েই সেদিন যাঁরা দেশ ও সমাজভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, তার একটা রূপরেখা এই লেখাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

থিয়েটার দীর্ঘায়ু স্মৃতি এবং শ্রুতিতে। জোছন দস্তিদারের মতো বাংলা নাট্য জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্বকে যখন ফিরে দেখার আয়োজন ‘চৌরঙ্গী’ পত্রিকার নতুন সংখ্যায়, তখন স্মৃতিই সেই অতীতে প্রবেশের চাবিকাঠি। প্রবেশক হিসাবে বহুজনের বহু কথার ভিতর থেকে তুলে নেওয়া যেতে পারে রাজা সেনের এই উক্তিটিকে– ‘শেষ পর্যন্ত শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাই ছিল জোছন দস্তিদারের নাটকের মূল উপজীব্য।’ আপাতসরল এই বাক্যটিই বস্তুত একটা সচেতন সময়ের ইশ্তেহার। জোছন দস্তিদারের মতো সচেতন মেধাবী যুক্তিবাদী মানুষ, যিনি নিজেকে ‘মার্কসবাদী মিশনের একজন কর্মী’ বলেই স্পষ্ট ঘোষণা করেন, তাঁর চৈতন্যের জগৎও প্রত্যাশিত ভাবে এই লড়াইকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সময়ের ভিতর এই যে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসে পৌঁছনোর জন্য লড়াই– রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দুই ক্ষেত্রেই, আদতে যা একই গন্তব্যের অভিমুখী, তাই-ই প্রকৃতপক্ষে শিল্পের নবজাগরণের প্রেক্ষাপট রচনা করে। সঙ্গত ভাবেই জোছন দস্তিদার নিজে যখন সময় ও আধুনিক নাটক বিশ্লেষণ করতে বসেন, তখন বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’কেই সেই আধুনিকতার উন্মেষকাল হিসাবে ধরে নিয়ে এগোন। উদ্দেশ্যবিহীন শিল্প থাকতে পারে না। সুতরাং নাট্যকর্মী হিসাবে তিনি নিজেও তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে স্পষ্ট ছিলেন। আদিযুগ থেকে বিবর্তিত হয়ে নাটক যখন আধুনিকতায় পৌঁছল, তাঁর কাছে নাটক তখন কেবল লোকরঞ্জনের মাধ্যম থাকল না, হল ‘লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম এবং মানব সমস্যার দরদী অংশীদার।’ সমাজ-সমস্যার অংশীদার হওয়াই নাটকের মূল কাজ বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস তাঁর সারা জীবনের সব কাজের মধ্যেই ছড়িয়ে গিয়েছে।
আরও পড়ুন: গুপ্তধনের সন্ধানে
‘চৌরঙ্গী’ পত্রিকা যে বিন্যাসে ও বিস্তারে জোছন দস্তিদারের জীবন আর কাজকে ধরতে চেয়েছে, তা ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকের সংলাপ-সম্ভাবনাকেই জায়মান করে তোলে। তাঁর নিজের লেখালিখি ও বিভিন্ন সময়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারগুলি সংকলিত হয়েছে ‘স্বগতোক্তি’ এবং ‘থিয়েটার প্রসঙ্গ’ পর্বে, যা আদতে বাংলা নাটকের ক্রমবিবর্তনের পদছাপটিকে স্পষ্ট করে দেয়। মার্কসবাদী বীক্ষা চৈতন্যে নিয়েই সেদিন যাঁরা দেশ ও সমাজভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, তার একটা রূপরেখা এই লেখাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি নিজে তাঁর পারিবারিক সূত্রেই এই সাম্যের দর্শনে পৌঁছেছিলেন। বুঝেছিলেন, মানুষের কথা বিশেষত বহু মানুষের মঙ্গলের কথা যদি ভাবতে এবং বলতেই হয়, তাহলে এই দর্শন নির্বিকল্প। বিশ্বের রাজনীতিও তখন নতুন একটি অভিমুখেই এগিয়েছিল। তবে, সমাজ বদলের সে-পথ যে মসৃণ হতে পারে না, তা সহজেই অনুমেয়। সংকট এবং লড়াই সেখানে অবধারিত। এই ভাবনার ভরকেন্দ্রে দাঁড়িয়েই শিল্পের অভিপ্রায় খুঁজতে ও বুঝতে গিয়ে প্রায় অনিবার্য ভাবেই তাই যেন তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন উৎপল দত্ত নামে এক আলোর কাছে– ‘এইরকম এক রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে সচেতন দায়বদ্ধ নাট্যকর্মীদের কী করা উচিত, উৎপলদা কয়েক রাত দিন পরিশ্রম করে লিখে এনেছেন। তিনি পড়লেন। আমি মুগ্ধ। সংস্কৃতি যে বিপ্লবের ধারাল এক অস্ত্র হতে পারে উৎপলদার লেখার যুক্তিতে কত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল আজও আমার মনে আছে। আবিষ্কার করলাম তাত্ত্বিক উৎপল দত্তকে। মনে মনে তখন তাঁকে গুরু মেনে, নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি বললে কমই বলা হবে।’ জীবনের এই পর্ব নিয়ে যখন লিখেছেন, বাংলা নাটকের দিকচিহ্ন নিয়ে নিজের ভাবনার কথা তাঁর যে লেখালিখিতে উঠে এসেছে, সেই সূত্রে আমরা সেই সময়ের চিন্তাবিশ্বটিকেই চিনতে পারি। সংস্কৃতি জগতে এক পরম্পরার সন্ধানও পাই। যে-আলোয় পড়ে নেওয়া যায় জোছন দস্তিদারের নিজের নাট্যভাবনাকেও। পরবর্তী পর্যায়ে বহু গুণীজনের স্মৃতি, যা বিন্যস্ত হয়েছে ‘সমালোচকের কলম’-এ, ‘শিক্ষকের ভূমিকা’য়, ‘অনুজের প্রণাম’ ইত্যাদি পর্বগুলিতে– সেখানে এই কথাটাই ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। আদল পেয়েছেন একজন সামাজিক দায়বদ্ধ সাংস্কৃতিক কর্মী। যাঁর ভাবনা ও নির্মাণের সঙ্গে মানুষের ভাবনা জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোত ভাবেই। আবার একই সঙ্গে এই সাক্ষ্যও মেলে যে, সেই সৃষ্টি কোনও ভাবেই নন্দনতত্ত্বকে ছলনা করে না। মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বে যেভাবে নান্দনিক ও ঐতিহাসিক– দু’টি দিককেই গুরুত্ব দেওয়া বিধেয়, তাঁর নাট্যভাবনাও সেই পথেরই অনুবর্তী। বহু বয়ানের ভিতর থেকে পাঠক তাই আবিষ্কার করেন সেই মানুষটিকে, যিনি শিল্প দিয়েই মানুষকে সর্বোত্তম স্বীকৃতি দিতে চাইছিলেন। সেটিই তাঁর সংস্কৃতির সচেতন চিহ্ন, এবং একই সঙ্গে রাজনীতির জোরাল বয়ানও।
আরও পড়ুন: ইউরোপের তিন দেশের গল্প, কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে অনুবাদ ও পাঠ
এর ভিতর কি কোনও সংকট নেই? আছে। সময় বদলাতে থাকলে রাজনৈতিক দর্শনও বহু প্রশ্ন এবং অন্তর্গত সংকটের মুখে পড়ে। যে মতবাদে সাংস্কৃতিক কর্মী বিশ্বাস করেন, সেই মতবাদেরই অনুসারী দল যখন ক্ষমতায় এসে ক্ষমতার চরিত্র আয়ত্ত করে ফেলে, তখন যে স্ববিরোধের জন্ম হয়, তা একজন শিল্পীকে ক্রমাগত ফালাফালা করে ফেলতে থাকে। জোছন দস্তিদারও ব্যতিক্রম নন– ‘অনেক কিছু মনোমতো না হলেও, সমর্থক হয়ে তার সমালোচনা করা যায় না। সমালোচনা করলে যে ক্ষতিটা হবে, তার ফায়দা তুলবে আর একদল, যে দলকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। ফলে অনেক সত্যই বলতে পারা যায় না। আমার পক্ষে সেই পিরিয়ডটাই চলছে।’ এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৯৮ সালে, যে সময়ে শুধু এ রাজ্য নয়, গোটা ভারতবর্ষেরই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বুননে একটা বড় বদল ঘটে গিয়েছে। ফলে শিল্পীর এই যে সংকট, তা ব্যক্তিগত নয়। খেয়াল করলে দেখা যায়, একটা সংকটকালের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মোকাবিলা করতে করতে তিনি এসে পৌঁছলেন নবতর এক সংকটে। কোন দর্শনে বা কোন সংস্কৃতিতে তার মুখোমুখি হওয়া যায়? উত্তর ভাবীকালের হাতেই ন্যস্ত। তবে, থিয়েটার ছাড়া অন্য শিল্প মাধ্যমেও যে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সফল কাজ করা যায়, সে নমুনাও তিনি রেখে গিয়েছেন।
অতএব জোছন দস্তিদার এই সময়ে এক অবশ্যপাঠ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ও কাজে তিনি ইতিহাসের পরম্পরা মেনেই বহুদূর হেঁটেছেন, এবং নতুন এক ইতিহাসের মুখে এসে নতুন সম্ভাবনার ইশারাটুকু দিয়ে গিয়েছেন। আজ যখন মানুষ-বর্জিত অসার শিল্পের রাজনীতি ক্রমশ মানুষকেই সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরগামী করে তুলেছে, তখন এই ভাবনাবিশ্বের কাছে ফেরাটাই সময়সচেতন জরুরি পদক্ষেপ। ‘চৌরঙ্গী’ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন, সময়ের কাজটি সময়ে করার জন্য।
চৌরঙ্গী: জোছন দস্তিদার সংখ্যা
সম্পাদক: শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মূল্য ৪৪০ টাকা
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
