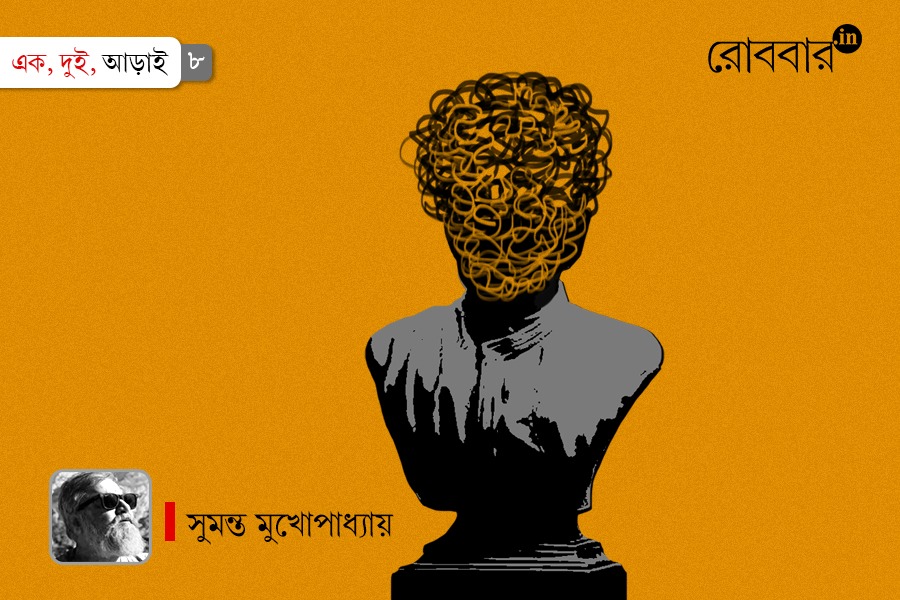
বাজারে দেখা সহাবস্থান থেকে শুরু করে এই ছড়িয়ে থাকা ইমেজগুলোর ধরন-ধারণ গভীরভাবে পড়তে পারলে আমাদের এই মুহূর্তের রাজনৈতিক বাস্তবতাটার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দৃশ্য নিয়ে কোথাও কোনও কন্টিনিউটি নেই। নিত্য ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে খবর আসছে। সেটা ধরতে পারলে বেশ হত। সব যেন কাটা ঘুড়ির মতো ফসকে যাচ্ছে। অথচ তাঁতের শাড়ির ডিসাইনে, ব্লক প্রিন্টের ছাপে, নকশার কতদিনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ রামকিংকর-কে বলেছিলেন আশ্রমের ভেতরটা তুই এইরকম কাজ দিয়ে ভরে দে। আর কলকাতার পথঘাটের মূর্তি দেখে রামকিংকরের মনে হয়েছিল মেরে-কেটে খান তিনেক। বাকি আবর্জনা।

ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।
………………………….
৮.
সন্ধেবেলা মাছের বাজার থেকে বেরিয়ে চোখে ধাঁধা লেগে গেল। বাজারের ঠিক মাঝ-বরাবর তিনজোড়া স্পট তক্ষুনি জ্বলে উঠেছে। একই সঙ্গে এই শহরে ৫০ পার করা বন্ধু, ছোটা বলে উঠল: ‘যাঃ শালা! এরা আবার কে?’ ততক্ষণে চোখ সয়ে এসেছে, তিনটি দেড় হাত প্রমাণ আবক্ষ মূর্তি আমাদের এনকেডিএ বাজারের নতুন সংযোজন। বললাম, ‘ভালো করে দেখ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বোধহয়।’ আমাদের এই বাজারটা ছোটা-র অঞ্চলের সঙ্গে যেমন মেলে না তেমনই ছোটবেলার বরানগর বাজারের সঙ্গেও মিশ খায় না। এর মধ্যে একটা গঞ্জ-বাজার ভাব আছে। এমন অনেক ধরনের জিনিস এখানে দেখা যায়, যা তুমি মানিকতলা বাজারে পাবে না। যদিও ‘জামাই’ নামক জনৈক মৎস্য ব্যবসায়ী মাঝখানে আধুনিকতার আশায় অক্টোপাস বিক্রি করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাটাকাটিতে ভুল করে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকটা পাড়ায় বাজারে অঞ্চলে কয়েকজন থাকে– যাদের ‘জামাই’ বলে ডাকাই রেওয়াজ এবং অধিকাংশ সময়ে এরা তাদের অদেখা, অভাগা শ্বশুরের নাম ডুবিয়ে এলাকা ছাড়ে! তবে বাজারের বাইরের তিনজন ভারতবিখ্যাত মানুষ সেরকম কেউ নন। এঁরা বামদিক থেকে যথাক্রমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, বিবেকানন্দ এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর। আম্বেদকরের পোশাক, মানে কলার থেকে বুক পকেট কটকটে নীল। বিবেকানন্দ– গেরুয়া। আর নেতাজি জলপাই সবুজ। এই ত্রিদেব বা তিনমূর্তি দেখে ছোটা, আমাদের আশৈশব বন্ধু, ঘাবড়ে যায়। কারণ এর আগে আমরা কেউ এই তিন জন-কে একসঙ্গে এইরকম রং আর আধহাত দূরত্বে দেখিনি। দেখার কথাও নয়। ভারতের কাহিনি ঠিক কোন যুক্তি মেনে এঁদের পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে গেল, সেইটাই ভাবনার বিষয়। ফলে, সব তালগোল পাকিয়ে গিয়ে ওই স্বগতোক্তি– যাহ শালা! সাদা খোপ খোপ টাইলসে ঢাকা একটা পাঁচিলের মতো জিনিসের ওপর ওঁদের বসানো হয়েছে। সামনে একটা হাঁটু সমান পিলার আড়াআড়ি কাটা। তার বুকে লেখা শহিদ বেদি। মাঝখানে ফুটো। বিশেষ বিশেষ দিনে এখানে হয়তো পতাকা উত্তোলন হয়।
এই তিন মূর্তির ব্যাপার-স্যাপার আমাদের খুব অপরিচিত নয়। ১৯৭৭ সালে, অমর-আকবর-অ্যান্টনি বোধ করি মুক্তি পায়, এই তিনটি নায়ক ভাগ্যের ফেরে হারিয়ে যাওয়া তিন ভাই। হিন্দু, মুসলমান আর খ্রিস্টান ধর্মের ছায়ায় বেড়ে উঠেছিল। জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও ত্রিধারায় কারও কোনও সমস্যা ছিল না। যে যার মতো তস্য তস্য সঙ্গিনী নিজ নিজ ধর্মেই খুঁজে পান। নাচে-গানে-মেরে-কুটে-হেসে-কেঁদে এ-জিনিস আমরা দেখেছি। ভাই বেরাদরি নেই কিন্তু শত্রু নিধনে তিন-মূর্তির আগমন বার্তা রেডিওতে শুনতে পাচ্ছি, ১৯৮৪ সালের পুজোর আগে কি? তিইইইইইন মূউউউরতি– পথ হল বন্ধুর এই তিন মূর্তি আজ থেকে তলোয়ার হয়ে/ হাতে শুধু জ্বলব। ধর্মেন্দ্র, ড্যানি আর মিঠুন চক্রবর্তীর সেই লীলা ১০ বছর বয়সে প্রত্যক্ষ না করলেও আরও ৫ বছর পর ‘ত্রিদেব’ দেখেছিলাম। নাসিরুদ্দিন শাহ, সানি দেওল আর জ্যাকি শ্রফ। তিন দেবতা, ট্রিনিটি, তিন বন্ধু, তিন ভাই, তিন ডাইনি, তিন বুড়ো পণ্ডিত– এই রকম নানাবিধ তিনের চক্করে বড় হয়ে উঠেও বাজারের এই মূর্তি তিনটিকে বোঝা গেল না। এ কি বাজার কমিটির মাথা থেকে বেরল? না কি এনকেডিএ? মানে নিউটাউন ডেভলপমেন্ট অথরিটি? বাজারটায় যত দোকান, তাতে শাক-সবজি, মাছ আর খাসির মাংস বিক্রি করেন রাজারহাট বা আরেকটু দূরের মানুষজন যাদের অধিকাংশই ধর্মাচরণে মুসলমান। বাকি বিক্রেতারা অপেক্ষাকৃত কাছের, নিউটাউন লাগোয়া জনবসতি থেকে আসেন। অধিকাংশই বাংলার আজব ইতিহাসের হাতে দাগা খাওয়া মানুষ, কেউ কণ্ঠিধারী, কেউ শাক্ত– কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রায় নেই। নমঃশূদ্র অথবা জাত-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ।
এবার কলকাতার রাস্তাঘাটে, অথবা পশ্চিম বাংলার পথেঘাটে একবার যদি ঘুরে তাকানো যায়, আম্বেদকারের মূর্তি ক’টা আছে? স্বাধীনতা পরবর্তী ৮০ বছরের ইতিহাসে বাংলায় আম্বেদকরের মূর্তি লাগানো হয়নি কেন? বরিশালের যোগেন মণ্ডল এ-ধাঁধার উত্তর দিতে পারতেন। আম্বেদকরকে বাংলা থেকে ভোটে জিতিয়ে ১৯৪৬-র কন্সটিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে পাঠানো নিশ্চিত করেন যোগেন মণ্ডল। বাংলায় সিডিউল কাস্ট ফেডেরেশনের শাখা সংগঠন খোলেন তিনিই, আম্বেদকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে । বাংলার বিপুল তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষের নেতা হয়ে তিনি মুসলিম লিগে যোগ দেন এবং তাঁর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের প্রথম শ্রম-আইন মন্ত্রী হিসেবে যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ হয় ১৯৫০ সালে। ইতিহাসের এই গোলকধাঁধায় পশ্চিম বাংলায়, প্রথমত কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে শ্রেণিসচেতন রাজনীতি আম্বেদকারকে বাজারের মাঝখানে বসাতে ভুলে যায়। সুভাষচন্দ্র আর আম্বেদকরের রাজনীতি এক ছিল না। নেতাজির থেকে বয়সে ৬ বছরের বড় আম্বেদকর গান্ধীকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। নেতাজি অন্তর্ধানের পর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে আম্বেদকর জানান ব্রিটিশ এদেশে তল্পিতল্পা গুটানোর কারণ গান্ধীবাদী আন্দোলনে নেই। আইএনএ-র গঠন এবং বিচারের সময় নেভি-র বিদ্রোহে টের পাওয়া যায় ভারতীয় মিলিটারি ইংরেজদের কথা শুনে চলতে না-ও পারে। আর এই ভয় থেকেই সাম্রাজ্যের অস্তগতি। আম্বেদকরের এই ব্যাখ্যা ঠিক না ভুল– সে তর্ক এখানে তুলে লাভ নেই। কিন্তু তফসিলি জাতির মানুষদের নিয়ে আম্বেদকারের প্রশ্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র লাগসই জবাব খুঁজে পাননি। একটু দূরত্বেই ছিলেন দু’জন। সুভাষচন্দ্র মিলিটারি ফৌজ গঠনের আগে দুই রাজনীতিবিদ অন্তত একটি মিটিং করেছিলেন বম্বে-তে। ১৯৪০ সালের ২২ জুলাই। সেখানেই সুভাষচন্দ্রের অবস্থান ভালো করে বুঝতে পারেননি আম্বেদকর। এই এত কথা বলতে চাইছি আমাদের চারপাশের প্রতিদৈনিক দেখা-শোনা-বোঝার বড় রকম অদল-বদলের দিকে তাকিয়ে। এঁদের দু’জনের মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দ এলেন কীভাবে? সুভাষচন্দ্র যে নানা ভাবে বিবেকবাণী-তে ছোটবেলা থেকেই মজে ছিলেন সেকথা জানা সবার। আম্বেদকরের কাছেও গান্ধী নন, বিবেকানন্দই ভারতের গত শতকের মহোত্তম মানুষ। নতুন ভারত কোথা থেকে বেরবে– তার সুলুক সন্ধান বিবেকানন্দের লেখায় যা পাচ্ছি, আম্বেদকরের স্বপ্নেও সে পথের কিছু মিল ছিল।
তাহলে এই যৌগপত্যের মূল ভাবনাটা হল বাঙালি মধ্যবিত্তের দুই স্বপ্ন-পুরুষ ধর্ম আর রাজনীতির টানে এই বাজারের মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আর সঙ্গে থাকলেন আম্বেদকর, গত বছর ৫০-৬০ ভ্যানিশ হয়ে থাকার পরে তাঁকেও আবার দরকার পড়েছে। চোখের সামনে রোজ যা দেখছি, শুনছি তার একটা গভীর রাজনীতি আছে। একটি মূর্তিতে কাজ চলছে না, চারপাশ আজকাল তাই ছেয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে জুড়ে থাকা কোয়ালিশন ভাস্কর্যে। আর ধর্মীয়ভাবে মূর্তি-ছবিতে যেসব মানুষের বিশ্বাস নেই, তাদের উপস্থিতির হিসেব একা নজরুল ইসলামকে দিয়ে হবে কী করে? সেই রাজনীতির ইতিহাস বয়ান চোখের সামনে থাকছে কোথায়? একটা বিপুল রাজনৈতিক মতামত চোরাপথে তাই চালান হয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের জানা-বোঝার বাইরে কোথাও।
একজন ট্রেন-ফেরিওলা খুব মজা করে বলতেন ‘এই এসে গেছে বাবার উল্টোডাঙা ছেলের বিধাননগর’। সেই বিধানগরে স্টেশন পার করে যে বিপুল আকার হনুমানটি গত দশ বছর ধরে মুচিবাজারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে রামনবমীর ঠিক আগে বসানো হয়। মাথায় মস্ত ছাতা ছিল। আমফান ঝড়ের দিনে সে ছাতা হয়তো ভেঙে পড়ে। এখন একটি সীতা ছাতা ফিট করা হয়েছে। দিনকয় আগে রং করে আগের ছেয়ে পেশি-টেশিগুলি উন্নত করা হয়েছে। অই পথে খানিক দূর এগিয়ে গেলে বামদিকে দেখা যাবে বিবেকানন্দ রথে করে চলেছেন। পিছনে যে বসতি আছে সেটি সৌন্দর্যায়ন পলিসির ফাইবারে ঢাকা। তার ঠিক পাশেই বিপুল একটি শিব মূর্তি। শিবের রং নীল, বিবেকানন্দ গেরুয়া। সামঞ্জস্যের কোনও বালাই নেই। উল্টোফুটের কাউন্সিলর আলাদা। সেখানে ঝুলন সাজের মতো পর পর সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে আছে। আঙুর ফল টক, একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়া ছিল, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে– এই রকম অজস্র। আর ল্যাম্পপোস্টে নানা বাঙালি আইকনের ছবি। সব ক’টার নীচে লেখা এ কে রাউত। মানে চুনি গোস্বামী হাসছেন, এ কে রাউত। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়– এ কে রাউত। চলেছে। আর খান্নার দিকে এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে বহু বছরের বিধায়ক মানুষটির মৃদু হাসি মুখ সম্বলিত বিশাল ব্যানার। ঝড়ে ছিঁড়ে যায়, হাওয়ায় ফেঁড়ে যায়, না জানি কীসে ফেঁসে যায়, তবু বার বার বদলে বদলে চার বছর ধরে তাঁকে সাদা-কালোয় স্মরণ করে আঞ্চলিক মানুষ জানিয়ে দেন– ‘তুমি রবে সরবে, মানিক তলার মননে’।
নেতা-ত্রাতা মানুষ অমর্ত্যধামে গিয়ে নীরবে থাকবেন এমন দুঃস্বপ্ন রবীন্দ্রনাথও দেখেননি। আর বাংলা সংস্কৃতি অনেক দিনই ‘প্যারডি’ নির্ভর। আছেই যখন ওটাকেই টিপেটুপে নিজের বলে চালিয়ে দি’, এরকম একটা বিষয়। ভাণ্ডারও বিপুল। সবই ঠিক আছে, কিন্তু ওই দৈববাণীর মতো ঊর্ধ্বকমা দু’টি দু’ধারে কে দিলে রাঙিয়া? সেইটে বড় জানতে ইচ্ছে হয়। যাই হোক, বলছি চারপাশে যা দেখি– তা কিন্তু শুধুই ইউনেস্কো লাঞ্ছিত দুর্গাপুজো নয়। পাবলিক আর্টের একটা ইতিহাস লেখা উচিত। বিশেষত ফাইবারে তৈরি গত ১২ বছরের মূর্তিগুলোর। কোমর পর্যন্ত দু’টি পা, না, নীচ দিয়ে নয়, সে মূর্তির পেট ফেটে বেড়িয়ে এসেছে হাফ ফুটবল! বাকিটা ভেতরে হজম হচ্ছে। এই রকম আশ্চর্য সব ব্রাঁকুশি-বোবা কীর্তি বাংলার পথঘাটে জমে আছে।
বাজারে দেখা সহাবস্থান থেকে শুরু করে এই ছড়িয়ে থাকা ইমেজগুলোর ধরন-ধারণ গভীরভাবে পড়তে পারলে আমাদের এই মুহূর্তের রাজনৈতিক বাস্তবতাটার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দৃশ্য নিয়ে কোথাও কোনও কন্টিনিউটি নেই। নিত্য ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে খবর আসছে। সেটা ধরতে পারলে বেশ হত। সব যেন কাটা ঘুড়ির মতো ফসকে যাচ্ছে। অথচ তাঁতের শাড়ির ডিসাইনে, ব্লক প্রিন্টের ছাপে, নকশার কতদিনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ রামকিংকর-কে বলেছিলেন আশ্রমের ভেতরটা তুই এইরকম কাজ দিয়ে ভরে দে। আর কলকাতার পথঘাটের মূর্তি দেখে রামকিংকরের মনে হয়েছিল মেরে-কেটে খান তিনেক। বাকি আবর্জনা। আবস্ট্রাকশনের ভেতর বিষয়ের অবস্থা আর অবস্থান্তর থাকে– সেটা উৎকট নির্মাণে ধরা পড়ে না। এই নানা ধরনের উপস্থাপনা দেখতে দেখতে মন একটা প্রশ্ন-উত্তরের পর চোখের মনের ওপর নির্ভর করতে পারে। দেখতে শেখা খুব বড় শেখা। ভারতে এই দৃশ্যনন্দন হাজার বছর ধরে সবার জন্য তৈরি করা ছিল। তাই একটা সামঞ্জস্য এখনও কাপড়-জামার ভেতর টের পাই। তবে যে যুগ পড়েছে বেশিদিন আর সে সুযোগ পাব বলে মনে হয় না। জয় গোস্বামীর লেখা উন্মাদের পাঠক্রম যুগলক্ষণ তাক করেই বলা। তখন আর কীসের সঙ্গে কী, পান্তা ভাতে ঘি।
… এক, দুই, আড়াই-এর অন্যান্য পর্ব …
৭. ভাবা প্র্যাকটিস করা, কঠিন এখন
৬. লেখার অত্যাচার, লেখার বাঁচা-মরা
৫. বিশ্বকর্মা পুজোর সন্ধেবেলাটার মতো বিষাদ আর হয় না
৪. কথা শেষ হতে পারে, ‘শেষ কথা’ বলে কিছু হয় না
৩. দেখা হলে বলে দিও, আজও বেঁচে আছি
২. ফুলের রং শেষ পর্যন্ত মিশে যায় নন্দিনীর বুকের রক্তের ইমেজে
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
