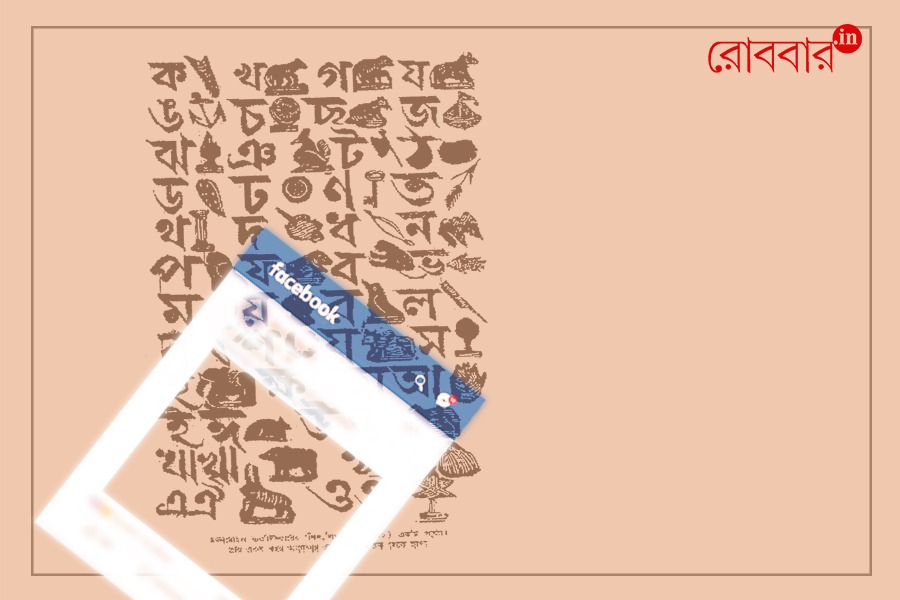
এক প্রকাশক বইয়ের বিজ্ঞাপনের শিরোনাম দিলেন মননশীলতার অভিব্যক্তি। ধরা যাক, কোনও এডিটর যদি কেটে করতেন মননের প্রকাশ! ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করতে পারি ঠিক পছন্দ হত না তাঁর। বলতেন, না বাংলাটা ঠিক ভালো হচ্ছে না। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ। প্রচ্ছদ দীপঙ্কর ভৌমিক

আজ আবার একুশে ফেব্রুয়ারি। বর্ষে বর্ষে যে-একুশে আসে এবং আমাদের আবেগময় বাংলা-ধারা উপচে উপচে পড়ে। তদুপরি এই একুশে আসে বাঙালির বচ্ছরকার আর এক বাংলা-ধারা-বাহিক বইমেলার কয়েক দিন পরেই। তার ফলে আহা, আজি এ বসন্তে বাঙালিটোলা বাংলা-ধারায় একেবারে গড়াগড়ি যায়।
রসের স্রোতে সেই রঙিন গড়াগড়ি চেয়ে চেয়ে দেখলেই ভালো হত। কিন্তু দু’-একটি উদাহরণ টেনে নেওয়ার লোভ সামলানো গেল না। তারা দু’-এক খণ্ড মাত্র, তবু তারাই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেয় মাতৃভাষারূপ খনিটি কেমন মণিজালে পূর্ণ। চারদিকের ব্যবহারের বাংলা ভাষার দিকে তাকান, চোখে পড়বে লজিক্যাল নয়, ভেগোলজিক্যাল প্রয়োগের বিবিধ নমুনা। যেমন, এক প্রকাশক বইয়ের বিজ্ঞাপনের শিরোনাম দিলেন মননশীলতার অভিব্যক্তি। ধরা যাক, কোনও এডিটর যদি কেটে করতেন মননের প্রকাশ! ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করতে পারি ঠিক পছন্দ হত না তাঁর। বলতেন, না বাংলাটা ঠিক ভালো হচ্ছে না।

এই ভালো বাংলা, খারাপ বাংলা ধারণাগুলো আমাদের মধ্যে সেই স্কুলজীবন থেকেই চারিয়ে যায়। ভালো বাংলা মানে বেশ তথাকথিত ভালো ভালো শব্দ আছে যে বাংলায়। মানে ওই শুকনো কাঠ না বলে ‘নীরস তরুবর’ বলার মতো আর কী! এরই জন্য আমরা ভাবি এক রকম আর সভাসমিতিতে বলি বা লিখি আর এক রকম করে। আর ওই ‘ভালো বাংলা’র কথাটা সারাক্ষণ আমাদের ভয় দেখায় বলে ছড়িয়ে ফেলি। যেমন, আর একটি উদাহরণ, কোনও এক পুরনো লেখিকার রচনাসমগ্রের ব্লার্ব: সেখানে শুধু নারীপুরুষের সমানাধিকার বোধের সাম্য নয়, রোম্যান্সও ধরা পড়েছে অবগুণ্ঠনহীন চেহারায়।
সোজা কথা সোজা করে না বলে এই যে ঘোমটা পরিয়ে আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে বাংলা ভাষায়, তার জন্যও ইংরেজি-লালিত নতুন প্রজন্ম দূরে সরে যাচ্ছে এই ভাষাটা থেকে। এক প্রয়াত প্রখ্যাত গণিতবিজ্ঞানী সাধারণের জন্য বাংলায় গণিত নিয়ে লিখতে গিয়ে ভাষাটিকে প্রায় অবোধ্য করে তুলেছিলেন। তার কারণ, তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, ইংরেজিতে ভেবে বাংলায় লেখা। আর আমার ছোটবেলার স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক পইপই করে বলতেন, ওরে ইংরেজিতে ভাবতে আর স্বপ্ন দেখতে পারলে তবেই ইংরেজিতে সুন্দর করে লিখতে পারবি।
……………..
বাক্য যেমন, শব্দও তেমন মাঝে মাঝে বাঙালিটোলার বাংলা-ধারার বশে মাথায় চড়ে বসে। তখন কিছু কিছু শব্দের মায়া আর ছাড়তেই চায় না। শব্দের সার্কাস একদা কবিত্বের এবং কবিওয়ালাত্বের মাপকাঠি ছিল। তার পরে বিখ্যাত মানুষদের সৃষ্টি-নাম দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর নামাবলি হল। তার পরে জটায়ুর প্রভাবে হরিদ্বারে হাহাকার কিংবা গোলকোন্ডায় গোলমালের ছড়াছড়ি হল সংবাদ-হেঁশেলে। আর এখনও জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ, বিতর্ক তুঙ্গে, স্ববিরোধের দোলাচল, শিল্পসম্মত এমন সব শব্দ-ব্রহ্ম বেহ্মতালু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে।
……………..
তলিয়ে দেখলে এখন বুঝতে পারি, যে সরস্বতীর চেয়ে হাঁসটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়েই যত বিপত্তি। চিন্তার চেয়ে চিন্তার বাহন ভাষাটাকে নিয়ে আমাদের এই বেশি মরি মরি ভাবটাই যত নষ্টের গোড়া। একেই সুকুমার রায় বলেছিলেন ভাষার অত্যাচার: যে কারণে মানুষ শাস্ত্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাহার অনুশাসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, ঠিক সেই কারণেই মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতগুলি বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। এ অবস্থায় বাক্য যে মাথায় চড়িয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কী?
মাথায় উঠে গেলে সত্যিই কেলেঙ্কারি হয়। বাক্যি তখন এত সরতে থাকে যে ভেগোলজি ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞান দিয়েই সেই নিঃসরণের ব্যাখ্যা চলে না। এ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য এবং একমেবাদ্বিতীয়ম বিজ্ঞানী পরিমল রায় অর্ধশতাব্দেরও বেশি আগে বিজ্ঞানটির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছেন:
‘ভেগোলজি কথাটি ‘ভেগাস’ এবং ‘লোগোস’ এই দুইটি প্রাচীন শব্দের সমন্বয়ে উৎপন্ন। প্রথমটির অর্থ পথ বিলাস। নিছক কতকগুলি জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ পরিবেশে যথেচ্ছ বিচরণের যে-আনন্দ, ভেগোলজি তাহারই পরিবেশক। যেখানে গন্তব্য নাই অথচ গমন আছে, ক্ষুধা নাই অথচ ভুঞ্জন আছে, বক্তব্য নাই কিন্তু বাক্য আছে,– অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় সন্ধান-বিকৃত মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বে লক্ষ্যনিরপেক্ষ নভোচারী চিলের মতো কেবলমাত্র ভাসিয়া বেড়াইবার উৎসাহ আছে, সেখানেই ভেগোলজির প্রকৃষ্টতম প্রকাশ।’
বাক্য যেমন, শব্দও তেমন মাঝে মাঝে বাঙালিটোলার বাংলা-ধারার বশে মাথায় চড়ে বসে। তখন কিছু কিছু শব্দের মায়া আর ছাড়তেই চায় না। শব্দের সার্কাস একদা কবিত্বের এবং কবিওয়ালাত্বের মাপকাঠি ছিল। তার পরে বিখ্যাত মানুষদের সৃষ্টি-নাম দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর নামাবলি হল। তার পরে জটায়ুর প্রভাবে হরিদ্বারে হাহাকার কিংবা গোলকোন্ডায় গোলমালের ছড়াছড়ি হল সংবাদ-হেঁশেলে। আর এখনও জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ, বিতর্ক তুঙ্গে, স্ববিরোধের দোলাচল, শিল্পসম্মত এমন সব শব্দ-ব্রহ্ম বেহ্মতালু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে।
চিন্তা যদি লজিক্যাল হয়, নিজেই যদি নিজের ডেভিলস অ্যাডভোকেট হওয়া যায় লেখার আগে, তবে সহজেই বোঝা যায় নিজের শব্দচয়ন সম্পর্কে লেখকের গদগদ ভাবই গদ্যের উঠোনটিকে কুয়াশাচ্ছন্ন, ধুলোবালিময় করে দিচ্ছে। জনপ্রিয়তাকে শিখরে বা বিতর্ককে তুঙ্গে ওঠানোর আগে বুঝে ওঠা উচিত ওই শিখর বা তুঙ্গের মানদণ্ডটা কী। দোলাচলেই থাকলে স্ববিরোধটা কী করে ঘটান কেউ সেটা ভাবা দরকার। আর শিল্প কী করে কোনও কিছুর সম্মতি দেবে– সে প্রশ্নও করা দরকার।

এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদের কোনও লেখা লিখেই সেটা প্রকাশের জন্য হাঁকুপাঁকু না করে ফেলে রাখতে বলেছিলেন। এই জন্যই সে কালের সম্পাদকদের কেউ কেউ বার বার লেখকদের লেখা ফেরত পাঠাতেন। এই জন্যই লেটারপ্রেসের যুগে টাইপ ফাউন্ড্রিতে ফুটকির আকাল হওয়া ভাল ছিল। কিন্তু সে সব অতীতের ছবি। প্রকাশের জন্য সাধনা-টাধনা চুলোয় গেছে, ভাষাহারা সব বিজন রোদনও এখন এক ক্লিকেই পোস্টেড!
এই ‘পোস্ট’-মডার্ন যুগে বাঙালির আবেগায়িত কথামালার উঠোনটিকে নিকিয়ে না তুলতে পারলে বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে রোদ আজও ঝরবে কি?
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
