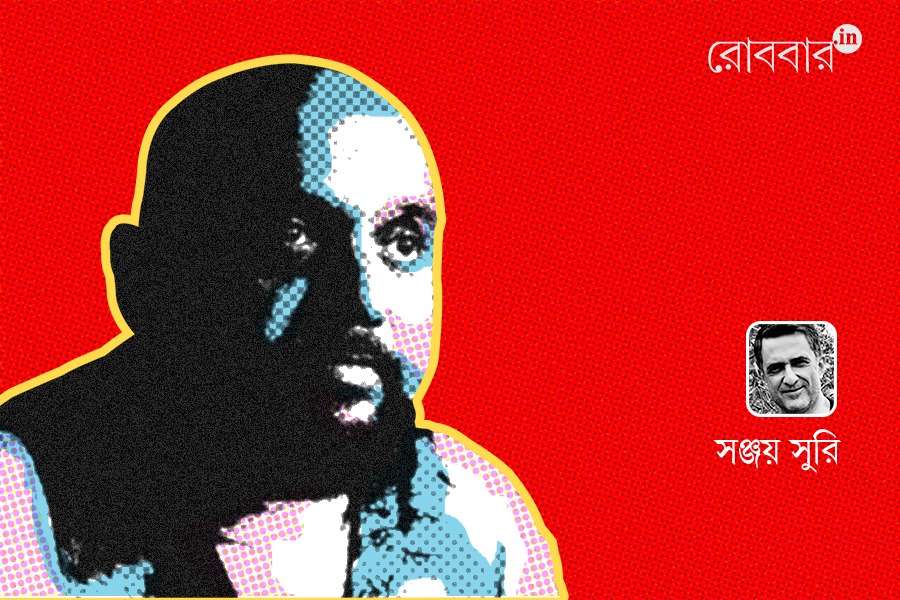
প্রীতীশ নন্দীর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল স্ক্রিপ্ট চেনার। সেই ক্ষমতাটা ছিল বলেই এত অন্য ধরনের সিনেমা করতে পেরেছেন তিনি। পরিচালক চিনেছেন, স্ক্রিপ্ট চিনেছেন, নতুন অভিনেতাদের চিনেছেন। এমন এমন সিনেমা বানিয়েছেন, যেগুলো কি না আজও প্রাসঙ্গিক। চাপা পড়ে থাকা, ধুলো জমে থাকা বিষয় নিয়ে সিনেমা করার ধক প্রীতীশ নন্দীরই ছিল। কিন্তু কোনও দিন নাক গলাননি কোনও সিনেমায়। কোনও পরিচালকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেননি, কখনও অভিনেতাদের এসে বুঝিয়ে যাননি। সেই যে ‘ঝংকার বিটস’-এর সময় ১০ মিনিটের মিটিং করেছিলাম, তারপর সিনেমার প্রিমিয়ারে আমাদের দেখা হয়। মাঝে তিনি উধাও।

২০০১-২০০২ সাল হবে তখন। নারিমান পয়েন্টে ওঁর অফিসে প্রথম আলাপ হয় প্রীতীশ নন্দীর সঙ্গে। আমি ভেবেছিলাম আমি এক প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কিন্তু কথা শুরু হতেই বুঝলাম আমার ভাবনা এক্কেবারে ভুল। আমি একজন শিল্পীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

প্রীতীশ নন্দীকে আমি দেখেছি শুধুই একটা সিনেমার ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে কথা বলতে। ব্যবসায়িক চিন্তাগুলো বোধহয় রঙ্গিতা বেশি দেখতেন। প্রীতীশ নন্দীর কাছে সেটা মুখ্য বিষয় ছিল না। বরং তাঁর কাছে ওই দর্শনটা জরুরি ছিল, প্রীতীশ নন্দীরই সেই সাহসটা ছিল অপ্রচলিত ভাবনাগুলোকে নিয়ে সিনেমা করার। শুধু ‘ঝংকার বিটস’ নয়, ‘হাজারো খোয়াইশে অ্যায়সি’, ‘সুর’, ‘চামেলি’, ‘কাঁটে’। খুব কম প্রযোজকই এমন ছিলেন বলিউডে, যে অপ্রচলিত পথে, অচেনা পথে হাঁটতে পেরেছিলেন। আর ছিল নতুন মানুষের প্রতি আস্থা। কত নিউ কামারকে তিনি জায়গা দিয়েছিলেন, যেমন সুজয় ঘোষ। যতদূর মনে পড়ছে, এর আগে সুজয় কারও সহযোগী হিসেবে কার করেননি, তবুও সুজয়ের প্রতি এই আস্থাটা তাঁর তৈরি হয়েছিল। তিনি আসলে দেখতে পেয়েছিলেন সুজয়ের দর্শন, সুজয়ের ক্ষমতা।

আমার মনে আছে প্রথমবার দেখা হওয়ার পরই প্রীতীশ নন্দী আমার প্রথম সিনেমা ‘প্যায়ার মে কভি কভি’-র প্রশংসা করেছিলেন। মাত্র ১০ মিনিটের মিটিং হয়েছিল। তাতেই আমি প্রীতীশ নন্দীর এনার্জিটা বুঝতে পেরেছিলাম। খুব পজিটিভ একটা এনার্জি– চলো সিনেমাটা হয়ে যাক– এমন কথা বলে সবাইকে উত্তেজিত করে দিয়েছিল সিনেমাটার প্রতি। প্রীতীশ নন্দীর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল স্ক্রিপ্ট চেনার। সেই ক্ষমতাটা ছিল বলেই এত অন্য ধরনের সিনেমা করতে পেরেছেন তিনি। পরিচালক চিনেছেন, স্ক্রিপ্ট চিনেছেন, নতুন অভিনেতাদের চিনেছেন। এমন এমন সিনেমা বানিয়েছেন, যেগুলো কি না আজও প্রাসঙ্গিক। চাপা পড়ে থাকা, ধুলো জমে থাকা বিষয় নিয়ে সিনেমা করার ধক প্রীতীশ নন্দীরই ছিল। কিন্তু কোনও দিন নাক গলাননি কোনও সিনেমায়। কোনও পরিচালকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেননি, কখনও অভিনেতাদের এসে বুঝিয়ে যাননি। সেই যে ‘ঝংকার বিটস’-এর সময় ১০ মিনিটের মিটিং করেছিলাম, তারপর সিনেমার প্রিমিয়ারে আমাদের দেখা হয়। মাঝে তিনি উধাও। একটা সিনেমা চালু করে দিয়ে তিনি অন্যদিকে চলে গেছিলেন। হ্যাটস অফ প্রীতীশ নন্দী।

অন্য প্রযোজকদের সঙ্গে কী পার্থক্য ছিল প্রীতীশ নন্দীর? অন্য প্রযোজকরা হয়তো ব্যবসার কথা ভাবছেন, সেই চিন্তার কথা মুখেও বলছেন। প্রীতীশ নন্দী ব্যবসার কথাটা কখনও আমাদের সামনে উচ্চারণ করতেন না। কিন্তু নিশ্চয় তিনি ভাবতেন, নিশ্চয় তিনি সেই বিষয়েও নজর রাখতেন। কিন্তু সেটা বলে কলাকুশলীদের ওপর চাপ বাড়াতেন না। প্রীতীশ নন্দী শুধু সিনেমার উৎকর্ষের কথাই উচ্চারণ করতেন। ‘আশক’ বলে একটা সিনেমার কথা হয়েছিল প্রীতীশ নন্দীর সঙ্গে। অনেক দূর কথাও এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ সেটা হয়নি। এখন খুব আফশোস হচ্ছে।
প্রীতীশ নন্দীর চলে যাওয়া আসলে শিল্পের ক্ষতি হওয়া। যে শিল্পীসত্তাকে তিনি সকলের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
