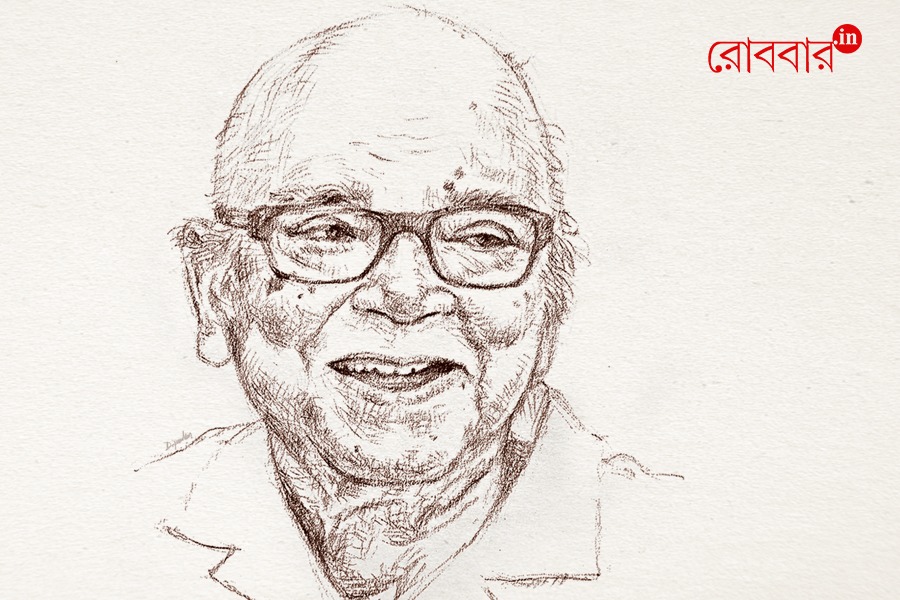
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন কিংবা চলনে সাধারণ মানুষের যে অসহায়তা, যে আকাঙ্ক্ষা, যে স্বপ্ন-ব্যর্থতা সেসবকে ধরে মনোজ মিত্র তার ভিতর থেকে অদ্ভুতভাবে একটা গল্পকে আমাদের সামনে হাজির করে, কীভাবে তার সঙ্গে চলতে হবে, তার পথ দেখিয়েছেন। ইতিহাস-পুরাণের ভিতর থেকে কোনও রাজার কথা হয়তো তিনি বলছেন, কিন্তু তা পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে, এই রাজা তো আমার মতোই চেনা মানুষ। দেবতা যেন পাশের পাড়ার বাসিন্দা। এই যে দূরস্থিত নানা বিষয়-ভাবনাকে টেনে নামিয়ে সাদারণের নাগালের মধ্যে এনে তাকে ফুটিয়ে তোলা, আমাদের সামনে পরিবেশন করা, এটা মনোজবাবুর মুনশিয়ানা।

‘নান্দীকার’-এ আমার অভিনয় জীবন শুরু বটে, তবে নাটক দেখার শুরুটা আরও আগে। আমি বিশ্বাস করি, নাটক দেখার মধ্য দিয়েও অনেক কিছু শেখা যায়, সেই শেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। আমিও সেভাবেই এগিয়েছি। যদিও জানতাম না, একদিন অভিনেতা হব। অভিনেতা যে হয়ে উঠলাম, তার নেপথ্যে এসবই মূল কারণ ছিল। সেই দেখার মধ্যে যেমন উৎপল দত্ত মানে পিএলটি-র থিয়েটার ছিল, যেমন ‘বহুরূপী’-র থিয়েটার মানে শম্ভু মিত্র পরবর্তী যে থিয়েটারের ধারা– তার সঙ্গে ছিল ‘নান্দীকার’ও। সেই টানেই নান্দীকার-এ হাজির হয়েছিলাম। এসবের বাইরে আরও একজন আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলেছিলেন– তিনি মনোজ মিত্র এবং অবশ্যই তাঁর ‘সুন্দরম’ নাট্যদল।
মনোজবাবুর একাধিক প্রযোজনা আমরা অ্যাকাডেমিতে গিয়ে সেসময় দেখতাম। এবং বলতে দ্বিধা নেই, অন্যান্য প্রযোজনার মধ্যে যে বৌদ্ধিক চলন, যে বুদ্ধিমত্তা, যার মাধ্যমে পিএলটি কিংবা নান্দীকার নাট্যজগতে একটা আলাদা ভাষ্য তৈরি করে, মনোজ মিত্র বা সুন্দরম-এর নাটকের মধ্যে তা তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল একটা সহজ গল্প বলার ধরন এবং সেই সহজ চলনের মাধ্যমে একটা গভীর কথা বা তত্ত্ব, এত সহজে উঠে আসত মনোজ মিত্রর নাটকে, যা আমাদের মুগ্ধ করত। সেই ভালোলাগার সূত্র ধরেই মনোজবাবুর সঙ্গে আলাপ।
যদিও, সেই আলাপের অনেক আগে থেকেই মনোজ মিত্রর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই লেখার অন্তর্নিহিত অর্থ সবটাই যে বুঝেছি, তা নয়। কিন্তু নাটকগুলোর মধ্যে যে মজা, সে ‘নরক গুলজার’ হোক বা ‘চাকভাঙা মধু’, কিংবা ‘রাজদর্শন’ – তুলনাহীন! আরও পরে গিয়ে তাঁর নাট্য-ভাবনাকে বুঝতে পেরেছি, যখন মনোজবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ হয়েছে। অবাক হয়ে ভেবেছি, ওঁর লেখার মাধ্যমে যে মানুষটিকে চিনি, যে কি না এইরকম অভূতপূর্ব সৃষ্টি করতে পারেন, আবার একইসঙ্গে যিনি অভিনেতা, আবার সংগঠনও করেন, একইসঙ্গে পরিচালনা করেন, এরকম একজন ব্যক্তিত্ব যখন অসাধারণ নাটক লেখেন, তখন অভূতপূর্ব আনন্দ হয়। অথচ মানুষটি যে এত গুণের আধার, সেটা ওঁকে দেখে বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয়। একটা শান্ত, সমাহিত ভাব, প্রশান্তি খেলা করতে দেখেছি তাঁর চোখেমুখে। আসলে এই প্রশান্তির মধ্যে ভীষণ একটা আলোড়ন ছিল, সেই আলোড়নটাই মনোজবাবুর সৃষ্টিকর্মের উৎস। দেখতাম, চুপ করে তাকিয়ে আছেন। হয়তো কথা বলছেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জরিপ করছেন। আর যখন বলছেন, তখন এমন রসবোধের পরিচয় দিচ্ছেন, ছোট একটা-দুটো কথায়, তা ভোলার নয়।
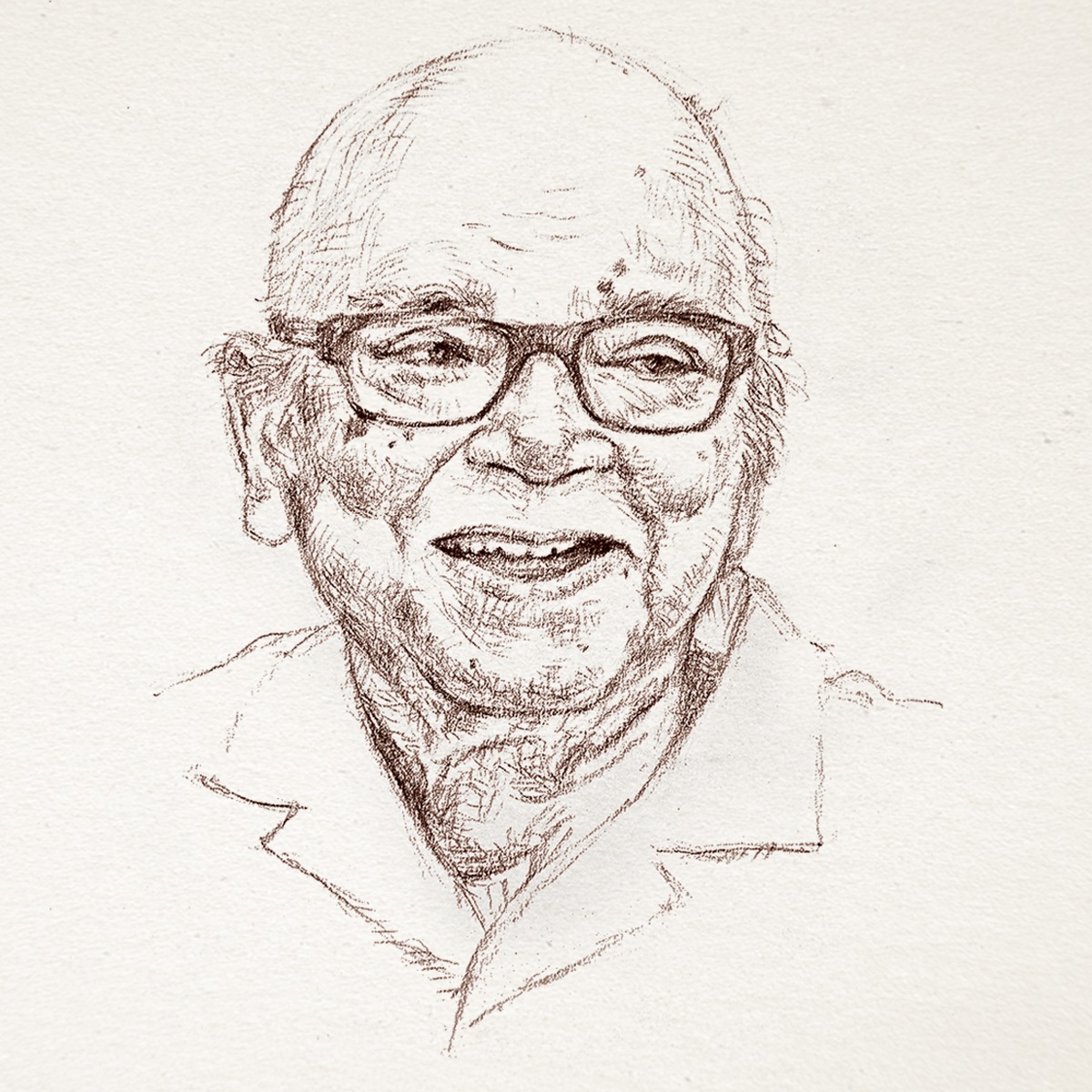
আমার সুযোগ হয়েছিল, বারকয়েক ওঁর সঙ্গে কথা বলার। একটি টেলিভিশন চ্যানেলের হয়ে আমি ওঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎকারের আগে ওঁর সম্পর্কে বিশদে পড়াশোনা করে গিয়েছিলাম। সন-তারিখ ধরে যখন প্রশ্ন করছি, মনোজ মিত্র নিজেই বললেন, ‘বাবা, আমি কি সেরকম একজন, যার সম্পর্কে সন-তারিখ ধরে প্রশ্ন করা যায়? আমি কি গবেষণার উপযুক্ত? তুমি এত কিছু মনে রাখলে কী করে?’ তারপর নিজেই বললেন, ‘ঠিকই, তুমি তো অভিনেতা। অভিনেতাকে সব কিছু মনে রাখতে হয়।’
মনোজ মিত্র-র লেখার যে দিকটা বরাবর আকর্ষণ করে, তা হল, যে ইতিহাস-পুরাণকে আশ্রয় করেন তিনি নাটক এবং লেখায়, সেই অতীতকে দূরের বস্তু না করে রেখে তাকে সমসময়ে ফেলে তার মধ্যে থেকে যেমন মজাটাকে আবিষ্কার করেন, তেমনই সেই মজা থেকে তৈরি হয় একটা অন্য ভাষ্য বা দর্শন, যা একেবারে সমসময়ের সমস্যা ও জটিলতাকে চিহ্নিত করছে। সেটা শুধুমাত্র কোনও রাজনৈতিক ভাষ্য নয়, নয় কোনও সাময়িক আলোড়ন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন কিংবা চলনে সাধারণ মানুষের যে অসহায়তা, যে আকাঙ্ক্ষা, যে স্বপ্ন-ব্যর্থতা সেসবকে ধরে মনোজ মিত্র তার ভিতর থেকে অদ্ভুতভাবে একটা গল্পকে আমাদের সামনে হাজির করে, কীভাবে তার সঙ্গে চলতে হবে, তার পথ দেখিয়েছেন। ইতিহাস-পুরাণের ভিতর থেকে কোনও রাজার কথা হয়তো তিনি বলছেন, কিন্তু তা পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে, এই রাজা তো আমার মতোই চেনা মানুষ। দেবতা যেন পাশের পাড়ার বাসিন্দা। এই যে দূরস্থিত নানা বিষয়-ভাবনাকে টেনে নামিয়ে সাদারণের নাগালের মধ্যে এনে তাকে ফুটিয়ে তোলা, আমাদের সামনে পরিবেশন করা, এটা মনোজবাবুর মুনশিয়ানা।
অভিনেতা হিসেবে তিনি কতটা দক্ষ, কোন মাপের সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অভিনেতা হিসেবে অভিনয়ের যে জায়গাগুলো তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা আমি আগেও বলেছি, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষা, জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষ যা প্রকাশ করতে পারে না চট করে। মনোজ মিত্র তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাকে বড় করে দেখিয়েছেন। তাকে সবার সামনে মেলে ধরেছেন। এবং তা যখন আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, বুঝতে সক্ষম হয়েছি, সাধারণের এই আকাঙ্ক্ষাগুলো ঠুনকো নয়, মানুষ প্রান্তিক হতে পারে, কিন্তু তার স্বপ্নগুলো আকাশছোঁয়া হতে দোষ নেই।
অসম্ভব রসিক মানুষ ছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও চুপ করে যেতেন। হয়তো কাউকে চিনতে পারছেন না, কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ না করে একটা ‘হু’ বলতেন এমন কায়দায়, যে উত্তরপ্রার্থী ধরতেই পারতো না, মনোজবাবু তাকে চিনতে পেরেছেন কি না। সেই মজাদার ঘটনার সাক্ষী থেকেছি আমি। সেই চুপ করে থাকার মধ্যে দিয়ে অনেক কথা বলতে পারতেন তিনি। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এসব মিলিয়ে মিশিয়ে মনোজ মিত্র দারুণ একজন মানুষ। আমরা যখন নাটকে অভিনয় শিখছি, সেই সময়ে আমাদের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন মানুষ ছিলেন মনোজবাবু। আমাদের নিজেদের লোক, আমাদের হিরো। সাধারণ মানুষ, সাধারণ জীবনযাপনের মুখপাত্র। এবং একইসঙ্গে সাধারণের স্বপ্নগুলোকে রঙিন ডানা দেওয়ার কারিগর ছিলেন।
সেই মনোজ মিত্র চলে গেলেন। অবশ্যই এমন প্রবাদপ্রতিম মানুষটির অভাব অনুভব করব, ঠিকই। কিন্তু আবারও বলছি, সাদামাটা জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত হয়েও অসাধারণ সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। অসাধারণ সব লেখা লিখে গেছেন। আজও বাংলা নাটক যেখানে যেখানে মঞ্চস্থ হয়, দেখবেন কোথাও না কোথাও মনোজ মিত্রের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। এতটাই তাঁর অমোঘ উপস্থিতি। তাঁর আকর্ষণ এতটাই তীব্র, সংযোগ এতটাই গভীর। তাঁকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে মনোজ মিত্র চিরকাল বেঁচে থাকবেন মানুষের মনে।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
