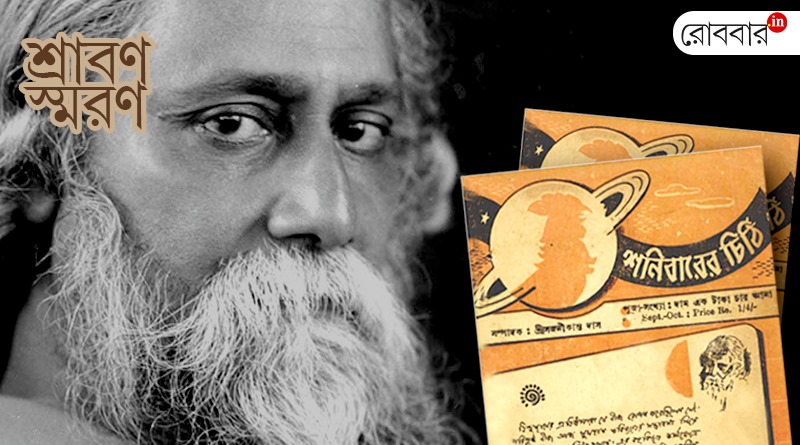
শনিবারের চিঠি-র এই কার্যত-রবীন্দ্রসংখ্যাটি ইতিহাসের তথ্যের খাতিরে মনে রাখতে হবে আমাদের। কিন্তু এরই সাক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সজনীকান্তের মনোভাব বুঝতে চাইলে তা অন্ধের হস্তীদর্শন হতে বাধ্য। সজনীকান্তের নানা হঠকারিতায় রেগে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রাগের যথেষ্ট কারণও ছিল। ১৩৩৬-এর ২২ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখলেন, প্রবাসী প্রেসে শনিবারের চিঠি ছাপা হলে তিনি আর কোনও প্রকার ‘প্রবাসী’র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। এর পিছনে রবীন্দ্রনাথের যে-মনোভাব তা নিঃসন্দেহে দণ্ড দেওয়ার ইচ্ছে। অথচ এই আষাঢ়েই বিচিত্রা-য় সজনীকান্ত লিখছেন, ‘শ্রীচরণেষু’ কবিতা, ‘অপরাধ করিতেছি’, কহিতেছে জনে জনে,/ ‘হব গুরুহত্যা-পাপভাগী’–/ হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জানো মনে মনে,/ কে বা কত গুরু-অনুরাগী’।

সুনীল গাঙ্গুলির দিস্তে দিস্তে লেখা, কত কবি মরে যায় চুপি চুপি একা একা…
মঞ্চে যখন সুমন চট্টোপাধ্যায় গাইতেন এই দু’কলি, নীরবে কলকলিয়ে উঠত তার সমকালের কবিতা-কিশোরের ক্ষোভ, ভাষা পেত দুরন্ত এক প্রকাশ-বেদনা।
প্রবীণ, পরম পাকাদের চাপে তরুণের সে যন্ত্রণা সাহিত্যে চিরকালীন। গত শতকের গোড়ার দিকে সে যন্ত্রণার কল্লোল উঠেছে রবীন্দ্রঠাকুরের চাপে। ক্ষুব্ধ সেই সময়েই অরসিক রায় ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকায় লিখে ফেললেন নটরাজ প্রবন্ধ। জল বেশ ঘোলা হতে থাকল। অরসিক রায় যাঁর ছদ্মনাম, সেই সজনীকান্ত দাস প্রায় ঘৃণাই কুড়োতে লাগলেন রবীন্দ্র-ভক্তদের কাছে।
১৩৩৪, ১৯২৭। রবীন্দ্রনাথের জীবনের তখনও ১৪ বছর বাকি। শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হল বিচিত্রা মাসিকপত্র, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই বিচিত্রাই পরে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ ধারাবাহিক প্রকাশ করবে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ‘নটরাজ’ গীতিনাট্যটি নন্দলাল বসুর অলংকরণ-সহ প্রকাশিত হল। বেশ একটু নাড়া পড়ে গেল রবীন্দ্র-রসিকদের মধ্যে। কিন্তু তারই মধ্যে এক ঘোর অরসিক তরুণ তাঁর প্রবন্ধে লিখে বসলেন, ‘নটরাজ রবীন্দ্র-প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ।… ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ, এবং অক্ষম অনুকরণ…।’
………………………………………………………………………………..
রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা নিয়ে বিশ্বজিৎ রায়ের লেখা: তথ্যনিষ্ঠায় বাঙালিদের অখ্যাতি মোচন করতে চেয়েছিলেন অমল হোম
………………………………………………………………………………..
আর তার সঙ্গে যা লিখলেন তা ওই চুপি চুপি একা একা মরে যাওয়া কবিদেরই কণ্ঠ যেন, ‘প্রত্যেকের দেয় আছে– প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ দিবে। কিন্তু বাণী-মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত যাঁহারা অন্য সকলের দান উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শুধু রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই বাণীর অর্চনা সারিতে চাহিতেছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথেরও অপমান করা হইতেছে এবং উপেক্ষিত সাধকদিগকেও নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ভাল লিখিতেছেন কি মন্দ লিখিতেছেন তাহা বিচার করিবার সাহস কাহারও নাই। অর্ধ শতাব্দীর অভ্যাসের মোহে তিনি যাহাই লিখিতেছেন, চরমতম কাব্য হইতে তুচ্ছতম বাজার হিসাব পর্যন্ত সকলই সাদরে সাহিত্যভোজে উপাদেয় ভোজ্যরূপে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং নিরীহ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে যাহা পাইতেছ তাহাই মাথায় তুলিয়া লও, লোভ করিবার মত বস্তু অন্য কুত্রাপি কিছুমাত্র নাই।’
এই নটরাজ-ই সম্পর্ক নষ্ট করল রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের। অথচ তার আগে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমযাত্রার কাহিনি ‘প্রবাসী’ পত্রিকার জন্য অনুলিখন করেছেন, করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর ‘আত্মস্মৃতি’তে সেই ধন্যবাদ, ‘রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁহার সহিত কৌশলে পত্র ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার সান্নিধ্যেও আসিয়াছি, কিন্তু এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সম্ভাবনার কথা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। দিনরাত্রি সর্বদা কয়েকদিন একসঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল, এক টেবিলে আহার করিতাম, এক ঘরে শয়ন করিতাম। খেয়াল হইলেই তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নোট-বইটি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মুখে মুখে ডায়েরি রচনা করিয়া চলিতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম।’
অথচ এই সজনীকান্তই রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে কতটা নীচে নেমে যেতে পারেন, তা বোঝা যাবে শনিবারের চিঠি-র একটি কার্যত রবীন্দ্রসংখ্যায়। ‘কার্যত’ বললাম এই কারণে যে, সরাসরি রবীন্দ্রসংখ্যা বলা না-হলেও ‘জয়ন্তী’ (মাঘ ১৩৩৮) সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে। সে সংখ্যার সূচিপত্রটি পড়লেই রুচিবিকারটি ধরা পড়বে।
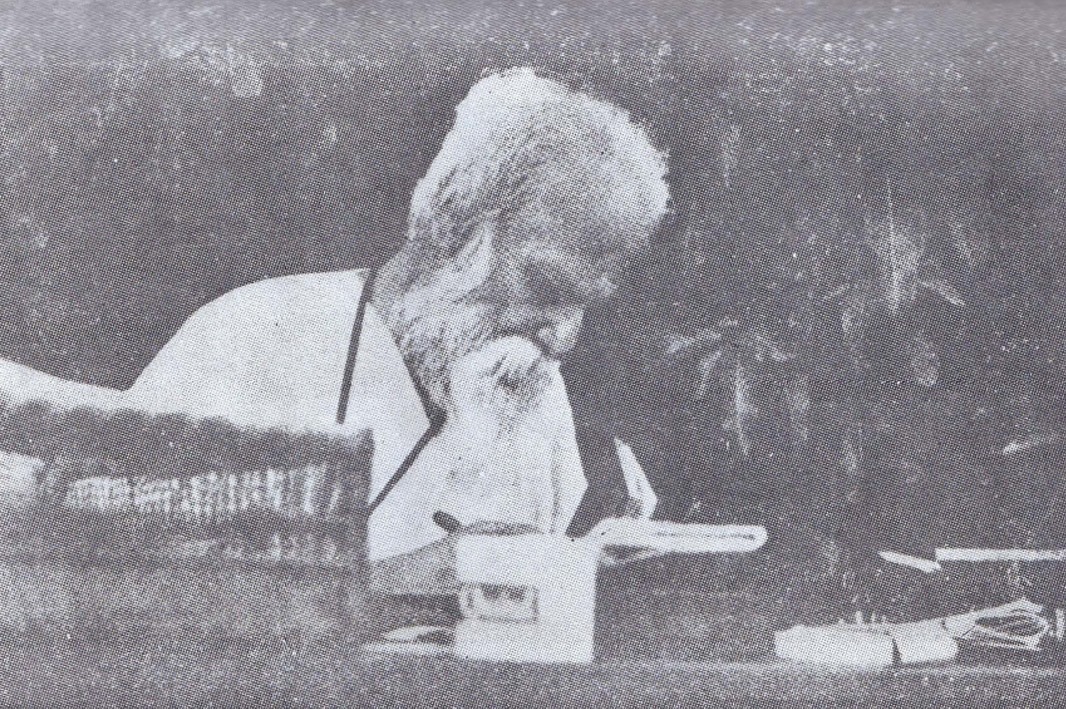
কবিবরণ (কবিতা) মোহিতলাল মজুমদার; জয়ন্তী (প্রবন্ধ); প্রসঙ্গকথা; নৃত্যময়ী (প্যারডি কবিতা); জয়জয়ন্তী (জনগণমন অধিনায়ক-এর প্যারডি); চলচ্চিত্র (ব্যঙ্গচিত্র); রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংবেদনা বা ছবিতা (সচিত্র প্রবন্ধ); বড়ো বুধুর বন্দনা (কবিতা); দি গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর ও জয়ন্তী উৎসর্গ (প্রবন্ধ); লটির পূজা (ব্যঙ্গ নাটিকা); সংবাদ সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথ (প্রশস্তি কবিতা) সজনীকান্ত দাস।
এ সংখ্যার প্রথম ও শেষ দু’টি কবিতা ছাড়া সব লেখা তীব্র বিদ্বেষে ভরা। তার তীব্রতা এতটাই ছিল যে স্বয়ং সজনীকান্তও ‘আত্মস্মৃতি’-তে লিখেছেন, ‘মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসাপরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।’
‘শনিবারের চিঠি’-র এই কার্যত-রবীন্দ্রসংখ্যাটি ইতিহাসের তথ্যের খাতিরে মনে রাখতে হবে আমাদের। কিন্তু এরই সাক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সজনীকান্তের মনোভাব বুঝতে চাইলে তা অন্ধের হস্তীদর্শন হতে বাধ্য। সজনীকান্তের নানা হঠকারিতায় রেগে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রাগের যথেষ্ট কারণও ছিল। ১৩৩৬-এর ২২ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখলেন, প্রবাসী প্রেসে শনিবারের চিঠি ছাপা হলে তিনি আর কোনওপ্রকার ‘প্রবাসী’র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। এর পিছনে রবীন্দ্রনাথের যে-মনোভাব, তা নিঃসন্দেহে দণ্ড দেওয়ার ইচ্ছে। অথচ এই আষাঢ়েই বিচিত্রা-য় সজনীকান্ত লিখছেন, ‘শ্রীচরণেষু’ কবিতা, ‘অপরাধ করিতেছি’, কহিতেছে জনে জনে,/ ‘হব গুরুহত্যা-পাপভাগী’–/ হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জানো মনে মনে,/ কে বা কত গুরু-অনুরাগী’। তার পরে ১৩৩৮-এর আশ্বিনে পত্রিকা নিজস্ব প্রেস থেকে ফের প্রকাশিত হতে শুরু করল। সে বছরই মাঘ মাসে ওই কলঙ্কিত জয়ন্তী সংখ্যা। ধুনোর গন্ধও কিছু কিছু ছিল!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে, শনিবারের চিঠির ঘোষিত রবীন্দ্রসংখ্যাটি বুঝিয়ে দিল সত্যিই কে কত গুরু-অনুরাগী! সেই আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যার (১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা) প্রচ্ছদে শনিবারের চিঠির সিগনেচার মোরগ ছোট হয়ে নেমে এল শেষের মার্জিনে। বড় করে ছবি ছাপা হল রবীন্দ্রনাথের, পাশে আনতপদ্ম।
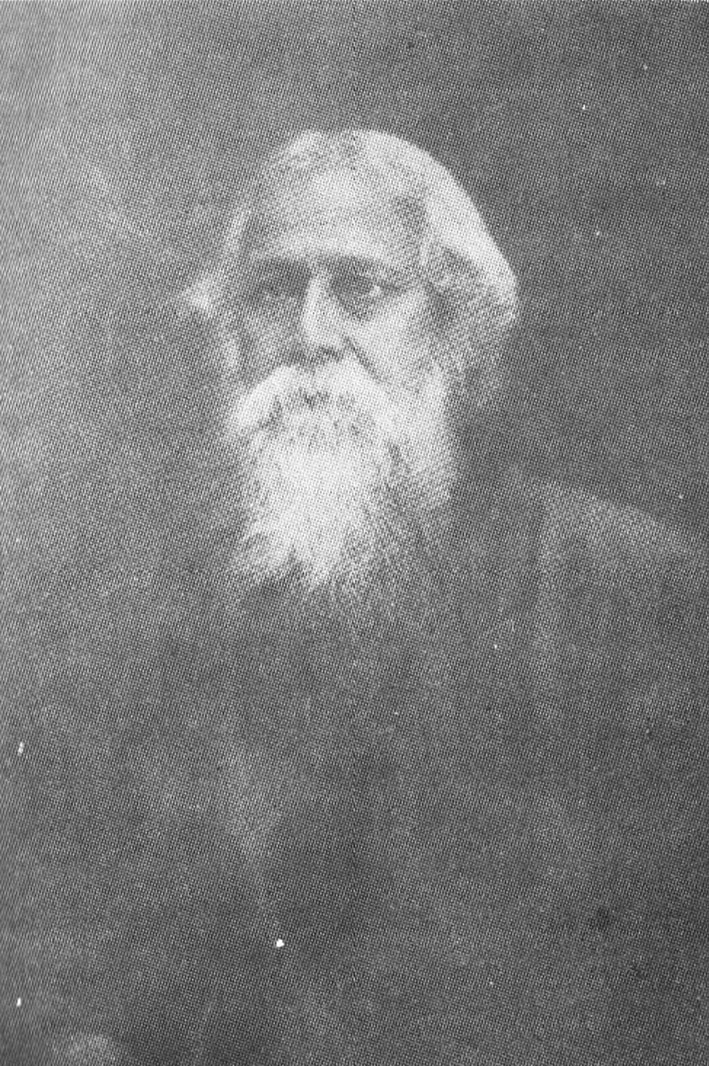
ওপরের ছবিটি পিনাঙ-এ তোলা, ১৩৩৪-এর। সেই ১৩৩৪, যে-বছর নটরাজের সূত্রে সজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ভেঙে গেল! রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় প্রথমেই ছাপা হয়েছে ‘হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা’ কবিতাটি
“হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে,করিতে পারি নে সেবা।’
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
“তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি,এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।’
“আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।’
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
“ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।’
রবীন্দ্রনাথকে কত বড় করে দেখতেন সজনীকান্ত, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কী শূন্যতা তৈরি করেছিল তাঁর মধ্যে, তার একটা আভাস হয়তো এই কবিতার নির্বাচনেই আছে! সেই সংখ্যায় আর যেসব লেখা ছিল তা প্রমাণ করে নিছক ভক্তি আর আবেগ দিয়ে সম্পাদক সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে দেখেননি।
কথাটা আরও ভাল করে খেয়াল করি যখন দেখি কেবল কবি বা কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ নন, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ এবং অ-পূর্ব ব্যক্তিত্বের রবীন্দ্রনাথ এই সংখ্যার অন্বিষ্ট। ‘রবীন্দ্রনাথের একটি দান’ প্রবন্ধে যদুনাথ সরকার লিখছেন এই সংখ্যায়, রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরেজী নাম– refined delicacy, এবং তাহার বিপরীতটির নাম– vulgarity of taste…। সজনীকান্ত এই বিপরীতটির সাধনা একদিন করেছিলেন, এই লেখার নির্বাচন কি তারই প্রায়শ্চিত্ত!
প্রায়শ্চিত্ত শব্দটা একটু বাড়িয়েই ব্যবহার করে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথকে ঋষি এবং মহামানব হিসেবে দেখার অভ্যাসেরই স্মৃতি সেটা। নইলে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কিছু রচনাকে নিয়ে শালীনতার-সীমা-ছাড়ানো কিছু ব্যঙ্গ ছাড়া তো আর কিছু করেননি, তাকে এত সহজেই পাপ বলে ভেবে নিতে পারি আমরা! ইতিহাসের স্বার্থে, রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণতর রূপে উত্তর-প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর অনামী বা ছদ্মনামী শৈশব-রচনাগুলিকে উদ্ধার করার যে বিপুল কাজটা করেছিলেন সজনীকান্ত, তা-ও তো ভুলে যাই থেকে থেকে। এই রবীন্দ্রসংখ্যাটিতেই তো প্রকাশিত হচ্ছে চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সেন্সাস, রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণের মতো রচনা– যারা কেবল চর্বিত কবি রবীন্দ্রনাথকেই চর্বণ করে চলছে না।
এই সংখ্যাতেই তো প্রকাশিত হয়েছিল যামিনী রায়ের প্রবন্ধ ‘চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’, যেখানে ২৫ মে ১৯৪১-এ যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিটিও আছে,
‘আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে । আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না…’
আট দশকেরও বেশি পেরিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। তাঁকে দেখার দৃষ্টির আবরণ আমাদের আজও ঘোচেনি। হয়তো সে-কারণেই সজনীকান্তের দুষ্টুমিগুলোকেও আজও আমরা বড় বেশি গুরুতর করে দেখি!
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
