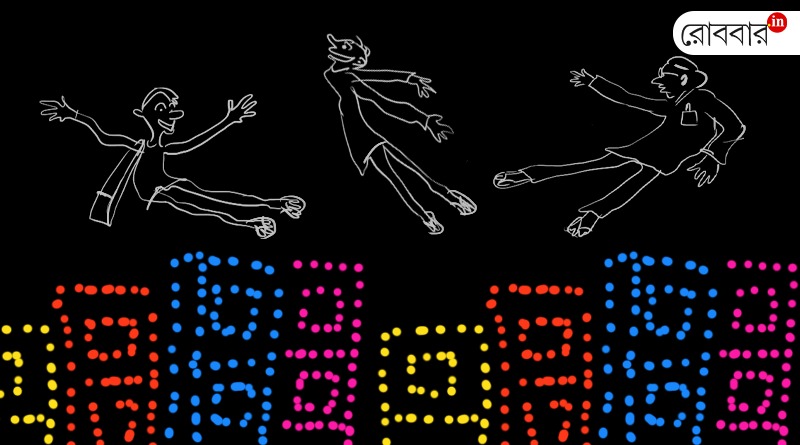
এই নিয়ন-মেটাল-এল.ই.ডি শাসিত চোখ-ধাঁধানো নগর বাস্তবতায় ঢুকতে শুরু করে অন্যরকম হাওয়া। হাওয়া কিংবা হাওয়াকলে বানানো অবয়ব। সেই ছায়াময় অশরীরীদের আনাগোনায় ধীরে ধীরে অপার্থিব, অচেনা হয়ে যায় চারপাশের এলাকা। এ কলকাতার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে আরেকটা কলকাতা! আমার বন্ধু রঞ্জিত ওরফে দুলদুল, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সেই নয়ের দশকের গোড়ায় সন্ধের ঝোঁকে বলেছিল, ‘এই যে কালীপুজোর এত ভিড়-ভাট্টা দেখছিস, এত লোক কোথা থেকে হঠাৎ এল? ওরে পাগলা, এরা কেউ মানুষ না!’

১.
কলকাতার এমন এক রাস্তার ধারে আমার জন্ম-কর্ম, হেদুয়া আর মিনার্ভা থিয়েটার ছুঁয়ে যে রাস্তা পশ্চিমে সোজা চলে গেছে গঙ্গানদীর দিকে। ফলে, কলকাতার যত প্রতিমা, সবই ওই পথেই ভাসান হবে। আমরা গভীর, গভীরতম রাত পর্যন্ত দেখব সেই মিছিল, শুনব ঢ্যাম কুড়কুড় ঢাকের বাদ্যি, আতশবাজির চমকানি আর গর্জন। কালীপুজোয় একটা ভয়ের গল্প শুনতাম বড়দের কাছে। রং চড়িয়ে সেই গল্প আমাদের পাড়ায় আজও শিশুদের শোনানো হয়। বিশেষত যারা বেয়াড়া গোছের। ঘুমোতে চায় না সহজে। মা-কালীর সঙ্গে আসে দুই বীভৎস, মানুষখেকো, ভীষণা ডাকিনি-যোগিনী। তারা নাকি বিসর্জনের টেম্পো বা লরি থেকে নেমে সুড়ুৎ করে মিশে যায় রাস্তার পাশের জনবসতিতে, ঢুকে পড়ে বিভিন্ন বাড়িতে। তারপর ওত পেতে থাকে আড়ালে-আবডালে। ঘুমহীন শিশুদের খোঁজে। একবার হাতে পেলে ভয়ংকর কোনও পদ্ধতিতে তারা খেয়ে ফেলবে শিশুদের। শিউরে শিউরে উঠতাম, আর ওই কয়েকদিন ভয়ে নীল হয়ে থাকাই ছিল নিয়তি। তারপর কালীপুজোর বিসর্জন শেষ হত। কিন্তু ভয়ংকর সেই ডাকিনি-যোগিনী মূর্তি মনে বহুদিন রেশ ফেলত।
প্রকৃতপক্ষে, কালীপুজোর সঙ্গে এই ভয়াল গা-ছমছমে ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। কালীপুজোর হাত ধরে আসে ঘনান্ধকার অমাবস্যা। গাঢ় তমিস্রার মধ্যে একটা রহস্য আছে। যাকে বোঝা যায় না, জানা যায় না, যার গভীরে থাকে ব্যাখ্যাহীন। ভূত-প্রেত-পিশাচ-কবন্ধ সবই সেই কালীপুজোর সঙ্গে জড়িত থাকে। মা-কালীর রূপটিও এক্ষেত্রে মৃত্যু আর জীবনের মেলবন্ধন। তাঁর ঘোরবর্ণা, মুক্তকেশী, শ্মশানচারিণী মূর্তি, জনপদের গার্হস্থ্য জীবনচর্যার এক সম্পূর্ণ বিপরীত ইশারা। যেন এক বিকল্প। ‘মহাকালের মনমোহিনী’ হলেন ‘সদানন্দময়ী কালী’। এই কাল, মহাকাল আর বিনাশের নিশ্ছিদ্র, নীরন্ধ্র, অনাদি অমা তাঁর শক্তি, তাঁর রূপ। কালী-উপাসনায় কার্তিকী অমাবস্যার আগের দিন আসে ভূত-চতুর্দশী। সেদিনই আসলে এই নিয়ন-মেটাল-এল.ই.ডি শাসিত চোখ-ধাঁধানো নগর বাস্তবতায় ঢুকতে শুরু করে অন্যরকম হাওয়া। হাওয়া কিংবা হাওয়াকলে বানানো অবয়ব। সেই ছায়াময় অশরীরীদের আনাগোনায় ধীরে ধীরে অপার্থিব, অচেনা হয়ে যায় চারপাশের এলাকা। এ কলকাতার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে আরেকটা কলকাতা! আমার বন্ধু রঞ্জিত ওরফে দুলদুল, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সেই নয়ের দশকের গোড়ায় সন্ধের ঝোঁকে বলেছিল, ‘এই যে কালীপুজোর এত ভিড়-ভাট্টা দেখছিস, এত লোক কোথা থেকে হঠাৎ এল? ওরে পাগলা, এরা কেউ মানুষ না!’
ভূত-চতুর্দশীর দিন সন্ধেবেলা রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ান। মায়াময় ছায়া এবং কায়া বুঝতে চেষ্টা করুন। দীপায়ন পর্ব বা আলোকপর্ব, যাকে ‘এনলাইটেনমেন্ট’ তকমায় পশ্চিমা তুফানে দেশদুনিয়া দখল করতে দিলাম আমরা, তার বাইরে আছে আরেক অঞ্চল। যেথা আলোক নাহি রে!
২.
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মুখে শোনা যেত এমন আশ্চর্য উক্তি– ‘কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। আকাশ দূরে তাই নীল, কাছে রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে দেখায় নীল, হাতে নাও, কোনো রঙ নেই।’ কালী যেন শূন্যের ভিতরে ঢেউ। নিরাকার কিন্তু আমরা তাঁকে অবয়বে, বর্ণে, অনুপুঙ্খে দেখি। সেই মূর্তির আদি-অন্ত নেই। সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়-কে ছুঁয়েও যেন অন্তরের প্রতিরূপ। তিনি একই সঙ্গে প্রসন্না আবার সংহারিণী। দুষ্টের দমন এবং শিষ্ঠের পালনে সমভাবে উদযোগী। ‘‘দেবী কালিকার হাত চারটি। দু’হাতে নিধন করেন। বাঁদিকের দুই হাতে তাঁর খড়্গ ও মুণ্ড ধ্বংসের চিহ্ন। ডানদিকের দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রার পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক হাতে আঘাত আর এক হাতে সান্ত্বনা। এক হাতে ভীতি প্রদর্শন আর এক হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ।’’ বলেছিলেন দেবদেবী বিশেষজ্ঞ সুধীরকুমার মিত্র। একই কথা লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ‘মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!/ করালি! করাল তোর নাম,/ মৃত্যু তোর নিশ্বাস প্রশ্বাসে/ তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ/ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!/ কালী, তুই প্রসন্নরূপিনী, আয় মাগো,/ আয় মোর পাশে।/ সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,/ মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে। কালনৃত্য করে উপভোগ,/ মাতৃরূপা তার কাছে কাছে।’
(তর্জমা: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
যদি, উৎস খুঁজতেই হয়, তাহলে আমাদের মনে পড়বে চৈতন্য ভাগবতের অঙ্গুলিনির্দেশ: ‘সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতি/ অসাধুর করে তুমি কালরূপাকৃতি।’
কালী আসলে দ্বি-কোটির সমাহার। তাঁর মহিমা আঁধারের মহিমা। সবার গোচর সে নয়, সাধকের অনুভবে ধরা দেয় সংকেত। আলো আর আলোকপর্বে শুধু জ্ঞানদীপ্তির দম্ভ। সে আলোয় বাইরের সুন্দর ঝকমক করে। আলোর গরিমা ছদ্মের, অর্থাৎ বাহ্যিকের, আঁধারে স্তরে স্তরে বিকশিত হয় প্রকৃত। যে আঁধার আলোর অধিক। কাজী নজরুলের গানে সেই ইশারা– ‘আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়/ দেখে যা আলোর নাচন/ মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব/ যার হাতে মরণ-বাঁচন।/ আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে/ শিশু রবি-শশী দোলে,/মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক ঐ/স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।’
হিন্দু দেব-দেবীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে দশমহাবিদ্যা অর্থাৎ শক্তিদেবীর দশ প্রধান রূপভেদে আছে বিকল্পের ইঙ্গিত। সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী– নানা নামে, নানা ক্ষেত্রে তিনি পূজিতা। সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে মিশে থাকে সৃষ্টি আর সংহারের বৈপরীত্য। দেখা না-দেখায় মেশা। জানা-অজানায় মেশা। কখনও তন্ত্র-কাপালিক, কখনও শবসাধনা, কখনও গোপ্য আচারে তাঁর অর্চনা। ঢাকেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, আনন্দময়ী, করুণাময়ী– নানা নামে তিনি জনবৃত্তে পূজিতা হন। তাঁর উপাসনা পদ্ধতির কোষগ্রন্থ দু’টির নামও এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো। ‘তন্ত্রসার’ আর ‘শ্যামারহস্য’। শাক্তপ্রধান বাংলায় কালী উপাসকের সংখ্যা সর্বাধিক। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় সন্ধানী। এই চিররহস্যের।
প্রকৃতপক্ষে, যতই ‘যুক্তি’ আর ‘প্রযুক্তি’ দিয়ে শৃঙ্খলা আর শান্তির নতুন নতুন কলাকৌশলে মন বাঁধা হবে, ততই খোঁজ পড়বে বিকল্পের। প্রশ্ন উঠবে মৃত্যুর স্বরূপ নিয়ে, জন্মের অত্যাশ্চর্য অব্যাখ্যাত মুহূর্ত নিয়ে। পুঁথিজ্ঞানে সব-জানার পাটোয়ারি লাভ-লোকসান পেরিয়ে দেখা দেবেন আমূল বিপরীতের দর্শন। সেই জাদুমন্ত্র, সেই রোমাঞ্চ, সেই মুঠো-মুঠো রাঙাজবার দ্যুতি আর বিদ্যুৎ! দেখা দেবে বিকল্প।
৩.
অবশ্যই তখন আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে অলৌকিক রামপ্রসাদের, যিনি বাংলা গানের বিশেষ বিষয় এবং আঙ্গিকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনশ্বর শ্রষ্ঠা। ‘রামপ্রসাদী’ সুরের কাঠামো তথা গানের কাঠামো যেমন বিষ্ময়কর এক রূপকল্প, তেমনই গানের শব্দব্যবহার, সহজ শব্দ জুড়ে জুড়ে অপ্রাকৃত অতিপ্রাকৃত অনির্বচনীয়কে পরশ করা। সেই রামপ্রসাদের একটি গান আছে– ‘শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি/ ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।’ ছবিটি একসঙ্গে অনেক কথা বলে দেয়। এই ভব-সংসার আর বাজারের বাস্তবতা থেকে মন ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়ার কথা। এই প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়া, ঠকা-ঠকানো, শ্রেষ্ঠী-মুদ্রা, ক্ষুণ্ণিবৃত্তি-নিদ্রারমণ থেকে বিমূর্ত দর্শনের, তথা সন্ধানের উড়ানের কথা। কিন্তু, কেবল তাই নয়, শ্যামা মাকে ভবসংসার বাজারের মাঝে নিয়ে এলেন রামপ্রসাদ। যেন বলতে চাইলেন, এই চেনা-জানা ভিড় আর বিচিত্র মানব মিলনের হাটবাজারে মা আছেন। সে দেবী অলৌকিকতার। এক মুহূর্তে একদিকে যেমন ভবসংসার-বাজারের গুরুত্ব স্পষ্ট হল, অন্যদিকে বুনিয়াদ হিসেবে এই হইহল্লা, গুজব-রটনা-বাতেল্লার পরিসরকে স্বীকৃতিও দেয়া হল। দৃশ্যটি শুধু অর্থময়ই নয়, কল্পনা হিসেবেও দুর্দান্ত। দেবী এবং আপাততুচ্ছ ঘুড়ির সহাবস্থানে তৃতীয় নেত্রের উদঘাটন যেন।
এই যে বাংলার শহর-মফসসলের জনপরিসর তার বহু স্বর এবং বহু সরিক, ‘বাজার-বাস্তবতা’ তথা বিচিত্র জীবনচর্যার মহাসম্মিলন– তার সঙ্গেই থাকেন কালীমাতা। তার সঙ্গেই থাকে বিকল্প। থাকে মৃত্যুর নিশ্চয়তা, মুহূর্তের হাস্য-উল্লাস, বিশদ-বিসংবাদ বিতর্ক-শ্লেষ-আড্ডা-ইয়ার্কি-মশকরা। তাকে অবরিত জীবনস্রোত। যে কোনও জনপদের সঙ্গেই থাকে শ্মশান। একদিকে প্রসূতিসদন আর অন্যদিকে চিতাভস্মের মধ্যবর্তী এই বাজার। এই ভবের হাটের কড়চা।
কড়চা বলতেই মনে পড়ে হুতোমের দৈনন্দিনের গল্প। সেই সময়ের প্রবহমান আদি কলকাতা। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, হুতোমই কালীপ্রসন্ন সিংহ কি না। সে বিতর্ক এখানে নিরসন করার নয়। শুধু মনে রাখা ভাল, বাবু কালীপ্রসন্নের নামে কালী। আর তাঁর সময়েই কলকাতা শহরে নবজাগরণের দীপায়ন। এনলাইটমেন্টের হুজুক। হই হই কাণ্ড। বীরকৃষ্ণ দাঁ আর তাঁর মোসাহেবদের মোচ্ছব। সাহেব-মোসাহেব বাউল-সাধক, পাগলা-ভিখিরি, রাঁড় আর মহারানি ভিক্টোরিয়া সব মিলেমিশে অত্যাশ্চর্য জাদুবাস্তব। ঠিক সেখানেই, পাঠক লক্ষ করুন, হুতোমের কলমে, হুতোমের নকশার দ্বিতীয়ভাগে–
‘‘এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল, ছেলেরা ‘ব্যোমকালী’ ‘কলকেত্তাওয়ালি’ বোলে চেঁচিয়ে উঠলো।’’ (দুর্গোৎসব)
কলকাতার নগরজনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহলে সেই কালী। হুতোম মনে করিয়ে দিলেন। ‘কোথাও যাত্রা হচ্চে, মণিগোঁসাই সং এসেচে ছেলেরা মণিগোঁসাইয়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আশে পাশে চিকের ভিতর মেয়েরা উঁকি মাচ্ছে, মজলিসে মজলিসে রামমসাল জ্বলচে; বাজে দর্শকদের বায়ুক্রীড়ায় ও মসালের দুর্গন্ধে পূজাবাড়ী তিষ্ঠান ভার। ধূপ-ধুনার গন্ধও হার মেনেচে।’

এই সেই আশ্চর্য উৎক্রমিক বাস্তবতা। ছোটলোকের বাস্তবতা। বহুশরিকের বাস্তবতা। এই ভববাজারে মা কালী ঘুড়ি ওড়ান। রামপ্রসাদের কল্পনায়। কেটে যেতে থাকে শতকের পর শতক। বীরকৃষ্ণ দাঁ ঢুকে পড়েন নাট্যশালায়। টিনের তলোয়ার যেখানে ঝলসে উঠছে।
৪.
৭ নভেম্বর ১৯৯৯। এই তারিখটি আপনি মনে করতে পারেন কি? এই দিন ছিল কালীপুজো। সেই কালীপুজোর রাতেই ঘটবে ভূতুড়ে সব ঘটনা। একদিকে নাশকতা আর অন্যদিকে অন্তর্ঘাত নিয়ে কার্নিভালেস্ক উদভাবনে সে-রাতে দেখা দেবে ভৌতিক শক্তি। বুলগাকভের ছায়াও দেখা যাবে। স্তালিনের ভূত-সহ ফ্যাতাড়ুরা ডানা মেলবে হাটবাজেরর মধ্য থেকে আকাশে। দেখা দেবে চোক্তার। বনবন করে আকাশে উড়বে চাকতি। তন্ত্রমন্ত্র আর রহস্যময়তার সঙ্গে সমাজবদলের স্বপ্ন মিশিয়ে নবারুণ ভট্টাচার্য গড়ে তুলবেন সেই অকল্পনীয় জগৎ। এ উপন্যাসের নাম ‘কাঙাল মালসাট’। মালসাট মানে হুংকার, রণবিজয়ের গর্জন। ‘‘কলিকাতার কালীপুজোর আগেকার রূপটি আমরা যেমন রসঘনভাবে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ‘কালীপুজোর রাত’-এ পাই যে তারপর আর কোনও পাঁচুকেই ভাবা যায় না। সবই প্রায় আলগা ঠাসা বসন তুবড়ি যা থেকে থেকে ভ্যাঁস ভ্যাঁস শব্দ করে এবং অচিরেই নিঃশোষিত তামাশায় পর্যবসিত হয়।’’ কাঙাল মালসাট উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৩ সালে। কালীপুজোর রাত মদ-নেশা হুল্লোড় এবং প্রতিরোধ থেকে বিকল্প খুঁজে নিচ্ছিল। একইভাবে, তার আগেই, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে কালীপুজোর রাত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নবারুণ বারংবার এই রাতটিকে তাঁর লেখালেখিতে ব্যবহার করেন। সাতের দশকের বিপ্লবী রণজয় ওই কালীপুজোর রাতেই জেল নয়, পাগলাগারদ থেকে পালাবে। তার স্থান-কাল সব মিলেমিশে গেছে। তার স্বপ্নকে ছিড়েখুঁড়ে ‘স্বাভাবিক’ বানানোর চেষ্টা করছে শ্রেষ্ঠী-সভ্যতা। দিন বদলানোর স্বপ্নটুকু নিয়ে ‘অস্বাভাবিক’ শহরে বোমা আর পটকার আওয়াজ, মুর্হুমুর্হু গগনভেদি শব্দদানব আর আলোর ঝিলিকে সে পালাচ্ছে। ‘এক প্যাকেট বিড়ি আর দেশলাই কিনলো রণজয়। দেশলাই কাঠির মাথায় মিশমিশে বারুদটা দেখে বড় ভাল লাগল রণজয়ের। কাঠিটা জ্বেলে আগুনটা দেখতে আরও ভাল লাগল। ফাটা পটকার কাগজ, তুবড়ির খোল, বমি, বোতল, প্যান্ডেলের আলো, গান সারা শহরে ছড়িয়ে। নিভে আসা কাঠিটা ছুঁড়ে দিল রণজয়।’
(যুদ্ধ পরিস্থিতি)

পাঠিকা/পাঠক আপনারা বুঝতে পারছেন, কীভাবে বাস্তবে-জাদুবাস্তবে বোধগম্যতা আর রহস্যময়তায় মিলেমিশে নবারুণ নির্মাণ করেছেন কালীপুজোর রাত আর তার জনপরিসর। জনপরিসরের ব্যস্ততা, আলস্য, গোঙানি, চিৎকার এবং ঘুম। ঘুমের সূত্রেই স্বপ্ন বা খোয়াব। দুঃস্বপ্নও।
এই প্রাত্যহিকের এলাকায় শ্মশানকালীর বিদ্রোহী কল্পনা, প্রকৃতপক্ষে মনে করিয়ে দেয় আমাদের মুক্তিসন্ধানী মনোভঙ্গির কথা। যাকে ভুলে এই ক্ষুদ্রতায় আমরা মজ্জমান হয়ে আছি। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এই দিকেই নজর টেনেছিলেন। তুচ্ছতা থেকে বিপুলতায় সেই যাত্রা।
‘কালীর নামে দাও রে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না।
যে যে মুক্তকেশীতে শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।’
(রামপ্রসাদ)
‘যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না হে মা,/ মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?’
(কমলাকান্ত)
৫.
বিডন স্ট্রিটে কত যে শ্যামা প্রতিমার বিসর্জন দেখেছি মোটামুটি স্মরণে আছে, গত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তখন কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ একটি নাম ‘ফাটাকেষ্ট’। তাঁর নব যুবক সঙ্গ আমহাসর্ট স্ট্রিট কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে বিখ্যাত এক ক্লাব। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল সোমেন মিত্রের পুজোর। দু’জনেরই প্রতিমা হত সেকালে বিশালাকার। তার ভাসান ছিল বিপুল জাঁকজমকে ভরা। পরবর্তীকালে সেই পুজো নিয়ে অনেক হাসাহাসি, বিদ্রুপ শুনেছি, কিন্তু কেউই বলে না, প্রতিবার ফাটাকেষ্ট-র উদ্যোগে প্রকাশ পেত ‘শ্রী শ্রী কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ’ (যুবক সংঘ)। সেই বইগুলি গুরুত্বপূর্ণ সারস্বত সংকলন। ১৯৭৪ সালের সংকলনটির নাম ‘সেকালের কলকাতা’। প্রায় ২৩৩ পাতার চমৎকার সংকলন। এরকম সাত-আটটি আমার সংগ্রহে আছে। সেই গ্রন্থ থেকে পাচ্ছি– ‘‘এই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আকবরের রাজত্বকালে কালীঘাট মহাতীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে যে ‘কালীকোটা’-র উল্লেখ আছে, অনেকে তাকে কালীঘাট বলেই মনে করেন।’’
বিডন স্ট্রিটে এসে দাঁড়াই। আলোর রোশনাই, বাজি আর ভিড়ে মনে হয় এই পথ, এই অমাবস্যা, নদী আর অনন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ থেকে নবারুণ ভট্টাচার্য সেই অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর দিকে তাকিয়েছিলেন। আমরা তাকাব না?
প্রচ্ছদের ছবি: অর্ঘ্য চৌধুরী
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
