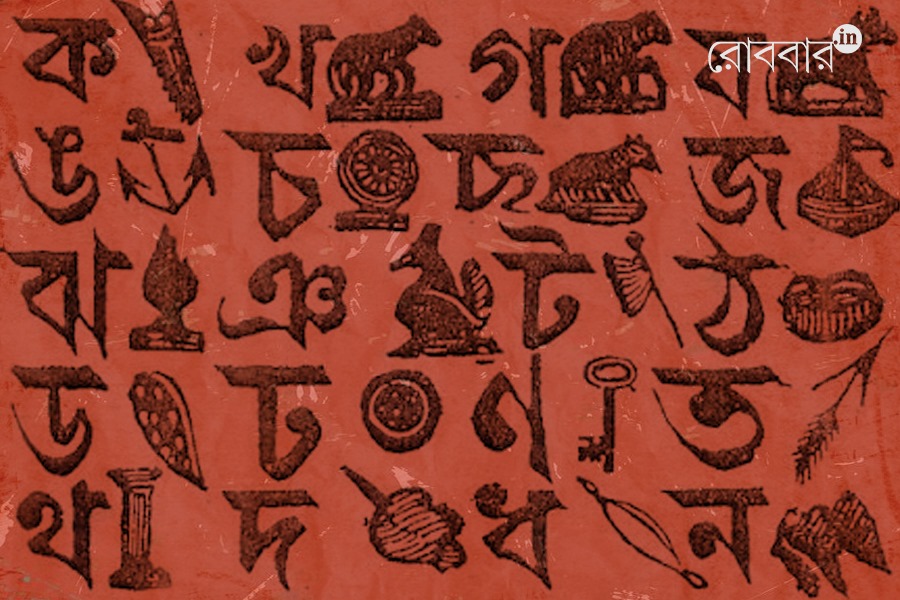
অসমের ব্যবস্থা কী হবে সেটার কথা বাদ দিয়ে, পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কারা ভারতীয় আর কারা বাংলাদেশি (কিছু বাংলাদেশি থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা অস্বীকার করি না, কারণ পেটের খিদে অনেক সময় রাজনৈতিক সীমানা মানে না)– সেটা ভারত সরকার নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করুন, আর ভারতীয় বাঙালি শ্রমিকদের অনুচিত আর অন্যায় হেনস্থা রোধ করবার নিখুঁত উপায় নির্ধারণ করুন। বাংলাভাষীরা নিজেদের মধ্যে কথা বললেও তাঁদের ওপর জুলুম করা হবে, এই অমানবিক আর অসাংবিধানিক ঘটনাগুলি বন্ধ করুন।
গ্রাফিক্স: সোমোশ্রী দাস

কিছুদিন আগে ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মশাই ইংরেজি বলার জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তা আমরা তার উল্টোটাই করি, হয়তো ভবিষ্যতেও করব– ইংরেজি বলার জন্য জামার কলার উঁচিয়ে অহংকার করতে ছাড়ব না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেও না। কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই ইংরেজি ভাষা একটা আধিপত্যের অস্ত্র। কিন্তু এদিকে, ভারতে এমন একটা দিন ঘনিয়ে এসেছে যে, বাংলা বলার জন্য আমাদের সত্যি সত্যি লজ্জিত হতে হচ্ছে। শুধু লজ্জিত কেন– ভীত, পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত হতে হচ্ছে।
নিছক লজ্জিত হওয়ার একটা ঘটনাও ঘটেছে, আর বিস্ময়ের কথা যে, তার ঘটক বাঙালি। জনপ্রিয় বাঙালি চিত্রনায়ক প্রসেনজিৎ মুম্বইয়ে এক বাঙালি সাংবাদিককে তিরস্কার করলেন এই কিছুদিন আগে, তাঁকে বাংলায় প্রশ্ন করার জন্য। তিনি সম্ভবত লজ্জিত বোধ করেছেন। সাংবাদিকটির কেন এ দুর্বুদ্ধি হল কে জানে! তিনি কি ভেবেছিলেন যে, প্রসেনজিৎ ইংরেজি বা হিন্দিতে উত্তর দিতে পারবেন না বা আমাদের হৃৎকম্পন ঘটানো নায়ক কি ভেবেছিলেন যে, সাংবাদিকটি ওই রকম ভেবেছিলেন– এ সব প্রশ্নের উত্তর এখন আর আমরা পাব না, কারণ সেটা এখন ত্যক্ত অধ্যায়, প্রসেনজিৎও তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই তিক্ত বার্তাটা তবু থেকেই গিয়েছে যে, কোনও কোনও উপলক্ষে কোনও কোনও বাঙালি বাংলা বলতে অস্বস্তি বোধ করে, বাঙালির সঙ্গেও।

২.
এটা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সমস্যা, এর কোনও জাতীয় তাৎপর্য নেই, কিন্তু বাঙালির ভাষাগত আত্মসম্মানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। আমরা নিজেরা কেউ কেউ আমাদের ভাষাটাকে কীভাবে দেখেছি, আমাদের সামাজিক আচরণে কোথায় রেখেছি, এটা তার কিছু ইঙ্গিত দেয়।
কিন্তু ভারতের জাতীয় স্তরে বাংলা ভাষা যে, বাঙালিদের জন্য নানা বিড়ম্বনা আর সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তা অনেক ব্যাপক একটি ঘটনা, এর তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী। তা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছে। এই জন্য যে, ভারতীয় জাতি যে, ‘নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’ জাতীয় একটা কিছু, তা আমরা এতদিন ধরেই নিয়েছিলাম। আমাদের সংবিধান-রচয়িতারাও আমাদের তাই বুঝিয়েছিলেন। বহুভাষী রাষ্ট্রের ভাষায়-ভাষায় যাতে বিরোধ না ঘটে, সে জন্য তাঁরা আমাদের দেশের প্রধান ভাষাগুলির একটা ক্ষমতার বিন্যাস করে দিয়েছিলেন। সংবিধানের ৩৪২ থেকে ৩৫১ ধারার মধ্য সেই ভাষা-ব্যবস্থাপনা আছে। তা ছাড়াও ‘অষ্টম তপশিল’ বলে একটি পরিশিষ্টও যোগ করেছিলেন। তার মোদ্দা কথা এই যে, দু’টি ভাষা হবে ভারতের সর্বভারতীয় প্রশাসনিক বা সরকারি কাজকর্মের ভাষা– ইংরেজি আর দেবনাগরি বর্ণে হিন্দি। এগুলো কিন্তু ‘রাষ্ট্রভাষা’ নয়, ‘রাজভাষা’ও নয়– কিছু অজ্ঞ হিন্দিভাষী যে-রকম দাবি করেন। বাকি প্রধান ভাষাগুলোর (এখন ২২টা) বেশিরভাগই বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা বা সহ-প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এইগুলি হল অষ্টম তপশিলের ভাষা। বাংলা তার মধ্যে অন্যতম। সংবিধানে বাংলার এই বৈধতা স্বীকৃত। এখনকার ‘ধ্রুপদি’ তকমাটা সেরকম কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি বা ক্ষমতায়নের চিহ্ন নয়। এই তপশিল বা তালিকার মধ্যে উর্দু, সাঁওতালি, বোড়ো ইত্যাদি কয়েকটি ভাষা কোনও কোনও রাজ্য সহযোগী বা গৌণ প্রশাসনিক ভাষা। কিন্তু যেগুলি রাজ্যের প্রধান এবং প্রশাসনিক ভাষা সেগুলি হল, সরকারি হিন্দি ছাড়া, বাংলা, অসমিয়া, নেপালি, ওডিয়া, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মলয়ালম, মারাঠি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, ডোগরি (কাশ্মীর) ইত্যাদি।
তা সংবিধান এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই রকম করে ভাষার ক্ষমতাবণ্টন করে দওয়ার পরে ‘অল লিভ্ড হ্যাপিলি এভার আফটার’ হল কি? না, তা হয়নি। ভাষা নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছে, এবং তা বহুরূপী। একটা হল হিন্দির একাধিপত্য চাপানোর জন্য কেন্দ্রীয় শাসকের নানা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রকল্প, যা নানা প্রদেশকে শঙ্কিত করে তুলেছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে স্কুলে হিন্দি ‘অবশ্যপাঠ্য’ করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তার একটি প্রকাশ দেখা গেল। দক্ষিণের দ্রাবিড়ভাষী রাজ্যগুলিও আগাগোড়াই এর বিরুদ্ধে।
৩.
কিন্তু হিন্দির সঙ্গে অন্যান্য ভাষার ঠোকাঠুকি এখানে আমার আলোচ্য নয়। আলোচ্য হচ্ছে একটি প্রাদেশিক ভাষা এবং আর কেউ নয়, আমাদের বাংলার অন্যান্য ভাষা-অঞ্চলে দুর্গতি, অস্যার্থে, বাংলাভাষীদেরও দুর্গতি।
এর একটা কেন্দ্র অসম, যেখানে বাংলাভাষার সমস্যার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সমস্যার একটু তফাত আছে। তা অসমের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। অসমে বরাক উপত্যকা অঞ্চলে– কাছাড়, ধুবড়ি ইত্যাদি জেলায়– প্রচুর ভূমিপুত্রকন্যা বাঙালি তো ছিলেনই, তা ছাড়াও উনিশ শতক থেকেই কৃষিকাজের জন্য তৎকালীন পুব বাংলা থেকে প্রচুর মুসলমান বাঙালিকে অসমিয়া জমিদাররাই আমন্ত্রণ করেন। এর ফলে এক সময় অসমিয়াদের মনে হয়, অসমে তাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন এবং এই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তারই ফলে স্বাধীনতার পরে অসমের বাঙালিদের ‘অসমিয়াকরণের’ একটি চেষ্টা শুরু হয়। চেষ্টাটি দু’-ধরনের। এক, অসমিয়া স্কুলে অন্যদের অসমিয়া পড়া, কখনও অসমিয়া মাধ্যমে পড়া চাপিয়ে দিয়ে বাংলাভাষাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হয়, আবার অন্যদিকে গত শতকের পঞ্চাশের বছরগুলির শেষ দিকে, বিশেষত, ১৯৬১-তে ‘বঙ্গাল খেদা’ বলে বাঙালিদের অসম থেকে তাড়ানোরও একটি আন্দোলন শুরু হয়। ওই আন্দোলনে অনেক বাঙালি অসম থেকে পালিয়ে আসেন।
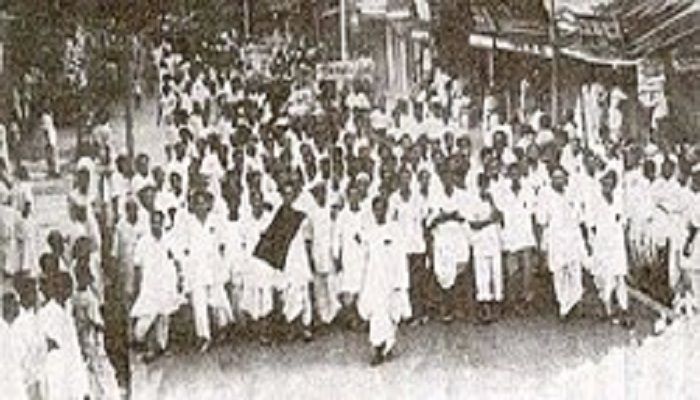
পরবর্তী কালে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে দাঙ্গা পরিস্থিতি থামে এবং বরাক উপত্যকায় বাংলাকে একটি সহকারী সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিতেও অসম সরকার বাধ্য হয়। কিন্তু অসমিয়া জনগোষ্ঠীর কট্টর অংশ এই সমাধান নিয়ে ক্ষুব্ধ থাকে, পরে অসমের রাজনীতিতে তা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকী, ১৯৮১-র জনগণনাতে অসমের ভাষাচিত্র ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়নি, তার কারণ প্রতি জনগণনাতেই অসমিয়া প্রশাসনের কেউ কেউ, আজকের হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতোই বাঙালিদের তাদের মাতৃভাষা অসমিয়া লেখার জন্য প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে হুমকি দিয়ে এসেছেন। ফলে অসমের বাংলাভাষা বিরোধের একটা কারণ জনসংখ্যার হিসেব নিয়ে অমূলক দুশ্চিন্তা। অবশ্যই আর-একটা কারণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এতে সাম্প্রদায়িক মাত্রা লাগে, অসমিয়াদের কাছেও বাংলাভাষী মানেই মুসলমান এবং বাংলাদেশি। অথচ, এটা বলার সময় তাঁরা ভুলেই যান যে, তাঁদের প্রদেশেই বরাক উপত্যকায় ও অন্যত্র প্রচুর বাংলাভাষী হিন্দু, তাঁরা ভূমিপুত্রকন্যাও বটে– বাস করেন।
৪.
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে– দিল্লি, হরিয়ানা (১৮ জুলাই, ’২৫– গুরগাঁও-এ বাঙালিদের হেনস্থার খবর এল), গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে বাঙালি বস্তিবাসী (দিল্লিতে) আর পরিযায়ীদের যে হেনস্থা আর নির্যাতন করা হচ্ছে, তার মূলে আছে বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা। দিল্লির বস্তিবাসীরা হয়তো এক সময় বাংলাদেশ থেকেই এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধের পরে, তাদের ভারত সরকারই আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তাদের অধিকাংশ মুসলমান, সেহেতু এখন তারা ভারতের হিন্দুত্ববাদী (হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান) রাজনীতিতে দীক্ষিত জনগোষ্ঠীর চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ভাষাবিদ্বেষ। তাদের অনেকেই ভারতীয় নাগরিক,–এবং ভারতীয় নাগরিকদের ভারতে থাকার বৈধ অধিকার আছে, ওই দুই বিদ্বেষ এ সত্যকে আড়াল করে দিচ্ছে।

অন্যান্য অঞ্চলেও কমবেশি তাই ঘটছে। আমরা জানি যে, পশ্চিমবাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা রাজ্যের বহু জেলা থেকে ভারতের নানা অঞ্চলে পরিযায়ী হন– করোনার সময়ে সেটা দেখা গেছে। তাতে হিন্দু মুসলমান– দুই জনগোষ্ঠীই থাকেন। এবং যেখানে কাজ পান, সেখানকার ভাষা তুলে নিতে অনেকেরই দেরি হয়, একেবারে ভিন্ন বংশের দক্ষিণি ভাষাগুলি তুলে নিতে তো আরও দেরি হবার কথা। ফলে স্থানীয়দের সঙ্গে যাওয়ামাত্রই তাঁদের ভাষায় কথা বলতে শুরু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা তাঁরা ভাঙা হিন্দি দিয়ে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলবেন, এই ব্যাপারটাতে স্থানীয়রা অসহিষ্ণু ও সন্দেহগ্রস্ত হয়ে তাদের বাংলাদেশি বলে নির্যাতন করবে– এ তো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। তাতে ভারতীয় নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে।
ফলে, অসমের ব্যবস্থা কী হবে সেটার কথা বাদ দিয়ে, পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কারা ভারতীয় আর কারা বাংলাদেশি (কিছু বাংলাদেশি থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা অস্বীকার করি না, কারণ পেটের খিদে অনেক সময় রাজনৈতিক সীমানা মানে না)– সেটা ভারত সরকার নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করুন, আর ভারতীয় বাঙালি শ্রমিকদের অনুচিত আর অন্যায় হেনস্থা রোধ করবার নিখুঁত উপায় নির্ধারণ করুন। বাংলাভাষীরা নিজেদের মধ্যে কথা বললেও তাঁদের ওপর জুলুম করা হবে, এই অমানবিক আর অসাংবিধানিক ঘটনাগুলি বন্ধ করুন।
৫
শেষে এই কথাটা বলার জন্য রেখেছি। ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েদের একটা ভাষা-সাক্ষরতা দরকার। তার মানে শুধু একাধিক ভাষা বলতে পারার ক্ষমতা নয়। তার মানে ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে তাদের জানতে হবে ভারতের ক’-টা প্রধান ভাষা আছে, ভারতের সংস্কৃতিতে তাদের গুরুত্ব কী রকম, সব ভাষাই, এমনকী ক্ষুদ্রতম বা অলিখিত ভাষাও সমান মর্যাদার, ভাষার সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই ইত্যাদি। ভারতের সব ভাষার স্কুলপাঠ্য বইয়ে এ সম্বন্ধে পাঠ থাকা উচিত, যা এখন এভাবে নেই। ভাষা সংক্রান্ত অশিক্ষা আর কুশিক্ষাও অনেক নাগরিক সমস্যার মূলে।
………………………………
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল
………………………………
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
