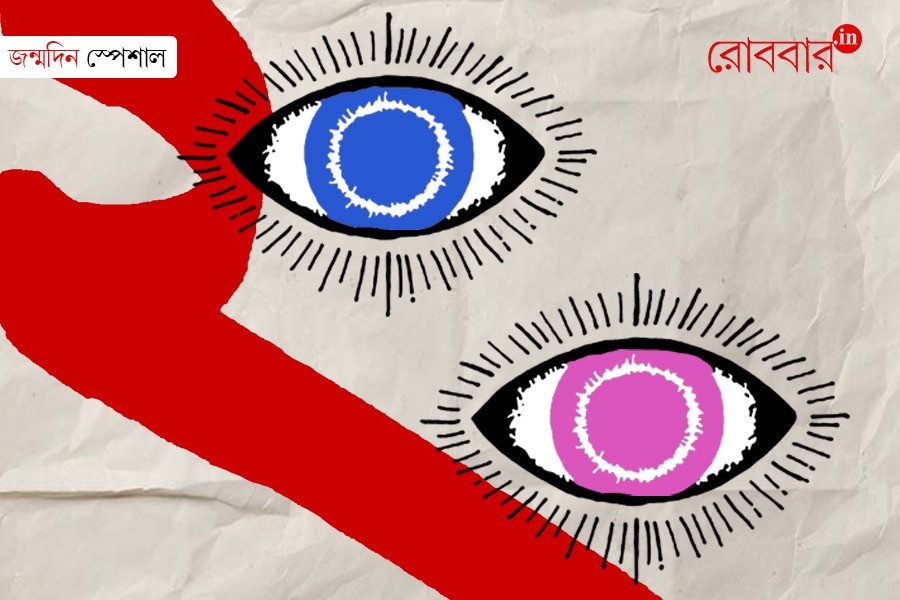
আমাদের মতো সাধারণ লোকের দিন তো আর দর্শনের পরিভাষা গুনে চলে না। আমরা বহুদিন ধরে বুঝি এবং মানি, ঈশ্বরের থাকা-না-থাকা নিয়ে যে দু’টি তরফ আছে দেশে, তারাই যথাক্রমে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’। তাঁর অস্তিত্ব মানে যে সে আস্তিক, যে তাঁর না-থাকায় ভরসা রাখে সে নাস্তিক। তিনি ছাড়া কিছুই আর নেই, এই যা কিছু দেখছি কিংবা দেখছি না– এই সবই তিনি কিংবা তাঁরই বিচ্ছুরণ, এমনকী, আমিও তাই, তাঁরই অন্তর্গত, তাঁরই ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা। এই অর্থে সবচেয়ে বেশি আস্তিক আসলে চরম না-পন্থী। এমনকী, আমিও একটি না-ই শেষ পর্যন্ত। হয় তিনি ছাড়া কিছু নেই, নয়তো আমি ছাড়া সবই অনুপস্থিত। উল্টোদিকে, কী আশ্চর্য, নাস্তিক হিসেবে যিনি চিহ্নিত, তাঁর সমস্তটাই ভরে আছে অস্তিত্ব।

নাস্তিক-আস্তিকের তর্ক সেই কবেকার… আরও বহু বহু দিন সেই তর্ক বেঁচে থাকবে নিশ্চিত। এক হিসেবে এই তর্ক বেঁচে থাকাটাই চমৎকার! একে অন্যের দিকে চোখ ঠেরে কথা বলছে, যেন জিতে গিয়েছে সে–ই, অন্যের ভাগে কেবল একগুঁয়ে গোঁড়ামি। শুধুমাত্র জেদ করছে বলেই অন্যজন, এখনও মেনে নিচ্ছে না ভুল। কখনও-বা হাল ছেড়ে দিয়ে একে অন্যকে বলে, থাক আজকের মতো, ফের একদিন বসা যাবে, আছে নাকি নেই তা নিয়ে কথা চলবে আবার, এখন ওঠা যাক। একে অন্যকে এ-ও বলে ফেলতে পারে, আপাতত ওইদিকে তাকাও দেখি, কী আশ্চর্য বেদনা ছিটিয়ে টিলার ওপারে ডুবে যাচ্ছে সূর্য, কীরকম গনগনে ঘা মাড়িয়ে দু’-তিন মাইল ছুটে এসেছে বাচ্চা ছেলেটি– শুনেছে কিছু খাবার বিলোনো হবে আজ এইখানে, হাত পেতে খাবার প্যাকেট নিয়ে দাতার দু’হাতে কেমন স্বতঃস্ফূর্ত চুমু দিয়ে চলে যাচ্ছে বালক, অচেনা মানুষটির দিকে সে ছড়িয়ে দিল কী এক মনোরম কৃতজ্ঞতা, আর তার পরেই কোন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা বুলেটের সামনে গিয়ে পেতেছে শরীর সেই ছেলে, তুমি দ্যাখো! বেদনায় ছিটকে পড়ছে, আছাড়িপিছাড়ি কোনও পাখি, দয়া নেই, প্রীতি নেই, মরমের চিহ্নমাত্র নেই, দ্যাখো দু’হাতে প্রকাণ্ড সিরিঞ্জ ধরে ছুটছে ও কে লোক, সারমেয়কুল বন্ধ্যা করে দিতে হবে, নির্বীজ করে তুলতে হবে তাদের, নইলে বিপদ খুব, মানুষের ঘরে আজ উপচে পড়া আদর জমানো আছে কত, কাকে দেব, কাকে স্নেহদান করব, পাত্র চাই, যে কেবল আমার স্নেহ-প্রীতি নেবে চুপ করে, নিজের দাবিটি তুলে বারবার বিড়ম্বনায়, বিরক্তিতে ফেলবে না কখনও, যখন ইচ্ছে হবে, ক্লান্ত মনে হবে, বিষণ্ণতা ফেনিয়ে উঠবে মুখে, ঠোঁটে, তখনই ডাকব কাছে, ও তো আমাদের অতিরিক্ত বাড়তি স্নেহ বইয়ে দেওয়ার এক পাত্র শুধু, কী হবে নিজের মতো বংশবৃদ্ধি করে, শুধু আমাদের স্বার্থে ওর বংশরক্ষা, তা নইলে এই একা শূন্যতা, এই উপচে পড়া প্রীতি আমি রাখব কোথায়? এই সব দৃশ্যে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার কথা বলে আপাতত নাস্তিক ও আস্তিক দু’জন স্থগিত রাখতে পারে স্রষ্টা পরমের অস্তিত্ব-বিষয়ক তর্ক।

২.
ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের এলাকায় নাস্তিক-আস্তিকের অর্থ যে আলাদা, ওখানে যে শ্রুতিবাক্যের ওপর অবিচল আস্থা রাখা-না-রাখার কথাই বিবেচ্য, সে আমরা জানি। কিন্তু কী করা যাবে, আমাদের মতো সাধারণ লোকের দিন তো আর দর্শনের পরিভাষা গুনে চলে না। আমরা বহুদিন ধরে বুঝি এবং মানি, ঈশ্বরের থাকা-না-থাকা নিয়ে যে দু’টি তরফ আছে দেশে, তারাই যথাক্রমে ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’। তাঁর অস্তিত্ব মানে যে সে আস্তিক, যে তাঁর না-থাকায় ভরসা রাখে সে নাস্তিক। তিনি ছাড়া কিছুই আর নেই, এই যা কিছু দেখছি কিংবা দেখছি না– এই সবই তিনি কিংবা তাঁরই বিচ্ছুরণ, এমনকী, আমিও তাই, তাঁরই অন্তর্গত, তাঁরই ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা। এই অর্থে সবচেয়ে বেশি আস্তিক আসলে চরম না-পন্থী। এমনকী, আমিও একটি না-ই শেষ পর্যন্ত। হয় তিনি ছাড়া কিছু নেই, নয়তো আমি ছাড়া সবই অনুপস্থিত। উল্টোদিকে, কী আশ্চর্য, নাস্তিক হিসেবে যিনি চিহ্নিত, তাঁর সমস্তটাই ভরে আছে অস্তিত্ব। আমার এবং সবার– সব কিছুর। এই ভরাট নদী, এই ধুলো, এই খেত, জমিজিরেত, বাগিচা, এই হিংসা-ঘৃণা-প্রীতি, এই ফিলিস্তিন, মণিপুর, নোয়াখালি, ভাগলপুর, মজফ্ফরনগর, এই হত্যালীলা– কী চমৎকারভাবে হত্যার পাশে আলগোছে বসিয়ে দেওয়া ‘লীলা’, এই মানব রচিত ঈশ্বরে প্রণত মানুষজন, এই হনুমানচল্লিশার পাশে লক্ষ্মীর আসনখানি– এই মাজার, মদিনা, মইনুদ্দিন চিশ্তি, মানুষের দরবার, উজাড় বসতি, সব সব। সমস্ত জুড়ে শুধু আছে আছে আর আছি। আমি আছি, ব্রহ্মাণ্ড নিকিয়ে তুলে, সাজিয়ে-গুছিয়ে, আছি। আছে আর আছি নিয়ে নাস্তিকের জগৎ-সংসার। অথচ সে ‘নাস্তিক’ নামে খ্যাত। এই সব প্রবল, প্রকট থাকার ঐশ্বর্য ছেড়ে কাল্পনিক না-থাকার জগতে চলে যেতে তার মন ওঠে না বলেই তার শিরোভূষণ হয়ে আছে নাস্তিক্য। থাকার জগতের সঙ্গে মানব-আকাঙ্ক্ষাধৃত জগতের মধুর ও তিক্ত সংলাপ কতদিন ধরে চলছে। নাস্তিক ও আস্তিকের নাম নিয়ে যাই বিভ্রাট হোক না কেন, তারা একে অপরের জন্য প্রাণান্ত করে। কিছুতেই অন্যকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কেননা তাহলে নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।
৩.
উপনিষদের প্রজ্ঞা ব্রহ্মের কথা এনেছিল। সে এক আশ্চর্য ধারণা! এই যা কিছু আমার চারপাশে তার অতিরিক্ত, তার বেশি সর্বদাই, তা বৃহৎ। কতটা বৃহৎ? না, এই প্রশ্নটাই অবান্তর। কতটা– এই মাপই এখানে অচল। কেননা তা অপার, অশেষ। পার এবং শেষ নেই বলেই তাকে ‘কতটা’ দিয়ে ধরা যাবে না। তা অনেক, প্রচুর, অমিত। মাপ বহির্ভূত। সেই যে বৃহৎ, অশেষ, অপারের ধারণা, তার কোনও ইচ্ছা আছে কি? চাহিদা আছে তার? বেদনা, আকুলতা আছে? সে নিয়ে আলাদা আলাদা মত। কেউ বলবেন, না নেই, কিছুই নেই তার মানবের মতো। চাওয়া নেই, দুঃখ নেই, বিষণ্ণতা নেই। তা আসলে চৈতন্যস্বরূপ। মহাচৈতন্য। মানুষের ক্ষুদ্র চৈতন্যের সাহায্যে তার আভাসটুকু মাত্র পাবে। সে মহাচেতন সব কিছু আবৃত করে রেখেছে, সর্বত্র ব্যাপ্তি তার। সেই অতিরিক্ত একইসঙ্গে অতি রিক্ত। সে সমস্তকে অন্তর্ভূত করে রাখে। সে এক।
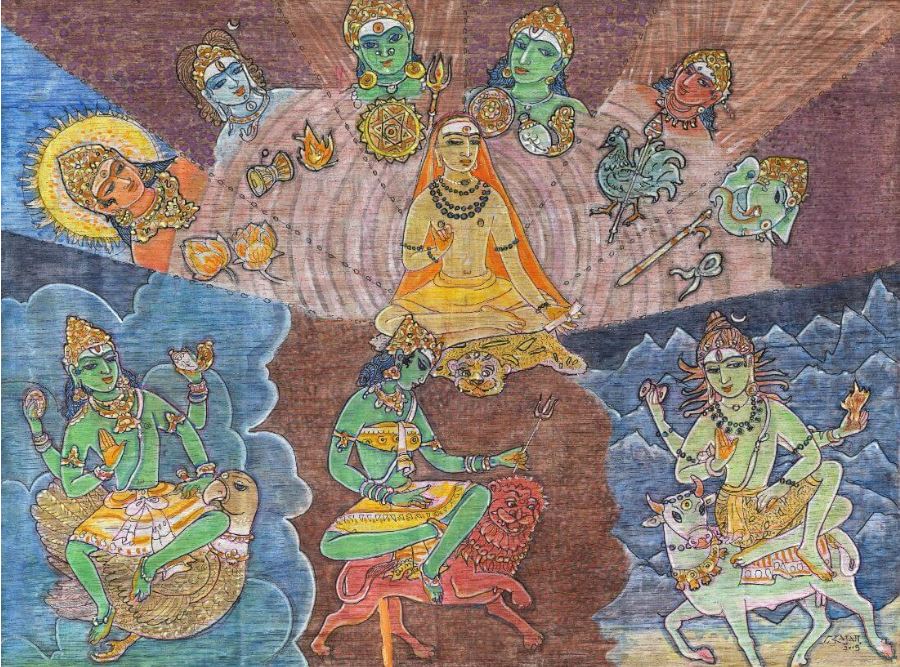
অন্য দল আবার এতে ব্যথিত হবেন। বলবেন, এই যে আমার অনুভূতিমালা, অঘ্রানের হোক আর পৌষের, প্রাপ্তির হোক আর ক্লান্তির, শূন্যতার হোক আর আহ্লাদের– এসব অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় সে বিরাট? তাকে আমার যাবৎ বেদনের অংশীদার করে নিতে যদি না-ই পারি, তবে সে বিরাট যে নিষ্ঠুর একাকিত্বে মরেই থাকবে সদা। তা কী করে হতে দিই আমি? আমার বেদনার ভাগ তুমিও নাও হে বিরাট। এই চাওয়ার রন্ধ্রপথেই এবার সেই বিরাটে জাগল গুণ, কেমনে নির্গুণ রাখি আমার সে পরমের অস্তিত্ব? তাই বর্ণচ্ছটা এল আমারই রংপাত্র থেকে। যতনে সাজানো হল বিরাট শূন্যতা। উপনিষদের ঋষিবচনে সেই শূন্য-পূর্ণ পরম আদিতে ছিল ‘যা’, ক্রমে সেই ‘যা’ হয়ে উঠল ‘যে’ এবং শেষে তাকে ছাপিয়ে এল ‘যিনি’। যার বস্তুরূপই ছিল অগ্রাহ্য, সে-ই ধরা পড়ল ‘তিনি’ সর্বনামে। তিনি এলেন; ক্রমশ সর্বনামের ছাতা বন্ধ করে, তিনি এসে দাঁড়ালেন প্রবল প্রতাপময় একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে, পরম বিশেষ্য রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঢেকে দিল আর সব কিছু। সর্বনামের মৃদুমন্দ আলোছায়া রূপান্তরিত হয়ে গেল চোখ-ধাঁধানো স্থায়ী আলোকবৃত্তে। কত কত মানুষ, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মায় ভেদ রাখতে ভুলে যায়। স্রেফ একটি আকার চিহ্নের তফাত একটি সার্বিক আকারের পরিবর্তন সূচিত করে দেয় একেবারে। ব্রহ্ম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ফুটে ওঠে ঈশ্বর।
শুধু এইমাত্র নয়। বিরাট পরম এক নিয়ে কী করব আমি? সমস্তই মায়া আসলে, প্রতিভাস, বিপুল প্রচ্ছায়াময় এ সংসার জেনে কী এমন লাভ? স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁর জগৎমিথ্যার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেও তো ‘আনন্দলহরী’ আর ‘সৌন্দর্যলহরী’র মতো কাব্যের ভিতরে গিয়ে পেতেছেন দর্শকের আসন– তাঁর চোখের সমুখে পার্বতীর রূপের প্রবাহ, ছুটে যাচ্ছে কটাক্ষ, কপোলে নরম মৃদু আলোড়ন তোলে কর্ণ-আভরণ, চোখে সুন্দরের নম্র আয়োজন– স্বয়ং মহেশ্বর স্তব্ধ হয়ে রন পার্বতীর লাবণ্যপ্রভায়। শিব-পার্বতীর এই সৌন্দর্যলীলার সামনে ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর কেমন মোহিত হয়ে যান। কৃপা চেয়ে নেন তিনি গিরিকন্যার কাছে, তাঁর সুরূপের দিকে যাতে চেয়ে থাকতে পারেন তিনিও– এমন প্রার্থনা করেন কাতরে। যেমন এই শ্লোকে, এইখানে পার্বতীর স্তুতির আড়ালে দেখুন, কেমন ফুটে আছে কাতরতা। শঙ্করাচার্যের ‘সৌন্দর্যলহরী’ থেকে এক টুকরো তরজমা–
‘হে শিবানী, সংসারে কাতর আমি,
তোমার নিকট থেকে আছি বহু দূরে,
তোমার ওই প্রসারিত দীর্ঘ দৃষ্টি যেন
আধেক-স্ফুরিত নীলপদ্ম মনে হয়,
সেই চোখ কৃপাস্নানে ভেজাক আমায়।
আমি দীন, ধন্য হয়ে যাব,
তোমারই বা তাতে কোন ক্ষতি?
বনে আর উঁচু ইমারতে
এক ভাবে কিরণ ছড়ায় চাঁদ, নেই তার কোনও পক্ষপাত।’
অমন নিখুঁত যুক্তিতর্কজালে বাঁধা শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, অমন এক অভেদসন্দর্ভ, কিন্তু তাকে প্রণতি জানিয়ে একে একে নেমে আসেন ভেদবাদী সন্ন্যাসীর দল, নিম্বার্ক, মধ্ব, রামানুজাচার্য। এ মহাজগৎ এক, দ্বৈতহীন– এই সত্য এক পাশে রেখে দুই-এর তাৎপর্য নিয়ে টীকাভাষ্য রচেন সকলে। বহু পরে, বিশ শতকের গোড়ায় সদ্যচল্লিশ রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে লিখেছিলেন, প্রাচীন ভারতের মনীষা যে এক-এর আদর্শ এনেছিল, তা কত মহান, কী অকাট্য। দশক না ফুরতে, এই একবাদী ভাবুকই দুই-এর রহস্যে মজে উঠলেন নতুন করে। ক্ষিতিমোহনের সাহচর্য তাঁকে মনে করিয়ে দিল, ভারতেরই অন্য এক ধরনের প্রজ্ঞা ‘দুই’ নিয়ে কী মহোৎসব রচনা করেছিল একদিন। উপনিষদের পৃষ্ঠা মেলে ধরে নতুন করে পড়তে থাকলেন রবীন্দ্রনাথ। ছাত্রদের ডেকে নিলেন সেই উল্লসিত নতুন আবিষ্কারের ভোরবেলাগুলিতে। উপনিষদের দীর্ঘ পুরাতন ঋষিবচনের ওপরে এসে পড়ল শীতসকালের আলো, একালের কবিদৃষ্টি। হয়ে উঠল ‘শান্তিনিকেতন’ প্রবন্ধমালা।

এক আর দুই-এর মধ্যে চুপিচুপি কত কথা চালাচালি হল মৃদুভাষে। দেখা গেল, সেই কবে থেকে, তুকারামে, আলোয়ার ও বীরশৈব কবিদের রচনায়, আরও কত সন্তবাণীতে এক ও দুই-এর এই কথাপরম্পরা চলেছে। এক-এর তীব্র কঠিনতা, নিরাসক্ত দৃঢ় যুক্তিক্রমে যখনই হাঁসফাঁস করে উঠেছে মানুষ, অনিবার্যভাবে তার মন টেনেছে দুই-এর রহস্য, লীলাময়তা। সে আবিষ্কার করেছে, ‘দুই’-এর হাতছানিটুকু না থাকলে, ‘এক’ কী ভীষণ একাকী। তার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই। তার বলারও কিছু নেই, শোনার লোক তো নেই-ই। অন্যদিকে, ‘দুই’ যতই রত থাক টানাপোড়েন রচনায়, বিরহিত হোক কিংবা প্রাপ্তিতে বিভোর, তারও অনিবার্য গতি ‘এক’ অভিমুখে। একে নিমজ্জিত হওয়ার বাসনাই তার যাবৎ অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, চপলতা সৃষ্টি করে। দুই মাঝে মাঝে বহুও হতে চায় ঠিকই, হয়ও, কিন্তু অন্তিমে তারা এক-অভিসারী। দুই-এর দুই প্রান্তে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসে যদি, তখন দুই বিরহ তৈরি করে নেয় চটজলদি। বিরহ বিচ্ছেদনাশক। বিচ্ছেদের শত্রু। শুধু চাওয়া দিয়ে বিরহ রুখে দেয় বিচ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষায় ধরে রাখে অপরকে। সেই অপরের নাম দেয় ‘তুমি’।
৪.
নাস্তিক-আস্তিকের মতোই এক এবং দুই-এরও অন্যকে ছাড়া চলে না। এক আর দুই-এর এই চিরসংলাপ যে ভাষায় চলে, তার ডাকনাম প্রেম। সে ভাষার যতিচিহ্নগুলির নাম কাতরতা।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
