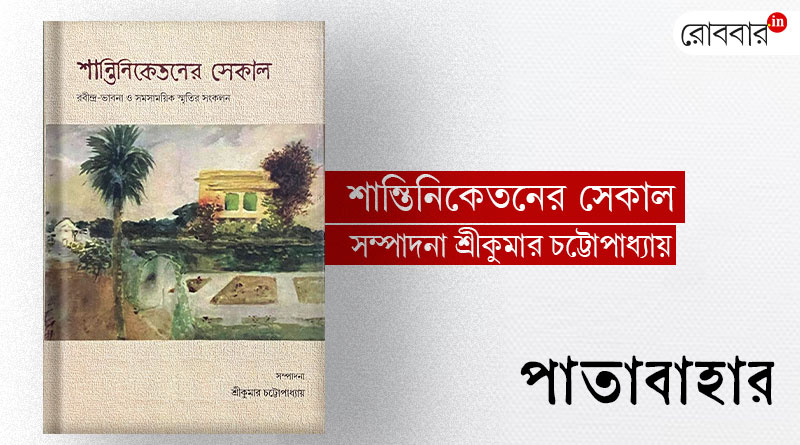
ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে রবীন্দ্র-প্রয়াণ– এই সময়কালকেই ধরতে চাওয়া হয়েছে বইটিতে। তবে নির্দিষ্ট কোনও পারম্পর্য মেনে যে রচনাগুলিকে সংকলিত করা হয়েছে, তা নয়। কিন্তু পরপর রসোত্তীর্ণ লেখাগুলির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ফেলে আসা সময়ের রোদ-বৃষ্টি-আলো পাঠককে ছুঁয়ে যেতে থাকে। লিখছেন বিশ্বদীপ দে।

‘শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।’ ১৩ বছর বয়সে স্কুলের শিক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। কবি যথার্থই প্রবেশ করেছিলেন ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে’। সেই জীবনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন ‘সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি।’ এই অনুভবই বুঝি তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তোলার। ‘শান্তিনিকেতনের সেকাল’ নামের এক সংকলনের প্রথম রচনা ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’-এ ধরা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের এই নিবিড় প্রতিফলন। ‘শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের’ কাজ শুরু করেন কবি। সেই বীজ কী করে মহীরুহে পরিণত হল, তারই খোঁজ দেয় এই বই।
কেবল রবীন্দ্রনাথ নন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র থেকে শুরু করে সৈয়দ মুজতবা আলী, লীলা মজুমদার-সহ বহু গুণীজনের রচনায় ধরা রয়েছে শান্তিনিকেতনের সেই শুরুর দিনের স্মৃতির জলছবি। সম্পাদক শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন রচনাগুলিকে। রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনার সমান্তরালে রয়েছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও নীহাররঞ্জন রায়ের তিনটি রচনা। এই রচনাগুলিতে রয়েছে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামের একটি স্কুল থেকে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হওয়ার সংক্ষিপ্ত রূপকে বোঝার চেষ্টা। যদিও নীহাররঞ্জনের লেখাটি একেবারেই সংক্ষিপ্ত। সংকলনের বাকি ১৪টি রচনা মূলত স্মৃতিকথাই। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে রবীন্দ্র-প্রয়াণ– এই সময়কালকেই ধরতে চাওয়া হয়েছে বইটিতে। তবে নির্দিষ্ট কোনও পারম্পর্য মেনে যে রচনাগুলিকে সংকলিত করা হয়েছে, তা নয়। কিন্তু পরপর রসোত্তীর্ণ লেখাগুলির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ফেলে আসা সময়ের রোদ-বৃষ্টি-আলো পাঠককে ছুঁয়ে যেতে থাকে।
রচনাগুলির চরিত্রে যে বৈচিত্র, তা সংকলনটিকে নিঃসন্দেহে আরও আকর্ষণীয় করেছে। যেমন লীলা মজুমদারের ‘আর কোনখানে’ শীর্ষক রচনায় তাঁর ঝরঝরে গদ্যে অম্লমধুর সব অভিজ্ঞতাই ধরা পড়েছে। পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে– কোদাল কাঁধে নন্দলাল বসু চলেছেন সদলবলে ‘ফাগুন লেগেছে বনে বনে’ গাইতে গাইতে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নীচু গলায় গাইছেন ‘বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে’। কিংবা কারও নামে রেগেমেগে নালিশ করায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘গায়ে ফোস্কা পড়েছে নাকি?’ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ‘যারা কাজ করতে চায় তাদের সমালোচনা শুনবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়, যারা কাজ করে না, তারা সমালোচনাও শোনে না।’ সব স্মৃতিই যে অভিনব, তা নয়। কিন্তু ‘জীবনের বহু ব্যর্থ বিফল বন্ধ্যা দিবস-মাসের মধ্যে অমনি একেকটি দিন তারার মতো জ্বলজ্বল করে।’ সেই সব দিনের কথায় চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে শুরুর দিনের সেই সব দিন।
আরও পড়ুন: জীবন থেকে হারানো জীবিকার অণুকথা
আবার সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘ভাণ্ডারে-গুরুদেব’ নামের দু’-পাতার ছোট্ট রচনায় আশ্চর্য হাস্যরসের সমাহার। ভাণ্ডারে নামের এক অবাঙালি পড়ুয়া সটান রবীন্দ্রনাথের জোব্বার পকেটে আধুলি পুরে দিলে সবাই অবাক হয়ে যায়। এমন কাজের অর্থ কী, জানতে চাওয়া হলে সে অম্লানবদনে জানিয়ে দেয়, ‘গুরুদেব কোনো্? ওহ তো দরবেশ হৈ।’ আসলে ঠাকুরমার নির্দেশ মেনে ‘সন্ন্যাসী-দরবেশকে দানদক্ষিণা’ করতে চেয়ে কবির বেশভূষায় ধোঁকা খেয়ে তাঁকে দরবেশ ঠাউরে বসেছিল সে।
প্রমথনাথ বিশীর ‘প্রথম অভিজ্ঞতা’ পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট্ট বোলপুর রেল স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গরুর গাড়ির সারি। সদ্য তৈরি হওয়া ‘বীথিকা’র ভেতরে ‘নূতন-ছাওয়া চালের খড়ের সিক্ত গন্ধ’ নাকে এসে লাগে। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার বর্ণনায় তিনি লিখছেন, ‘তখনও তাঁহার চুলদাড়ি সব পাকে নাই; কাঁচাপাকায় মেশানো, কাঁচার ভাগই বোধ করি বেশি।’
কেবল প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের লেখাই নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ– শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র থেকে অধ্যাপক, কিংবা এমন কেউ যিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আশ্রমের কাজে, তাঁদের লেখা রাখার পরিকল্পনা সংকলনটিকে বৈচিত্রময় করেছে। রয়েছে অনূদিত রচনাও। উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সন, রসা হায়নঅসির মতো বিদেশাগতদের লেখা এই বইয়ের অন্যতম সম্পদ। সংকলনের একেবারে শেষ লেখাটি বলরাজ সাহানীর। কিংবদন্তি এই অভিনেতার লেখাটি বিশেষ ঐশ্বর্যময়। শান্তিনিকেতনে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়েছিলেন সদ্যবিবাহিত বলরাজ। পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যৌবনের তেজে রূঢ়ভাবে জানিয়ে দেন, শান্তিনিকেতন দেখে তিনি হতাশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথায় বিচলিত হলেও ধৈর্য না হারিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাঁকে। সেদিন তা না বুঝলেও পরে কালের ফেরে শান্তিনিকেতনেই চাকরি করতে আসেন বলরাজ। আর এরপরই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনের প্রকৃত স্বরূপ তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। সেই উপলব্ধির কথা মন ছুঁয়ে যায়।
সব মিলিয়ে সেদিনের শান্তিনিকেতন ও তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের খোঁজ যেমন এই বই দেয়, তেমনই রবীন্দ্রনাথের চৌম্বক ব্যক্তিত্ব ও তাঁর দিনযাপনের বহু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বর্ণনা রক্তমাংসের মানুষটিকে পাঠকের চোখে প্রত্যক্ষ করে তুলতে থাকে। বইয়ের প্রচ্ছদটি সুন্দর। বানানের ভুলও যেটুকু চোখে পড়ে, একেবারেই নগণ্য। তবে একটি অনুযোগ থেকেই যায়। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের কিছু ছবি এই সংকলনকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে পারত। যে বর্ণনা কেবল লেখায় পড়া যাচ্ছে, তাকে আরও জীবন্ত করে তুলতে পারত একগুচ্ছ সাদা-কালো ছবি। বইটি পড়তে পড়তে সেই আক্ষেপটুকু থেকে যায়।
শান্তিনিকেতনের সেকাল
সম্পাদনা: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
কিশলয় প্রকাশন। ৩৩০ টাকা।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
