
‘সাড়ে চুয়াত্তর’ সিনেমার মেসবাড়িটি বাঙালির দিশিত্বে ভরা। সেখানে আমার ‘এ যৌবন’ গানের সঙ্গে নাচে-তালে যে শরীরগুলি সংগত করছিল সেই ধুতিপরা, খালি-গা, গেঞ্জিপরা নানা কিসিমের রোগা-মোটা-লম্বাটে-বেঁটে অবয়বগুলি বাঙালির অম্বলে জ্বলন্ত, সকালের পেট-পরিষ্কারের চিন্তায় অফুরন্ত। তাদের দাপটে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ সিনেমায় উত্তমকুমারকেও ম্লান লাগে। শুধু মনে থাকে ‘মাসিমা মালপো খামু’ এই সংলাপ।
গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

দিশি চেনার চোখ চাই, দিশি বোঝার মন চাই। সবার থাকে না, মধ্যবিত্ত বাঙালি ও তার একটু উপর-নিচের লেয়ারের যাঁরা বাঙালি, তাঁদের নাকি দিশি চেনার চোখ-মন থাকে, আছে। অন্তত থাকুক বা না-থাকুক দাবি করেন আছে। বাঙালি ইশকুল মাস্টার বাংলা ক্লাসে শেখায়, “দেশ থেকে পদান্তরে দেশি। দেশ বিশেষ্য। দেশি বিশেষণ। নিধুবাবু সেই কবে গেয়েছিলেন ‘বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা’। সেই দেশী বা দেশি তারপর দিশি। ই-কার, এ-কারকে ই-কার করে দিয়েছে। স্বরধ্বনির সংগতি সাধন। স্বরসংগতি।”

বাজারু বাঙালি ওদিকে স্বর সংগতি-টংগতিকে পাত্তা দেয় না। পটলের রং দেখে এক লহমায় বলে দেয় কোনটা দিশি, কোনটা হাইব্রিড। হাতে বেগুন নিয়ে লুফতে লুফতে বলে দেয় পাকা না কচি। বলে দেয় বেগুনপোড়া করলে কেমন লাগবে! ভাগ্যিস বলতে পারে, তাই জাতি হিসেবে বাঙালি এখনও পটল তোলেনি। রুটির সঙ্গে তেল-লঙ্কামাখা বেগুনপোড়া খাচ্ছে। তার দিশি-সংস্কৃতি দিশি-বাংলার অলিতে-গলিতে বিরাজ করছে। তার কোনওটা ভালো– কোনওটা খারাপ, কোনওটা স্বাস্থ্যকর– কোনওটা অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু দিশি বাঙালিত্বের স্বাদে-গন্ধে ভরা। সেই ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর আগের আমল থেকে এই ‘দিশিপনা’ চলে আসছে। যেমন এই বাজার করা। বাজার করার নানা রকম, বাজারের দ্রব্যও বিবিধ। সেকেলে দিশি বাংলায় শব্দটি অবশ্য ‘বাজার’ নয়, বেসাতি!
ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণলেখয় ফুট কেটেছিলেন যে, ঈশ্বর গুপ্তের মতো খাঁটি বাঙালি আর হয় না, ঈশ্বর গুপ্তের মতো খাঁটি বাঙালি আর চাই না। বঙ্কিম ‘খাঁটি’ বলতে একরকম জিনিস বুঝতেন, পুরো ঠিক বুঝতেন কি না, সে অন্য কথা। তবে না চাইলে কী হবে? রয়ে গেল। বাঙালির ঈশ্বর গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত পূর্ব সংস্কৃতি রয়ে গেল নানা রূপে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ু দত্ত যেভাবে বেসাতি করে সেই হল বাঙালির বাজার করা। ঝোপ বুঝে কোপ মারার দিশি বাঙালি কৌশল, ভাঁড়ু নানা কায়দায় জিনিস তুলছে। একবার চালওয়ালার কাছে যায়, আরেকবার তেলওয়ালার কাছে। দ্বিজমাধব লিখেছিলেন–
‘কি তৈল কি তৈল বলি হাত জাবড়ায়ে।
আপনার গোপে দিল ছাবালের মাথায়।।’
এই হল দিশি-বাঙালির দিশি চরিত্র আর দিশি কবির দিশি ভাষা। দাম না দিয়ে বিনি-পয়সায় কীভাবে জিনিস আদায় করতে হয় তার মোক্ষম ছবি। হাত দিয়ে জাবড়ে তেলের পাত্র থেকে খানিকটা তেল আদায় করে নিজের গোঁফটিকে তেল চুকচুকে করে তুলল ভাঁড়ু, তারপর যা বাঁচল, তা দিয়ে ছেলের রুক্ষ মাথা সিক্ত করে নিল। ‘জাবড়ায়ে’ এই শব্দটি অনবদ্য– ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত বহুল বাংলার থেকে গোত্রে আলাদা, কিন্তু কী চিত্রময়! ভাঁড়ুর হাতের থাবাটি তেলের ওপর পড়ে তেল সাঁটাচ্ছে। জাবড়াচ্ছে।
…………………………….
বাঙালির রান্নায় আগে পড়ত না এখন যেটি পড়ে তার নাম বাঙালি উচ্চারণে ‘টমেটো’। এই ‘টমেটো’কে অনেক বাঙালি এখনও ‘বিলিতি বেগুন’ বলে। সুতরাং, আর কী? সংকর সাধনাতেই বাঙালি স্বাধীন। সংকরই বাঙালির দিশি। বাঙালির দিশি খাঁটি নয়। বাঙালির কমলকুমার দিশি মদ খেতেন, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণে মজে থাকতেন, আবার ফরাসি ভাষায় বাঁচতেন। বাঙালির কমলকুমার সংকর, বাঙালির কমলকুমার দিশি।
…………………………….
সাধে কি বিদ্যাসাগর যে হাতে ‘বর্ণপরিচয়’ লিখেছিলেন, সেই হাতেই দিশি বাংলা শব্দ সংগ্রহ করতে বসেছিলেন! ঐক্য, বাক্য, মাণিক্যের বর্ণপরিচয়ের বাইরে বাংলা ভাষার সে আরেক রূপ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্যসম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অনুমতিক্রমে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সংকলিত ও স্বহস্ত লিখিত ‘শব্দ সংগ্রহ’ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে আঁকুবাঁকু, কসকস, কাতুর কুতুর, কুটুরকাটুর, কেঁটকেঁট, খুটখুট, খিটখিট জাতীয় শব্দের ছড়াছড়ি। বিদ্যাসাগর দিশি বাংলা ভাষার শব্দগুলির পদান্তরিত রূপ তাঁর শব্দ সংগ্রহে রাখতে কসুর করেননি। শব্দের রূপ না বদলালে শব্দ ব্যবহার করা যায় না। ‘খিটখিট’, ‘খিটখিটান’, ‘খিটখিটিআ’– তিনটেই আছে তাঁর সংগ্রহে। বিদ্যেসাগরের শব্দ সংগ্রহ তো এক অর্থে শব্দের বেসাতি, শব্দের বাজার। সেই বাজার করার মূল লক্ষ্যই হল দুই বাঙালির শব্দ ঝোলায় নেওয়া। বিনি পয়সায় পাচ্ছি যখন নেব না কেন! বাঙালির ভাষার আবার হিন্দু-মুসলমান! ইন্তিহাম, ইমাম, ইমামদার, ইমারত, ইমারতি– বিদ্যাসাগর তুলে দিব্য নিয়েছেন।

ভাঁড়ুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য একটাই। ভাঁড়ু স্বার্থপর আর বিদ্যাসাগর পরার্থপর। দেশে দুর্ভিক্ষ। বিদ্যাসাগর অন্নসত্র খুললেন। মুদির দোকানে বলে দিলেন রুক্ষচুল বাগদি মায়েদের তেল দিতে। মুদি জাত মানেন। তাই তেল দিচ্ছেন দূর থেকে, পড়ে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর হাতে তেল নিয়ে বাগদি মায়ের রুখু চুলে লাগিয়ে দিচ্ছেন। নিজের গোঁফ কিংবা ছেলের মাথা তৈলসিক্ত করার জন্য বিদ্যাসাগর বিনাপয়সায় তেল নেওয়ার পাত্র নন। পরার্থপর দয়ারসাগর সংকীর্ণ অর্থে দিশি বাঙালি হতে পারলেন না। পরনে তাঁর দিশি পোষাক। ধুতি আর চাদর। কিন্তু মন বা স্বভাব মধ্যবিত্ত দিশি বাঙালির মতো নয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাঙালিকে ‘আত্মঘাতী’ বলে দাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট। বিদ্যাসাগরকে ধুতি-চাদর পরা ‘বিদেশি’ বলেই তিনি মান্য করতেন। আমরা বলি বিদ্যাসাগর খাঁটি নন, সংকর, তবে দিশি। সংকর মানে মিশ্র। বাঙালি দিশির চাদরে বিদেশিকে ঢুকিয়ে সংকর করে তোলে, বিদ্যাসাগরও তাই করেছিলেন।
বাঙালি বাজার করবে, খাবে আর অম্বলে জ্বলবে। এ বাঙালির দিশি রোগ। সর্ব রোগের শিরোমণি। বলা ভালো, বাঙালি মনে করে যে কোনও রোগের মূলে আছে অম্বল। বাঙালির হৃদয় নেই, মাথা নেই, আছে শুধু পেট। বঙ্কিমচন্দ্র মনের দুঃখে লিখেছিলেন– বন্দেমাতরম্ লিখে লাভ নেই, বন্দেউদরং লেখাই বিধেয়। অম্বলের জ্বালায় বাঙালি কী করে? হজমিগুলি খায়, জোয়ান চিবোয়। আর সকালবেলায় পেট পরিষ্কারের সাধনা করে। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ সিনেমার মেসবাড়িটি বাঙালির দিশিত্বে ভরা। সেখানে আমার ‘এ যৌবন’ গানের সঙ্গে নাচে-তালে যে শরীরগুলি সংগত করছিল সেই ধুতিপরা, খালি-গা, গেঞ্জিপরা নানা কিসিমের রোগা-মোটা-লম্বাটে-বেঁটে অবয়বগুলি বাঙালির অম্বলে জ্বলন্ত, সকালের পেট-পরিষ্কারের চিন্তায় অফুরন্ত। তাদের দাপটে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ সিনেমায় উত্তমকুমারকেও ম্লান লাগে। শুধু মনে থাকে ‘মাসিমা মালপো খামু’ এই সংলাপ।

এই সব দিশিত্ব হারিয়ে অনেকে বলে, যেমন বঙ্কিম বলেছিলেন, বাঙালি সংকর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের মতো খাঁটি বাঙালি আর চাই না। গোড়াতেই গলদ। বাঙালি কবে আর খাঁটি? চিরকালই বাঙালি সংকর! সেই যে চর্যাপদের বাংলা ভাষার কবিরা তাঁরা যে বৌদ্ধ ধর্মের সাধক সে বৌদ্ধ ধর্ম তো বুদ্ধদেব প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম নয়। তার মধ্যে তন্ত্রের মিশেল। নগরের বাইরে ডোম্বির কুটীর। শবর-শবরী মহাসুখ সন্ধানী। এই বাঙালির দিশি ধর্মের বিশেষ রূপ। দিশি মানে ‘খাঁটি’ নয়। দিশি মানে নিজের করে নেওয়া। দিশি মানে মিশেল দিতে শেখা। বাঙালির মতো মিশেলবাজ আর কে আছে? যেখান থেকে যা পাচ্ছে নিজের মিশেলে দিশি করে নিচ্ছে। বিদ্যাসাগরের ‘শব্দ সংগ্রহ’টি ইষ্টকিং, ইষ্টাম্প, ইষ্টিমার, ইষ্টেট শব্দকে ঠাঁই দিয়েছে। এগুলি আদতে ইংরেজি শব্দ হতে পারে। তবে বাঙালির পাল্লায় সব সংকরত্ব নিয়ে দিশি শব্দ হয়ে উঠেছে।
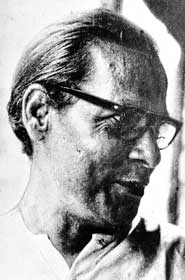
সুতরাং, যাঁরা বলেন, এই ভুবনায়ন বাঙালির ‘দিশিত্ব’ ও ‘খাঁটিত্ব’ হরণ করছে, তাঁরা ভুল বলছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই বাঙালি বিলিতিকে সংকর করে দিশি বানিয়ে ছাড়বে। বাঙালির রান্নায় আগে পড়ত না এখন যেটি পড়ে তার নাম বাঙালি উচ্চারণে ‘টমেটো’। এই ‘টমেটো’কে অনেক বাঙালি এখনও ‘বিলিতি বেগুন’ বলে। সুতরাং আর কী? সংকর সাধনাতেই বাঙালি স্বাধীন। সংকরই বাঙালির দিশি। বাঙালির দিশি খাঁটি নয়। বাঙালির কমলকুমার দিশি মদ খেতেন, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণে মজে থাকতেন, আবার ফরাসি ভাষায় বাঁচতেন। বাঙালির কমলকুমার সংকর, বাঙালির কমলকুমার দিশি। বাঙালি অহর্নিশি দিশি থাকুক, দিশিতে বাঁচুক।
………………………..
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন
………………………..
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
