
সধবা নারী হয়ে অঘোরকামিনী নিঃসংকোচে একদিন পরে নিয়েছিলেন সাদা থান। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে মুছেছিলেন মাথার সিঁদুর, খুলেছিলেন হাতের শাঁখা-পলা। নারীর শরীরে এই বস্তুগুলোর ভূমিকা কতটা অসার, এইটা অনুভব করার মতো মন তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন অবলীলায়। কতটা যুক্তিবাদী মন হলে তবে এটা সম্ভব, আজকে একুশে দাঁড়িয়েও সেটা বিস্ময় জাগায়। আসলে পোশাক, অলংকার একটা আভরণ মাত্র। সেটা নিজের সুবিধামতো, নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে প্রতিটি মানুষের বেছে নেওয়া উচিত– এই সহজ কথাটা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন সহজে।
প্রচ্ছদ শিল্পী: দীপঙ্কর ভৌমিক

১৮৯১ সালের এক সকাল। পাটনার বাঁকিপুর স্টেশনে সেদিন বহু মানুষের জমায়েত। হঠাৎ তারই মাঝে এক পুরুষ তাঁর প্রিয় নারীর ললাটে এঁকে দিচ্ছেন চুম্বনরেখা। আকস্মিক এই ঘটনায় অনেকের চোখেই সেদিন বিস্ময়, আবার কারও কারও চোখে আনন্দ। অপলকে দেখছে সকলেই। আজকের মতো তো সাবলীল হয়নি সেদিনের নারী-পুরুষের সম্পর্ক। তাই মিশ্র এক অনুভূতির ঘোর লাগে উপস্থিত জনতার চোখে। আর যে নারী এবং পুরুষটিকে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতি, তাঁদের উভয়ের চোখে তখন ভয়, চিন্তা এবং অনাবিল আনন্দ মিশ্রিত একদৃষ্টি।
এই ভয়, চিন্তার কারণ, নারীটি চলেছেন একা একা বহুদূর, পিছনে ফেলে যাচ্ছেন এই পুরুষটিকে, নিজের ছয় সন্তানকে, আর বৃহৎ একটা পরিবারকে। আর আনন্দ, এক নবজগতকে আলিঙ্গনের। তাই সম্ভবত পুরুষটি নিজের স্পর্শে আশ্বস্ত করতে চাইছিলেন এই নারীকে। এরপর দীর্ঘ ১০ মাস তিনি কাটাবেন লখনউয়ের উওমেন কলেজে। পরিচিত হবেন খ্রিস্টান ধর্ম ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির সঙ্গে। এই নারীর তৎকালীন পরিচয়, তিনি বাঁকিপুর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী অঘোরকামিনী রায়।

উনিশ শতকের আর পাঁচটা মেয়ের মতই মাত্র ১০ বছর বয়সেই প্রকাশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় অঘোরকামিনীর। সেই সময় স্বামীর আয় কম, তাই সংসারের অনেক দায়িত্ব এই ছোট মেয়েটাকে সামলাতে হয়েছিল। কিন্তু স্বামী প্রকাশচন্দ্র কলেজে পড়া ছেলে, তাই কলকাত্তাইয়া হাওয়া গায়ে মেখে স্ত্রীকে শিক্ষিত করার চেষ্টা তাঁর প্রবল। রাতের অন্ধকারে বন্ধ ঘরে চলে স্ত্রীকে পড়ানোর প্রক্রিয়া। স্ত্রীর উৎসাহে দ্রুতই সাফল্য আসে। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র হঠাৎই গ্রহণ করে বসলেন ব্রাহ্মধর্ম। তার রোষ গিয়ে পড়ল স্ত্রী অঘোরকামিনীর ওপর। প্রকাশচন্দ্র বুঝলেন স্ত্রীকে গ্রামে রাখা যাবে না। তাই নিয়ে এলেন নিজের কাছে। এরপর স্বামীর শিক্ষায় আর নিজের বুদ্ধিমত্তায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্ম সমাজের রীতি-নীতিতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে লাগলেন অঘোরকামিনী। যে ব্রাহ্মসমাজ নারী শিক্ষা, নারী প্রগতির কথা বলে, সেই ব্রাহ্মসমাজেই যে পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসে উপাসনা করার অধিকার নারীর নেই– এই ভাবনা তাঁকে আহত করেছিল। ১৮৮১ সালের এক সকালে নিজের মনের জোরেই সকল নারীর জন্য এই অধিকার অর্জন করেন অঘোরকামিনী। শুরু হয় অঘোরকামিনীর প্রথা ভাঙার অধ্যায়।
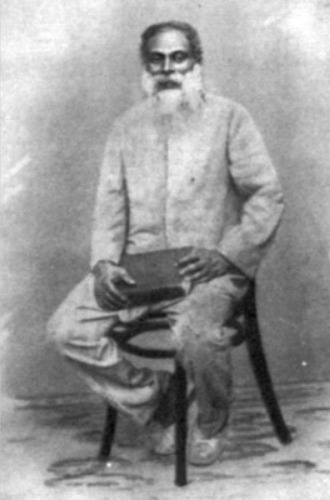
যে নবজাগরণের ঢেউ নারীকে প্রথাগত শিক্ষার অঙ্গনে কিংবা বিদেশের মাটিতে পা রাখতে শিখিয়েছিল। অঘোরকামিনীর মতো গৃহিণীরা সেই ঢেউয়েই ভাসিয়েছিলেন সংসারের চিরাচরিত প্রথাকে। সধবা নারী হয়ে নিঃসংকোচে একদিন পরে নিয়েছিলেন সাদা থান। এক্ষেত্রে সংসারের খরচ বাঁচানোর যুক্তি বড় সহজ ‘কেজো’ যুক্তি। সধবা হয়ে অবলীলায় সাদা থান পরে নেওয়া অন্তত উনিশ শতকে তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে মুছেছিলেন মাথার সিঁদুর, খুলেছিলেন হাতের শাঁখা-পলা। নারীর শরীরে এই বস্তুগুলোর ভূমিকা কতটা অসাড়, এইটা অনুভব করার মতো মন তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন অবলীলায়। কতটা যুক্তিবাদী মন হলে তবে এটা সম্ভব, আজকে একুশে দাঁড়িয়েও সেটা বিস্ময় জাগায়। আসলে পোশাক, অলংকার একটা আভরণ মাত্র। সেটা নিজের সুবিধামতো, নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে প্রতিটি মানুষের বেছে নেওয়া উচিত– এই সহজ কথাটা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন সহজে। তাই শাড়ি পরে পাহাড়ে ওঠার ঝক্কি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। আবার রোজ বাহিরে কাজে যেতে হলে ঘোমটা মাথায় দেওয়াটা কতটা অসুবিধার সেটাও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্টে তৈরি পোশাকে খসে গিয়েছিল ঘোমটা, বদলে গিয়েছিল শাড়ি।
ভূনাগ রাজার রানির মতো পরপুরুষকে পত্র না লিখলেও, নিজের রাজা প্রকাশচন্দ্র রায়কে ‘প্রকাশ’ নামে সম্বোধন করে পত্র তিনি লিখেছিলেন, উনিশ শতকের নারীর সহজাত সংকোচ কাটিয়ে। আবার ‘প্রকাশ’ কখনও কখনও বদলে গিয়েছিল আদুরে নাম পিকু-তে। লখনউ থাকাকালীন রোজকার পত্রাবলি উনিশ শতকের সংকোচহীন আধুনিকা এই নারীর পরিচয় বহন করে।

তাঁর উপাসনা কক্ষের দ্বার চিরকাল সকল ধর্মের মানুষের জন্য ছিল মুক্ত। নিজের মনকেও ঠিক এতটাই মুক্ত করেছিলেন যে, হরিনাম করতে কিংবা খ্রিস্টান ধর্মের নিয়ম নীতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। আসলে, ধর্ম অঘোরকামিনীকে বাঁধেনি, অঘোরকামিনী নিজেই রপ্ত করেছিল ধর্মকে। তাই ব্রাহ্ম হয়ে হরিনামের বুলি নিয়ে অবলীলায় পৌঁছেছিলেন, মানুষের দ্বারে, নিঃসংশয়ে, নিঃস্বার্থে। বিধবা-বিবাহ, কিংবা অসবর্ণ বিবাহ কোনও কিছুই এই নারীর মনে দ্বিধা তৈরি করেনি। কোনও জাত, ধর্ম, বর্ণ কোনও দিন বড় হয়নি তাঁর কাছে। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’– এই সহজ সত্য নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন, নিজেই বিশ্বাস করেছিলেন। আসলে নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে, যে মুক্ত মন, যে মুক্ত চিন্তার প্রয়োজন, অঘোরকামিনীর কাছে সেটা ছিল সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র।
…………………………………………
ধর্ম অঘোরকামিনীকে বাঁধেনি, অঘোরকামিনী নিজেই রপ্ত করেছিল ধর্মকে। তাই ব্রাহ্ম হয়ে হরি নামের বুলি নিয়ে অবলীলায় পৌঁছেছিলেন, মানুষের দ্বারে, নিঃসংশয়ে, নিঃস্বার্থে। বিধবা-বিবাহ, কিংবা অসবর্ণ বিবাহ কোনও কিছুই এই নারীর মনে দ্বিধা তৈরি করেনি। কোনও জাত, ধর্ম, বর্ণ কোনও দিন বড় হয়নি তাঁর কাছে। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’– এই সহজ সত্য নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন, নিজেই বিশ্বাস করেছিলেন। আসলে নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে, যে মুক্ত মন, যে মুক্ত চিন্তার প্রয়োজন, অঘোরকামিনীর কাছে সেটা ছিল সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র।
…………………………………………
মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতটা, সেটা অনুভব করে একসময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নিজেই প্রতিষ্ঠা করবেন মেয়েদের স্কুলের। এই মেয়েদের স্কুল চালানোর জন্য নিজের যে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, সেটা অনুভব করে ৩৫ বছর বয়সে অঘোরকামিনী গিয়েছিলেন লখনউতে মিস থাবর্ন প্রতিষ্ঠিত কলেজে। ফিরে এসে নিজের বাড়িতেই শুরু করলেন মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল। যে স্কুল আজও বাঁকিপুর গার্লস হাই স্কুল নামে দাঁড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের এক গৃহবধূর সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা চিন্তা-চেতনার চিহ্ন হয়ে। অথচ মাত্র ২৯ জন বাঙালি মেয়ে আর ১৫ জন হিন্দুস্থানী মেয়েকে নিয়ে এই স্কুলের পথচলা শুরু।

নারী জন্মলগ্ন থেকেই সমাজপ্রদত্ত দু’টি অধিকার নিয়েই জন্মায়। এক, সন্তান প্রসবের দুই, রান্নাঘরের। তাই তার জন্য ছোটবেলাতেই বরাদ্দ হয়, রান্না করার ছোট হাঁড়ি-কুঁড়ি। এই ছোট্ট ছোট্ট খেলার সামগ্রীগুলোই কবে যে বড় হয়ে যায় সেটা সে টেরও পায় না, অথচ রান্নাবাটি খেলাও তার শেষ হয় না আমৃত্যু। অঘোরকামিনী বুঝেছিলেন এই দু’টি অধিকারের অসাড়তা। তাই তাঁর স্কুলের মেয়েদের তিনি মাত্র ১৫ দিনে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, রান্না করা। যাতে কষ্টে করে পড়াশোনার জন্য পাওয়া মাত্র সাত-আটটা বছর, রান্নাঘরেই হারিয়ে না যায়। কিন্তু, প্রথম অধিকারের যন্ত্রণা বুঝতে দেরি হয়েছিল তাঁরও। কিন্তু বুঝেছিলেন, সন্তানের জন্মের নিয়ন্ত্রণ করাটা প্রয়োজন– আর সেটা নারী চাইলে করতেই পারে।
পিতা-মাতা মেয়ের নাম রেখেছিলেন, অঘোরকামিনী। তাঁরা কী ভেবে নাম রেখেছিল, ইতিহাসে সে তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু, যে নারী গভীর, কিন্তু ভয়ংকর নয়। অথচ রুদ্রের মতো যে পুনর্গঠিত হতে পারে, সেই অঘোর। নিজের নামের অর্থের, প্রকাশ তাঁর কর্মে। নিজের জীবনের চর্চায় আর চর্যায় উনিশ শতকীয় এই নারী দেখিয়েছিলেন, নারী চাইলে নিজেদের জীবনযাপনের পথটা নিজেই এঁকে নিতে পারে। সমাজের বিছিয়ে দেওয়া কাঁটার বদলে সে নিজের পথে বিছিয়ে নিতে পারে, পছন্দের ফুল। তাই অঘোরকামিনী সময়ের রীতি মেনে দেবী হননি, হয়েছিলেন– ‘রায়’, ‘মিসেস রায়’। এই কারণে যদি বলি, অঘোরকামিনী রায়, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের মা, তাহলে বোধহয়, নিজেকে আবদ্ধ করলাম সমাজের প্রথাগত চিন্তার আবদ্ধতায়। অপমান করে বসলাম, প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, ব্যতিক্রমী সেই নারীকে। বরং মনের মুক্তি সঙ্গে কলমের শান্তি লেগে থাকে, অঘোরকামিনী রায়ের কনিষ্ঠ সন্তান পশ্চিমবঙ্গের রূপকার তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়– এই শব্দবন্ধের মধ্যে।
……………………………
ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন
……………………………
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
