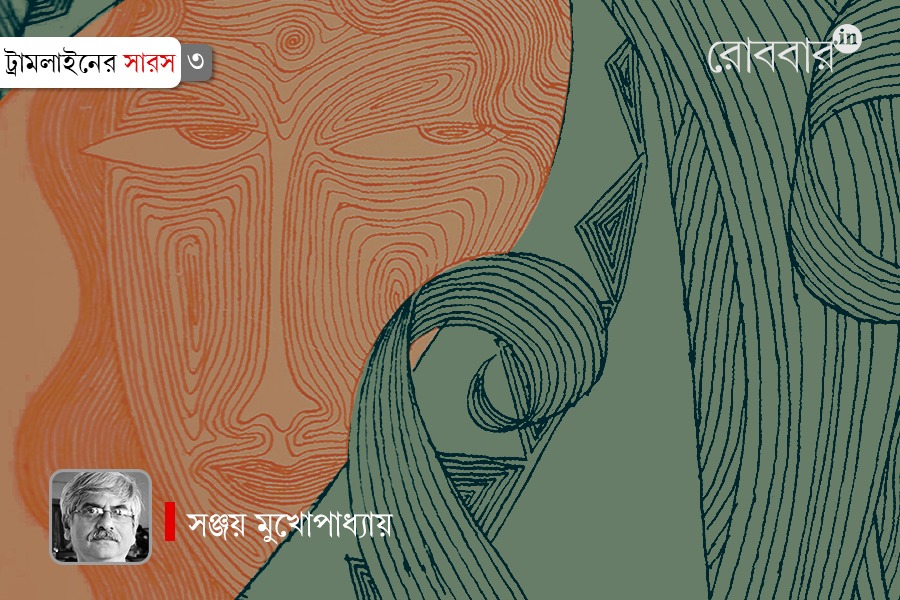
বনলতা সেন ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নকলনবিশরা এডগার অ্যালান পো-এর ‘ওড টু হেলেন’ কবিতাটির উল্লেখ করেন বনলতা সেন প্রসঙ্গে, কিন্তু কিঞ্চিত ইতিহাসবোধ অস্থিতে ও ধমনীতে প্রবাহিত থাকলেই বোঝা যায় এই কবিতার প্রকৃত আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের ১৯৯৭ সালে লিখিত কবিতা ‘স্বপ্ন’। দুই কবিতাতেই অলৌকিক ও অতিলৌকিক দু’জন নারী, অথচ অন্তর্গত দার্শনিকতায় উভয়ে কত যোজন যোজন দূরত্বের।

৩.
অতএব রবীন্দ্র বিরোধিতা তো তুচ্ছ একটি উপলক্ষ: তুমুল সতর্কতায় জীবনানন্দ পার হয়ে যাচ্ছিলেন ঐতিহ্যের ধারা-উপধারা। তাঁর কাব্যে প্রখর সচেতনতায় বর্জন করেছিলেন, বরিশালের এক বাঙালির পক্ষে যা অচিন্তনীয়– বর্ষা ঋতু। আদি রোমান্টিকতার অবসান ঘোষণা করে তাঁর কাব্য পরিহার করে যায় বসন্ত ঋতু, গোলাপের মতো ফুল বা কোকিলের মতো পাখি, নয়তো দক্ষিণ সমীরণ, যেহেতু তা প্রচলিত বাংলা কবিতার আঙরাখা। তবু আমি বলব– এ সমস্তই তাঁর প্রসাধন চর্চা। ‘মহাপৃথিবী’ ও ‘সাতটি তারার তিমির’ শুধু ভৌগলিক স্থানান্তরণ নয়, বরং অধিকতর ভাবে, ইতিহাসের এক ধরনের রূপান্তরণ। নাগরিকতার এ ধরনের অভিব্যক্তি কখনও উজ্জয়িনী বা আথেন্স জানত না। পাপের ফুল্লকুসুমিত প্যারিস অথবা ট্রামলাইনমথিত কলকাতা এমন এক ইতিহাস চেতনার পরিসর যে, আমরা নিশ্চিত হই বোদলেয়ার বা জীবনানন্দ আধুনিক সময়ের প্রভু।

হয়তো আমাদের কবিতার মূল গতিধারার অদূরে তিনি নিজেই প্রবর্তন করেছিলেন অন্য এক অন্তঃশীলা প্রবাহ। সর্বজনস্বীকৃত ‘বনলতা সেন’ কবিতার দিকে তাকালে মনে হয় এই সৌন্দর্য চর্চার পান্ডুলিপি আমাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল প্রথম থেকেই। আমরা খেয়াল করিনি ভাষা-শরীরের অন্তর্ঘাত।
একটু তথ্যের দিকে নজর দিলেই আধুনিকতার মর্মপ্রদেশ উন্মোচিত হবে আমাদের কাছে। বনলতা সেন ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নকলনবিশরা এডগার অ্যালান পো-এর ‘ওড টু হেলেন’ কবিতাটির উল্লেখ করেন বনলতা সেন প্রসঙ্গে, কিন্তু কিঞ্চিত ইতিহাসবোধ অস্থিতে ও ধমনীতে প্রবাহিত থাকলেই বোঝা যায় এই কবিতার প্রকৃত আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের ১৯৯৭ সালে লিখিত কবিতা ‘স্বপ্ন’। দুই কবিতাতেই অলৌকিক ও অতিলৌকিক দু’জন নারী, অথচ অন্তর্গত দার্শনিকতায় উভয়ে কত যোজন যোজন দূরত্বের।
জীবনানন্দের কাল অখণ্ডিত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্ররোচনায় তিনি জানেন ‘সবই আছে সব সময়ের ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে– আজকাল সব সময়েরই একই রঙ রয়েছে নানা রঙের ভিতর বিলম্বিত হয়ে– সব সময়কে একই সময় গ্রন্থির ভিতর নিবিষ্ট করে রেখে।’ এ তো আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিকতার অল্প পরিসরের উপলব্ধি!
সেজন্যই– ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’। ‘হাঁটিতেছি’– পুরাঘটিত বর্তমান– প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। শ্রাবস্তী… বিদিশা… মালয় সাগর– কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ভ্রমণ। বিদায় নিয়েছে সর্গবন্ধ রোমান্টিক সময়চেতনা। অপর দিকে ‘দূরে বহুদূরে/ স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে’– বাস্তব নয়। স্বপ্নাবিষ্ট প্রিয়া-অভিসার।
‘রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।’
নিতান্তই জাতিস্মরতা। নিজের যুগের আদেশে রবীন্দ্রনাথ অসহায় ছিলেন কালের পর্ব-বৈষম্যে। কবিতার শুরুতে তিনি ক্রমান্বয়িক পশ্চাদাপসরণ করেন, কারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে তাঁর ধারণা ধ্রুপদী। অপরদিকে জীবনানন্দ প্রেমিকাকে পেয়ে যান সদাবর্তমান তিমিরে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো অন্ধকার নেমে আসে। এখানেও থাকে শুধু অন্ধকার, আরতি থেমে যায় না তবু– মুখোমুখি বসে থাকেন বনলতা সেন। রবীন্দ্রনাথে ভূত ও সাম্প্রতিক বিযুক্ত, জীবনানন্দে সাময়িক ও শাশ্বত কো-লিনিয়ার। মহাকাল পটভূমিতে একজন অপসৃয়মান মালবিকা, অন্যজন স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত। একজন প্রাচীন উজ্জয়িনীর সম্ভ্রম, অন্যজন ধ্বনি-তরল নাটোরের বাঙালিনী। একজনের রক্তের গহন থেকে আকুলতা: ‘হে বন্ধু, আছো তো ভালো?’ অন্যজনের পথচলতি কথকতা: ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’
দু’টি কবিতাতেই দুই কালের সাঁকো পারাপার। রবীন্দ্রনাথে সরল সমীকরণ। জীবনানন্দের সাইম্যালটানিয়াস, জয়েসের মতো, এলিয়টের মতো। কীটসের মানসিকতায়, রবীন্দ্রনাথের অনুভবে হেলেনিক তটরেখা বা মেঘদূতের গবাক্ষসমূহের প্রতি আসক্তি আছে, লুপ্ত অভিজ্ঞান ফিরে পেলে ভালো হত যেন! এলিয়টে, জীবনানন্দে অতীত-অনুধ্যান টেকনিক। আধুনিক সময়চেতনার প্ররোচনায় কল্পনার মানসঅতীত:
‘অগ্নিসংস্কারের মতো– আধুনিকতাকে নিজের সত্তায় ও সম্ভাবনায় বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যে– মহাভারতীয় কাল বা সেই দেশকালের শুদ্ধ উপলব্ধিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নয়।… সময়ের মানুষের ধারা ধারণার– যেন এক চতুর্থ বিস্তারের দেশে দাঁড়িয়ে বিরাট নাট্যকে ঘিরে মহাভারতের মহাপ্রস্থান আমাদের কোন পথ দেখিয়ে দেয় না।’
‘কি হিসেবে শাশ্বত’ প্রবন্ধে জীবনানন্দ নিয়ে এসব কথা চালাচালির মুহূর্তে মনে হয় কি অন্ধই না ছিলাম! আমরা আপেক্ষিকতা পরবর্তী চতুর্থ মাত্রার জ্যামিতি যে দেশ-কাল বিষয়ক ধারণা পাল্টে দিয়েছে তার জরিপই করিনি কবিতা পাঠে!
…ট্রামলাইনের সারস…
পর্ব ২. জীবনানন্দেরই বিড়ালের মতো তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নৈশ সড়কে, ইতিহাসে
পর্ব ১. রবীন্দ্রনাথের নীড় থেকে জীবনানন্দর নীড়, এক অলৌকিক ওলটপালট
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
