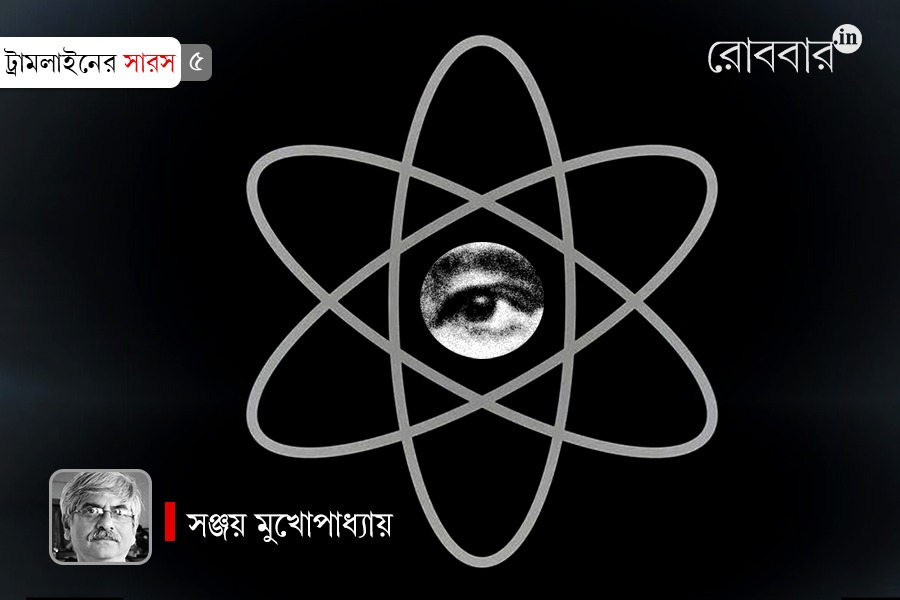
এবার আমরা বুঝতে পারছি খানিকটা যে কেন আমাদের ঘড়ির আধারে সময় নেই। আধুনিক আপেক্ষিকতার পরীক্ষায় এ ঘড়ি কাজে নাও লাগতে পারে। ক্রমে ক্রমে মেধায় আসছে ‘সময় কীটের মতো কুড়ে খায় আমাদের দেশ’ বাঁধা আছে কি রহস্যডোরে! দেশ-কাল সন্ততির ইতিহাস এখন। ইতিহাস চতুর্থ বিস্তারের। অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে পাল্টে গেলেন জীবনানন্দ। অব্যর্থ ভাবে তিনি ঘোষণা করেন:’ দেশকাল সন্ততি (আজ পর্যন্ত মানুষের ধারণায় তাদের যে রূপ আমরা পাই সেই রূপ) যে কোনো যুগের প্রাণ বস্তু বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে কাব্যে লাভ করেছে সে কবিতা আধুনিক।’

৫.
ভিড়ের হৃদয় থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার জেনেই নির্বাচিত শব্দের ভিড়ে, আমরা দেখলাম, পদার্থবিদ্যার আঁশ লেগে আছে কবির সমস্ত শরীরে। মিনকভস্কি বা হাইসেনবার্গ সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন– সে প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে এখনকার মতো বরং– জলতলে অর্কপ্রভ একটি বাক্য উদ্ধার করি যা উত্তরসাধকের পক্ষে দীপান্বিতা পটভূমির দিকে যাত্রা, যা আমার বিবেচনায় দ্বিতীয় জীবনানন্দের (‘অন্ধকার’ কবিতাকে সীমারেখা মেনে নিয়ে) নিউক্লিয়াসে সংলগ্ন হয়ে আছে অদৃশ্য জলবিন্দুর মতো: ‘গত তিন চার হাজার বছর ধরে মানুষের সভ্যতায় দর্শন কাজ করে গেছে; এইবারে বিজ্ঞান কাজ করবে বলে মনে হয়।’ (সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা)
মনে হতেই পারে জীবনানন্দ এমন কী অভিনব কথা বললেন? বিজ্ঞানই তো মানবপুত্রের প্রথম প্রণয়িনী। নয়তো ইতিহাসের পরপারে থাকা ‘অগ্নিশুদ্ধি’ আমাদের চরৈবতি মন্ত্র শোনাবে কেন? বিজ্ঞান মানুষের প্রণয়িনী নয় শুধু, পরিণীতাও। একটি মানুষ যবে তার নারীটিকে ভালোবেসে ফুল দিয়েছিল, যদি সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় সেই দিন– তবে তারও আগে থেকে দু’জনের ঠোঁটে লেগে আছে নিহত পশু বা গুল্মের স্বাদ; খাদ্যগ্রহণের পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন উভয়ে। কিন্ত বিজ্ঞান যেন এতদিন– প্রোষিতভর্ত্তৃকা নয় হয়তো– অন্তঃপুরচারিকা মাত্র। সে আমাদের গৃহসংস্কার করে, জীবনের শুশ্রূষা করে, মধ্যনিশীথে ব্রীড়াবনতাও এমনকী অথচ মর্মে প্রবিষ্ট হয়নি। ১৯১৬ সাল। দেশ-কাল ও বস্তুর বিবাহসভায় এই প্রথম তার জীবন আমার হল। অচলায়তন-ভ্রমে আমরা তাকে অনেকটাই প্রায়োগিক ব্যবহার করেছি। আজ মায়ার বদলে সত্যের উদ্বোধন। বিজ্ঞানই দর্শনকে গঠন করবে প্রধানভাবে; ধর্ম নয়, অখণ্ডনীয় কিছু নয়– ভেবেছেন জীবনানন্দ। বুঝতে পারি গুণগত পরিবর্তন। জীবনানন্দ অকুতোভয়ে লিখে চলেন: ‘বিজ্ঞানের প্রকর্ষের দিনে আজকের কবি বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করে কবিতা সৃষ্টি করবার কোন আবেদন অনুভব করছেন না।’ (কবিতার আত্মা ও শরীর)
প্রচলিত ধারণা যে বস্তু এবং গতি-নিরপেক্ষভাবে দেশ ও কাল পরস্পরেরও নিরপেক্ষ। দেশ ত্রিমাত্রিক ও গতিহীন। সময় স্বগুণচালিত; বস্তুসম্পর্করহিত; অবিচল প্রবাহ। ধ্রুপদী, নিউটনীয় চেতনা দাবি করে যে কাল-জ্ঞান সমস্ত অভিজ্ঞতার অতীত এবং দার্শনিকভাবে প্রায় একশো বছর পরে তা কান্ট কর্তৃক চিত্রিত হয়। অপরদিকে আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন স্থানীয় বিস্তৃতি ও কালগত ব্যবধান দ্রষ্টার অবস্থান ও গতিসাপেক্ষ। দেশ-কাল যুগল সম্মিলনে প্রকাশিত হলে সরলরেখায় ধৃত সময়চেতনার প্রচলিত নিয়মে বিক্ষোভ দেখা দেবে। মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে আমরা চতুরায়তনিক দেশ-কাল পরিবারের সদস্য। পরমতত্ত্ব বিনষ্ট। ঘটনার যুগপত্তা সংশয়মদির। বেগের তারতম্যে সম্ভব অতীত ও ভবিষ্যতের যৌথ ও সন্নিহিত মঞ্চক্রিয়া। মিনকভস্কির চৌমাত্রিক জ্যামিতি স্বাভাবিক হয়ে গেল। বিশ্ব আর অসীম নয়; মিতমাত্রার কিন্ত সীমাহীন। টের পেলাম গতির মহিমা। বস্তুত ১৯০০ সালে মাকস প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে ১৯২৬-এ শ্রয়ডিঙ্গার ও হাইসেনবার্গ প্রদত্ত অনিশ্চয়তার আঙ্কিক অভিব্যক্তি আমাদের কার্যকারণবাদের ভিত ধ্বসিয়ে দিল।
অথচ জীবনানন্দ এই নতুন দর্শনের পক্ষপাতী হয়েও বোঝেন: ‘রাদারফোর্ড বা প্লাঙ্কের মতো নিরেট এক সজাগচেতনাস্বামীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে উপাদানগুলো কবি ডেকে আনছে না তার হৃদয়ে… কবির চেতনা খুব ভালো, কিন্ত তার বিজ্ঞানী চিত্ত দিয়ে কিছু হবে না।’ (সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা)।
এবার আমরা বুঝতে পারছি খানিকটা যে কেন আমাদের ঘড়ির আধারে সময় নেই। আধুনিক আপেক্ষিকতার পরীক্ষায় এ ঘড়ি কাজে নাও লাগতে পারে। ক্রমে ক্রমে মেধায় আসছে ‘সময় কীটের মতো কুড়ে খায় আমাদের দেশ’ বাঁধা আছে কি রহস্যডোরে! দেশ-কাল সন্ততির ইতিহাস এখন। ইতিহাস চতুর্থ বিস্তারের। অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে পাল্টে গেলেন জীবনানন্দ। অব্যর্থ ভাবে তিনি ঘোষণা করেন: ‘দেশকাল সন্ততি (আজ পর্যন্ত মানুষের ধারণায় তাদের যে রূপ আমরা পাই সেই রূপ) যে কোনো যুগের প্রাণ বস্তু বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে কাব্যে লাভ করেছে সে কবিতা আধুনিক।’ (আধুনিক কবিতা)।
আরও প্রবীণ ঈক্ষণ। আরও পরিণত। স্পেস টাইম কনটিনিউয়াম: দেশ কাল সন্ততি। আধুনিকতা স্বয়ংপ্রভ হয়ে উঠল তাঁর মধ্যে। এই কালপ্রতিমা তাঁরই অপত্য বাংলা সাহিত্যে। হে পাঠক! খেয়াল করুন: ‘বেবিলনে একা-একা এমনি হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর/ কেন যেন, আজো আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।’ (পথ হাঁটা)
কাল অখণ্ডিত। চলিষ্ণু, বস্তু ও শক্তির অস্তিত্ব যেমন অনুপস্থিত দেশকালের বক্রতার মাধ্যমে সৃষ্টি করে মাধ্যাকর্ষণের মায়া, এক চলমান বর্তমানের বিক্রিয়ায় তেমনই ব্যবিলন-কলকাতা: স্মৃতি সত্ত্বা একাকার। একটি মুহূর্ত ধরে থাকে নিত্য প্রবহমানতা। যে দ্যাখে, কবি ওই বহমান বক্ররেখার স্পর্শক।
‘সবই আছে সব সময়ের ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে– আজকাল সব সময়েরই একই রঙ রয়েছে নানা রঙের ভিতর বিম্বিত হয়ে– সব সময়কে একই সময়গ্রন্থির ভিতর নিবিষ্ট করে রেখে।’ (রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা)
আপেক্ষিকতা প্রথম দৃঢ়ভাবে অন্বিত হল বনলতা সেন বইটির ‘অন্ধকার’ কবিতায়। ‘অনন্ত আকাশগ্রন্থি’। ‘অনন্ত’ শব্দটির মুক্তি ও ‘গ্রন্থি’ শব্দটির বন্ধন অত্যন্ত প্রখরভাবে ইঙ্গিত দেয় আইনস্টাইনীয় মহাবিকর্ষে কল্পিত finite yet unbounded universe-এর। পরে শেষ গ্রন্থ ‘বেলা অবেলা কালবেলা’য় আরও স্বাচ্ছন্দ্যে সময়ের মুখাবরণী সরিয়ে দিলেন: ‘সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে।’ (অবরোধ)
ত্রিকালের সম্মিলন বইয়ের নামকরণে অনুভূত– প্রাণ পাচ্ছে বৃত্তীয় ধর্ম। অবশেষে সমীক্ষা ও প্রস্তুতি: ‘এতদিন বসে পুরোনো বীজগণিতের শেষপাতা শেষ করতে না করতেই/ সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল;/ কোন এক গভীর নতুন বীজগণিত যেন/ পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে;/ আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে বলে?/ সেই শেষ সত্য বলে?’
স্নায়ু আস্থা হারিয়েছে চরম সত্যে। রক্তে আপেক্ষিকতার দ্বন্দ্ব অনিবারণীয়:
‘যে ঘোড়ায় চড়ে আমি/ অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো।’
পুনশ্চ: এলিয়টের দিকে তাকালাম– Where past and future are gathered!
জীবনানন্দ আমাদের অজান্তে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠলেন!
…ট্রামলাইনের সারস…
পর্ব ৪. জীবনানন্দ কি তবে ‘দেশ’ বলতে স্পেস বুঝিয়েছেন?
পর্ব ৩. জীবনানন্দ কি তবে ‘দেশ’ বলতে স্পেস বুঝিয়েছেন?
পর্ব ২. জীবনানন্দেরই বিড়ালের মতো তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নৈশ সড়কে, ইতিহাসে
পর্ব ১. রবীন্দ্রনাথের নীড় থেকে জীবনানন্দর নীড়, এক অলৌকিক ওলটপালট
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
