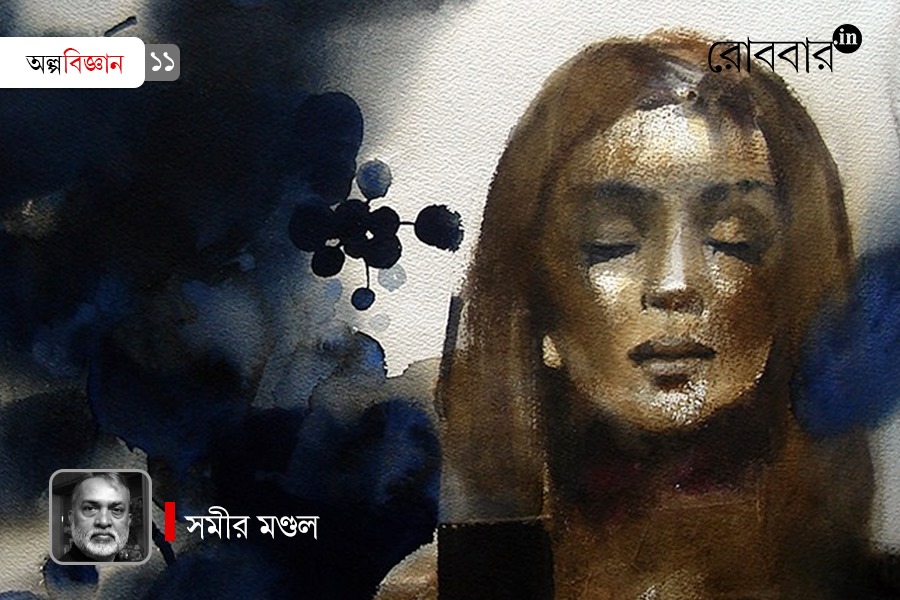
শব্দ থেকে দৃশ্য অথবা দৃশ্য থেকে আওয়াজ, এই বিষয়ে মাস্টারমশাই গণেশ হালুইয়ের সঙ্গে অদ্ভুত গভীর এক আলোচনা হয়েছিল। মূর্ততা এবং বিমূর্ততা নিয়ে, শব্দের রূপ থেকে দৃশ্যের রূপে যাওয়ার সেই আলোচনা। সেটা যেমন, তেমনই জলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, গুহায় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেখানে শব্দের মানে বদলে যায় পরিপ্রেক্ষিতে।

১১.
‘দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া,
…
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া’
গভীর রাতে কড়া নাড়ার অর্থ কী? চমকে যাওয়ার মতো ব্যাপার! ডাকাত পড়ল নাকি মাঝরাতে? না কি অনেক রাতেও যে ঘরে ফেরেনি, সে ফিরে এল!
দৃশ্য না শব্দ– কে আগে আসে? আলোর গতি, শব্দের গতি ইত্যাদি। অঙ্ক সবসময় আমার কাছে আতঙ্ক। ‘শব্দ’ মানে শুধু আওয়াজ নয়, শব্দ মানে ভাষা, যোগাযোগ, অনুভূতি, অস্তিত্বের সাড়া। আমরা জন্মের পর প্রথম যে জগৎটাকে চিনি, তা আলো নয়, শব্দের জগৎ। মায়ের কণ্ঠ, বাতাসের আওয়াজ, কিংবা কোনও শঙ্খ বা ঘণ্টার ধ্বনি অথবা পশু-পাখির ডাক। সবই মিলেমিশে আমাদের চারপাশের পৃথিবী। শব্দ শুনে চিনে নিই জীবন, বিপদ, আনন্দ, সোয়াস্তি, এমনকী ভালোবাসা।
বধিরের যেমন চোখে শ্রবণ, দৃষ্টিহীনের তেমনই শব্দই দৃশ্য।

বিজ্ঞান বলছে, শব্দ হল কম্পন। কোনও বস্তু যখন কাঁপে তৈরি হয় তরঙ্গ, যাকে আমরা শব্দ তরঙ্গ বলি। এই তরঙ্গ আমাদের কানে প্রবেশ করে কানের পর্দায় আঘাত করে, আর সেই কম্পন পৌঁছে যায় অন্দর-কর্ণে। সেখান থেকে শ্রবণ স্নায়ু সংকেত পাঠায় মস্তিষ্কে, আর মস্তিষ্ক সেই কম্পনকে ‘শব্দ’ হিসেবে চিনে নেয়।
মানুষের দু’টি কান থাকা কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয়। দুই কানে শোনার ফলে আমরা শব্দের দিকনির্ণয় করতে পারি। এক কানে শব্দ একটু আগে পৌঁছয়, আরেক কানে একটু পরে। এই সামান্য সময়ের পার্থক্য থেকেই মস্তিষ্ক বুঝে নেয়, শব্দটি বাঁ-দিক থেকে আসছে না ডানদিক থেকে। যদি কখনও এক কান বন্ধ করে শোনেন, বুঝবেন কতটা নীরস হয়ে যায় শব্দের জগৎ। দু’ কান খুলে দিলে হঠাৎ চারপাশে গভীরতা ফিরে আসে, পৃথিবী ত্রিমাত্রিক হয়ে ওঠে। বলছি বটে, তবে দর্শনের দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিকতা আর শোনার দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিকতার মধ্যে তফাত অনেক।
বিজ্ঞানকে পাশে রেখে বরং একটু খেলা করবেন? চলুন খেলি, একটু হালকা মেজাজে থাকি এ পর্বে। ছোটবেলার সেই কানামাছি খেলা এখানে। তবে খেলাটা বাইরে নয়, খেলতে হবে শান্ত পরিবেশে ঘরের মধ্যে।
শব্দের দিকনির্ণয় এবং দূরত্ব মাপার একটা সুন্দর খেলা। আমরা একসময় খেলতাম। খেলাটার জন্য পারিবারিক পরিবেশে সবাই মিলে একটা ছোট গ্রুপ করে অথবা সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গেও আলাদা করে খেলা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় ছোট একটা গ্রুপ, মানে পাঁচ-সাত জন মিলে খেললে।

প্রথমে দু’ জন এই খেলাটা খেলবে। বাদবাকিরা সেটা দেখবে এবং সেটা থেকে মজা পাবে আর ব্যাপারটা বুঝতেও চেষ্টা করবে। এই দু’জনের মধ্যে একজনের চোখ বাঁধা থাকবে। আর একজন শব্দ তৈরি করবে। চোখ বন্ধ করে বসলেও হবে, কোনও কাপড় দিয়ে বাঁধার দরকার নেই। তবে সে সত্যিকারেরই চোখ বন্ধ করে থাকবে, কোনও ফাঁকি দেবে না। না হলে খেলাটায় আর কোনও শিক্ষণীয় ব্যাপার থাকবে না। যে চোখ বন্ধ করে থাকবে, সে থাকবে ঘরের মেঝেতে শান্ত হয়ে বসে। অন্যজন হাতে কিছু জিনিস দিয়ে শব্দ তৈরি করবে। যেমন, একটা ছোট গ্লাস আর চামচ কিংবা দুটো কয়েন, ঘণ্টা-ঘুঙুর অথবা জোরে আঙুলে তুড়ি মেরেও করা যেতে পারে। শুধু তীব্র, তীক্ষ্ণ শব্দ চাই, যেটা সহজে সবাই শুনতে পাবে– সেরকম শব্দ হলেই ভালো হয়, যে শব্দে কোনও অস্পষ্টতা থাকবে না।
এখন যে শব্দ তৈরি করবে সে চোখ বাঁধা অবস্থায় বসে থাকা সঙ্গীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে শব্দ করবে। ধরা যাক সে প্রথমে তার নাকের সামনে ছ’ ইঞ্চি দূরে শব্দটা করল। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই খেলোয়াড় শুধু আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করবে যে, শব্দটা ঠিক কোথা থেকে আসছে! শব্দের উৎস কোথায়? এরপরে চোখ বাঁধা অবস্থাতে বসে থাকবে দ্বিতীয়বারের জন্য। হয়তো এবার মাথার ওপরে শব্দ করল, তৃতীয়বার আস্তে করে সরে গিয়ে ডানদিকের কানের পিছন দিকে, মাথার উপরে অনেক উঁচুতে, মাথার কাছে ইত্যাদি নানাভাবে ঘুরে ঘুরে শব্দ তৈরি করবে। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই খেলোয়াড় শুধু আঙুল দিয়ে শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে ইঙ্গিত করবে!
যারা খেলা দেখবে, তারা চুপ করে বসে দেখবে, কোনও কথা বলবে না। অর্থাৎ, কোনও শব্দ করার পরে আঙুল দেখানোটা যদি ভুল হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে, ‘হয়নি হয়নি’ বলে চেঁচিয়ে ওঠার কোনও দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, এই খেলাটা কিন্তু আসলে হারজিতের খেলা নয়, একটি অনুভূতির খেলা। যে চোখ বন্ধ করে খেলছে, সে তার সত্যিকারের অনুভূতি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে যে, আমি ঠিক কী শুনছি; আর যারা দেখছে তারাও কিন্তু বোঝার চেষ্টা করবে, যখন সে ঠিক বলছে– কী করে ঠিক বলছে; অথবা যখন সে ভুল করছে– তখন সে কেন ভুল করছে।

এক্ষেত্রে যেটা লক্ষ করার মতো সেটা হচ্ছে, ধরা যাক বসা খেলোয়াড়ের পিছন থেকে সামনে পর্যন্ত মাথার ওপর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটি কাল্পনিক লাইন ভাবা হল, যা সমান দু’ ভাগে ভাগ করছে ডানদিক আর বাঁদিকে। এখন এই সামনে-পিছনে মাথার উপর দিয়ে যে কল্পনার রেখা দিয়ে ভাগ করা হল, তার বাঁদিকের অংশে কোনও একটা জায়গায় যদি শব্দ তৈরি করা হয়, খেলোয়ার কিন্তু চোখ বন্ধ অবস্থায় আঙুল দিয়ে দেখাবে বাঁদিক থেকে শব্দটা আসছে। কিন্তু বাঁদিকে শব্দটা কি মুখের কাছে না দূরে– সামনের দিকে না পিছনের দিকে– উৎসটা ঠিক কোথায় নির্দেশ করতে পারবে না। ঠিক তেমনিভাবে ডানদিকের বেলাতেও তাই হবে।
আগেই বলেছি, যেহেতু দুটো কান দিয়ে শুনছি তাই শব্দটা যে কানের কাছাকাছি মানে, যে কানে শব্দ আগে পৌঁছবে সেই দিকেই দিকনির্ণয় করি আমরা। ডানদিক, বাঁ-দিক বুঝতে পারলেও শব্দের দূরত্বটা কিন্তু কান ধরতে পারে না। এটা আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত বুঝে থাকি। মগজ সেইভাবে কাজ করে। এবার সেটা বোঝার জন্য সবচেয়ে মজা হবে, সামনে থেকে পিছনে ঠিক মাথার মাঝখান দিয়ে যে লাইনটা ভেবেছি সেই লাইনের ওপর যে কোনও জায়গায় শব্দ করলে, যেখানে শব্দের দূরত্ব দুটো কান থেকে সমান, সেখানে সব সময় গোলমাল হতে থাকবে। এমনকী মাথার ঠিক ওপরে শব্দ করলে সেটা মাথার সামনে না পিছনে সেটাও পর্যন্ত বলা সম্ভব হবে না। অদ্ভুত না?
এরপরে খেলোয়াড় বদল করে করে খেলতে হবে। কারণ, যে চোখ বন্ধ করেছিল, সে কী কী করেছিল নিজে দেখতে পায়নি। তাকে দেখানোর জন্য এবারে চোখ বাঁধা খেলোয়াড় বদল হবে। আর একটা মজার ব্যাপার ঘটবে এখানে। যারা খেলাটি দেখছে বসে বসে, একজন বা দু’জনের খেলার পরে তাদের একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে যে, আমি এটা ভালো করতে পারব। কী কী ভুল হতে পারে, সে ব্যাপারে নিজের মতো করে একটা আইডিয়া তৈরি করে নেবে। কিন্তু সে যখন চোখ বন্ধ করে সত্যিকারের খেলবে কখনওই তার কোনও আইডিয়াই কাজে লাগবে না।
তাহলে দাঁড়াল কী? শব্দ কোন দিক থেকে আসছে, তা অনেকটা বুঝতে পারলেও কত দূর থেকে আসছে তা সহজে বুঝতে পারি না। ঘরের মধ্যের খেলা ছেড়ে এবার বাইরের খোলা পরিবেশে, আমাদের সবারই জানা অভিজ্ঞতার গল্প বলি। আমরা যখন সত্যিকারের শব্দ শুনি, ধরা যাক আওয়াজ করে একটি গাড়ি, কিংবা ধরা যাক একটা অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমার সামনে দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এখন কিছুক্ষণ আমি যদি চোখ বন্ধ করি তাহলে বুঝতে পারি যে গাড়িটা অমুক জায়গায়, সেখান থেকে যেন ডানদিকে ঘুরে গেল, তারপরে সে এতক্ষণে অমুক জায়গায় পৌঁছে গেল। এই যে, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে সেটা আন্দাজ করতে পারছি– তা কিন্তু আমাদের অভ্যাসবশত; এবং এই জায়গাটা আমার চেনা, তার মানচিত্রটা আমার জানা আছে বলেই আমরা বুঝতে পারছি। তা না হলে দূরত্বের বদলে আসলে আমরা যত দূরে যাচ্ছে তত তার শব্দের জোর কমে যাচ্ছে, ফেড হয়ে যাচ্ছে, সেটাই শুনছি। দূরত্ব অনুপাতে শব্দের ওজন কমছে, সেই ঘটনাটাই ঘটছে আসলে।

এ তো গেল আসল শব্দ। সত্যিকারের শব্দের বেলায় যেমন ঘটছে, নকল বা কৃত্রিম শব্দের বেলাতেও কিন্তু সেই একই ঘটনা ঘটবে, অর্থাৎ শব্দের ওজনের কম-বেশিতে কাছে দূরের শব্দ ভ্রম। ভাবুন আপনি রেডিওতে নাটক শুনছেন, টেলিভিশনে ছবি দেখছেন বা সিনেমাহলে সিনেমা। সেক্ষেত্রে যদি আপনার সামনের ছবিতে অ্যাম্বুলেন্সটা সাইরেন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে চলে গিয়ে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে অনেক বাড়ির মধ্যে হারিয়ে যায়– সেই জায়গাটা আপনার কিন্তু চেনা নয়, আর ব্যাপারটা ঘটছে ছবিতে– অথচ আপনি বুঝতে পারছেন গাড়িটা দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। সত্যিকারের শব্দ আর কৃত্রিম শব্দের বেলায় মগজের কাজ কিন্তু একইরকম। এখানে আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, অবিশ্বাস্য, সেটা হচ্ছে সামনের রাস্তায় যে অ্যাম্বুলেন্সটা গেল সেটাকে আমরা চাক্ষুষ করলাম! সত্যিকারের শব্দের উৎসটা তো কান থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সিনেমার বেলাতে অদ্ভুতভাবে শব্দের যে উৎস সেটা কিন্তু সরছে না। শব্দ আসছে পর্দার কাছাকাছি একটা স্পিকার থেকে। সেই স্পিকার আর আমাদের কানের দূরত্ব কিন্তু সবসময় এক। শুধু রেকর্ডের শব্দের ওজন কম-বেশি হচ্ছে। এই যে ইলিউশন, একটা ভ্রম তৈরি হচ্ছে, তাতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমাদের সামনে থেকে গাড়িটা দূর থেকে দূরে, আরও দূরে মিলিয়ে গেল।
ছবি আঁকার কৌশল থেকে দৃশ্য এবং শব্দ সম্পর্কে আরেকরকম জ্ঞান হল আমার। পার্সপেক্টিভ বোঝাতে আমরা কাছের জিনিসকে বড় এবং সেই একই জিনিস দূরে গেলে তাকে ছোট করে আঁকি। একটা দূরত্বের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। দ্বিমাত্রিক পটে ত্রিমাত্রিকের একটা ম্যাজিক তৈরি হয়। একই সাইজের জিনিস দূরত্ব বোঝাতে যেমন সাইজটা ছোট করে আঁকতে হবে, তেমনই কাছে থেকে দূরের রঙেরও পরিবর্তন ঘটবে। সেটাকেও আমরা ছবির ভাষায় কালার পার্সপেক্টিভ বলে থাকি। অর্থাৎ কাছের জিনিস যতটা পরিষ্কার দেখায়, দূরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে যায়, রঙের বদল ঘটে। অনেকটাই ধূসর হয়ে যায়, তার কারণ বাতাস কিন্তু একেবারেই শূন্য নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত আলো আসছে। আলোর তরঙ্গের পথে বাধাবিঘ্ন। ধুলো-ধোঁয়ায় দূষিত বায়ুর মধ্য দিয়ে দেখার ক্ষেত্রে রং বদলে যায়, ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়।
ছবির ক্ষেত্রে ধরা যাক একটা রাস্তার ধার দিয়ে কিছু মাইলস্টোনের মতো সিমেন্টের খুঁটি পরপর লাগানো আছে। যেগুলোর গায়ের রং অর্ধেকটা কালো আর অর্ধেকটা সাদা। আমরা যখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরের খুঁটিগুলো দেখি, সেগুলো আর সাদা-কালো থাকে না। অর্থাৎ, কালোটাও ধূসর হয়ে যায়, সাদাটাও ধূসর হয়ে যায়। একসময় সে একরঙা একটা ধূসর খুঁটি মনে হয়। দূর বোঝাতে সত্যি আমরা ছবিতে দূরের খুঁটিগুলোর গায়ে ধূসর রং লাগাই, সাদা-কালো নয়।
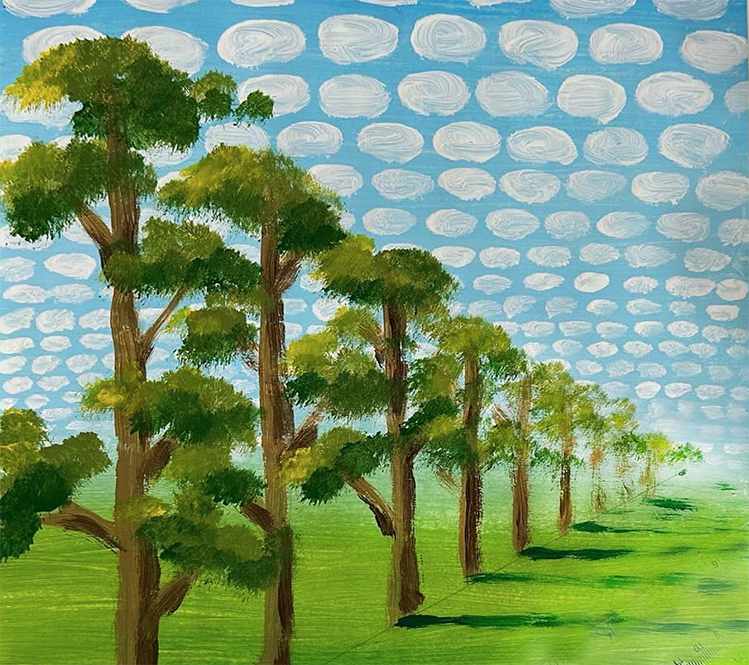
এখন যদি ওই ছবিটার একটা ধূসর খুঁটিকে শুধুমাত্র খোলা রেখে পুরো ছবিটা কাগজ চাপা দিয়ে ঢেকে দিই এবং সেটা কাউকে দেখাই, তা দেখে দর্শক কী বলবে? একজন যদি আমার ছবিটা পুরোটা দেখে থাকে, তাহলে সে বলবে, এটা একটা সাদা-কালো খুঁটি কিন্তু দূরে গিয়ে ধূসর দেখাচ্ছে। তার মনের চোখে পুরো ছবিটা সে দেখছে। কিন্তু যে ছবিটাকে দেখেনি, শুধু ওই ছবির অংশটুকু দেখছে, সে বলবে– একটা কোনও ধূসর বস্তু, কিন্তু কী বস্তু সেটা সে বুঝতে পারছে না। পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে ওই আকারের, ওই রঙের কিছু কিছু বস্তুর নাম হয়তো করতে পারে।
শব্দের ক্ষেত্রেও ধরা যাক আগের ওই অ্যাম্বুলেন্সটা চলে যাওয়ার শব্দ পুরোটা রেকর্ড করা হল। আপনার সামনেই সেটা করা হল এবং আপনাকে যদি এখন বাজিয়ে শোনানো হয়, এখানেও ছবির মতো বিভ্রান্তিকর ঘটনা ঘটবে। শুরুর দিকের কয়েক সেকেন্ড শুনে আপনি শব্দ পাবেন– প্যা-পু, প্যা-পু, প্যা-পু– এরকম। পরিষ্কার দুটো শব্দ মিশিয়ে একটা আওয়াজ। কিন্তু যদি শেষের দিকের কয়েক সেকেন্ড শোনেন তাহলে সেটা হয়তো শোনাবে– অস্পষ্ট পোঁ, পোঁ, পোঁ এমন কোনও আওয়াজ। প্যা-পু মিশে একরঙা হয়ে পোঁ।

এবার ভাবুন, রেকর্ড করার সময় রাস্তায় ছিল না এমন একজনকে শুধুমাত্র শেষের দিকের কয়েক সেকেন্ড শোনালে সেই শব্দটাকে ও বলবে, দূরে কোনও সাইরেনের শব্দ হালকা করে শুনতে পাচ্ছি। সেটা বলবে তার পুরনো অভিজ্ঞতা মিলিয়ে; অথবা বলবে, বহু দূরে কোনও কলকারখানার যান্ত্রিক শব্দ হালকা করে শুনতে পাচ্ছি, কিংবা পাশের বাড়িতে কোনও একটা মেশিন চলছে। ওয়াশিং মেশিন বা রান্নার কোনও মেশিনের মধ্যে থেকে পোঁ পোঁ আওয়াজ আসছে।
রাতের অন্ধকারে, কিংবা অচেনা কোনও জায়গায়, অচেনা শব্দ আমাদের নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ধরুন, আগের দিন রাতে ডাইনোসর নিয়ে ‘জুরাসিক পার্ক’ ছবিটা দেখে এসেছেন। পরের দিন গভীর রাতে জানালার বাইরে একটা থপ করে আওয়াজ হল। আওয়াজটা শুনে, তার চরিত্র বুঝে, মনে হতে পারে যে একটা ইঁদুর জানলার বাইরে মানে ফুট দুয়েক দূরে লাফাল; এবং তার পায়ের আওয়াজে একটা থপ করে শব্দ হল। আবার ঐ শব্দের ওজন বুঝে এমনও মনে হতে পারে যে, এক কিলোমিটার দূরে একটা ডাইনোসর পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অতএব শব্দটা শুনে মানসিক প্রক্রিয়াটা কেমন হবে? ইঁদুরের লাফালাফি মনে করে আপনি পাশ ফিরে শোবেন, অথবা ডাইনোসর আসছে ভেবে আপনার হৃদকম্পন বদলে যাবে কিংবা অ্যাড্রিনালিন মাথায় উঠে যেতে পারে।

শব্দ থেকে দৃশ্য অথবা দৃশ্য থেকে আওয়াজ, এই বিষয়ে মাস্টারমশাই গণেশ হালুইয়ের সঙ্গে অদ্ভুত গভীর এক আলোচনা হয়েছিল। মূর্ততা এবং বিমূর্ততা নিয়ে, শব্দের রূপ থেকে দৃশ্যের রূপে যাওয়ার সেই আলোচনা। সেটা যেমন, তেমনই জলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, গুহায় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেখানে শব্দের মানে বদলে যায় পরিপ্রেক্ষিতে। শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ নাটকে, সংগীতে। জীবজগতে শব্দের আলাদা জগৎ। কবির কল্পনায়, ‘শিশিরের শব্দ’ অথবা ‘তুমি রবে নীরবে’। কথা তো ফুরয় না। আরও কথা বলার ইচ্ছে রইল পরের পর্বে।
শব্দের অনুভূতি, আওয়াজের আন্দাজ, কল্পনা করা বড়ই অদ্ভুত। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। আমরা জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত অগুনতি সব শব্দ, দৃশ্য, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ, নানা রকমের তথ্য মগজে গাদা গাদা ঢুকিয়েই যাচ্ছি, ঢুকিয়েই যাচ্ছি। আর সেই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই আমাদের যাবতীয় বোঝাপড়া। অতএব আমার মগজে যা নেই, তা কিন্তু আমার জীবনেও নেই, আমার জগতেও নেই।
…পড়ুন অল্পবিজ্ঞান-এর অন্যান্য পর্ব…
পর্ব ১০: শিল্পকলায় বিষ্ঠা মানে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ অথবা প্রতিবাদ
পর্ব ৯: বাস্তব আর ভার্চুয়ালের সীমান্তে দাঁড়িয়ে হাইব্রিড আর্ট প্রশ্ন করতে শেখায়– শিল্প কী?
পর্ব ৮: মগজে না ঢুকলে শিল্পও আবর্জনা
পর্ব ৭: ছবির অসুখ-বিসুখ, ছবির ডাক্তার
পর্ব ৬: বিসর্জনের মতোই একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর রং ও রূপ
পর্ব ৫: জীবন আসলে ক্যালাইডোস্কোপ, সামান্য ঘোরালেই বদলে যায় একঘেয়ে নকশা
পর্ব ৪: কুকুরেরই জাত ভাই, অথচ শিয়াল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?
পর্ব ৩: অন্ধকারে অল্প আলোর মায়া, ফুরয় না কোনওদিন!
পর্ব ২: বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আমাদের চিরকালের নায়ক হয়ে আছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
