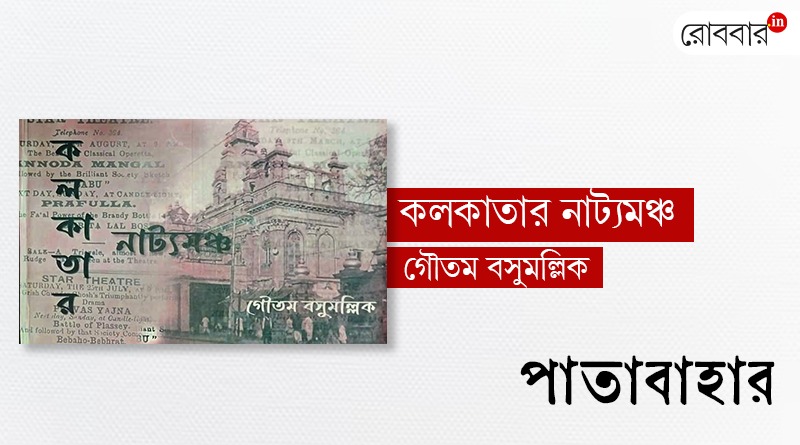
মূলত দু’টি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। যার একদিকে রয়েছে স্মারক পুস্তিকার সূত্র ধরে পেশাদার নাট্যচর্চার প্রাকলগ্নের বিবরণী। চর্যাপদের ‘বুদ্ধ নাটক’ কিংবা ভারতচন্দ্রের ‘চণ্ডী’ নাটকের প্রসঙ্গ উল্লেখে তিনি তৈরি করেন বাংলা থিয়েটারের ‘নান্দীপাঠ’। আবার বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের নাট্যগীতির মূল্য বিচার থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্বের ‘কলি রাজার যাত্রা’-য় ধরা পড়ে কয়েকশো বছরের যাত্রাপথ। না হলে কোনওভাবেই সম্ভব নয় ‘যাত্রা’ ও ‘থিয়েটার’ নামের দু’টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যমের তারতম্য দেখানো।

‘রেতে মশা দিনে মাছি, এই তাড়্য়ে কলকেতায় আছি।’– কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাছে এই ছিল সাবেক তিলোত্তমা। অথচ এই শহরকেই কি না ইংরেজরা গড়ে তুলতে চেয়েছিল ‘প্রাচ্যের লন্ডন’ রূপে! শুধু শ্বেতাঙ্গ পাড়ার আভিজাত্য থাকলে তো হবে না। চাই আমোদ-আহ্লাদ। এদেশীয় কবিগান, পাঁচালি বা গ্রাম্যযাত্রায় কি আর ইংরেজদের মনোরঞ্জন হয়? তাই নিজস্ব রুচি-সংস্কৃতি অনুযায়ী তাঁরা নাচ-গান-অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে উঠেপড়ে লাগল। ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসে পড়ল থিয়েটার নামক পাশ্চাত্য রীতির বিনোদন। যাত্রার খোলা মঞ্চের বদলে ভারতীয় নাট্যচর্চাকে বেঁধে ফেলল ‘প্রসেনিয়াম’-এর তিনদিক ঘেরা মঞ্চ। সেই পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়েই ফুলে-ফলে মহীরুহ হয়ে উঠেছে বাংলা থিয়েটার।
কিন্তু ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরও কিছু প্রাককথন থাকে। থিয়েটার বিষয়টি বাঙালির কাছে অভিনব আমদানি। তা বলে শতাব্দী প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার প্রভাব মুছে ফেলার প্রশ্ন ওঠে না। ভরত মুনির ‘নাট্যশাস্ত্র’ থেকে চিৎপুরে ঘড়িবাড়ির ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’। বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাস খুঁজতে গেলে এই বিস্তৃত সময়কালকে স্মরণ করতেই হয়। অতি সংক্ষেপে সেই কাজটিই করেছেন গৌতম বসুমল্লিক। তাঁর ‘কলকাতার নাট্যমঞ্চ’ গ্রন্থ যেন বাঙালির এক সমৃদ্ধ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত টীকাভাষ্য।
মূলত দু’টি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। যার একদিকে রয়েছে স্মারক পুস্তিকার সূত্র ধরে পেশাদার নাট্যচর্চার প্রাকলগ্নের বিবরণী। চর্যাপদের ‘বুদ্ধ নাটক’ কিংবা ভারতচন্দ্রের ‘চণ্ডী’ নাটকের প্রসঙ্গ উল্লেখে তিনি তৈরি করেন বাংলা থিয়েটারের ‘নান্দীপাঠ’। আবার বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের নাট্যগীতির মূল্য বিচার থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্বের ‘কলি রাজার যাত্রা’-য় ধরা পড়ে কয়েকশো বছরের যাত্রাপথ। না হলে কোনওভাবেই সম্ভব নয় ‘যাত্রা’ ও ‘থিয়েটার’ নামের দু’টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যমের তারতম্য দেখানো।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
এই শহর দেখেছে স্বপ্নের নবনাট্য মন্দির থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়েছে শিশির ভাদুড়ীর জিনিসপত্র। দেখেছে উন্নয়ন ও অযত্নের পরস্পরবিরোধী যুক্তিতে কতশত মঞ্চ ভাঙা পড়তে। সেই দুশো বছরের সময়সীমার মধ্যে গৌতম বসুমল্লিক ছাই ঘেঁটে খুঁজে দেখেন কলকাতার থিয়েটারের পথঘাট। ‘দ্য প্লে হাউস’, ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’, ‘সাঁ সুচি’-র মতো প্রসিদ্ধ মঞ্চগুলি তো আছেই। সেই সঙ্গে তিনি শহরের পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে থাকা এথিনিয়াম, কার্জন, ক্রাউন, জুপিটারের মতো মঞ্চগুলির আজকের চেহারা ঘুরিয়ে দেখান।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
তবে অপেশাদারি উদ্যোগের অভিনয় নিয়ে গ্রন্থকার যে পরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেন, তার জন্য এই পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। থিয়েটারের ইতিহাসের প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে অপেশাদার প্রচেষ্টাগুলি প্রায় অনালোচিত। গৌতম বসুমল্লিক বিশ শতকের চারের দশক পর্যন্ত অসংখ্য নাট্যসমাজের নাম ও তাদের নাটকের দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপন করেছেন। একই সঙ্গে রয়েছে উনিশ শতকে ‘ঠাকুর দাসের দল’-সহ বেশ কয়েকটি শখের যাত্রাদলের প্রসঙ্গ। কলকাতায় থিয়েটারচর্চার সার্বিক বাতাবরণ তৈরিতে তাদের কম ভূমিকা ছিল না।
দ্বিতীয় পর্বটির গুরুত্ব অন্য ধাঁচের। যার ফলে এই গ্রন্থ শুধু শহরের প্রাচীন থিয়েটারের ইতিহাস বর্ণনা নয়। যেন তাদের গাইডম্যাপ। আজকের ঝাঁ-চকচকে কল্লোলিনীর গলিঘুঁজি ধরে হাতড়ে বেরনো তাদের ঠিকানা। এই অনুসন্ধানের মধ্যে কাজ করে গ্রন্থকারের খাঁটি কলকাত্তাইয়া সত্তা। থিয়েটারের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে তিনি পাঠককে নিয়ে যান কলকাতার তস্য গলিতে। এই শহর দেখেছে স্বপ্নের নবনাট্য মন্দির থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়েছে শিশির ভাদুড়ীর জিনিসপত্র। দেখেছে উন্নয়ন ও অযত্নের পরস্পরবিরোধী যুক্তিতে কতশত মঞ্চ ভাঙা পড়তে। সেই দুশো বছরের সময়সীমার মধ্যে গৌতম বসুমল্লিক ছাই ঘেঁটে খুঁজে দেখেন কলকাতার থিয়েটারের পথঘাট। দ্য প্লে হাউস, বেঙ্গলি থিয়েটার, সাঁ সুচির মতো প্রসিদ্ধ মঞ্চগুলি তো আছেই। সেই সঙ্গে তিনি শহরের পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে থাকা এথিনিয়াম, কার্জন, ক্রাউন, জুপিটারের মতো মঞ্চগুলির আজকের চেহারা ঘুরিয়ে দেখান।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
আরও পড়ুন: ‘বহুরূপী যাপন’ স্মৃতি নামক এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর থেকে ধার করে আনা গল্প
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
গ্রন্থের শুরুতেই গৌতমবাবু একটি সতর্কীকরণ রেখেছিলেন পাঠকদের কাছে। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলা সাহিত্য এবং নাট্যজগৎ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন বা পড়াশোনা করেন, এই বই তাঁদের জন্য নয়। এ বই একেবারেই সাধারণ পাঠক এবং বিশেষ করে অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে, যাঁদের পক্ষে নাট্য সাহিত্যের বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত বইপত্র পড়া সবসময়ে সম্ভব হয় না, আলোচ্য বই মূলত তাদের জন্য।’
কথাটা সত্যি। চেনা তথ্য, চেনা ইতিহাস। কিন্তু এক মলাটের ভিতরে অসংখ্য হারিয়ে যাওয়া নাটকের অভিনয়পত্রী ও থিয়েটারের ছবির সংকলন প্রাপ্তির আস্বাদ কীভাবে অস্বীকার করা যায়? ইতিহাস লেখাটাও তো একটা চলমান প্রক্রিয়া। বিশেষত থিয়েটারের মতো তিলোত্তমা শিল্পের ক্ষেত্রে। তার জন্য যে প্রতিনিয়ত উপাদানের প্রয়োজন, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে উঠতে পারে ‘কলকাতার নাট্যমঞ্চ’।
কলকাতার নাট্যমঞ্চ
গৌতম বসুমল্লিক
সম্পর্ক
১৭৫ টাকা
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
