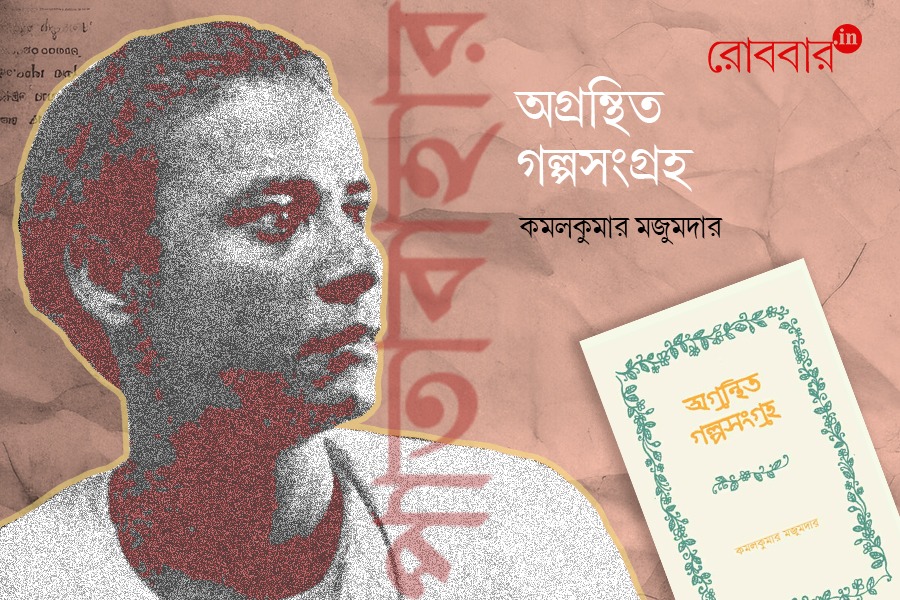
কমলকুমার মজুমদারের গল্প পড়া ফ্যাশন নয়, প্যাশনের দাবিদার। তিনি প্রতিভাধর, ভয়ংকর পণ্ডিত লেখক, কিন্তু বড্ড ছড়ানো-ছিটানো। নীতিগত সিদ্ধান্তে সাময়িকপত্রেই গল্প ছেপেছেন। আবার নিজের লেখা সংগ্রহ করে রাখার পরিপাটি লেখকদের পথও অনুসরণ করেননি। তাই তাঁর ‘গল্পসমগ্র’ নামক সংকলন আদতেই কোনও দিন ‘সমগ্র’ হওয়ার কথা নয়। হয়নিও। তাই আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত ওই ‘গল্পসমগ্র’ সংগ্রহ করার পরেও সন্ধানী কমলকুমার পাঠককে তুলে নিতে হবে ব্রেনফিভার প্রকাশিত ‘অগ্রন্থিত গল্পসংগ্রহ’।

পাঠ করার প্রশিক্ষণ যাঁর আছে, তাঁকেই ‘পাঠক’ বলা গেলে আভিধানিক সমাধানের স্বস্তি কিছুটা পাওয়া যায়। এবং পঠনবিশ্বে সেই স্বস্তির জায়গা কিন্তু বাড়ন্ত। সিরিয়াস লেখক পাঠককে কোনও দিনই সাক্ষরের পালিশ-অবতার ভাবতে রাজি হননি। অভিনব গুপ্ত সহৃদয় পাঠক বা নির্মলহৃদয় পাঠকের পক্ষে যে দাবি রাখলেন, দিনে দিনে সেই দাবিই আরও শক্তপোক্ত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তরা সচেতন পাঠকের যে কথা বলেছিলেন, তা তো সেই সহৃদয় পাঠকেরই উত্তরপুরুষ! সচেতন পাঠক মানেই যথেষ্ট শিক্ষিত পাঠক। ওদিকে কমলকুমার মজুমদাররা হলেন সেই ধরনের লেখক, যাঁদের কেবল সচেতন শিক্ষিত পাঠক হলেই চলে না, দরকার হয় দীক্ষিত পাঠক। রীতিমতো পড়াশুনো করে গায়ে মনন মন্দিরের ধ্যানপবিত্র অগুরু মেখে তাঁর লেখা স্পর্শ করতে হয়। শুধু গভীরে যাও। থেমো না, তল মাপতে যেও না, কেবল ঝিমিঝিমে সাহিত্যরসে বুঁদ হয়ে অনিকেত এগিয়ে যাও। কমলকুমার মজুমদার বহুশ্রুত, কিন্তু বহুপঠিত নন। তিনি মানচিত্রের সেই বাস্তব রহস্যবিন্দু, যাঁর প্রবল অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাঁর অভিমুখে অভিযানের দৃষ্টান্ত হাতেগোনা। মহাকব্যের কাহিনি বলে দেওয়া যায়। কিন্তু কতজন পড়ে বলেন! তিনিও তেমন। তাঁকে পড়ার লোক কম, কিন্তু সমীহ না করার মতো লোকও বিরল। অর্থাৎ তাঁকে অস্বীকার করা যায় না। একজন মানুষ, যিনি কাঠখোদাই কাজ করছেন, গয়নার ডিজাইন করছেন, আঁকছেন, শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিচ্ছেন, ব্যালে নাচ শিখছেন, সেই নাচের প্রশিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন, লোকশিল্পের পেশাদার সংগ্রাহক হয়ে যাচ্ছেন, বারবার স্কুল বদলে প্রথাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন, আবার সেই তিনিই বিপরীত বিশ্বের বিষয় নিয়ে ‘তদন্ত’ বা ‘অঙ্ক ভাবনা’-র মতো পত্রিকা সম্পাদনা করছেন, সওয়াল করছেন পরিমিতি বোধ শিখতে সাহিত্যিককে অবশ্যই অঙ্ক শিখতে হবে– এই প্রবল অগোছালো অথচ ভয়ংকর প্রতিভাধর মানুষটির লেখা অদীক্ষিত পাঠকের হজমের বিষয় হবে, তা কি প্রত্যাশা করা যায়? তাঁর গল্পবিশ্বের ক্ষেত্রেও কথাগুলো খাটে।
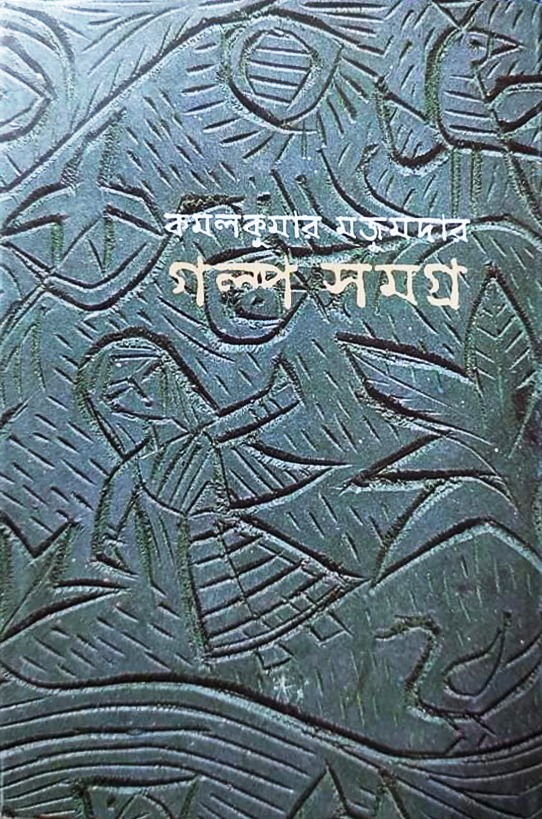
তাঁর গল্প পড়া ফ্যাশন নয়, প্যাশনের দাবিদার। আগেই বলেছি তিনি প্রতিভাধর, ভয়ংকর পণ্ডিত লেখক, কিন্তু একইসঙ্গে বড্ড ছড়ানো-ছিটানো। নীতিগত সিদ্ধান্তে সাময়িকপত্রেই গল্প ছেপেছেন। দম্দার পাবলিশারের উমেদারি করেননি। আবার নিজের লেখা সংগ্রহ করে রাখার পরিপাটি লেখকদের পথও অনুসরণ করেননি। তৈরি করেননি পাটীগণিত সচেতন সংগ্রহপটু অনুগামীদল। তাই তাঁর ‘গল্পসমগ্র’ নামক সংকলন আদতেই কোনও দিন ‘সমগ্র’ হওয়ার কথা নয়। হয়নিও। তাই আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত ওই ‘গল্পসমগ্র’ সংগ্রহ করার পরেও সন্ধানী কমলকুমার পাঠককে তুলে নিতে হবে ব্রেনফিভার প্রকাশিত ‘অগ্রন্থিত গল্পসংগ্রহ’। মনে রাখতে হবে এটাও কিন্তু সংগ্রহ। এর বাইরে কমলকুমারের আর কোনও গল্প নেই, এমন কোনও দাবি প্রকাশকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে না।
‘গল্পসমগ্র’ যে বইটি কমলকুমারের গল্প আস্বাদনের একমাত্র আলম্বন ছিল, তার বাইরে পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে থাকা ১০টি সম্পূর্ণ গল্প, দু’টি অসম্পূর্ণ গল্প ও দু’টি পরিত্যক্ত গল্প অর্থাৎ মোট ১৪টি লেখা কমবেশি তেরো-চোদ্দটি পত্রিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা শেষে যত্ন করে সংগ্রহ করে ততোধিক যত্নে দু’মলাট বন্দি করেছেন প্রকাশক।
কমলকুমার নিরীক্ষাপ্রিয় লেখক ছিলেন, এই তথ্যসঙ্গত কারণেই আমাদের বারবার স্মরণ করে নিতে হয়। আর সেই নিরীক্ষার হকিকত কেবল ‘সুহাসিনীর পমেটম’ উপন্যাসের আড়াইশো পাতা জুড়ে চলা বাক্যের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। বরং দীর্ঘবাক্য তাঁর সাহিত্যিক সপর্যার জেগে থাকা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। গভীরতা আসলে বহমানতায়। কমলকুমারের গল্প এক ধরনের মৃদুমন্দ মেধাবী বহমানতা। সেই বহমানতার সঙ্গে পাঠককে প্রথমে মানিয়ে নিতে হবে। তারপর অভিযান করতে হবে ব্রেনফিভার প্রকাশিত কমলকুমার মজুমদারের ‘অগ্রন্থিত গল্পসংগ্রহ’-এর পাতা ধরে ধরে।
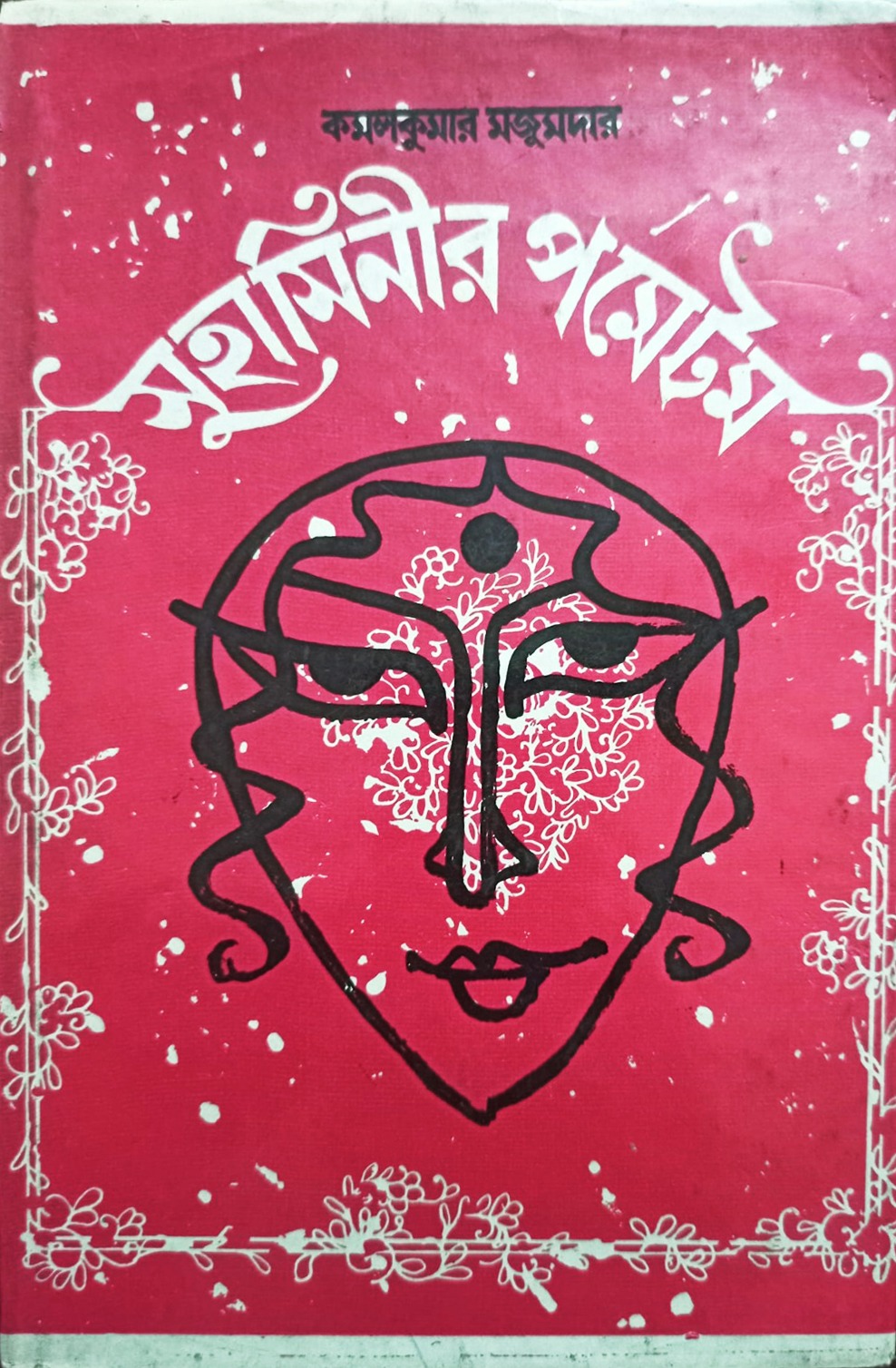
প্রথমেই পাঠক পাবেন ‘মহামানবের জন্ম’ গল্পটা। কমলকুমার মজুমদার সম্পাদিত ‘উষ্ণীষ’ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা থেকে সংগ্রহ করা। সেইসময় অবশ্য লেখক কমল মজুমদার নামে সম্পাদনা করতেন পত্রিকাটি। গল্পটা পড়লেই পাঠকের মনের স্টক রেসপন্স ম্যাক্সিমিলিয়েন রোব্সপিয়রের সুপ্রিম বিইং-এর কথা মনে করাবে। মনে করাবে কাল্ট অফ পার্সোনালিটি নামক যুগশঙ্খের নিনাদ। কিন্তু কথকের পাশেই যমুনার চিন্তাস্রোত সেই মহামানবের আবাহনের মোমের শরীরটা গলিয়ে শেষ করে দিতে থাকবে। পৃথিবীতে মহামানবের আবাহন কোনোদিন শান্তির বার্তা নিয়ে আসেনি, এসেছে মৃত্যুর অগণন পরিসংখ্যান নিয়ে। রেভারেন্ড জিম জোন্স যতই পিপলস্ টেম্পলের কথা বলুন, আসলে তো তা বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য নরমেধ যজ্ঞ! গল্পটা যেন যমুনার স্বপ্নের পথে বিরাট পুরুষের আবাহনের প্রতিক্রিয়ায় একটা গথাম সিটির জলছবি আমাদের চোখে এঁকে দেয়। অন্ধকার আর অন্ধকার। কোনও প্রবাদপ্রতিম পুরুষ সেখানে এক টুকরো আলোও আনতে পারবেন না। আমাদের শিরদাঁড়া সোজা করে ভাবতে বাধ্য করে। মোহাবরণ ছিন্ন করা এই গল্পের স্বাদ তো আমরা আগে পাইনি! পরের গল্প ‘সমাহিত’ কমলকুমারের ট্রেডমার্ক শৈলীতে লেখা। এটিও ‘উষ্ণীষ’ পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। গল্পটা পাঠককে ১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পল সাইমন আর আর্ত গারফাঙ্কেলের ‘দ্য সাউন্ড অফ সাইলেন্স’ গানটার কথা মনে করাতে পারে। শব্দহীন স্তব্ধতা, গানহীন বর্ণের মধ্যে বুঁদ হয়ে কল্লোলিনী পারিপার্শ্বের সঙ্গে খেই হারিয়ে ফেলা মন্টু আর ভদ্রলোকটি সর্বহারী নীরবতায় সম্মোহিত। অথচ এই ‘অপর’ মানুষগুলোর বাঁচার সাড়ে তিন হাত জায়গা সংসারে সংকুলান হয় না। ফলে তাঁদের এই শূন্যতার পিছনে নিঃসঙ্গ ধাবমান হওয়াই ভবিতব্য। আশ্চর্য গল্প এই ‘সমাহিত’। ওদিকে ‘সেকেলে বুড়ী’ গল্প পড়তে বসলে দীক্ষিত পাঠকের স্মরণরেখায় সোমেন চন্দের ‘সত্যবতীর বিদায়’ গল্পের প্লট ভেসে উঠতেই পারে। এই গল্পের নদোন ঠাকরুনকে অনুভব করতে গেলে একটা পিরিওডিক্যাল ডিটাচমেন্ট লাগবেই। একই অনুভব নিয়ে বসতে হবে ‘আত্মহত্যা’ গল্পটির সঙ্গেও। বার্নার্ড মার্চল্যান্ডের এজ অফ অ্যালিয়েনেশন-এর সঙ্গে যে পাঠকের পরিচিতি আছে, তিনি নরহরির মনে সিঁধ কাটতে পারবেন। কিন্তু তার পরেও গল্পটা রয়ে যাবে আপাদমস্তক এক প্রেমের গল্প হয়ে।
বড় বিচিত্র সংগ্রহ এই বইটিতে এক জায়গায় করেছেন প্রকাশক। শুধু অবগাহনের গল্প নয়, ‘সিংহ শিকারে বিপদ’-এর মতো নিখাদ গল্পবাজির গল্পও এই সংগ্রহে আছে। তবে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। গভীরতার প্রত্যাশাই অধিক। ‘ময়নাডির ছাতা পরব’ দীর্ঘগল্পে পাঠক যখন পড়বেন ‘সকল সময়ই তাঁর মনে হয়েছে মুখটির পিছনে খাড়া শহর রয়েছে’ বা ‘এইরূপ বাক্যালাপ বিকেলের শেষ রোদ পেয়েছিল, এখন হিমসিক্ত’ ধরনের চূর্ণ কবিতা আশ্লিষ্ট পঙক্তি, তখন কি তাঁর মনে হবে না কমলকুমারের গল্পের ভাষা নিয়েই কয়েকটা সন্ধ্যে প্রতর্ক আর পরিপ্রশ্নে অতিক্রম করা যায়! ‘বাগান লেখা’ পড়লে মনে হতে বাধ্য শুধু বাংলা গল্পের লিখন শৈলী নিয়ে একটা গবেষণা করলে এই গল্পটা দিয়ে তার একটা অধ্যায় রচনা করা যাবে। অসমাপ্ত গল্পের নমুনা আর সোমনাথ দাশগুপ্ত লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘পরিশিষ্ট’ অংশ এই সংগ্রহের সম্পদ বললে ভুল উচ্চারণ হবে না। মূলানুসারী রাখার জন্যেই কমলকুমারের পত্রিকায় ছাপা বানান সংগ্রাহকরা অপরিবর্তিত রেখেছেন। যে দাবি থেকে এখন ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণের বাজার তৈরি হচ্ছে, সেই একই দাবির খোরাক এমন নিষ্ঠাবান সংগ্রহ অনেকখানি মেটাতে পারবে। পাঠকের উপরি পাওনা গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট কমলকুমারের খান ষোল পিক্টোরাল ইলাসট্রেশনের সযত্ন সংগ্রহ। রাজীব দত্তের করা প্রচ্ছদটিও ছিমছাম। এত নিটোল সংগ্রহেও যেটা অভাব, সেটা হল সুচারু সম্পাদনার। হ্যাঁ, সুচারু সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে এমন সুদক্ষ সংগ্রহও। অনেক প্রশ্ন সম্পাদকের নিষ্ঠার দাবি নিয়ে অপেক্ষা করে আছে এই সংগ্রহে। সেই সুযোগও রয়েছে। কারণ গল্পকার কমলকুমার পূর্ণ আবিষ্কৃত, এমন দাবি তো আর এই গ্রন্থের সংকলকরা করছেন না! জেমস্ জয়েসের ‘ইউলিসিস’ বইটার লেওপোল্ড ব্লুম ডাবলিনের পথে হেঁটেছিল। ক্রমে হাঁটতেই থাকে সে। কিছু কিছু খোঁজ শেষ হওয়ার নয়। কমলকুমার মজুমদারের এই গল্পসংগ্রহটাও তেমন। দীক্ষিত পাঠককে অভিযানে উসকে দেয়।
অগ্রন্থিত গল্প সংগ্রহ
কমলকুমার মজুমদার
ব্রেনফিভার
৬০০
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
