
‘অর্বিটাল’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত এক মহাকাশযানের ছয় মহাকাশচারী। চারজন এসেছে আমেরিকা, ইতালি, ব্রিটেন এবং জাপান থেকে, বাকি দু’জন– অ্যান্টন আর রোমান, রাশিয়ান। এদের মধ্যে দু’জন মহিলা– চিএ এবং নেল। প্রথম থেকেই বোঝা যায়, এ উপন্যাসে পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা থাকলেও তা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেখা হয়নি, বিশ্ব-রাজনীতি এখানে পার্শ্বচরিত্র। খর্ব রাজনীতির কাটাকুটির ঊর্ধ্বে গিয়ে মহাকাশযান হয়ে উঠেছে এক হারানো পৃথিবীর আশ্রয়বৃত্ত, যেখানে কোনও দেশের মানুষ অন্য কারও থেকে বেশি গুরুত্বের নয়।

আজ অবধি সবচেয়ে ছোট যে উপন্যাসগুলো বুকার পেয়েছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রইল ব্রিটিশ সাহিত্যিক সামান্থা হার্ভ-এর লেখা এবারের বুকারবিজয়ী উপন্যাস ‘অর্বিটাল’। ১৯৭৯ সালে বুকার পেয়েছিল পেনেলপি ফিটজেরাল্ড-এর উপন্যাস ‘অফসোর’। এখনও অবধি সেটিই ক্ষুদ্রতম। এবারের বিচারকদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ছোট আকারের উপন্যাসকে পুরস্কার দিয়ে এই ব্যস্ত পৃথিবীতে যে ‘অণু’-সাহিত্য’ই ভবিতব্য, বুকার কি তবে সেদিকেই ইঙ্গিত করছে? এর স্পষ্ট উত্তর ছিল, ‘না।’ উপন্যাসের আকারের সঙ্গে তার গুণের মূল্যায়নের কোনও সম্পর্ক নেই। সামান্থার যা বলার ছিল, তা ওই ১৪৪ পাতাতেই বলা হয়ে গিয়েছে। এর বেশি প্রয়োজন ছিল না। উপন্যাস পড়লেই বুঝতে পারা যায় লেখিকার ভাষার দক্ষতা কতখানি! শুধু মহাকাশচারীরাই নয়, পাঠকও যেন ভাষাশকটে চড়ে মহাকাশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কয়েক পাতা পড়তে পড়তেই বোঝা যায়, এ ভ্রমণ ‘থ্রিল রাইড’ নয়, বরং এ সেই নীড়মুখী পাখির উদাস দৃষ্টি, যে-বাচ্চাদের বাসায় রেখে দূরে খাবার আনতে গিয়েছিল; ফেরার পথে দূর থেকেই বুঝতে পারে, কালবৈশাখী ঝড়ে সে তার সব হারিয়েছে। এ ভাষা-কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ মহাকাশযানের মতোই পাক খেতে খেতে কুণ্ডলিত হতে থাকে। কোনও ‘হলিউডি সাইন্স ফিকশন’ সিনেমার সঙ্গে এর তুলনা হয় না, এমনকী, এ স্তানিসলাভ লেম-এর ‘সোলারিস’ও নয়। মাধ্যাকর্ষণহীন, দিনরাত গোলমাল হয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড গতিশীল এক বস্তুপিণ্ডে আবদ্ধ মানুষের রোজনামচা ধরতে পারে, এমন ভাষা সহজে মেলে না। সামান্থা নিজের জীবন নিংড়ে সে ভাষা আবিষ্কার করেছেন। এর আগে যে চারটে উপন্যাস লিখেছেন, তার মধ্যে ‘The Shapeless Uneasy: My years in search of sleep’ এই উপন্যাসের সঙ্গে হয়তো খানিক তুলনা করা চলে। বুকারের লং লিস্টে ছিল সে বই। The Shapeless Uneasy লেখিকার ইনসোমনিয়ার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে লেখা। সেই বইয়ে নিদ্রাহীনতা, ঘুম, মৃত্যু– এসব নিয়ে এক অদ্ভুত কুহকী গদ্য রচনা করেছিলেন। বইয়ের শুরুতেই লিখেছিলেন, সেটা উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প এসব কিছুই নয়। অর্বিটাল-ও খানিকটা সেই গোত্রের। উপন্যাসের মতো এর তেমন কোনও নিটোল প্লট নেই, ছেঁড়াছেঁড়া ভাবনাচিন্তার টুকরো। আগে শুরু করে রেখে দেওয়া এই বই আবার লিখতে শুরু করেছিলেন প্যান্ডেমিকের গৃহবন্দি অবস্থায়, ঘরে বসে। এ উপন্যাস দেখায় স্পেসক্রাফ্ট আর বদ্ধ ঘরের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই।

‘অর্বিটাল’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত এক মহাকাশযানের ছয় মহাকাশচারী। চারজন এসেছে আমেরিকা, ইতালি, ব্রিটেন এবং জাপান থেকে, বাকি দু’জন– অ্যান্টন আর রোমান, রাশিয়ান। এদের মধ্যে দু’জন মহিলা– চিএ এবং নেল। প্রথম থেকেই বোঝা যায়, এ উপন্যাসে পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা থাকলেও তা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেখা হয়নি, বিশ্ব-রাজনীতি এখানে পার্শ্বচরিত্র। খর্ব রাজনীতির কাটাকুটির ঊর্ধ্বে গিয়ে মহাকাশযান হয়ে উঠেছে এক হারানো পৃথিবীর আশ্রয়বৃত্ত, যেখানে কোনও দেশের মানুষ অন্য কারও থেকে বেশি গুরুত্বের নয়।
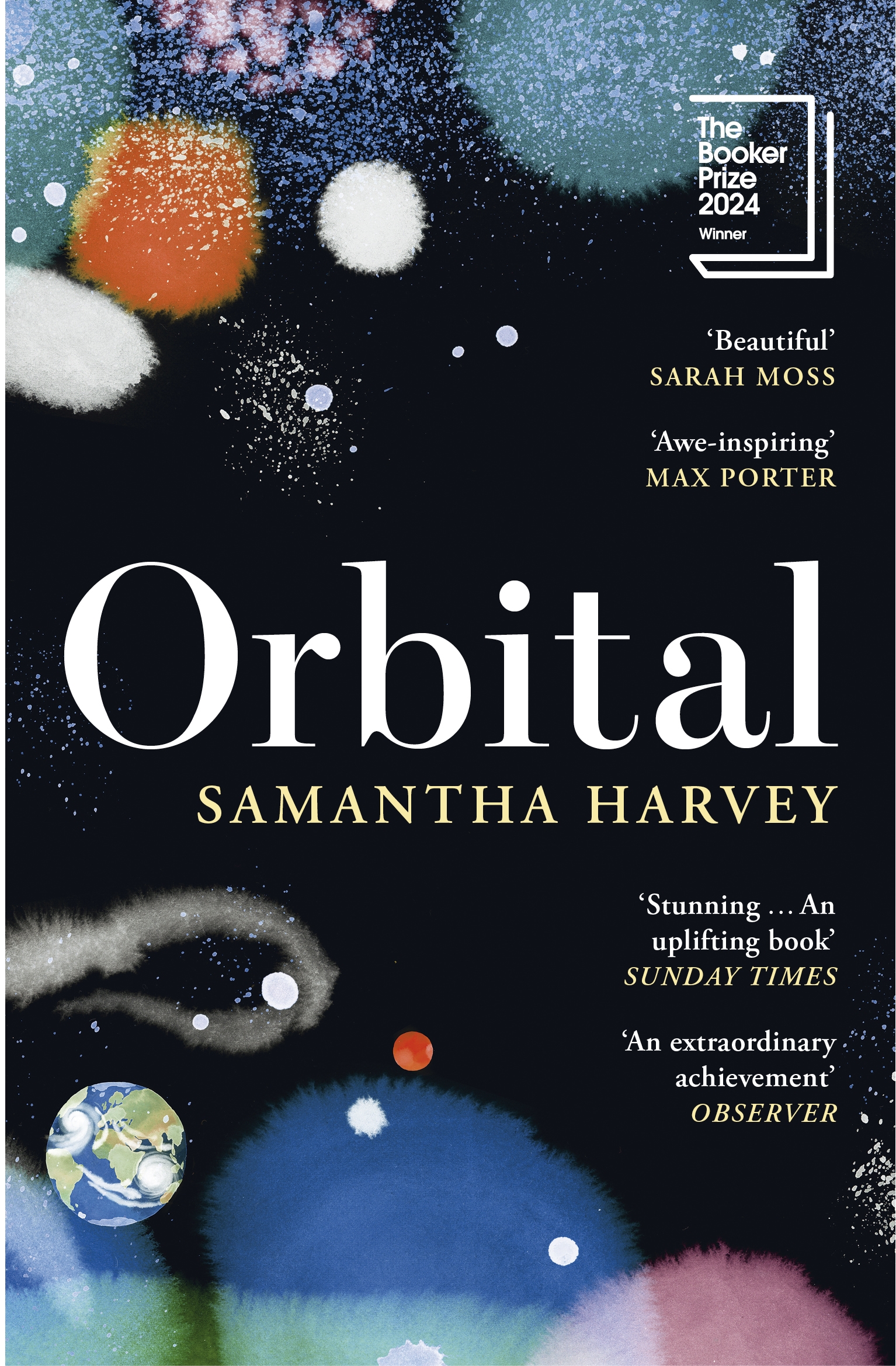
এই মহাকাশযানের প্রত্যেক চরিত্রই প্রয়োজনীয়। লেখিকার ভাষায়, তারা একই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ– অ্যান্টন সিনেমা দেখে, বাইরের দৃশ্য দেখে কাঁদে, একটু আবেগী, তাই সে এই মহাকাশযানের হৃদয়; পিয়েত্রো হল-এর মগজ, রোমান এই স্পেসশিপের বর্তমান কমান্ডার– রোবোটিক্সে দুর্দান্ত, তাই সে এই শরীরের হাত, শন যেহেতু নিজে আত্মায় বিশ্বাস করে আর লোককেও বিশ্বাস করাতে চায়, সে এই মহাকাশযানের আত্মা; চিএ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও নিয়মনিষ্ঠ, তাকে কোনও ছকে ফেলা যায় না, সে এর বিবেক। নেল যেহেতু প্রচুর দম ধরে রাখতে পারে, সে এর শ্বাসবায়ু। অভিযানের মেয়াদ ন’মাস। উপন্যাসের বিস্তার গোটা একটা দিন। মহাকাশযানটি একদিনে পৃথিবীকে ১৬ বার প্রদক্ষিণ করে, ১৬টা সূর্যোদয় এবং ১৬টা সূর্যাস্ত দেখে। উপন্যাসের চ্যাপ্টারগুলো সেভাবেই বিন্যস্ত। এই স্পেসক্রাফটে মহাকাশচারীদের প্রাথমিক কাজ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। চিএ-এর কাজ মানুষের মস্তিষ্কে মাইক্রোগ্র্যাভিটির কী প্রভাব পড়ে তা দেখা, সে নেলের সঙ্গে ৪০টা ল্যাবের ইঁদুরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে– নজর রাখছে মহাকাশে এদের পেশির পরিবর্তনের খুঁটিনাটির তথ্যে; শন-এর কাজ সূর্যের আলো-বাতাস না পেলে গাছের শিকড়ে কী পরিবর্তন হয়, তা পরীক্ষা করা; পিয়েত্রোর কাজ মহাকাশযানের ফাঙ্গাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস নিয়ে; রোমান আর অ্যান্টন হার্টসেল, বাঁধাকপি, একটা বিশেষ প্রজাতির গম মহাকাশে এবং রাশিয়ান অক্সিজেন জেনারেটর নিয়ে কাজ করে। এছাড়াও তাদের বিভিন্ন দরকারে মাঝে মাঝে স্পেসক্রাফটের বাইরে বেরতে হয়। বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ। প্রত্যেক দেশের জন্য আলাদা আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা। রাশিয়ার শৌচাগারের দরজায় লেখা: RUSSIAN COSMONAUTS ONLY, আমেরিকার দরজায় লেখা AMERICAN, EUROPEAN AND JAPANESE ATRONAUTS ONLY. মহাকাশে গিয়ে ইংরেজি প্রতিশব্দ চয়নেও লুকিয়ে থাকে রাজনীতি। রাশিয়ায় যা কস্মোনট এবং বাকি দেশে তা ‘অ্যাস্ট্রোনট’। দরজায় সাঁটানো আছে সতর্কবার্তা, ‘Because of ongoing political disputes please use your own national toilet.’ এ হাস্যকর ব্যবস্থায় শন ফুট কাটে, ‘যাই, আমি জাতীয় পেচ্ছাপ করে করে আসি।’
সামান্থা লেখেন, ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা যেমন শুধু ভবিষ্যৎ দেখতেই পারে, তাকে পাল্টাতে পারে না, তেমনই এই মহাকাশচারীরাও, প্রচণ্ড গর্জনে স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসা টাইফুনকে দূর থেকে নজরদারিই করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মহাকাশচারীরা যান্ত্রিক মনিটরে কয়েক হাজার মাইল দূরত্বে বসে ঝড়ের গতিবিধি লক্ষ করে। পৃথিবী থেকে বহু বহু দূরের সেই মহাকাশযানের ভেতরটা নিস্পন্দ, নিরুপদ্রব। সেখানে টাইফুন শুধু কিছু বিন্দুসংকেত মাত্র। স্থলভাগে আছড়ে পড়া ঝড়ের কিছুই সেখানে টের পাওয়া যায় না। মহাকাশযান যেন বিধাতার চোখ। নিঃসঙ্গ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখার মধ্যে যে প্রগাঢ় ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা আছে, তার বিবরণ এই উপন্যাসের এক বড় সম্পদ। চিএ-এর মা যখন মারা যায় সুদূর জাপানে, তখন সে মহাকাশযানে পৃথিবীকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। খবর পেলেও দূরের নীল গ্রহটার দিকে বিষণ্ণ মনে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কাছে কোনও উপায় থাকে না। ন’মাসের সফর সেরে সে যখন বাড়ি ফিরবে, ততদিনে সব ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়ে যাবে। তার বাবা মারা গিয়েছে বহু বছর আগে। মা মারা যেতে সে এবার অনাথ বোধ করে। মহাকাশে একমাত্র প্রাণ বিশিষ্ট অনাথ পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে মহাকাশে অনাথ হতে কেমন লাগে, লেখিকা তার কয়েক পাতা জুড়ে অলৌকিক বিবৃতি দিয়েছেন। বিপুল গতিবেগে ঘুরে চলা ওই নীল গ্রহতে নিয়মিত দিন-রাত, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত হয়ে চলেছে। শন যেহেতু ঈশ্বরবিশ্বাসী, সে সকলের জন্য প্রার্থনা করে, চিএ-এর মায়ের আত্মার শান্তি কামনা করে, সে চোখ বন্ধ করলেও উল্লুকের ডাক শুনতে পায়, যেন ঘোড়ার গলায় হাত বোলানোর আরাম বোধ করে, জলের নীচে যেন দেখতে পায় পাইক মাছের ছায়া, ঝোপের মধ্যে লাফ দেয় খরগোশ– পৃথিবীর সব প্রাণীকেই তার মনে পড়ে। এ জায়গাটা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের ‘গুপ্তধন’ গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের কথাই মনে পড়ে, রাশি রাশি সোনার মধ্যে বসেও যখন তার কাছে গ্রামের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। এমনকী, ভোলা কুকুরটা যে লেজ গুটিয়ে উঠোনের কোণে শুয়ে থাকত, সে-ও কল্পনায় জ্বলজ্বল করে। সামান্থাও উপন্যাসে বড় মনকেমনিয়া ভাষায় পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। মহাকাশ থেকে মহাদেশগুলো মেঘের ফাঁক পেরিয়ে দেখা যায়, কিন্তু সেখান থেকে রাষ্ট্রের বানানো কাঁটাতারের বেড়া চোখে পড়ে না। স্পেসক্রাফটের মধ্যে থেকে চিএ আকুতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে নীল গ্রহটার দিকে, যেখানে তার মা পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল, যখন তার মায়ের পরিবারের বাকিরা কালো বাষ্প আর ছায়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর বহু বসন্ত পেরিয়ে সে যে আজ এত বড় অভিযানের অংশ হতে পেরেছে, সে তার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া শিক্ষা। এরকম আরও কত অজস্র বিষণ্ণ চিন্তা কাটাকুটি খেলে তার মনে। স্পেসক্রাফটে আটকে থাকা চিএ-র মাকে শেষ বিদায় না জানাতে পারা আর প্যান্ডেমিকে প্লাস্টিকে মুড়ে পরিচিত আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য বোধহয় কার্যত এক। ইংল্যান্ডে যেমন ‘ব্ল্যাক ডেথ’ বহু মহৎ শিল্পের জন্ম দিয়েছে, তেমনই এই উপন্যাস পড়তে পড়তে বহু দৃশ্যে থমকে দাঁড়াতে হয়। মহৎ উপন্যাসের যে যে লক্ষণ এ উপন্যাস শরীরে বহন করছে, তাতে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, পৃথিবীর গভীর অসুখই এমন সব আশ্চর্য উপন্যাস লিখিয়ে নেয়।

নেলের স্বামীর সঙ্গে ছ’বছরের সম্পর্কে, তাদের বিয়ের বয়সই পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছর কেটেছে অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার ট্রেনিংয়ে। সেই চার বছরে কয়েকমাস মাত্র সে সময় পেয়েছে স্বামীর সঙ্গে থাকার, তারও এক-তৃতীয়াংশের কম সময় সে কাটাতে পেরেছে তার স্বামীর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আয়ারল্যান্ডের ভিটেয়। তার স্বামী স্বেচ্ছায় গ্রাম্য জীবন বেছে নিয়েছে। তার বক্তব্য, একলা জীবনই যদি কাটাতে হয় তো ঘিঞ্জি শহর থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে মেষপালকের জীবনই ভালো। তারা পরস্পরকে ছবি পাঠায়। তার স্বামী তাকে পাঠায় সূর্যাস্ত, বেড়া, ফুল, সূচালো হয়ে জমে থাকা বরফ, ভেড়ার কানের ছবি, সে পাঠায় মহাকাশ থেকে তোলা বাড়ির ছবি। আয়ারল্যান্ড দ্বীপটা বেশিরভাগ সময় অর্ধেকের বেশি মেঘেই ঢেকে থাকে। তার স্বামী প্রতিনিয়ত স্ত্রীয়ের অবস্থানের নিঁখুত হিসেব পায়। শুধু সে একা নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষই ইচ্ছামতো দেখে নিতে পারে সেই স্পেসক্রাফটের গতিবিধি। যার প্রতি সেকেন্ড মাইক্রোসেকেন্ডের অবস্থানের নজরদারি চলছে পৃথিবী থেকে। তার স্বামীর গতিবিধি বরং অনেক অস্পষ্ট, নাগালের বাইরে। তার স্বামী একটা ছবি পাঠিয়েছিল, সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে নিজের ছায়াবয়ব (ছবিটা তুলে দিল কে?)… নেল স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, কে কার কাছে বেশি অজ্ঞাত? তার স্বামীর উত্তর ছিল, দু’জনে ভিন্নরকমের কিন্তু একইভাবে অজ্ঞাত। তোমার মাথা ভর্তি গুচ্ছের ভারী ভারী বৈজ্ঞানিক শব্দে আর আমার মাথা ভর্তি ভেড়াদের গুচ্ছের রোগজ্বালার নামে। দু’জনেই দু’জনের কাছে একইরকম অপরিচিত।
……………………………………
শনের স্ত্রী প্রথম আলাপে তাকে এক পোস্টকার্ড দিয়েছিল। সেখানে আঁকা ছিল দিয়েগো ভেলাস্কাসের বিখ্যাত ছবি ‘লাস মেনিনাস’। ছবিতে শিল্পী ভেলাস্কাস নিজেই উপস্থিত। তিনি ছবি আঁকছেন। কার ছবি আঁকছেন? রাজারানীর ছবি। রাজারানী ছবিতে নেই, তাহলে কীভাবে বোঝা গেল তাঁদের ছবি আঁকছেন শিল্পী? কারণ পিছনের আয়নায় তাদের মুখ প্রতিফলিত হচ্ছে। শিল্পী কিন্তু আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছবি আঁকছেন। ছবির বাকিরাও আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রাজকন্যা সাদা পোশাক পরে। তার চারপাশে দাঁড়িয়ে অন্তঃপুরবাসিনীরা, রাজকুমারীকে দেখভালের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত।
……………………………………
নেল মাঝে মাঝে ভাবে শনকে জিজ্ঞেস করবে, অ্যাস্ট্রোনট হয়েও শন কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। নেল জানে, শন কী উত্তর দেবে– অ্যাস্ট্রোনট হয়েও কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে কীভাবে থাকতে পারে! একদিকে ঈশ্বরভাবনা আর অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর ধনকুবেরদের ঈশ্বর হওয়ার বাসনা, এই দুইয়ের বাদ-বিবাদ-সংবাদ চলতে থাকে সমান্তরালে। শন ভাবে, মানুষের উপনিবেশবাদ আর আধিপত্যকামিতা এখনও কমেনি। নিজের গ্রহ ছেড়ে এবার অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন করা চাই তার। শনের স্ত্রী প্রথম আলাপে তাকে এক পোস্টকার্ড দিয়েছিল। সেখানে আঁকা ছিল দিয়েগো ভেলাস্কাসের বিখ্যাত ছবি ‘লাস মেনিনাস’। ছবিতে শিল্পী ভেলাস্কাস নিজেই উপস্থিত। তিনি ছবি আঁকছেন। কার ছবি আঁকছেন? রাজারানীর ছবি। রাজারানী ছবিতে নেই, তাহলে কীভাবে বোঝা গেল তাঁদের ছবি আঁকছেন শিল্পী? কারণ পিছনের আয়নায় তাদের মুখ প্রতিফলিত হচ্ছে। শিল্পী কিন্তু আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছবি আঁকছেন। ছবির বাকিরাও আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রাজকন্যা সাদা পোশাক পরে। তার চারপাশে দাঁড়িয়ে অন্তঃপুরবাসিনীরা, রাজকুমারীকে দেখভালের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত। এদের বলা হয় ‘lady-in-waiting’. ‘লাস মেনিনাস’ শব্দের অর্থ তাই। এবার প্রশ্ন, ছবির মুখ্য চরিত্র তাহলে কে? নিশ্চয়ই রাজারানী? তাঁরা অভিজাত, তাঁদেরই ছবি আঁকা হচ্ছে! কিন্তু তাঁরাই তো ছবিতে নেই। আবার ছবির নাম কিন্তু লাস মেনিনাস, কিন্তু সেটা হলেও তাদের ছবি তাহলে কেন আঁকা হচ্ছে না? গোটা উপন্যাসের উত্তর লুকিয়ে আছে এই ছবিতে। নেলের স্বামীর সূর্যাস্তের সময় তোলা ফোটোগ্রাফ কে তুলে দিল? এই মহাবিশ্বে আসলে কে কাকে দেখছে? মহাকাশচারীরা তো পৃথিবীকে দেখছে, কিন্তু তাদের অবস্থানের গতিবিধিও যে নিয়ন্ত্রিত পৃথিবী থেকে।
এ উপন্যাস আসলে ভেলাস্কাসের ছবির আয়না, মহাকাশ থেকে কক্ষচ্যুত মানুষের মুখে তা আলো ফেলে। অথবা, এক দীর্ঘ প্রেমপত্র। অনেকটা ভালোবাসা থাকলেই পৃথিবীর গভীর অসুখের এভাবে রোগনির্ণয় করা সম্ভব।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
