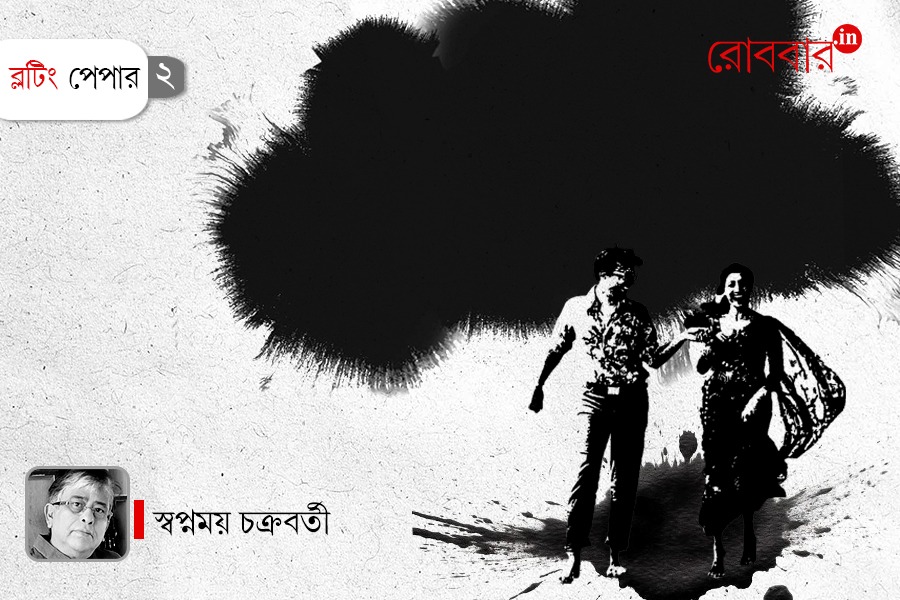
ফাউন্টেন পেন আসা সত্ত্বেও আমার পিতামহ হ্যান্ডেলের কলমেই লিখতেন এবং সেই অক্ষরগুলি আশ্চর্যভাবে ভালো বিরিয়ানি চালের মতো গোটা গোটা থাকত। তাঁর লেখা কয়েকটি হিসেবের খাতা এবং ডায়রির পাতা আমার কাছে যত্নে রাখা আছে। কাগজ ভেঙে যাচ্ছে, অথচ লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে। যে কালিতে লেখা হত, সেসব ছিল কালির বড়ি বা ট্যাবলেট। জলে গুলে কালি তৈরি করতে হত। মুদি দোকানে বা বই খাতার দোকানে কালির বড়ি কিনতে পাওয়া যেত।
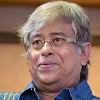
২.
হ্যান্ডেলের কলমে আমিও লিখেছি। একটা কাঠের তৈরি চার থেকে ছ’-ইঞ্চি লম্বা কলমের ডগায় নিব ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। দোয়াতে কালি ডুবিয়ে লিখতে হত। একবার ডোবালে ছ’-সাতটা শব্দ লেখা যেত। কখনও বা ঝপ করে কালি খসে যেত নিব থেকে। ব্লটিং পেপার রাখতে হত সঙ্গে। কালি শুষে নিত ব্লটিং পেপার। নিবগুলো ছিল পিতলের তৈরি। ধনী মানুষেরা সোনার নিব ব্যবহার করতেন। সোনা সহজে ক্ষয় হয় না, তাই বহু দিন একইরকম থাকে। জল বা বাতাসেও ক্ষতি হয় না। পেতলের নিবে সোনার টিপ বসানো নিবও পাওয়া যেত। স্লেট-পেনসিল ছাড়ার পর পেনসিলে লিখতাম। যখন ফাইভ বা সিক্সে উঠেছি, তখন ফাউন্টেন পেনে লেখার অধিকার পেলাম। ‘রাইটার’ পেন। ওটা তোলা জমা প্যান্টের মতো তোলা পেন। বাড়িতে লেখালেখির কাজ পেনসিল বা হ্যান্ডেল কলমেই করতাম, পরীক্ষার সময় ফাউন্টেন পেন নিয়ে যেতাম। ফাউন্টেন পেনের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন ছিল পাইলট পেন। একটা ছড়া বাজারে চলত।
‘নাইলন শাড়ি পাইলট পেন
উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন।’
ফাউন্টেন পেন আসা সত্ত্বেও আমার পিতামহ হ্যান্ডেলের কলমেই লিখতেন এবং সেই অক্ষরগুলি আশ্চর্যভাবে ভালো বিরিয়ানি চালের মতো গোটা গোটা থাকত। তাঁর লেখা কয়েকটি হিসেবের খাতা এবং ডায়রির পাতা আমার কাছে যত্নে রাখা আছে। কাগজ ভেঙে যাচ্ছে, অথচ লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে। যে কালিতে লেখা হত, সেসব ছিল কালির বড়ি বা ট্যাবলেট। জলে গুলে কালি তৈরি করতে হত। মুদি দোকানে বা বই খাতার দোকানে কালির বড়ি কিনতে পাওয়া যেত। পি.এম. বাগচির কালির বড়ি আর জে.বি. বড়ি কিনতে পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, সেই বাড়ির একতলায় একটা কালির কারখানা ছিল। সেই কালির নাম ছিল রাজা, স্বস্তিকা, আর পেন। কিন্তু রাজা কালি কলকাতার দোকানে পাওয়া যেত না। পি.এম বাগচি আর জে.বি. এদিকের বাজার দখল করে রেখেছিল। আর রাজা, স্বস্তিকা– এইসব কালির বড়ি চলে যেত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অসম, এমনকী, বার্মা মুলুকেও। এই কালির কারখানার মালিক ছিলেন আমার পিসেমশাই জাহ্নবীজীবন চক্রবর্তী। তাঁর পিতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বদেশি শিল্প তৈরির আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে কালির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। পি.এম বাগচিও তাই। তার আগে বিলেত থেকে কালির বড়ি আসত।
……………………………………
একটা বড়ি এক পয়সা, বড় দোয়াতে দুটো বড়ি লাগত এবং এক দোয়াত কালিতে অনায়াসে একমাস চলে যেত। কারখানায় পরপর তিন-চার দিন কালো কালি তৈরি হলে পাড়ার কাকেরা সব্বাই কালো পটি করত। লাল হলে লাল। কারণ মণ্ডটা তৈরি হত আলুর গুঁড়ো দিয়ে। রংটা নিশ্চয়ই বিষাক্ত ছিল না, কাকেরা আলুমাখা খেত এন্তার, আলুটা হজম করত, রংটা বর্জন করত। আর বর্ষাকালে একটা দর্শনীয় ব্যাপার হত। ছাদ থেকে রেন পাইপ যে জল পড়ত, সেই জল ছিল রঙিন। কখনও সবুজ, কখনও নীল, কখনও কালো। কী রঙের মণ্ড ছাদে শুকনো হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করত।
……………………………………
কাগজ প্রচলিত হওয়ার আগে তালপাতায় লেখা হত পুথি। তালপাতা মাপ মতো কেটে তুঁতে আর নিমপাতা সেদ্ধ করা জলে ভিজিয়ে, শুকিয়ে পৃষ্ঠা তৈরি করা হত। তার ওপর পাখির পালক কেটে তীক্ষ্ণ করে, কিংবা তামা/রুপো/সোনার নিব তৈরি করে কাঠের বা মোষের শিংয়ের বা হাতির দাঁতের কলমে লাগিয়ে কালিতে ডুবিয়ে পাখায় লিখতে হত। একটা পাতায় ছ’টি বা আটটি লাই ঢুকত। মানে প্রতি পাতায় একশোটার মতো শব্দ থাকত। এরকম ৪০-৫০টি পাতার একটা বান্ডিল তৈরি হত। একে বলে পটল। এক পটল শেষ হয়ে গেলে লেখা হত ‘ইতি প্রথম পটলম সমাপ্তম’। সমস্ত পটল পড়া শেষ হয়ে গেলে ব্যাগে পটলগুলি তুলে ফেলতে হত। শেষ হয়ে গেলে পটল তোলা হত। কালক্রমে মৃত্যুকে লঘুবাচনে ‘পটল তোলা’ বলা হয়। এইসব পুথি লেখার কালি তৈরি করতে হত ঘরে। নানারকম পদ্ধতি ছিল, তার দু’-একটি বলছি।
তিল ত্রিফলা বকুলের ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
তাহাতে হরিতকি ঘষি
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।

মানে তো বোঝাই যাচ্ছে। এমন কালি হবে যে পাতা ছিঁড়ে যাবে, কিন্তু কালি বিবর্ণ হবে না।
কিংবা,
কল কাষ্ঠ ভস্ম
যবচূর্ণ তস্য সিকি
তার অর্ধ্ব বাবলার আঠা
কালি বানা বামুনের ব্যাটা
পোড়া কুল কাঠের মিহি গুঁড়ো, মানে কার্বন পাউডারের চারভাগের একভাগ যবের গুঁড়ো মিশিয়ে, সামান্য আঠা মিশিয়ে জলে ফুটিয়ে কালো কালি বানানো যায়।
সম্ভবত এই লোকায়ত ফরমুলা গ্রহণ করেছিল আমাদের দেশীয় কালি প্রস্তুতকারকরা। রসায়নের ছাত্র হিসাবে যেটা বুঝেছি, রঞ্জক পদার্থকে কাগজে ধরানোর জন্য সূক্ষ্ম ফিল্ম তৈরি করতে হবে। এ জন্য একটা কার্বোহাইড্রেট চাই, এবং একটা বাইন্ডার চাই। আমার বাল্যকালের কালির কারখানাটি স্মৃতিতে এরকম। বস্তা বস্তা সাদা সাদা গুঁড়ো গুদামে আছে। কারখানার উঠোনে ত্রিপল পেতে সেই সাদাগুঁড়ো ঢালা হল। একটা ড্রামে রং গোলা হয়েছে। ধরা যাক, নীল রং, মগে মগে ঘন নীল রং ঢালা হচ্ছে ওই সাদা গুঁড়োয়। সাদা গুঁড়োগুলো আসলে ডেক্স্ট্রিন। মানে আলুর গুঁড়ো। কানাডা থেকে আসতে। সব রঙিন মণ্ড হত। ঠিক রুটি তৈরির আটার মণ্ডর মতোই। তারপর সেসব ছাদে নিয়ে গিয়ে শুকোতে হত। শুকিয়ে গেলে মুগুর দিয়ে ভাঙা হত। তারপর সেই ভাঙা শুকনো মণ্ডগুলো একটা মেশিনে ঢুকিয়ে চূর্ণ করে ফেলা হত, তারপর অন্য মেশিনে দিয়ে ট্যাবলেট তৈরি করে টিনের কৌটোয় ভরে ফেলা হত। মুদি দোকানগুলো ডিলারের কাছ থেকে কৌটো হিসেবে কিনত এবং খুচরো বিক্রি করত।
একটা বড়ি এক পয়সা, বড় দোয়াতে দুটো বড়ি লাগত এবং এক দোয়াত কালিতে অনায়াসে একমাস চলে যেত। কারখানায় পরপর তিন-চার দিন কালো কালি তৈরি হলে পাড়ার কাকেরা সব্বাই কালো পটি করত। লাল হলে লাল। কারণ মণ্ডটা তৈরি হত আলুর গুঁড়ো দিয়ে। রংটা নিশ্চয়ই বিষাক্ত ছিল না, কাকেরা আলুমাখা খেত এন্তার, আলুটা হজম করত, রংটা বর্জন করত। আর বর্ষাকালে একটা দর্শনীয় ব্যাপার হত। ছাদ থেকে রেন পাইপ যে জল পড়ত, সেই জল ছিল রঙিন। কখনও সবুজ, কখনও নীল, কখনও কালো। কী রঙের মণ্ড ছাদে শুকনো হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করত। আমরা জামা শুকতে দিতাম বারান্দার রেলিংয়ে, আমাদের কাপড় জামায় সূক্ষ্ম কালির রেণুর চিহ্ন লেগে থাকত।
এ নিয়ে কখনও কাউকে অভিযোগ করতে দেখিনি। ভাবখানা যেন কালির কারখানাটা থাকলে এমন তো হবেই। কালি না হলে লেখাপড়া শেখা হবে কী করে?
পাড়ার স্কুলে কিছুকাল পড়ার পর আমাকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ওখানে বেঞ্চির পরিবর্তে ডেস্ক ছিল। ডেস্কের এককোণে একটা গর্ত থাকত, এবং সেই গর্তে ঢোকানো থাকত একটা চিনামাটির ছোট পাত্র। সেটা ছিল দোয়াত। স্কুলের পিওনরা হয়তো ওই দোয়াতে কালি ভরে রাখতেন, ওইসব দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখে গেছেন রামতণু লাহিড়ী, রমেশ মিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা। ডেস্কগুলি ছিল সেগুন কাঠের তৈরি। শতাধিক বছরের পুরনো। কালি রাখার খোঁদলে পোকামাকড় বাসা বাঁধতে পারে বলে এক সময় ওগুলো প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হল।
আমার পিতামহ প্রয়াত হন ১৯৭২ সালে, তখন আমার ২০ বছর বয়স। কালির বড়ির যুগ শেষ হয়ে গেছে ছয়ের দশকেই, কিন্তু আমার পিতামহ ফাউন্টেন পেনে লিখতেন না। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। বলতেন দোয়াতে কলম ডুববে না-সেটা কি কোনও লেখা না কি? ওঁর মতো আরও অনেকেই ছিলেন নিশ্চয়ই সারা দেশে। হয়তো ফাউন্টেন পেনও সারা দেশে পৌঁছয়নি। হয়তো অনেকেই দেড় টাকা-দু’টাকা দিয়ে ফাউন্টেন পেন কিনতে পারতেন না, যেখানে নিব সমেত একটা ভালো হ্যান্ডেল কলমের দাম দশ বারো আনা, সে কারণে ওই কালির কারখানাটা ’৮০/’৮২ সাল পর্যন্ত টিকেও ছিল। কালির বড়ি তৈরি হত। এরপর একসময় বন্ধ হয়ে যায়। ফাউন্টেন পেনের যুগে পাইলট-পার্কারের পরই সোনালি ক্যাপওলা চিনা কলম ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ম ব্লাঁ বা ক্রশ– এসব কলমের নাম শুনিনি তখন। আমি ব্যবহার করতাম রাইটার এবং ডক্টর। ডক্টর একটু দামি কলম। দু’ৃটাকা। কলমের মাথার দিকটা প্রায়শই লিক করত। কলমের প্যাঁচ খুলে ভেজলিন লাগাতাম। কিছুটা সুরাহা হত। সে যুগে সস্তার ফাউন্টেন পেনে আমরা ‘হাতে কালি মুখে কালি বাছা আমার লিখে এলি’ প্রবাদের জীবন্ত মডেল ছিলাম। কলমের প্যাঁচ খুলে কালি ভরতে হত। সুলেখা ছিল বিখ্যাত দেশি কালি। এরপর এল সুপ্রা, ক্যামেল ইত্যাদি। বিদেশি কালিও ছিল। দামি কলমের ভিতরে এমন একটা ইনবিল্ট ছোট রবার টিউব ছিল, যেটা টিপে ধরলে কলমের শরীরে কালি ঢুকে যাবে। এই ঝর্ণা কলম বা ফাউন্টেন পেনগুলোকেও খেয়ে নিল ডট পেন, বা বল পেন। বল পেন ঢুকতে শুরু করেছিল সাতের দশকের মাঝামাঝি। প্রথম দিকে পাত্তা পেত না। বল পেনে পরীক্ষা দেওয়া যেত না, ব্যাঙ্কের চেকের সই গ্রাহ্যঅ হত না। তারপর আস্তে আস্তে সামাজিক সম্মতি আদায় করে নিল। সেটা অন্য কাহিনি।
A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved
